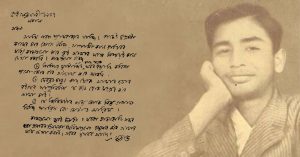পর্ব ৭
স্মৃতিতে বাবা
১৯৯১ সাল। এপ্রিলের ২৩ বা ২৪ তারিখ। ছাত্র সংগঠনের নববর্ষের অনুষ্ঠান দেখার জন্যই বাড়ি যাওয়ার তারিখ কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়া। দেশে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম। সেটা পেয়েছে কিনা জানি না। এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে এল তপু। ওদের বাসায় চলে গেলাম রাত থেকে পরের দিন মানিকগঞ্জ যাব বলে। ওখানে দেখা সাত্তার ভাই আর আরিফের সঙ্গে। সময় কাটল ভালই। পরের দিন তপু আমাকে গুলিস্তানে মানিকগঞ্জের বাসে উঠিয়ে দিল। তরা এসে যখন পৌঁছলাম বিকাল গড়িয়ে গেছে। বাসস্ট্যান্ড তখনও আগের মতই। দোকানপাট নেই বললেই চলে। শুধু আনোয়ার ভাইয়ের টি-স্টল। যতদূর মনে পড়ে উনি ছিলেন না। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রামের ছেলেরা। মস্কো যাবার আগে গ্রামে ওদের নিয়েই হিজল খেলাঘর আসর গড়েছিলাম। আজ ওদের কয়েকজন অপেক্ষা করছে। অথবা এমনিতেই এসেছিল। কে জানে? রাস্তা ক্রস করার পরেই ওরা এগিয়ে এল।
‘কাকা, ব্যাগগুলো আমাদের হাতে দিন। আমরা নিয়ে যাচ্ছি।’
কিছু বলার আগেই আমার হাতে যা যা ছিল, ওরা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। একটু অবাক হলাম, তেমন কোনও কথাবার্তা বলল না বলে।
‘জানতাম, কাকা খবর পেলেই চলে আসবে।’ ওদের কথা ভেসে এল আমার কানে। গণিত বা পদার্থবিদ্যায় পড়ার এই এক অসুবিধা, কোনও ইনফরমেশন পেলেই মাথায় সেগুলো ঘুরতে থাকে, বিভিন্ন সমাধান তৈরি হয় নিজের অজান্তেই। জানতাম বাবা অসুস্থ। তাহলে কি বাবার কিছু হয়েছে?
মনে পড়ল খোরশেদ ভাইয়ের কথা। খোরশেদ ভাই ডাক্তার। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়। খুব আদর করতেন আমাকে। ফার্স্ট মেডিক্যালের হোস্টেলে ওঁর ওখানে প্রায়ই যেতাম। বিশেষ করে ক্যামেরার কিছু কিনতে জরুরি টাকাপয়সা দরকার পড়লে ওঁর কাছে চাইতাম। বাবার অসুখের কথা বিস্তারিত আমি জানাই খোরশেদ ভাইকে। তিনি বাড়ি থেকে সমস্ত রিপোর্ট আনাতে বলেন। রিপোর্ট দেখে খোরশেদ ভাই বলবেন:
‘কবে দেশে যাবে বলে ভাবছ?’
‘এপ্রিলের মাঝামাঝি।’
‘মার্চে যাওয়া যায় না?’
‘এখানে কিছু ধারদেনা ছিল সেটা শোধ করে যেতে চাইছি। তা না হলে টেনশনে থাকব। বাবা শুনলে তাঁর টেনশনও বাড়বে।’
‘দেখো যেটা ভাল মনে করো। তবে আমার ধারণা এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।’
‘কেন? রিপোর্টে তেমন কিছু লেখা আছে?’
‘তা নেই। তবে সব দেখে আমার মনে হয় তোমার বাবা মার্চের পরে আর থাকবেন না।’
তাহলে কি বাবা সত্যি সত্যিই নেই? কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই খেলাঘরের ছেলেদের জিজ্ঞেস করলাম:
‘কী জানার কথা বলছ তোমরা?’
‘না না, আমরা এমনিতেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম।’
আমি আর কথা বাড়ালাম না। এর মধ্যে অনেকটাই বুঝে গেছি।
যেন ঘোরের মধ্যে চলছি। কীভাবে যে মন্টু, তাপসদের বাড়ি পার হয়ে নিজেদের বাড়ির পেছনে চলে এসেছি খেয়ালই করিনি। পরিচিত বাঁশঝাড় কেমন যেন অপরিচিত মনে হচ্ছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, তবুও বাড়িতে কোনও আলো নেই। এক ভূতুড়ে পরিবেশ চারিদিকে। ঘরের বারান্দায় বসে আছে রতন, দিদি, মা। বড়ঘরের বারান্দায় সুধীরদা, বউদি।
সব কিছুই বলে দিচ্ছে বাবা আর নেই। তবে কেউই কিছু বলছে না। মামা হাত-পা ধুয়ে জামাকাপড় বদলাতে বললেন। আমি যেন সেসব কিছুই শুনতে পেলাম না।
‘কবে?’
‘কী কবে?’ রতন প্রশ্ন করল।
‘বাবা কবে মারা গেলেন?’
‘তোকে এটা কে বলল?’
‘বাড়ির সব কিছুই তো সে কথাই বলছে।’
‘৩১ মার্চ।’
অনিশ্চয়তা খুব ভাল কিছু নয়। তবে কিছু কিছু নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তার চেয়েও ভয়ংকর। আমি চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর হাত-পা ধুয়ে বসলাম মার পাশে।
‘একটু কাঁদ। তাতে মন হালকা হবে।’ মা বললেন।
আমি কিছু বললাম না। মনে মনে বাবার উদ্দেশে বললাম, ‘কী বোকামিটাই না করলে এত তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে।’ তবে বললাম মনে মনে, বাবার কানে কানে।
অনেক বছর পরে ক্রিস্টিনা যখন ওর দাদু সম্পর্কে জানতে চাইবে আমার মনে হয়েছিল এ আর কঠিন কী? বাড়িতে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কেউ তেমন কিছুই জানে না। যারা বলতে পারত তারা কেউ নেই, যারা আছে তারা পূর্বপুরুষদের অতীতের ব্যাপারে ভালভাবে জানার জন্য কখনওই আগ্রহী হয়নি। তাহলে উপায়? বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা তথ্য সংগ্রহ করা আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে একটা পরিপূর্ণ চিত্র আঁকার চেষ্টা করা।
প্রথমেই প্রশ্ন আসে বাবার জন্ম কবে? পুরনো পাসপোর্ট থেকে হয়তো এসব তথ্য বের করা যেত অথবা কোনও সার্টিফিকেট থেকে। কিন্তু কোথায় সেসব সার্টিফিকেট? তাছাড়া আমাদের দেশে সে সময় ডকুমেন্টে তো ইচ্ছেমত বয়স বসিয়ে দেয়। মনে পড়ল ছোটবেলা থেকেই বাবাকে দেখেছি বেশ বয়স্ক একজন মানুষ হিসেবে। পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের বাবারা ছিল আমার দাদাদের সমবয়েসি। তারা বাবাকে কাকা বা জ্যাঠা বলে ডাকত। আমার কখনওই মনে হয়নি বাবার কবে জন্ম সেটা জিজ্ঞেস করার কথা। কিন্তু যখন তথ্য খুঁজতে শুরু করলাম, কলকাতার মিতু বউদির কাছে জানতে পারলাম আমার যখন জন্ম বাবার বয়স তখন ছিল ছাপান্ন। ১৯৮৯ সালে বাবাকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলাম। ওটাই ছিল আমাদের দুজনের একসঙ্গে একমাত্র দীর্ঘ ভ্রমণ। স্বপনদা কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে, মিতু বউদির সঙ্গে বাবার প্রথম আলাপ। তাই মিতু বউদি কৌতূহলী হয়ে এসব প্রশ্ন করতেই পারত। সব হিসেব করে দেখা গেল বাবার জন্ম ১৯০৮ সালে। আসলে ছোটবেলা থেকেই বাবাকে এমন বয়েসি দেখেছি যে নিজের যখন ছেলেমেয়ে হল অনেকদিন পর্যন্ত আমার কষ্ট হয়েছে নিজেকে বাবা ভাবতে। তাই ছেলেমেয়েরা আমার কাছে আগে বন্ধু তারপর সন্তান।
ওই সময় কমবেশি অবস্থাপন্ন পরিবারের এক-দুজন সন্তান কলকাতা পড়াশুনা করত। আমার ঠাকুরদা নিজে বাড়ির ব্যবসাপাতি দেখাশুনা করলেও তাঁর ছোটভাই কলকাতায় পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। একই ঘটনা ঘটে বাবা-কাকাদের সঙ্গে। বড় জ্যাঠামশাই নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। মেজ জ্যাঠামশাই আর ছোটকাকা এলাকায় ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াশুনা করে গ্রামেই থাকতেন। বাবা কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বড় জ্যাঠার মতই নীলরতন মেডিক্যালে ভর্তি হন। তবে পড়াশুনার এক পর্যায়ে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তাকে পাওয়া যায় আসামের জঙ্গলে এক সাধুর আশ্রমে। বাবা মাঝেমধ্যে কলকাতা জীবনের গল্প করলেও আসাম সম্পর্কে কোনওদিনই কিছু বলেননি। ছোটবেলায় আমাদেরও সাহস হয়নি এ নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করতে। যখন এসব নিয়ে কথা বলার মত সম্পর্ক গড়ে উঠল তখন বাবা নিজেই ছুটি নিলেন পৃথিবী থেকে। যদিও কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে বাবা মেডিক্যালে পড়তেন গত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ দিকে বা তিরিশের দশকের প্রথম দিকে। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯৪৩ সালে। তখন সুবোধদার বয়স তিন বা চার, তার মানে বাবা প্রথমবার বিয়ে করেছিলেন ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালে। অনেক খোঁজখবর করে বাবাকে আসামে পাওয়া গেলে প্রথমে তাকে কলকাতা পাঠানো হয় লেখাপড়া শেষ করার জন্য। কিন্তু ঠাকুরদা হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবার ডাক পড়ে গ্রামে ব্যবসার হাল ধরার জন্য। যাতে পরবর্তীতে আবার না পালায় সে জন্যে ঝিটকার জমিদার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। সেটা যদি ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালে হয় ধরে নেওয়া যায় বাবা আসামে বেশ কয়েক বছর নিরুদ্দেশ ছিলেন।
ওই সময় বাবার কাঁধেই ব্যবসার দায়িত্ব পড়ে। ছোটকাকা স্কুলে শিক্ষকতা করলেও তখন থেকেই জমিজমা দেখাশোনা করতে শুরু করেন। মেজ জ্যাঠামশাই সংসার নিয়ে ভাবতেন বলে মনে হয় না। কবিরাজি করতেন। আমাদের ছোটবেলায় কাটাছেঁড়া, মাথাব্যথা— এসব তাঁর হাতের টোকায় সেরে যেত। শুধু তাই নয়, কুষ্ঠ, আলসার এসব রোগীদের ডাক্তাররা বিদায় করে দিলে তাদের বেশ কয়েজনকে জ্যাঠামশাই কবিরাজির মাধ্যমে সারিয়ে তুলছেন। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত বাবা কেমন ছিলেন সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। তবে এরপর থেকে, মানে যখন থেকে আমি কমবেশি সব কিছুই মনে করতে পারি তখন থেকে বাবার একটা ছবি আঁকতে পারি মনে মনে। সেই ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাবা খুব একটা বদলাননি। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ঠান্ডা মাথার মানুষ। মা বলতেন ‘সাত চড়ে নড়ে না’। তাই এর আগেও যে বাবা অনেকটা এমনই ছিলেন সেটা অনুমান করা যায়।
বাবা সাধারণত ঘুম থেকে খুব ভোরে উঠতেন। হাতমুখ ধুয়ে বসতেন আহ্নিকে। কখনও দাঁত মাজতে মাজতে হাঁটতেন নদীর ধার দিয়ে আবার কখনও হাঁটতে যেতেন আহ্নিকের পরে মালা জপতে জপতে। আহ্নিকের সময় তিনি হয় গীতাপাঠ করতেন অথবা চণ্ডী। আমার পছন্দ হত চণ্ডী, বিশেষ করে যেখানে উল্লেখিত সৃষ্টিরহস্য। সেই ভাষ্য অনুযায়ী প্রলয়ের পর শান্ত মহাসাগরে অনন্তনাগের ওপর গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন ভগবান বিষ্ণু। অনন্তনাগের নামটাই এক রহস্য— অনন্ত, অন্তহীন— যার শেষ নেই। এই নাগের সাত মাথা। লেজ থেকে যতই মাথার দিকে যাচ্ছে নাগ ততই স্ফীত হচ্ছে ঠিক যেমনটা বিশ্বব্রহ্মান্ড ছোট থকে ক্রমাগত বড় হচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ মহাসাগরে ঘুমন্ত বিষ্ণুর নাভি থেকে যে পদ্ম ফুল ফুটেছিল সেখানে বসে ধ্যান করছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। এই পরিবেশে বিষ্ণুর কান থেকে খৈল বা কানের ময়লা বের হয় যা থেকে জন্ম নেয় শুম্ভ নিশুম্ভ দুই দৈত্য। ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মাকে দেখেই তাঁকে খুন করতে উদ্যত হয় দৈত্যরা। ব্রহ্মার আর্তনাদে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙে। তাঁদের আর সমস্ত দেবতাদের শরীর থেকে নির্গত শক্তি নারীমূর্তি ধারণ করে, যিনি মায়া বা মহামায়া। তিনিই দুর্গা। তাঁর হাতেই পরে মৃত্যুবরণ করবে অসুরদ্বয়। যদিও মিথ এই গল্পের মধ্যে অনেক উপমা আছে যা আমাকে মনে করিয়ে দেয় বিগব্যাং-পূর্ববর্তী শান্ত পরিবেশের কথা, পরবর্তীতে সিমেট্রি ভঙ্গ যেটা ঘটেছিল কানের খৈল থেকে অসুরের জন্মের মাধ্যমে। আর এরপর শক্তির উৎপত্তি। মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেও এই সিমেট্রি ভঙ্গ আর শক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চণ্ডীতে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞনিক তত্ত্বের সঙ্গে অন্তত প্রতীকীভাবে হলেও অনেকটাই মিলে যায়। নিয়মিত গীতা বা চণ্ডীপাঠ করলেও বাবা ধর্মীয় রীতিনীতি খুব একটা মানতেন বলে মনে হয় না। বাড়িতে কোনও পূজা হলে বেরিয়ে প্রণাম করতেন ঠিকই, তবে এ নিয়ে কোনও রকম বাড়াবাড়ি ছিল না। আমাদেরও কখনও প্রণাম করার জন্য জোরাজুরি করতেন না। আশেপাশের কোনও বাড়িতে বা অন্য কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেতেন বলেও মনে করতে পারব না। অন্তত ধর্মের বাহ্যিক ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। বাবা-কাকারা সবাই ছিলেন ফরিদপুরের জগদবন্ধু আঙিনার শিষ্য। যুদ্ধের আগে সেখানকার মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রতি বছর আমাদের বাড়িতে আসতেন গীতাপাঠ করতে। ওই একটা অনুষ্ঠান যেখানে বাবা আগাগোড়া পুরোটা সময় কাটাতেন।
ছোটবেলায় দিনের কাজের শেষে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে রংখোলা পর্যন্ত যেতেন। এই সময়টার জন্য আমি সারাদিন অপেক্ষা করে বসে থাকতাম। সাধারণত বাবা (কখনও কখনও ছোটকাকা) সোমবার আর বৃহস্পতিবার যেতেন নারায়ণগঞ্জ রং আর সুতা কিনতে। বুধবার, শনিবার আর রবিবার যেতেন ঘিওর, ঝিটকা আর জাবরা হাটে। বাকি দুদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আসত খদ্দেররা সুতার জন্য। তাই আমার সঙ্গে হাঁটার সময় খুব একটা হয়ে উঠত না। একটু বড় হয়ে আমি অবশ্য কখনও কখনও বাবার সঙ্গে সকালে হাঁটতে যেতাম। আর বাবা যখন মোকাম বা হাট থেকে ফিরতেন, আমি আর রতন প্রায়ই বাবার পা টিপে দিতাম। আমরা পালা করে মা’র পা-ও টিপে দিতাম।
মানুষ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত অসংখ্য কাজ করে। এসব কাজ নিয়েই মানুষের জীবন। তবে আমরা যদি কারও প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজের বর্ণনা দিতে শুরু করি সেটা হবে বড়জোর মানুষের রচনা, গল্প নয়। মানুষের এই নিস্তরঙ্গ জীবনে যখন কোনও ঘটনার ঢেউ খেলে যায় সেই জীবন তখন গল্প হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, ১৯৬৮ সালের আগের বাবার জীবন সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। যদি তাঁর ছাত্রজীবনে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা জানতাম তবে সেটা হতে পারত একটা গল্পের সুন্দর প্লট। কিন্তু সেটা উদ্ধার করা যায়নি, যে দুঃখটা আমার সারা জীবনই থাকবে। তাই আমার পরবর্তী গল্প হবে সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে যা ছিল অন্য দশটা দিনের চেয়ে আলাদা।
যুদ্ধের ঠিক আগেই বাবা নারায়ণগঞ্জ মোকামে যান সুতা আর রং আনতে। যদিও ৮ মার্চ থেকেই বাড়ির সবচেয়ে উঁচু আম গাছটার মাথায় অনেক লম্বা একটা বাঁশে কালো (নাকি আশু গোস্বামীর সেলাই করা সবুজ মাঠে লাল সূর্যের ভেতর সোনার বাংলাদেশ খচিত?) পতাকা উড়ছিল, তবে বঙ্গবন্ধুর হুকুম থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য মনে হয় কেউই প্রস্তুত ছিল না। ২৬ মার্চ থেকেই তরা ঘাটে নামল মানুষের ঢল। ঢাকা থেকে আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবাই ছুটে চলেছে সামনে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এত মানুষ আসছে, কিন্তু বাবার দেখা নেই। সেই সময় গ্রামের সবার সঙ্গে আমরাও চেষ্টা করছি পালিয়ে আসা মানুষের পাশে দাঁড়াতে, তাদের মুখে খাবার তুলে দিতে। এত কিছুর মধ্যেও মা গরম করছেন বাচ্চাদের জন্য দুধ। সে এক বিশাল সাহায্যযজ্ঞে নেমেছে দেশ। বেশ কয়েক দিন পরে কখনও নৌকায়, কখনও লঞ্চে করে, কখনওবা পায়ে হেঁটে দোহা, কলাকুপা বান্ধুটিয়া, বেউথা এসব জায়গা হয়ে শেষ পর্যন্ত ২ এপ্রিল বাবা বাড়ি এলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় শীতলপাটি পেতে দেওয়া হল। হাতমুখ ধুয়ে একটু খেয়ে শুয়ে পড়লেন সেখানে। আমি, রতন দুজনে পা টিপতে শুরু করলাম, মা, দিদি, বউদি পালা করে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। সেবারের মত বিপদ কাটল। এরপর অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে শুরু করলে আমাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাবার কথা উঠল। এরমধ্যেই এলাকায় মিলিটারি এসে গেছে। আমরা বাড়ি ছাড়লাম। প্রথমে মাইল্যাগি। ধারণা ছিল দু-চারদিন পরে অবস্থার উন্নতি হবে, সবাই বাড়ি ফিরে যাব। ৭ বা ৮ এপ্রিল নিতাই কাকা আর জগা কাকাকে মারা হল আমাদের গ্রামে। এরপর বাবা রতনকে নিয়ে বাড়ি গেলেন কিছু জিনিসপত্র আনার জন্য। আমার বায়না ছিল খেলনার। লুট হল গ্রাম। এর কয়েকদিন পরেই বলাই গোঁসাইকে সস্ত্রীক কূপে ফেলে মারা হল। আমাদের উপস্থিতি গ্রামে মিলিটারি নিয়ে আসতে পারে, এ নিয়ে মাইল্যাগির স্থানীয় চেয়ারম্যান ভীত হলে আমরা গেলাম বাঙ্গালা। সেখানে মাস দুয়েক থেকে গেলাম বৈলতলা। সেখানে আমরা ছোটরা খেলাধুলা করে সময় কাটালেও বড়দের সময় কাটছিল না। সবাই বসে সারাক্ষণ যুদ্ধের গল্পই করতেন। রেডিওতে খবর শুনতেন। এরপর একদিন বাড়িতে রাজাকার এল। তখন বর্ষাকাল। একটা ঢাকা একমালিয়া নৌকা আসতে দেখে সন্দেহ হল। মাখন কাকা বাবা-কাকাদের নিয়ে গেলেন অন্য দিকে। বাবা যেতে চাইছিলেন না। আমাকে মা, দিদিদের নিয়ে পালাতে বললেন। আমি ভেতরে গিয়ে সে-কথা বললে মা বারবার বললেন, ‘বাবা কোথায় দেখে আয়।’ দেখতে গিয়ে আমার কেন যেন মনে হল রাজাকাররা বাবাকে ধরেছে। মাকে বলাতে মা কিছুতেই যাবেন না। শেষ পর্যন্ত আমরা পালালাম। মা বিশাল ঝাউ (বা দেবদারু) গাছের ওখানে বেতের ঝোপে কোনও রকমে কালো জলে নাক ভাসিয়ে ডুবে রইলেন। আমরা নৌকায় করে গেলাম অদূরেই এক বাড়িতে। মা-বাবা কেউই সাঁতার কাটতে জানতেন না। সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বাড়ি ফিরলাম প্রচণ্ড আশঙ্কায় সময় কেটেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি সবাই ঠিকঠাক আছে, শুধু কল্যাণদা ধরা পড়েছিল। ওকে ছেড়ে দিয়েছে। যদিও বুঝতে পারি বাবাকে ধরার ব্যাপারটা ছিল ভয় থেকে জন্মানো গল্প, এখনও সেটা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। যুদ্ধ চলে, জীবনও চলে, তাকে চলতে হয়, চালাতে হয়। তাই জীবনের তাগিদায় আবার শুরু হল ব্যবসা। এর শুধু আর্থিক দিকই ছিল না, ছিল সাইকোলজিক্যাল দিক। অন্তত কিছু সময় হলেও যুদ্ধের দুশ্চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারতেন বাড়ির বড়রা। তারপর এল স্বাধীনতা।
আমাদের অবস্থা বরাবরই বেশ ভাল ছিল, তবে যুদ্ধের পর তা আরও রমরমা হয়। আগে আমাদের ছিল মূলত রং আর সুতার ব্যবসা। জমিতে ধান, কলাই, পাট সহ বিভিন্ন ফসল ফলত, ডাঙ্গায় মাছ (ডাঙ্গা মানে মাঠের মধ্যে পুকুর, তবে সেটা হত কালেভদ্রে, মাছ মূলত কিনতে হত প্রতিবেশী জেলেদের কাছ থেকে), বাড়ির গরুর দুধ। এখন শুরু হল কাপড় আর পেট্রলের ব্যবসা। বাবা তাই প্রায়ই মানিকগঞ্জ যেতেন। কখনও বাবার সঙ্গে, কখনও অন্য কারও সঙ্গে আমিও যেতাম। আসতাম বাবার সঙ্গেই, লাস্ট ট্রিপে। মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে পদার (খুব সম্ভব তারাপদ) দোকানে মিষ্টি খেতাম আমি। মার সঙ্গেও অনেক জায়গায় যেতাম, তবে বাবার সঙ্গে গেলে নিজেকে অন্য রকম, বড় হয়ে গেছি, বড় হয়ে গেছি ধরনের মনে হত। একবার মনে আছে বাবার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ মোকামেও গেছিলাম। স্বাধীনতার পর পর একটা ঘটনা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। তখন আমাদের ছুটি ছিল রবিবার আর শুক্রবার ছিল হাফ ডে। আমরা অবশ্য এটাকে বলতাম ভুট্টার ছাতুর দিন। এদিন বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া সাহায্য বিতরণ করা হত। আমার যেহেতু দরকার ছিল না তাই একদিন ভাবলাম স্কুলে যাব না।
‘তুমি স্কুলে যাবে না?’ বাবা জিজ্ঞেস করলেন।
‘না।’
‘কেন?’
‘আজ ভুট্টার ছাতুর দিন।’
‘ছাতু না আনলে, স্কুলে যাও।’
‘আমি যাব না।’
‘যাব না মানে? তোমাকে যেতেই হবে।’
কাকে যেন বললেন আমার বই নিয়ে আসতে। আমার হাতে বই দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন। একটু এগুই, আমি বই পেছনে ছুড়ে ফেলি। বাবা তুলে এনে আবার আমাকে নিয়ে হাঁটেন। ‘এক পা সামনে দু-পা পেছনে’ লেনিনের এই খেলার এক পর্যায়ে মারতে শুরু করলেন। তারপর এল কাঁচা কঞ্চি। কিন্তু আমি গোঁ ধরেছি, যাব না কিছুতেই। এভাবে প্রায় ৫০০ মিটার মানে স্কুলের অর্ধেক পথ আসার পর দেখা ছোট মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে।
‘নয়া কাকা ওকে মারছেন কেন?’
‘ও স্কুলে যাবে না।’
‘আজ আসলে ক্লাস হবে না, তাই আমিই বলেছি স্কুলে না আসতে।’
শেষ পর্যন্ত বাবা শান্ত হলেন। আমি এক দৌড়ে বাড়ি চলে গেলাম। এরপর বাবা আর কোনও দিন আমাকে মারেননি। আমি নিজে বাবা হয়ে মনিকার ছোটবেলায় দু-চার বার মেরে লজ্জিত হয়েছি। ক্রিস্টিনা বা সেভার গায়ে হাত তুলিনি। এতে কাজ হয় না। এটা বাচ্চাদের ব্যর্থতা নয়, নিজের বুঝিয়ে বলার অক্ষমতা। নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ কথাগুলো একান্তই আমার নিজের উদ্দেশে। বাবার সেদিনের ক্রোধ আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে।
যুদ্ধের সময় গ্রাম ছেড়ে পালালেও আমাদের প্রতিদিন কোথাও পালাতে হয়নি। স্বাধীনতার কিছুদিন পরে শুরু হল রাতে বাড়ি ছেড়ে পালানোর পালা। প্রায় প্রতিদিন এলাকায় ডাকাতি হত। যে সম্পদ আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল আজ সেটাই জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলল। তাই প্রতিদিন রাতের খাবারের পর বাড়ির মহিলারা আর ছোটরা আশেপাশের বাড়িতে ঘুমুতে যেতাম। নিজেদের মজবুত ঘরের চেয়ে ওদের ভাঙা ঘর বেশি নিরাপদ মনে হত। বড়রা রাত জেগে পাহারা দিত। মাঝে মাঝে শোনা যেত:
‘জাগরে বস্তিওয়ালারা! হৈ হৈ…’
একটা সময় ছিল কারও পায়ের শব্দ শুনলে সবাই তটস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করত, ‘কে যায়?’
ভয়। চারিদিকে ভয়ের যথেচ্ছ চলাফেরা। বাতাস যেন ভয়ে ভারী হয়ে আছে। আমার মনে পড়ে ১৯৭২ সালে যখন ইন্ডিয়া যাই তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। চারিদিকে দেওয়াল লিখন। রক্ত আর খুনের অশরীরী উপস্থিতি সর্বত্র। দেশেও তখন একই অবস্থা ছিল। এরকম এক সন্ধ্যায় একদল লোক এল আমাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছে। এটা নতুন কিছু নয়। বাবাকে বলায় বাবা আমাদের কাজের লোকদের বললেন ওদের থাকার ব্যবস্থা করতে। জনা দশেক সমর্থ পুরুষদের এক দল। দুদিন আগেই লোক নেওয়া হয়েছে। তাই বলা হল ওদের রাতের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা হবে। সকালে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে কাজের খোঁজে। বাড়িতে ঘরের অভাব ছিল না। কিন্তু বাধ সাধলেন জ্যাঠামশাই, কিছুতেই অজানা-অচেনা এতগুলো লোককে থাকতে দেবেন না। অগত্যা তাদের বলা হল সি অ্যান্ড বি-র জায়গায় থাকতে। সেটা ছিল ঢাকা-আরিচা রোডের পাশে, আমাদের বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটার দূরে। বাড়ির কর্মচারী হজরত ভাই পথ দেখিয়ে দিয়ে এল ওদের। কিছুক্ষণ পরে বাবা বললেন ওদের কিছু চালডাল দিয়ে আসতে যাতে রান্না করে খেতে পারে। হজরত ভাই সেটা দিতে গেলে ওরা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। মনঃক্ষুণ্ণ হজরত ভাই সেটা গিয়ে বলে ব্রিজের ওখানে পাহারারত পুলিশদের। পুলিশ খোঁজ নিতে গেলেই ওরা কী একটা পোটলা পুলিশের পায়ের কাছে ফেলে দৌড়। ওখানে পাওয়া গেল স্টেনগান আর যাদের মারা হবে তাদের তালিকা। বাবা, কাকা, জ্যাঠা সহ গ্রামের প্রায় ৫০ জনের নাম নাকি ছিল সেখানে।
হয়তো অনেক বয়সের সন্তান বলে বাবা আমাকে একটু বেশি আদর করতেন, একটু বেশি চোখে চোখে রাখতেন। এমনকি কলেজে পড়ার সময় একা একা যাতে না যাই সেদিকে খেয়াল রাখতেন। কিছু বলতেন না, শুধু টিফিনের জন্য অনেক টাকা দিয়ে বলতেন বন্ধুদের নিয়ে খেতে। ফলে কী কলেজে যাবার পথে, কী ফেরার পথে, কী দাস কেবিনে— সব সময় কয়েকজন বন্ধু থাকত সঙ্গে। যখন ছাত্র ইউনিয়ন করা শুরু করি তখনও বাধা দেননি, শুধু বলতেন পড়াশুনা ঠিকমত করতে আর সংগঠন যদি করি তার নিয়মকানুন যেন মানি। একবার সাইকেল নিয়ে গেলাম আরিচা। শিবালয়, তেওতা— এসব জায়গায় মিটিং করে দেরি হয়ে গেল। সাইকেল অবশ্য মোসলেমের ওখানে রেখে বাসে আসা যেত, তবে বয়স কম, তাই ওদের কথা না শুনে সাইকেলেই রওনা হলাম বাড়ির পথে। আরিচা থেকে তরার দূরত্ব প্রায় ১৪ মাইলের মত। ঢাকা আরিচা রোড কখনওই নিরাপদ ছিল না। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। কোথাও কেউ নেই, মাঝেমধ্যে বিকট শব্দ করে ট্রাক যাচ্ছে। যখন বগাধরের বিলের ওখানে আসি— সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওখানে একাত্তরে প্রচুর লোক মেরেছে। ভূতপ্রেতের আনাগোনা নিয়ে প্রচুর গল্প আছে। শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। এরপর ছিল ক্রস ব্রিজের ওখানকার তাল গাছ। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত। বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে একটু বকলেন। আমি না খেয়ে বই নিয়ে বসে পড়লাম। পড়ার ব্যাপার ছিল একেবারেই আলাদা। আমাদের বাড়িতে কারেন্ট আসে অনেক পরে। যতদিন দেশে ছিলাম পড়তাম হ্যারিকেনের আলোয়। অনেক রাত জেগে। মা খাবার রেখে দিতেন। বাবা কিছুক্ষণ পর পর বলতেন:
‘বাবা, এবার খেয়ে নাও।’
‘এই তো, আর দুটো অংক কষে নিই বা আর একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে নিই।’
এভাবে কত রাত যে না খেয়ে কাটত। সকালে কেউ খাবার সরিয়ে নিত। দিনের বেলায় মা ডাকতেন:
‘বিজন, খেয়ে যা।’
‘পাঁচ মিনিট পরে আসছি।’
‘আধ ঘণ্টা পরে আবার ডাক।’
‘বললাম তো পাঁচ মিনিট পরে আসছি।’
মস্কো আসার পর বাবা থাকতে দুবার দেশে যাই। ১৯৮৭ আর ১৯৮৯ সালে। তখন রীতিমত সিরিয়াসভাবে ছবি তুলি। বাবা খুব সকালে ডেকে দেন।
‘বাবা, যাও ছবি তুলতে। এখনই সবচেয়ে ভাল সময়।’
কখনও সকালে উঠে চলে যেতাম সাভার বা অন্য কোথাও ছবি তুলতে। বাবা সব সময় বলতেন ‘কী করো তার চেয়েও বড়কথা কীভাবে করো। যাই করবে, খুব যত্ন করে, ভালভাবে করবে।’ আমি আমার ছেলেমেয়েদের একই কথা বলি, ওরাও ওদের কাজ ভাল করে করুক সেটাই চাই। তাই ১৯৯১ সালে বাড়ি ফিরে যখন দেখলাম বাবা নেই, অনেকদিন বলতে গেলে ক্যামেরা হাতে নিইনি বা তত ছবি তুলিনি। নতুন করে শুরু করি মনিকার জন্মের পর। ১৯৮৯ সালে বাবার সঙ্গে যাই কলকাতা। এটা ছিল অন্ধ আর খোঁড়ার ভ্রমণ। বাবা সব চিনতেন, কিন্তু শারীরিক কারণে একা যেতে পারতেন না। আমি সুস্থ, সবল, তবে চিনি না কিছুই। সে সময়ই বহরমপুর থেকে ফেরার পথে রানাঘাটে যখন ট্রেন বদলাই, বউদিকে কামরায় বসিয়ে আমি যাই বাথরুম করতে। বাবাও যান, তবে বাথরুম খুঁজে পান না। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। বাবা বহুমূত্র রোগী। যেদিকে প্ল্যাটফর্ম তার উল্টো দিকে নেমে বসলেন প্রস্রাব করতে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় ট্রেন ছাড়ল। ওদিকে লোকজন বলতে শুরু করেছে ‘কী করছেন মশাই, ট্রেনে কাটা পড়বেন তো।’ বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে ট্রেনে তুললাম। ‘বাথরুম হল না।’ আমি তোমাকে ধরছি, তুমি এখানে বসে পড়ো। নিজেদের সিটে এসে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। বউদির ওপর সবাই চড়াও। কেন পুরুষ কামরায় উঠে আবার সিট দখল করে বসেছে। আসলে আমার ধারণাই ছিল না এখানে ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা কামরা। যাহোক, শেষ পর্যন্ত বাবা বসলেন বউদির জায়গায়, আমি আর বউদি শেয়ালদা পর্যন্ত এলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা বাড়িতে মা’র কারণে অনেকটাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতাম। তবে বাবা কথা কম বলতেন আর মূলত কথা বলতেন খদ্দেরদের সঙ্গে তাদের ভাষায়। কলকাতায় গিয়ে দেখলাম বাবা ওখানকার ভাষায় দিব্বি কথা বলে যাচ্ছেন, আর আমার কথা শুনে লোকজন বাঙাল বলে চিহ্নিত করতে পারছে।
আমার প্রতি বাবার অগাধ ভালবাসা, আস্থার প্রমাণ আমি অনেক বার পেয়েছি। তখন স্কুলে পড়ি। একদিন বাবা ডেকে বললেন, ‘সিগারেট খাও? যদি না খেয়ে থাকো, খেয়ো না। ওতে ভাল কিছু নেই।’ আমার বিশ্বাস, অন্যদের সিগারেট খেতে মানা করেছেন। বাবা ছিলেন নিরামিষাশী। তবে কলেজ লাইফে ডিম খেতেন। নিজেই বলেছেন। মাছ মনে হয় কখনওই খাননি। কে জানে, আমিও যে মাছ খুব একটা পছন্দ করি না, সেও হয়তো এ কারণেই কিনা। দেশে তো কিছুই করতে পারতাম না। মস্কো এসে টুকিটাকি রান্না করতে শিখি। এখন তবুও কিছু একটা পারি। আশির দশকে শুধু বাবার উৎসাহেই রান্নার সাহস পেতাম, মস্কোয় আমার রান্না কেউ মুখে তুলত না। যাহোক, একবার বাড়িতে মুরগি রান্না করলাম। কারওই পছন্দ হল না। বাড়িতে তো সবাই ভাল রাঁধে। কিন্তু না খেয়েই বাবা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দিদি বলল, ‘তুমি মাংস খাও না, কীভাবে বুঝলে যে মাংস খুব টেস্টি হয়েছে?’ ‘আমি গন্ধেই টের পেয়েছি।’ বাবার উত্তর। বাবা আমাকে সব সময় একটা কথাই বলতেন, ‘বিবেকের কাছে সৎ থাকবে। সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।’ এটাও আমার জীবনের একটা পাথেয়। বাবা চা খেতেন না। বলতেন কলকাতায় থাকায় সময় চা খেলে তাদের উল্টো পয়সা দেওয়া হত। তখন মনে হয় সাধারণ বাঙালির জীবনে চা ছিল অখাদ্য-কুখাদ্যের দলে। আমাদের এলাকায় অনেকেই বাবাকে আপনি আর মাকে তুই বলে ডাকত। আমরা বাবা-মা দুজনকেই তুমি বলতাম, বড় ভাইদের তুই, এখন অবশ্য বেশি বড়দের তুমি বলি। আর একটা ব্যাপার, আমার কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করলেও যখন টেলিস্কোপ বা এ জাতীয় জিনিস তৈরির জন্য লেন্স বা অন্য কিছু কিনতে ঢাকা যেতে হত তখন বাবা মানা করতেন না, উল্টো কীভাবে যেতে হবে এসব বলে দিতেন। গুলিস্তান থেকে রিকশায় যেতাম তিকাটুলীর ওদিকে। তবে এখন আর ওসব জায়গা চিনব বলে মনে হয় না।
আমাদের প্রতি বাবার ভালবাসা আর বিশ্বাস ছিল অগাধ, যদিও আমরা সব সময় সেটা অনুভব করতে পারতাম না। জন্মের পর থেকেই শুনছি দিদি বিয়ে বসবে না, কিন্তু বাবা এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। দিদির মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পেছনে অনেকে অনেক কথা বললেও সেসব কানে তুলতেন না। আমরা সবাই নিজেদের মত করেই চলেছি। কী পড়াশুনা, কী বিয়েথা, সব নিজেদের পছন্দমত। কোনও সময় বাবা তাঁর ইচ্ছা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। ১৯৭৭ সালে কাকা যখন ভিন্ন হওয়ার প্রস্তাব দেন, বাবা সেটা মেনে নিয়েছেন। কাকার তিন মেয়ের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সবাই ইন্ডিয়া থাকে। কাকা চাইলে ওখানে এমনিতেই চলে যেতে পারতেন, তাঁর ক্যাপিটাল বিশ্বস্ত হাতে থাকত। কাকা সেটা না করে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে যান টাকাপয়সা নিয়ে, এর ফলে আমাদের রমরমা ব্যবসা বলতে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মা বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কিছু বলেননি। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বাবা প্রায়ই সন্ধ্যায় আমাদের জড়ো করে কাকাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাতেন। চাইলে তিনি নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, তারপরেও আমাদের মতামত নিতেন। এ নিয়ে আমাদের পারিবারিক বন্ধুরা বাবাকে কাকাদের সঙ্গে কথা বলতে বললে (আমরা অনেকগুলো ভাইবোন, তখনও সবাই লেখাপড়া করছি) বাবা আমাদের দেখিয়ে বলতেন, ‘এরাই আমার সম্পদ। পড়াশুনা করবে যতদূর করতে চায়, তারপর নিজেদেরটা নিজেরাই করে খাবে।’ বাড়ির ব্যবসা মূলত বাবার হাতে গড়ে উঠেছিল তারপরেও এ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করতে চাননি। আসলে সংসার করলেও বাবা ছিলেন অনেকটা বিবাগী। কখনও তাঁকে হাহুতাশ করতে দেখিনি, আমরা যে ঠিকমত তাঁর ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছি না তা দেখেও বাবাকে হতাশ হতে দেখিনি। এক সময় স্ট্রোক করে মা পঙ্গু হয়ে যান। বাবা ধীরে ধীরে মাকে নিজের পায়ে দাঁড় করান। প্রতিদিন মাকে ধরে ধরে হাঁটাতেন আর মা একটু ভাল হয়ে উঠলে আমাদের দিতেন মা’র সঙ্গে হাঁটতে। কী মা, কী আমাদের প্রতি বাবার ভালবাসার প্রকাশ ছিল নীরব। এমনকি স্বপনদা যখন পলাতক বা জেলে ছিল, তখনও বাবাকে ভেঙে পড়তে দেখিনি, বরং মাকে সব সময় সান্ত্বনা দিতেন, মনে সাহস রাখতে বলতেন। আরও একটা ব্যাপার, গ্রামের লোকেরা বাবাকে সম্মান করলেও তিনি কখনও কোনও বিচার সালিশে যেতেন না। অনেক বিচার আমাদের বাড়িতেই হত। কাকা বা জ্যাঠামশাই এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু বাবা এসব একেবারেই পছন্দ করতেন না। যেমনটা করতেন না কারও সমালোচনা করা। তবে সব সময়ই পড়াশুনা করতেন। কয়েকটা সংবাদপত্র তো বাড়িতে নিয়মিত আসতই, এর বাইরে গল্পের বই। রেডিওতে খবর শুনতেন নিয়মিত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন বাড়িতে কেউ এলে, তা সে গ্রামের বয়স্করাই হোন আর আমাদের বন্ধুবান্ধবরাই হোক।
বাবা মনে হয় কাজের আনন্দেই কাজ করতেন। তাঁর কাছে খদ্দেররা ছিলেন লক্ষ্মীর মত। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি গ্রামের অনেকে ইন্ডিয়া চলে যান। তারা যখন বাবার কাছে বিদায় নিতে আসতেন, ধারদেনা শোধ করার অপারগতার কথা জানাতেন, বাবাকে কখনওই অধৈর্য হতে দেখিনি, তাদের মঙ্গলকামনা করতেই দেখেছি। হয়তো মনে করতেন ধনরত্ন এসবই মায়া! ২০১৬ সালে দেশে গিয়ে বাঙ্গালা আর বৈলতলা বেড়াতে যাই। সিংজুরিতে একজন আমাদের চিনতে পারেন। এখন সম্পন্ন অবস্থা। বললেন, ‘আমার এসব বাবুর (বাবার) কল্যাণে, যখন খুব বিপদে ছিলাম, টাকাপয়সার জন্য চাপ দেননি। আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। শুধু আমিই নই আমাদের গ্রামের অনেকেই।’ অনেক টাকাপয়সা রোজগার করলেও নিজের পোশাক-আশাকের প্রতি একেবারেই নজর দিতেন না। মা মাঝেমধ্যে ধুতিপাঞ্জাবি (আসলে ঠিক পাঞ্জাবি নয় ওই কাটিংয়ের জামা) আনিয়ে দিতেন, সেটা পরতেও কত অনীহা। খাবারদাবারের প্রতিও তেমন আগ্রহ ছিল না। নিরামিষ ভাত আর দুধ। শরীরের প্রতি একসময় যত্ন নিতেন। ব্যায়াম করতেন নিয়মিত। বাবার ভুঁড়ি ছিল আমাদের গর্বের বিষয়। আর চাবির তোড়া। বাবা যখন হাট বা মোকাম থেকে আসতেন অনেক দূর থেকেই শোনা যেত চাবির ঝনঝন শব্দ। মা যেতেন এগিয়ে। হাত-পা ধোয়ার জল তৈরিই থাকত, সেটা এগিয়ে দিতেন। এ ছিল ভালবাসার অন্য রকম প্রকাশ। বাড়িতে সন্ধ্যার চা হত সাতটার দিকে। ওই সময় সবাই হাজির হত। কেউ না থাকলে বাবা উচ্চস্বরে ডাক দিতেন। গ্রামের অন্যপ্রান্তে শোনা যেত সে ডাক। এটা ছিল এক রকমের হাজিরা দেওয়া। এরপর সবাই যে যার মত বাইরে যেতে পারত। একটা জিনিস খেয়াল করতাম বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে একটু হলেও তখন জড়তা ছিল। বাড়ির বউয়েরা বাড়ির মেয়ে বনে যেত। অনায়াসে ভাসুর-দেবরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। কাউকে নাম ধরে, কাউকে দাদা আবার কাউকে ভাসুর ঠাকুর বলে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীরা নিজের সম্ভাষণ ‘ওগো শুনছ’-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত। বাবাকে কিছু বলার দরকার হলে মা বলতেন, ‘যা তো, তোর বাবাকে (ছেলেকে) বল।’ বাবার নাম ছিল বৃন্দাবন, মা তাই কোনও কারণে বৃন্দাবন তীর্থের কথা বলতে হলে বলতেন বড় তীর্থ। একসময় আমার মনে হত বৃন্দাবন হিন্দুদের প্রধান তীর্থ। পরে বুঝেছি গুমরটা কোথায়।
১৯৯১ সালে আমি ঠিক ৫ সপ্তাহ দেশে কাটিয়ে মস্কো ফিরি ২৭ মে। একই প্লেনে ছিল দীপু। ওর বাবা তখন খুবই অসুস্থ। ওর ব্যবসায়িক কাজে মস্কো ফিরতে হবে, তবে কয়েকদিন পরেই আবার দেশে আসবে। আমি অবশ্য ওকে বাবার মৃত্যুর কথা বলিনি। অন্যান্য গল্প করতে করতে আসি মস্কোয়। খুব সম্ভব দীপুই আমাকে হোস্টেলে নামিয়ে দিয়েছিল। রুমমেট ঝেনিয়া তখনও ভার্সিটি যায়নি। কিছুক্ষণ পরে ও চলে গেলে এই প্রথম আমি সম্পূর্ণ একা। সেটা ছিল ২৮ মে ১৯৯১। অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে কাঁদলাম, এখনও পর্যন্ত জীবনে শেষবারের মত কান্না। এরপরে অনেকেই মারা গেছেন, কিন্তু কান্না আসেনি। ১৯৯৪ সালে তপু মস্কো আসে। আমি অসীমের ঘরে যাই ওর সঙ্গে দেখা করতে।
‘বাড়ির খবর জানেন?’ তপু জিজ্ঞেস করল।
‘হ্যাঁ, মা মারা গেছেন।’
‘আপনি, আপনি এত সহজে এই খবরটা বলতে পারলেন?’ অসীমের অবাক জিজ্ঞাসা।
‘অসীম আমি তো কান্না দিয়ে তাঁদের স্মৃতি ধুয়ে ফেলতে চাই না। তাঁরা থাকবেন আমার সাথে।’
দেশে যাওয়ার পর রতন ছবি দেখাচ্ছিল। একটা ছবি আমি চিনতে পারিনি।
‘এটা কে?’
‘বাবা। মৃত্যুর পরের ছবি।’
‘সরিয়ে ফেল আর কোনও দিন আমাকে দেখাবি না।’
হ্যাঁ, আমি না বাবা, না মা, না সুধীরদা, বউদি বা দিদি— কারওই মৃত্যুর পরের ছবি দেখিনি। ওঁরা সবাই আছেন জীবন্ত স্মৃতি হয়ে। ওঁদের প্রাণোচ্ছল মুখই ভেসে ওঠে আমার কল্পনায়, আমার স্বপ্নে। আগে বাবার কাছ থেকে কিছু জানতে হলে চিঠি লিখে অপেক্ষায় থাকতাম। এখন আর অপেক্ষা করতে হয় না। যদি কোনও সমস্যায় বাবার উপদেশ দরকার হয়, মনে মনে কথা বলি, জানি তিনি কী বলতেন, বলতে পারতেন। সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিই। কারণ জানি তাঁরা আমাকে কখনও খারাপ পথ দেখাবেন না। এই বিশ্বাসই আমাকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁদের মতামত জানতে সাহায্য করে।
হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী বাবা-মা মারা গেলে কয়েকদিন সেলাই ছাড়া সাদা কাপড় পরতে হয়। এই সময়টা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকমের। আমাদের বাড়িতে মনে হয় ১৫ দিনে অশৌচ। আমি দেশে ফেরার আগেই সেটা শেষ হয়ে গেছিল। তাই আমাকে মাত্র তিন দিন এই রীতি পালন করতে হয়। এ সময় শুধু নিজের হাতে রান্না সাদা ভাত খাওয়া যায়। রান্না করে কিছু ভাত রাখতে হয় কাকদের জন্য। কাক খেলে তবে নিজের খাওয়া। বাড়িতে কাকের অভাব ছিল না কখনওই। তাই অপেক্ষার পালা দীর্ঘ ছিল না। আর একটা রীতি হল ছেলেদের মাথা ন্যাড়া করা। আমি রাজি হইনি। এই নিয়ে একটু হৈচৈ। পুরুত মন্ত্র পড়িয়ে শ্রাদ্ধ করাবে না। এতে আমার অবশ্য কিছু এসে যায় না, তবে দেশে যারা থাকে তাদের একটা সামাজিকতা মেনে চলতে হয়। পরে তপনদা কোথায় এক পণ্ডিতের কাছ থেকে জেনে আসে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে মাথা ন্যাড়া না করলেও চলে। মা মারা যান ১৯৯৪ সালে। আমি দেশে ফিরি ১৯৯৭ সালে। তখনও একই রীতি মানি। তবে মানুষের মরার যেমন অধিকার আছে আমারও অধিকার আছে সেই মৃত্যুকে স্বীকার না করার। আর সে কারণেই বাবা, মা, সুধীর দা, দিদি, বউদি— এরা আমার কাছে এখনও আগের মতই জীবন্ত।
১৯৯১ সালে বাড়িতে কাটানো ওই পাঁচ সপ্তাহ ছিল খুব কষ্টের। বাবা কখনওই খুব বেশি কথাবার্তা বলতেন না, তবে সব কিছুতেই তাঁর অশরীরী উপস্থিতি ছিল। বাড়িতে সব কিছুই হত বাবাকে ঘিরে। কয়েকদিন আগে বাবা মারা গেলেও সব কিছুতেই আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতাম। যাই ঘটুক না কেন, মনে হত বাবা থাকলে কীভাবে নিতেন। বাড়ির, বিশেষ করে মা, দিদি, বউদি— সবার কথাই ছিল বাবাকে ঘিরে। বাবার শেষ দিনগুলোর গল্প। জ্যাঠামশাইয়ের মত বাবাও অনেক দিন অসুখে ভুগে মারা যান। শেষের দিকে প্রায়ই হাসপাতালে কাটাতেন। তবে তখনও চিকিৎসা ব্যবস্থা আজকের মত উন্নত ছিল না। এমনকি শেষদিনও কাটে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে। ওখানে সকালবেলায় ডাক্তার বাবাকে দেখে সব আশা ছেড়ে দেন, তিনিই বলেন বাবাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। অ্যাম্বুলেন্সে করে বাবাকে বাড়ি আনা হয়, মূলত পৃথিবী ত্যাগ করার জন্যই। বাড়ি ফিরে বাবা নাকি বলেছিলেন, ‘এ তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে এলি। এ তো আমার বাড়ি নয়। আমার বাড়িতে কত ফুল!’ শুনেছি জ্যাঠামশাইও নাকি মৃত্যুর সময় একই কথা বলেছিলেন। রংখোলায় পারিবারিক শ্মশানে তাঁকে দাহ করা হয়। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যুর আগে দিদিই শ্মশানের দেখভাল করত। কারও মৃত্যুবার্ষিকী এলেই আমরা কথা বলতাম। বলতাম বেল্লালকে ডেকে শ্মশানটা পরিষ্কার করাতে। দিদি শ্মশানে মোমবাতি জ্বালিয়ে আসত। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে, তবে গুলিয়াকে বলা আছে, আমার মৃত্যুর পর যেন বডিটা পুড়িয়ে ফেলে আর ছাইয়ের কিছুটা দেশে পাঠিয়ে দেয়। বাকিটার কিছু ভোলগায় আর কিছুটা বনে রেখে আসে। অবশ্য এক সময় বডিটা দান করার কথাও ভেবে দেখতে পারি।
তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙেনি, দেশের পার্টিও অবিভক্ত। তাই প্রায়ই সময় কাটত মানিকগঞ্জে, পার্টি অফিসে। ঢাকায় যেতাম পার্টি অফিসে আর তপুর বাসায়। একদিন তপু আর বাচ্চুকে নিয়ে চলে এলাম মানিকগঞ্জ। হঠাৎ শুরু হল কালবোশেখির ঝড়। রাত কাটল সাত্তার ভাইয়ের ওখানে। পরের দিন বেউথা থেকে নৌকা করে গেলাম তরা। ওই এক বারই আমি বেউথা থেকে নৌকায় তরা গেছি। ওদের পেয়ে বাড়ির পরিবেশ একটু হালকা হল। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে মার্বেল খেললাম। এ জন্যে দিদি সযত্নে তুলে রাখা আমার ছোটবেলার মার্বেলগুলো বের করে দিল। আমাদের বাড়িতে এক রাত থেকে তপুরা চলে গেল ঢাকায়। আমারও সময় হয়ে এল রাশিয়া ফেরার।
এরপর থেকে আমার জীবন অন্য দিকে মোড় নেবে। ১৯৯১ সালে দেশে যাবার আগে অকারণে হাতেগোনা যে ক’জন বন্ধু অবশিষ্ট ছিল তাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আমার হোস্টেলের নীচে রাতদুপুরে আড্ডা দিতে দিতে। ১৯৮৯ সালে পার্টির সঙ্গে ঝামেলার পর যে কয়জন মানুষের সঙ্গে মিশতাম এ ঝগড়ার পরে সেটাও নাই হয়ে যায়। খুব ঘনিষ্ঠ আর ভালবাসার মানুষ ফিরে যায় দেশে। নতুন জীবনের খোঁজে রাশিয়া ছাড়ে আরও কিছু মানুষ। চারিদিকে যখন চলে যাওয়ার হিড়িক তখনই কাকতালীয়ভাবে পরিচয় হয় একজন মানুষের সঙ্গে, যে এরপর থেকে আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, আমার জীবন ভরিয়ে তুলবে নব আনন্দে, নতুন প্রাণে।
২০২০ সালে দিদি মারা যাবার পরে মার্চের শেষদিকে আর কারও ফোনের অপেক্ষা করি না। দিদি সব সময়ই ফোন করে জানাত শ্মশানের চারিদিকে পরিষ্কার করার কথা, জানাত ওই দিন কী কী করবে। এখন আমি নিজেই ফোন করে ভাইদের মনে করিয়ে দিই যে ৩১ মার্চ সামনে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বাঁচেন ইতিহাসের পাতায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। তবে সেটাও নির্ভর করে বর্তমান ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর। বর্তমান আমেরিকায় সে দেশের ফাউন্ডিং ফাদাররা আগের মত আর পূজিত নন। লেনিন বিস্মৃতির আড়ালে চলে না গেলেও তাঁকে নিয়ে সোভিয়েত আমলের সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। গান্ধী বিতর্কিত। শেখ মুজিবের থাকা না-থাকাও নির্ভর করে দেশের ক্ষমতাসীন দলের মেজাজমর্জির ওপরে। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে কয়েক প্রজন্ম তাদের উত্তরসূরিদের স্মৃতিতে। একটা সময় যখন তাঁদের নিয়ে গল্প করার লোকেরা নাই হয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে মুছে যাবে তাঁদের স্মৃতি।
দুবনা, ৩১ মার্চ ২০২২
চিত্র: লেখক
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ২
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৩
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৪
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৫
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৬
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৮
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৯
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১০
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১১
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১২
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১৩
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১৪