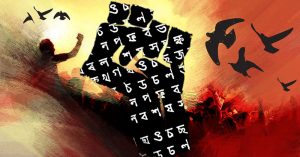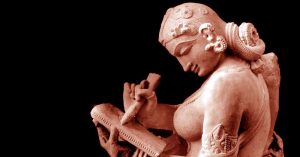পর্ব ৩
মাছের স্যুপ
কথায় আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। তবে যে কারণেই হোক দেশে থাকতে না ভাত, না মাছ কোনওটাই আমার প্রিয় ছিল না। মাছ খেতাম মাত্র কয়েক পদের— চিতল, রুই, কই, কাজলী আর বাতাসি। আমাকে নিয়ে মায়ের যে কত ঝামেলা ছিল। দুধ সহ্য হত না কখনওই। ফলে খাওয়াদাওয়া আমার জন্য ছিল সত্যিকারের পরীক্ষা। বাড়িতে রেগুলার ডিম থাকলেও মাংস হত কালেভদ্রে। জ্যাঠামশাই এসব পছন্দ করতেন না, তাই রান্না করা ছিল বিশাল ঝামেলা। উনি টের পেলেই সবার ‘শ্রাদ্ধ’ করে ছাড়তেন। তাই মা বাড়ির রাখালদের দিয়ে এসব রান্না করিয়ে নিতেন অনেক সময়। তবে মস্কো আসার পর এসব ঝামেলা কমে যায়। মাংস হয় প্রতিদিনের মেন্যু। সব্জিও নতুন করে সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তবে মাছটা আগের মতই অপ্রিয় থেকে যায়, যদিও ইদানীং কমবেশি খাই। মূলত সামুদ্রিক মাছ।
আমার ইচ্ছা ছিল পিএইচ.ডি থেসিস ডিফেন্ড করে দেশে ফিরে কাজ করব। তবে ১৯৯১ সালে বাবার মৃত্যু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, দ্বিধাবিভক্ত বাম রাজনীতি— এসব আমার সেই ইচ্ছের জোরটা কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। যদিও বেশ আগে থেকেই আমার সুপারভাইজার ইউরি পেত্রোভিচ রিবাকভ অন্তত কয়েক বছর হলেও দুবনায় কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলেছেন বেশ কয়েকবার, আমি সেটাকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু পিএইচ.ডি ডিফেন্ডের পরে ব্যক্তিজীবনে নতুন কিছু ঘটনা ঘটলে দুবনায় কিছুদিনের জন্যে হলেও কাজ করাটা অন্তত সেই পরিস্থিতির একটা সাময়িক সমাধান বলে মনে হল। আমি এবার সুপারভাইজারের শরণাপন্ন হলাম,
—ইউরি পেত্রোভিচ, এত দিন আপনি আমাকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দিয়েছেন, আমি চেষ্টা করেছি সেগুলো সমাধান করতে। এখন আমি নিজেই সমস্যায় পড়েছি। যদি দুবনায় কাজের ব্যাপারটা একটু দেখতে পারেন।
—দেখি কী করা যায়। আমার কোলাবোরেটর মাখানকভ কিছুদিন আগে আমেরিকা চলে গেছেন। অন্য কারও সাথে কথা বলতে হবে।
কয়েকদিন পরে ইউরি পেত্রোভিচকে ফোন করলে উনি জানতে চাইলেন ওখানে ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচ দুবোভিক নামে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে ইলেকট্রোডাইনামিক্সের ওপর কাজ করতে রাজি কিনা। এই সাবজেক্টে কাজ করার ইচ্ছে আমার কখনওই তেমন ছিল না। তখন পর্যন্ত আমার কাজকর্ম ছিল কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব আর কসমোলজির ওপরে। কিন্তু কী করা? বললাম তিনি যেন ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচের সঙ্গে কথা বলে নেন যাতে আমি একই সঙ্গে কসমোলজির ওপরেও কাজ চালিয়ে যেতে পারি।
আমি থেসিস ডিফেন্ড করলাম ১৯৯৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর। দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেল। ডিপ্লোমা ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছি, কিন্তু দুবনার নামগন্ধ নেই। তাই ইউরি পেত্রোভিচকে ফোন করে মনে করিয়ে দিলাম।
—আমি খুব ব্যস্ত। সময় একেবারেই বের করতে পারছি না। আমি বরং ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচকে ফোন করে দিই। তুমি নিজেই চলে যাও দুবনা। তার সাথে কথা বলো।
আমি রাজি হলাম। কয়েকদিন পরে ইউরি পেত্রোভিচ পরের সোমবার দুবনা যেতে বললেন। জানালেন সাভিওলভস্কি ভকজাল (রেলওয়ে স্টেশন) থেকে ভোর ৭টায় ট্রেন যায়। ওখানে নেমেই যেন ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচকে ফোন করি।
রাতে ঘুম হল না। ওই সময়ে ট্রেনের টিকেট পাওয়া খুব সহজ ছিল না। প্রায়ই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কিনতে হত। সোভিয়েত আমলে বিদেশিরা চাইলেই যেকোনও ট্রেনে যেতে পারত না। যদিও এখন জমানা বদলে গেছে, তবুও রিস্ক নিলাম না। তাছাড়া নব্বুইয়ের দশকে লোকাল ট্রেনে যাওয়াও তেমন নিরাপদ ছিল না, বিশেষ করে বিদেশিদের জন্য। তাই আমি খুব ভোরে উঠে রওনা হলাম সাভিওলভস্কি ভকজালের দিকে। মেট্রোর দরজা খোলে ভোর ৫.৪০-এ। এ সময় বাস খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই মিকলুখো মাকলায়ার হোস্টেল থেকে হেঁটে গেলাম মেট্রো ইউগো-জাপাদনায়া পর্যন্ত। মিনিট চল্লিশ পরে আমি ভকজালে এসে টিকেট কিনে বসে রইলাম ট্রেনের অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রমহিলা এলে জিজ্ঞেস করলাম দুবনার ট্রেনের কথা। ৪ বগির ছোট্ট একটা ট্রেন দেখিয়ে বললেন,
—ওই যে ছোট্ট ট্রেনটা, ওটাই দুবনা যাবে।
এটা ছিল এক্সপ্রেস ট্রেন। পথে কোথাও থামত না। লোকাল ট্রেনের টিকেটের দাম মাত্র ১২০০ রুবল, আর এই ট্রেনের ৫০০০। সে সময় পয়সার বড়ই অভাব, তবুও এ ট্রেনেই গেলাম। জীবনে এই প্রথম অনেকটা খেলনা ট্রেনে করে যাচ্ছি কোথাও। ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পরে এসে নামলাম দুবনায়। এটা শেষ স্টপ। খোলামেলা স্টেশন। অতি সাধারণ। জয়েন্ট ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ বলতেই লোকজন বলে দিল কোথায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে বললাম দুবোভিকের কথা।
—তাঁর ফোন নম্বর জানেন?
—হ্যাঁ।
—এই নিন, ফোন করুন।
বলে টেলিফোন সেট এগিয়ে দিলেন। মস্কোয় এমনটা কেউ করে না। একটু অবাকই হলাম। প্রথমেই তাঁর বাসায় ফোন করলাম। উনিই ফোন ধরলেন,
—ইউরি পেত্রোভিচ আমাকে বলেছেন, আমার বাসায় চলে আসুন। তারপর দেখি কী করা যায়।
ওঁর বলা ঠিকানামত বাসায় গিয়ে পৌঁছুলাম। তিনি তখন বাচ্চাদের জামাকাপড় পরাচ্ছিলেন কিন্ডার গার্টেনে দিয়ে আসবেন বলে। দুই বাচ্চাকে দুই জায়গায়।
—আপনি বসুন, আমি ওদের দিয়ে আসছি।
বলে এক বাচ্চাকে নিয়ে গেলেন এক স্কুলে, কিছুক্ষণ পরে এসে আরেক বাচ্চাকে নিয়ে গেলেন অন্য স্কুলে। ওঁর বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর। এত ছোট ছোট বাচ্চা দেখে অবাকই হলাম। তবে ভবিষ্যতের কাছে সেটা ছিল নস্যি। ২০০০ আর ২০০২ সালে ওঁর আরও দুটো সন্তান হয় তার চেয়েও ৩৫ বছরের ছোট নতুন বউয়ের গর্ভে।
বাচ্চাদের পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরেই বললেন,
—নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। চলুন খেয়ে নিই। উখা খান তো?
কিছু বলার আগেই এক প্লেট স্যুপ এগিয়ে দিলেন আমার সামনে। উখা হল মাছের স্যুপ। সেটা আমার জানা ছিল না। খেতে শুরু করে বুঝলাম এটা মাছের স্যুপ। আমি এমনিতেই মাছ তেমন খাই না, তার ওপর মাছের স্যুপ। আমার শরীর ঘামতে শুরু করেছে, কপালে একটু একটু ঘাম জমে গেছে। আসলে আমি না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলতে। একটু করে খাই আর ভাবি এই বুঝি সব উগরে ফেলব। জানি না, ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচ কী বুঝলেন, তবে মনে মনে হয়তো ভাবলেন, স্যুপটা মনে হয় তেমন সুস্বাদু হয়নি। বললেন,
—আপনাদের তো মশলা দিয়ে খাওয়ার অভ্যেস। যদি ভাল না লাগে রেখে দিন। চলুন আমরা এখন ল্যাবরেটরির দিকে যাই।
আমি যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। যদিও ভদ্রতার খাতিরে বললাম,
—না না, স্যুপটা বেশ টেস্টি, কিন্তু আমি মাছ খুব একটা খাই না, তাই…
খাবার নিয়ে আমার সমস্যা এটাই প্রথম নয়। সারা জীবনই আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে মায়ের অশান্তির শেষ ছিল না। এটা খাব না তো সেটা খাব না। বাড়িতে এসব মেনে নেওয়া যায়, তাই বলে বেড়াতে গিয়ে?
২০০৬ সালে ইতালি যাই মাসখানেকের জন্য। আমরা কয়েকজন মিলে এক অফিস শেয়ার করতাম থেওরেটিক্যাল ফিজিক্সের ইন্টারন্যশনাল সেন্টারে। একদিন বসে আছি, চিন দেশ থেকে আসা আমার কলিগ বলল,
—তোমার কাজ আমি জানি। নিজেও ইন্টারেস্টেড। চলো একটু কথা বলি।
আলাপের এক পর্যায়ে ও খেতে শুরু করল। ঝলমলে কাগজে মোড়ানো চকলেটের মত জিনিসগুলো ও মহানন্দে খেয়ে যাচ্ছিল। এক সময়ে আমাকেও অফার করল। আমি ভাবলাম এগুলো নিশ্চয়ই কোনও চকলেট বা টফি হবে। ওকে ধন্যবাদ বলেই সোজা মুখে চালান করে দিলাম। আমি একটু একটু করে বোঝার চেষ্টা করি কী খাচ্ছি। কারণ সেটা না মিষ্টি না ঝাল না টক না তেতো। এককথায় আমার বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এমন স্বাদ গ্রহণের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনওটাই আমার ঘটেনি। কয়েক মিনিট পরেও যখন বুঝতে পারলাম না খাবারটা আসলে কী, আমার মুখের ভেতর যেন একসঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, তেলাপোকা, বাদুড়, মানে বাঙালির কাছে যত ধরনের অখাদ্য আছে সব এসে ভিড় করল। ফেলার সুযোগ ছিল না, কারণ সেটা হত অভদ্রতা, আবার গিলতেও পারছিলাম না, কারণ যতই চিবুচ্ছি খাবারটা ততই রাবারের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভ্লাদিমির মিখাইলোভিচের মত এই বন্ধুও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল,
—শোনো, এসব আমাদের দেশের স্পেসিফিক খাবার। ভাল না লাগলে ফেলে দাও।
বলেই একটা ন্যাপকিন বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। সেদিন আর আমাদের কথা বলা হল না। পরেও হয়নি, কেননা ওই রাতেই ও পিকিং চলে যায়।
১৯৯৬ সালে আমার ফ্যামিলি দুবনা চলে এলে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে প্রায়ই মাছ খেত। কখনও মাছের স্যুপ অথবা লবণাক্ত কাঁচা মাছ। খাব কী, ওদের খেতে দেখেই আমার শরীর গুলিয়ে উঠত। তাই ওরা চেষ্টা করত, দুপুরে আমি যখন অফিসে থাকতাম তখন এসব খেতে।
পরে অবশ্য আমি ধীরে ধীরে মাছ খেতে শুরু করি, তবে এমনভাবে রান্না করি যেন মাছের গন্ধ তাতে না থাকে। অবশ্য এ বছরের শুরুতে যখন করোনা আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলাম তখন দু-একবার মাছের স্যুপ দিয়েছিল। বলতে বাধা নেই প্রচণ্ড তৃপ্তির সঙ্গে সেসব খেয়েছি। হয়তো প্রচণ্ড খিদে ছিল অথবা ভেবেছিলাম মৃত্যু যখন আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, সেখানে কী হবে এই মাছের ওপর গোঁসা করে! বলতে পারেন এটাও একটা পার্সোনাল করোনা পজিটিভ।
এবার ভাত নিয়ে দুটো কথা বলা যাক। ১৯৯১ সালে ভিসার জন্য গেলাম পোলিশ দূতাবাসে। অপেক্ষা করছি দূতাবাস খোলার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক ভারতীয় ছেলে। পোশাক দেখেই বোঝা যায় শিখ, তাই মনে হল ভারতীয়। অন্যদিক থেকে আসছে কেউ একজন— আমাদের উপমহাদেশের। সে সময় আমাদের এলাকা থেকে প্রচুর লোকজন সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে পশ্চিম ইউরোপে চলে যেত। হঠাৎ করেই সেই ছেলেটা শিখ ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরে বুঝলাম ও পাকিস্তানি। ভারতীয় দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। শুধুমাত্র এ কারণে বিদেশ-বিভুঁইয়ে একজন আরেকজনকে এভাবে আক্রমণ করতে পারে সেটা ভাবতেই পারিনি।
২০১৫ সালে গেলাম আবুধাবি, সেখানকার নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে একটা লেকচার দিতে। এয়ারপোর্টে নামতেই আমাকে রিসিভ করল আমাদের মতই দেখতে এক ছেলে। আরব দেশগুলোতে প্রচুর উপমহাদেশীয় লোকজন কাজ করে, তাই অবাক হইনি। কথা বলে জানলাম ও বাংলাদেশি। ও আমাকে অন্য একজনের হেফাজতে পৌঁছে দিল গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য। ঘটনাক্রমে সেই দ্বিতীয় জনও বাংলাদেশি। গাড়ির ড্রাইভারকে দেখেও আমাদের এলাকার লোক বলে মনে হওয়ায় জিজ্ঞেস করলাম ও বাংলাদেশ থেকে কিনা।
—না, আমি পাকিস্তান থেকে।
গল্পের এক পর্যায়ে জানাল ওরা জনা কুড়ি লোক একসঙ্গে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের।
—কেমন লাগে সবাই একসাথে থাকতে?
—এখানে আসার আগে ভারতীয়দের শত্রু মনে করতাম। এখন ওরাই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
—হ্যাঁ, দেশে ভেঙে, দেশ থেকে অনেক দূরে এসে বুঝি আমরা উপমহাদেশের লোকজন পরস্পরের শত্রু নেই। আমাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি।
—সে যা বলেছেন।
দেশে ভাত খুব একটা পছন্দ করতাম না। এমনকি এখানেও প্রথম দিকে নুডলস, গ্রেচকা এসবই তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম। এখন দু’দিন ভাত না খেলে মনে হয় কী যেন একটা মিস করছি। হ্যাঁ, দেশ থেকে অনেক দূরে এসে অনেক বছর পরে আবার ভেতো বাঙালি হয়ে গেছি।
(দুবনা, ০৭ ডিসেম্বর ২০২১)
কভার: মাছের মিছিল/ চিত্র: লেখক
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ২
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৪
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৫
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৬
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৭
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৮
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ৯
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১০
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১১
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১২
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১৩
রাশিয়ার চিরকুট পর্ব ১৪