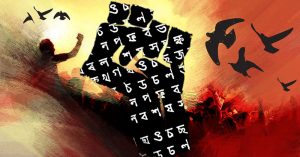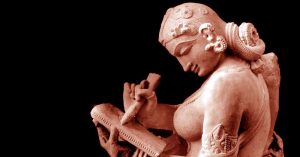পুরো নাম ছায়াছবি, ছোট করে ছবি। সেই ছবিকে আজকের স্তরে তুলে ধরতে যুগ যুগ ধরে মানুষের যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম জড়িয়ে আছে, তা ভাবতে বসলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এর পেছনে আছে কত সাফল্য, ব্যর্থতা, সুখদুঃখ ও নানান মজার কাহিনি। ছবির দুনিয়ার সেইসব অনবদ্য গল্পকাহিনি নিয়ে ধারাবাহিক ‘ছবিবৃত্তান্ত’।
দ্বিতীয় কিস্তি
ভিয়েনায় বসবাসকারী অস্ট্রিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বিতীয় রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট ফ্রানজ ফন উখাটিয়াস (১৮১১-১৮৮১) ১৮৫৩ সালে, কারচারের ম্যাজিক লণ্ঠন ও স্ট্যাম্পফারের স্ট্রোবোস্কোপিক ডিস্কের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিচ্ছবি প্রতিফলনের ব্যবস্থা করে ফেলেন, যার ফলে ফ্যান্টোস্কোপ যেমন একবার একজনই মাত্র দেখতে পেত, এটা অনেকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ পেল।
ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলের মন্ত্রিপুত্র উইলিয়াম জর্জ হর্নার (১৭৮৬-১৮৩৭) ফ্যান্টোস্কোপের আরও উন্নতিসাধন করেন, যে যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তা দেখালেন, তার নাম ডিডেলিয়াম (Daedaleum)।
১৮৪০ সালের মার্চ মাসে ওলকট প্রথম প্রতিকৃতি গ্রহণের স্টুডিও খোলেন। ১৮৪০ সালেই হাঙ্গেরির বৈজ্ঞানিক জোসেফ ম্যাক্স পেতভাল (১৮০৭-১৮৯১) ৩.৬ ফোকাসের লেন্স আবিষ্কার করে লেন্সের উন্নতিসাধন করেন আর এর সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামেরারও উন্নতি হয়।
১৮৪১-এ উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট তাঁর ক্যালোটাইপ (Calotype) পদ্ধতির পেটেন্ট নেন।
ফটোগ্রাফিতে পজিটিভ, নেগেটিভ শব্দগুলির প্রচলন করেন স্যার জন ফ্রেডেরিখ উইলিয়াম হার্শেল (১৭৯২-১৮৭১) ১৮৩৯ সালে। প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করার কাজে সোডিয়াম থায়োসালফেট (Sodium thiosulfate) ব্যবহার তিনিই প্রথম করেন।
১৮৩৯ সালেই আমেরিকান যন্ত্রবিদ আলেকজান্ডার ওলকট (১৮০৪-১৮৪৪) অবতল আয়নাযুক্ত ক্যামেরা তৈরি করেন, যা তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।
১৮৪৫ সালে জার্মানিতে শ্যনবিয়েন নাইট্রোসেলুলোজ আবিষ্কার করেন, যা থেকে প্লাস্টিক তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেয়।
১৮৬০ সালে দোভিনের (Desvignes) তৈরি উন্নতমানের ডিডেলিয়ামের নাম হল জোয়েট্রোপ বা জুট্রোপ (Zoetrope বা Zootrope)। একেই আবার ‘Wheel of Life’ বলা হত।
আমেরিকার কোলম্যান সেলারস্ তৈরি করেন কিনেমাটোস্কোপ (Kinematoscope)। গতির ক্রমান্বয় পর্যায়ের একের পর এক নিজের ছেলের ছবি তুললেন একটা সাধারণ twin lens ক্যামেরা দিয়ে। ছবিগুলিকে ঘনছক বা stereoscopic করে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
১৮৫১ সালে ইংল্যান্ডে আসে ফ্রেডরিখ স্কট আর্চারের (১৮১৩-১৮৫৭) কলোডিয়ান পদ্ধতি (collodion process) যা দ্যগিউর বা ট্যালবটের পদ্ধতির চেয়ে আরও উন্নত ও জনপ্রিয় ছিল। কাচের ওপর ছবি তুলে গতিশীল করার প্রচেষ্টা সত্যিই সময় ও খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, তাই পরবর্তী লক্ষ্য সেলুলয়েড।
 ১৮৫৬ সালে আলেকজান্ডার পার্কস নাইট্রো সেলুলোজ, ক্যাম্ফর ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে পারকেসাইট (parkesite) তৈরি করেন। তাঁর সহকর্মী ড্যানিয়েল স্পিল আরও উন্নত পর্যায়ের পারকেসাইট জাইলোনাইট (xylonite) তৈরি করেন আর এরই বিশেষ উন্নত অবস্থা সেলুলয়েড। জন ডব্লিউ হিয়াত আরচার-স্পিলের পদ্ধতির সমন্বয়ে সেলুলয়েডের যে প্রাথমিক অবস্থা আবিষ্কার করেন তা ১৮৬৯-এর ১৫ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট গ্যাজেটে পাইরোজাইলিন (pyroxylin) নামে পাওয়া যায়।
১৮৫৬ সালে আলেকজান্ডার পার্কস নাইট্রো সেলুলোজ, ক্যাম্ফর ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে পারকেসাইট (parkesite) তৈরি করেন। তাঁর সহকর্মী ড্যানিয়েল স্পিল আরও উন্নত পর্যায়ের পারকেসাইট জাইলোনাইট (xylonite) তৈরি করেন আর এরই বিশেষ উন্নত অবস্থা সেলুলয়েড। জন ডব্লিউ হিয়াত আরচার-স্পিলের পদ্ধতির সমন্বয়ে সেলুলয়েডের যে প্রাথমিক অবস্থা আবিষ্কার করেন তা ১৮৬৯-এর ১৫ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট গ্যাজেটে পাইরোজাইলিন (pyroxylin) নামে পাওয়া যায়।
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১ সেলারস কিনেমাটোস্কোপের পেটেন্ট নেন। গ্রিক শব্দ কিনেমার অর্থ গতি। ফিলাডেলফিয়ার হেনরি রেনো হেইল কিনেমাটোস্কোপের চেয়ে উন্নতমানের যন্ত্র ফ্যাসমাট্রোপ (phasmatrope) আবিষ্কার করেন। ১৮৭০-এর ৫ ফেব্রুয়ারি এই যন্ত্রের প্রদর্শনী হয়। হেইলই প্রথম ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করলেন। ক্যামেরায় তোলা ছবি জোয়েট্রোপ ধরনের যন্ত্রে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
১৮৭২-এর ২ জুলাই ‘Celluloid Manufacturing Company of Albany’ নামের মধ্যেই US Patent Gazette-এ প্রথম প্রথম সেলুলয়েড শব্দের উল্লেখ পাওযা যায়। সেলুলয়েডকে পুরোপুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সি এম ফেরিয়ার ১৮৫৭ সালে, লিওন ওয়ার্নারকে ১৮৭৫ সালে, থিয়েবল্ট ও ব্যালানি ১৮৮৩-তে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন।
১৮৮৪ সালে নমনীয় নেগেটিভ ফিল্ম চালু হয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর ১৮৮৬ সালে জর্জ ইস্টম্যান (১৮৫৪-১৯৩২) ও ডব্লিউ এইচ ওয়াকারের তৈরি ফিল্মে সেলুলয়েডের অবয়ব মেলে। জর্জ ইস্টম্যান ১৮৭৯ সালে যান্ত্রিক উপায়ে ফিল্মের ওপর রাসায়নিক প্রলেপ লাগান। ১৮৮৮ সালে স্বচ্ছ ফিল্ম তৈরি করে ওই বছরই বিশ্বের প্রথম রোল ফিল্ম ক্যামেরা ‘কোডাক’ উপহার দেন বিশ্ববাসীকে।
এদিকে ১৮৮৭ সালে রেভারেন্ড হ্যানিবেল গুডউইন (১৮২২-১৯০০) পাতলা, স্বচ্ছ, সেলুলয়েড ফিল্ম তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করার জন্য আবেদন করলেও তা পেতে সময় লেগে যায় প্রায় এগারো বছর, অর্থাৎ ১৮৯৮ সাল। কারণ ইস্টম্যান কোম্পানি ১৮৮৯ থেকেই ফিল্মের বাজারে প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। ফলে গুডউইন পেটেন্টের মালিক আনস্কো কোম্পানির সঙ্গে ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির আইনি যুদ্ধ শুরু হয়। যার নিষ্পত্তি ঘটে বারো বছর বাদে অর্থাৎ ১৯০১ সালে। ইস্টম্যান কোম্পানির পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে আনস্কোর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে।
শুরু হল পথচলা, তবে আরও পরে ১৯৩০ সালে সহজদাহ্য সেলুলয়েডের পরিবর্তে এল নিরাপদ সেলুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose Acetate)।
অবশ্য জন কারবাট নামে এক আমেরিকাবাসী ইংরেজও স্বচ্ছ সেলুলয়েড ফিল্ম তৈরি করেছিলেন।
১৯২৩-এ ১৬ মিমি ফিল্ম, ক্যামেরা, প্রজেক্টর ও রঙিন ছবি তৈরির ক্ষেত্রে ইস্টম্যান এক স্মরণীয় নাম।
চলমান ছবি তোলার ব্যাপারে ইংরেজ ফটোগ্রাফার এডওয়ার্ড জেমস মেব্রিজ (১৮৩০-১৯০৪)-এর নাম উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর লেল্যান্ড স্ট্যান্ডফোর্ড-এর। স্ট্যান্ডফোর্ড প্রমাণ করতে চান ছুটন্ত অবস্থায় ঘোড়া অন্তত কিছুক্ষণের জন্য শূন্যে অবস্থান করে।
১৮৭২-এ স্ট্যান্ডফোর্ড-এর অনুরোধে মেব্রিজ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাকরামেন্টো ঘোড়দৌড়ের মাঠে যান ছবি তুলতে, সবচেয়ে কম এক্সপোজার ১/১২ সেকেন্ডের মত সময়ের ওপর নির্ভরশীল এক ক্যামেরা নিয়ে। ফলে প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা সম্ভবই হল না। কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটা বছর।
স্ট্যান্ডফোর্ড দমবার পাত্র নন। তিনি জন ডি আইজ্যাক নামে ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহী এক ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে থমাস স্কেইফ নির্মিত একশো পাউন্ডের রবারের তৈরি শাটার-এর ১/১০০০ সেকেন্ডের ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন ক্যামেরার বৈদ্যুতিক চুম্বক দ্বারা শাটার ওঠানামার কাজ করিয়ে নেন আর মেব্রিজ পরপর ২৪টি ক্যামেরা রেখে গতিশীল ঘোড়ার ছবি তুললেন। তখনকার দিনে স্ট্রান্ডফোর্ডের খরচা হল চল্লিশ হাজার ডলারের মত। ছবির অ্যালবাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্ট্যান্ডফোর্ড এবং একদিন ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক জাঁ লুই মেসোনিয়ের-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। মেব্রিজের সঙ্গেও আলাপ হয় মেসোনিয়ের-এর। ক্রমান্বয়িক ছবিগুলোকে মেসোনিয়ের গতিসম্পন্ন করার জন্য ছবিগুলোর স্বচ্ছনকল (transparency) তৈরি করে জোয়েট্রোপ ধরনের মেশিনে দেখাবার ব্যবস্থা করেন।
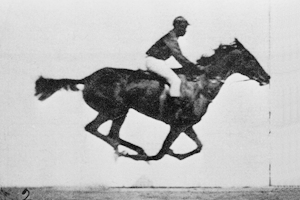
১৮৭৭ সালে ফ্রান্সে এম এমিলে রেনর্ড (১৮৪৪-১৯১৮) তাঁর প্র্যাক্সিনোস্কোপ (Praxinoscope) যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্চিত্রের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।
মেব্রিজের কাজে অনুপ্রাণিত হন ফ্রান্সের শারীরবিজ্ঞানী ই জে মারে (১৮৩০-১৯০৪)। তাঁর জ্যোর্তিবেত্তা বন্ধু পিয়ের জুলস সিজার জ্যানসেন ১৮৭৪ সালে যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের ছবি তোলার চেষ্টা করেন, তাকে আরও উন্নত করলেন মারে। সেটা দেখতে ছিল বন্দুকের মত। এই বন্দুকের ঘোড়া টানলেই গুলির বদলে নলের সামনে চলে আসত একটা বৃত্তাকার কাচের ওপর বসানো আলোক সংবেদনশীল নেগেটিভ। নলে বসানো লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত বিষয়বস্তুর ছবি গ্রহণ করেই অতিদ্রুত ঘুরে গিয়ে জায়গা করে দিত পরবর্তী নেগেটিভের। মনে হয়, এ থেকেই চলচ্চিত্র গ্রহণের প্রতিশব্দ ‘শুটিং’ চালু হয়।
জ্যানসেনের বন্দুকে সেকেন্ডে সত্তরটি ছবি তোলা সম্ভব ছিল। ১৮৮৭ সালে মারে এতে নমনীয় ফিল্ম (Paper Roll film) ব্যবহার করায় এর ক্ষমতা দাঁড়ায় সেকেন্ডে একশোখানা ছবি। ‘জুপ্র্যাক্সিস্কোপ (Zoopraxinicope) প্রক্ষেপণ যন্ত্রের পিতা হলে, মারের ক্যামেরাও ছিল আধুনিক মুভি ক্যামেরার প্রপিতামহ।’ উক্তিটি মারের।
থমাস আলভা এডিসন (১৮১৪-১৯৩১) ১৮৮৬ সালে নিউ ইয়র্কের Menlo Park ল্যাবরেটরিতে ফনোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। ইংল্যান্ডের এক তরুণ উইলিয়াম কেনেডি লরি ডিকশন (১৮৬০-১৯৩৫) এডিসনের সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে আবেদন জানালে, প্রথমে তা নাকচ হলেও শেষমেশ ডিকশনেরই জয় হয় ও দু-বছর পর ১৮৮৯ সালে এডিসনের ল্যাবরেটরির ইলেক্ট্রিক্যাল টেস্টিং বিভাগের প্রধান হন তিনি।
জার্মান বৈজ্ঞানিক আনশ্যুৎস (১৮৪৬-১৯০৭)-এর জোয়েট্রোপ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে ছবির ক্রমান্বয়িক পর্যায়ের প্রদর্শনে আলোর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ ধরনের (Geissler tube)। সরাসরি দেখার পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক হলেও প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ছিল না। তবুও জটিলতাভরা এই যন্ত্র ‘ত্যাচাইস্কোপ’ (Tachyscope) নামে বার্লিন, প্যারিস ও লন্ডনে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
এডিসনের ফনোগ্রাফে দু-ধরনের রেকর্ড ছিল। প্রথমে চোঙার আকারে সিলিন্ডার ও পরে চাকতির আকারে ডিস্ক। এই সিলিন্ডার রেকর্ডের ওপরই এডিসন ডিকশনকে চলমান ছবি গ্রহণ করতে বলেন। শব্দগ্রহণের সিলিন্ডার অব্যাহত গতিতে ঘুরলেও (চললেও) প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ব্যাপারটা সেভাবে সম্ভব হল না।
এডিসন সেকেন্ডে চল্লিশটা ছবি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যদিও ইতিমধ্যেই জানা গেছে সেকেন্ডে ষোলোটা ছবিই যথেষ্ট। সেকেন্ডে চল্লিশবার থেমে ও চলে যে ছবি ক্যামেরা গ্রহণ করল তার আকৃতি একটা লেড পেন্সিলের পিছনের পরিধির সমান। সিলিন্ডার মেশিনে ছবি উঠলেও তার মান ছিল অত্যন্ত খারাপ। এডিসনের স্টুডিওর এক মেকানিক ফ্রেড অট ছিলেন ক্যামেরার সামনে প্রথম অভিনেতা। পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে ফ্রেড অট-এর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
এর পেছনে একটা মজার গল্প আছে। অটের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা বিরাট সাদা কাপড়। কোমরে একটা বেল্ট আটকে সেটাকে ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দেখতে লাগছিল বেলুনের মত। অটকে বলা হয়েছিল বাঁদরের মত অঙ্গভঙ্গি করতে। সিলিন্ডারের গায়ে ছাপা হচ্ছিল অটের ছবি। বলা যেতে পারে, হাস্যরসের মধ্যে দিয়েই জন্ম হয়েছিল চলচ্চিত্রের। সালটা ১৮৮৮।
>>> ক্রমশ >>>
চিত্র : গুগল
ছবিবৃত্তান্ত প্রথম কিস্তি

ছবিবৃত্তান্ত তৃতীয় কিস্তি
ছবিবৃত্তান্ত চতুর্থ কিস্তি
ছবিবৃত্তান্ত পঞ্চম কিস্তি
ছবিবৃত্তান্ত ষষ্ঠ কিস্তি