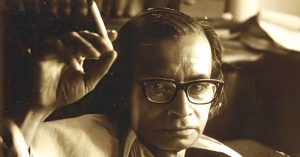দুশো টাকায় যখনতখন চলে, যাই দার্জিলিং।
কাল-ই টোটো স্ট্যান্ড থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল। ওপরে ওদের শোবার ঘর থেকেও। কাছের কালো পাহাড়ের রেখাগুলোর ওপারের সারিতে ধবধবে তুষার শৃঙ্গ, রোদে ধুইয়ে দিচ্ছে গা। পাহাড় নিয়ে কলকাতায় বসে যে রোমান্স ছিল, এখানে এসে বদলে গেছে। বাজারে, হাটে, অটো স্ট্যান্ডে, ছাদে, রান্নাঘরের জানলায় যখনতখন দেখা হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম, কুম্ভকর্ণ। আকাশ পরিষ্কার থাকলেই হল। কাল দার্জিলিং থেকে দেখলাম কাবরু সাউথ, কাবরু নর্থ, গোয়েচালা, রোটং, জোপুনো।
হিল কার্ট পেরিয়ে টার্ন নি, একঘেয়ে ছোট ছোট জানলা, কালো প্লাস্টিক মোড়া টব, অপরিসর অন্ধকার শীতার্ত ঘর, স্থির পর্দা। ঘিঞ্জি বস্তি। বিকেলবেলা কাঠের বালতি হাতে লেপচা মেয়ে শিস দিয়ে কুকুর ডাকে। কাঠের বাড়ি টিনের চালের এই টুংসুং, ভুটানি বস্তিতে থাকে শেরপারা। চ্যাপ্টা ঠোঁট, শক্তসমর্থ বেঁটে চেহারা, পাহাড়ি ভাল্লুকের মত হাঁটা, এক অদ্ভুত উপজাতি, পর্বতারোহীরা ছাড়া যাদের কেউ চেনে না। যাদের অসীম মনোবল, দক্ষতা, ঠান্ডা মাথা, দুর্জয় সাহসের ওপর ভর করে ফলে যায় বহু স্বপ্ন। মাইনাসের নীচে তাপমাত্রা, খুনি হিমপ্রপাত, হাঁ করা দানবের মত ক্রেভাস, হঠাৎ নেমে আসা মৃত্যুবাণ আভেলাঞ্জ, দড়ির ওপর ঝুলে থাকা অনিশ্চিত দেহ, খাড়াই সূতীক্ষ্ণ ঢাল, অক্সিজেনহীন পাতলা বাতাসের মারাত্মক মৃত্যু উপত্যকা পার করতে হাত বাড়ায় যারা, তাদের সবাই চেনে মালবাহক আর পথপ্রদর্শক বলেই।
তারা শেরপা। শেরপা কথার মানে পূর্ব দেশের মানুষ। মোঙ্গলের বংশধর। বহু বছর আগে তিব্বত থেকে গিরিপথ দিয়ে নেপালের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে শোলো খুম্বতে তারা এসেছিল। শোলো দক্ষিণের জেলা, অনেক উঁচুতে খুম্বু, রুক্ষ। এখানেই শেরপাদের গ্রাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোনও যোগ ছিল না। শোলো খুম্বুর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে দুধকোশী নদী। ভয়ংকর দুর্গম, গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা। শোলো খুম্বু রুক্ষ পাথরের বরফ জমাট দেশ। আদিম প্রকৃতি, ভেড়া ছাগল ইয়াক চরার তৃণভূমি। চোদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত চাষ হয় বার্লি আর আলু।
বিদেশি পর্বতারোহী আর এভারেস্টের কল্যাণে নামচে আজ পৃথিবী বিখ্যাত। এই উপত্যকার খুমজুং, পাংবোচে, ডামডাং, শাকসুম, শিমবুং ছড়ানো-ছিটানো সব গ্রাম। কাঠের ধোঁয়ায় ভরা অন্ধকার সব ঘর, ইয়াকের চর্বি জ্বলা প্রদীপ। কাঠের মেঝেতে গর্ত করা উনুনে টগবগ ফুটছে মাখন চা। নোনতা গন্ধে ভরে আছে ঘর। দিনে সাতশো বার চা খায় সবাই। রঙিন কার্পেট ঘেঁষে লোকজনের গুঞ্জন। পাশেই রাখা ডাঁই করা সেদ্ধ আলু। চিনামাটির পাত্রে লঙ্কা গুঁড়ো, নুন মেশানো। যখন পেটের টান খোসা ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে খেয়ে নিলেই হল। দোতলায় থাকে পরিবার আর নিচে লম্বা বড় প্রকোষ্ঠে পালিত পশুরা গাদাগাদি করে।
 সকালে ইয়াক চরানো, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর চলে যাওয়া, সন্ধ্যায় স্তিমিত অন্ধকারে ডোবা শীতার্ত গ্রামে সেঁকা মাংসের গন্ধে রাত নামে। ইয়াকের চামড়ার কম্বলে মুড়ে ঘুমোয় গোটা গ্রাম। পূর্ব পশ্চিম আর উত্তরে ঝুঁকে থাকে তুষারময় দানবের মত অচেনা পাহাড়ের সারি। দক্ষিণে দুধকোশী গ্রাম ছেড়ে উধাও গেছে জঙ্গলের মধ্যে। ব্যাস! এই তাদের জগৎ। এর বাইরে আর কিছু আছে শেরপারা জানত না।
সকালে ইয়াক চরানো, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর চলে যাওয়া, সন্ধ্যায় স্তিমিত অন্ধকারে ডোবা শীতার্ত গ্রামে সেঁকা মাংসের গন্ধে রাত নামে। ইয়াকের চামড়ার কম্বলে মুড়ে ঘুমোয় গোটা গ্রাম। পূর্ব পশ্চিম আর উত্তরে ঝুঁকে থাকে তুষারময় দানবের মত অচেনা পাহাড়ের সারি। দক্ষিণে দুধকোশী গ্রাম ছেড়ে উধাও গেছে জঙ্গলের মধ্যে। ব্যাস! এই তাদের জগৎ। এর বাইরে আর কিছু আছে শেরপারা জানত না।
তাদের বয়সের কোনও হিসেব নেই। শোলো খুম্বুর কোনও শেরপা শিশুরই নেই। সেখানে তো তিব্বতি ক্যালেন্ডার! সালের হিসেব নেই। বছরগুলো চলে পশুপাখির নাম ধরে। ছ’মাস পুরুষ প্রাণী, ছ’মাস স্ত্রী প্রাণীর নামে।
এভারেস্ট কী?
শেরপা শিশুরা ইয়াক চরাতে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখত উত্তরে ওটা চোমোলাংমা। কোনও পাখি ওটাকে টপকাতে পারে না।
উনিশশো একুশ বাইশ, তেইশ সালে বড় মাপের এভারেস্ট অভিযান হল। শোলো খুম্বু থেকে অনেক শেরপা গিয়েছিল। তারা ফিরে চিলিনাঙ্গাদের (দূর দেশের মানুষ) সম্পর্কে নানা মজার গল্প শোনাল। অদ্ভুত তাদের পোশাক জুতো। ভারী ভারী সব যন্ত্র, যা দিয়ে ফুসফুসে হাওয়া যায়। তখন কোথায় সেই নীলকণ্ঠের সংহারমূর্তি, প্রলয়নৃত্য।
এই গ্রাম থেকেই আঠেরো বছরে ঘর ছেড়েছিল তেনজিং। শোলো খুম্বু থেকে দার্জিলিং। উঁচুনীচু রাস্তা, কঠিন বাঁক, খরস্রোতা নদী, গভীর জঙ্গল, গিরিখাত, চূড়ান্ত কষ্টকর পথ। স্রেফ দুটো পয়সার জন্য। তখন কোথায় এভারেস্ট। পাহাড় মানে ভয়াল রহস্য মেশানো কৌতূহল, অপদেবতা ইয়েতি, অদ্ভুতদর্শন সব জানোয়ারের গল্পকথা।
শেরপা মানে কী?
নির্জন নিস্তব্ধ পৃথিবীর তুষারপথের অভিযাত্রী? মালবাহকের লম্বা মিছিল! নিত্যদিনের সঙ্গী ধুলো! তীব্র শ্বাসহীন ঠান্ডায় বরফে রোপ টাঙানো। তাঁবুর নিচে ফিরে আসা শ্রান্ত নিঃস্বপ্রায় দেহের দিকে গরম চা লেবু জল এগিয়ে দেওয়া! বেস ক্যাম্প থেকে সামিট ক্যাম্পে মাল তুলে দেওয়া?
না! সেই সৎ, বিবেচক মানুষ যারা পেছন ফিরতে জানে না। অভিযাত্রী যখন হ্যালুসিনেশন দেখে, বসে পড়ে বরফের দেওয়ালে পিঠ রেখে, চূড়ান্ত ঘুম পায় তার। তখন ঠেলে তুলে তাকে রওনা করায়। তাদের কাগজে নাম বেরোবে না, ছবি উঠবে না, টিভিতে ইন্টারভিউ হবে না। গ্রুপ ফোটোতে একটুখানি হাসিমুখ কুঁচকানো চোখ রয়ে যাবে। তারা এসেছে পয়সা রোজগার করতে। পায়ের তলায় বরফ তাদের পেশা।
কিন্তু শেরপা ছাড়া নীলকণ্ঠের সেই হলাহল পেরনো সম্ভব হয়নি কোনওদিন। এশিয়া মহাদেশের নেপাল ভূখণ্ডেই শেরপার বাস, পৃথিবীর আরও দেশের পর্বত অভিযানে শেরপা নামের টাইগারদের অস্তিত্ব নেই। তাদের এই উপাধিও ইউরোপীয়ানদের দেওয়া। ইমোশন, রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চারের তাড়না এসব তাদের অচেনা। তারা এসেছে সংসার চালাতে। নব্বই কেজি মাল হাই অল্টিটিউটে বইবার কোনও রোমান্স আছে কি?
স্ট্রাটেজি, পর্যবেক্ষণ, বরফের ধাপ কাটা, রোপ লাগানো, অক্সিজেনের ব্যবহার, জুতোয় ক্রাম্পন বাঁধা, এসব তাদের শিখতে হয়েছে বিদেশিদের থেকে। বাড়তি যেটা তাদের মাথায় ছেয়ে থাকে তা বরফের প্রতি নিরাসক্তি।
প্রথম দিকে অভিযানে শেরপাদের মালবাহক কুলির বেশি উৎকৃষ্ট পরিচয় ছিল না। ধীরে ধীরে বরফ-শার্দুলরা সম্মান আদায় করে নিয়েছে। তাদের সততা, সরলতা, মনোবল, দক্ষতা শেষ প্রাণবিন্দু দিয়ে সাহায্য করার মন। উদার চোমোলাংমার নীচে হিমেল তুষার হাওয়ায় তাদের মনে শহুরে নীচতা স্থান পায় না। একই দড়ির প্রান্তে ঝুলন্ত দুজন কমরেড ছাড়া বিশাল পাহাড়ের কাছে মানুষের আর কি পরিচয় হতে পারে।
ওঃ ওই লোকটা! আরে ওর তো তিনটে ফুসফুস। ও যতই ওপরে ওঠে ওকে তাজা দেখায়।
শোলো খুম্বুর বাড়ি থেকে পালানো সেই ছেলেটাই, সেই লোক। এভারেস্টম্যান তেনজিং। হাই অল্টিটিউটের মাথা ধরা, বমি ভাব, নিদ্রাহীন দুঃসহ রাত্রি তাকে কাহিল করে না।
আঠাশে মে, রাত্রি বেলা, ১৯৫৩ সাতাশ হাজার ন’শো ফুট উচ্চতায় দুজন মানুষ তাঁবুর মধ্যে। এত উঁচুতে কেউ কখনও শোয়নি এর আগে। গভীর রাতের চরাচর বিস্তৃত একাকিত্ব। নিদারুণ ঠান্ডা, অক্সিজেন ছাড়া অস্বস্তি, ঘুম আসে না। হিলারি জুতো খুলে শুয়েছেন, তেনজিং সব পরে। ঘণ্টাখানেক করে অক্সিজেন নিলেন দুজন। সকালে সামিট পুশ। একটু তো ঘুম চাই। দাওয়া থোন্ডুপ (সবচেয়ে বৃদ্ধ), তোপগে (মাত্র সতেরো), আং নরবু, আং পেম্বা, আং নিমা, আনুলু, দা নামগিয়ান সকলে বীর সৈনিকের মত ধাপ কেটে, দড়ি লাগিয়ে নীচে নেমে গেছে। হাওয়ার বেগ ভয়ংকর।
ভোরের আলো ফুটতে নীচে বহুদূরে থিয়াংবোচি মঠ নজরে এল। ওইখানে শেরপা তেনজিং-এর মা বাবা পুজো করে। ওই তার বাড়ির রাস্তা। হিলারির জুতো দুখণ্ড শক্ত লোহার টুকরোর মত পড়ে আছে। দুঘণ্টা ধরে স্টোভ জ্বেলে গরম করে তেনজিং। তারপর যাত্রা। আরও সাতশো ফুট বাকি। বিস্তৃত ঢেউ খেলানো বরফের প্রান্তর, পর পর ঢিবি। তারপর ইতিহাস।
কে উঠেছে আগে? তেনজিং না হিলারি? সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে পলিটিক্স। দরিদ্র এশিয়ান লোকটার কৃতিত্ব খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে। সে নাকি মাছের মত খাবি খাচ্ছিল, হিলারি তাকে টেনে তুলেছে। সাংবাদিকরা হাজার বার প্রশ্ন করেছে, কে আগে? কেমন অনুভূতি?
সেই নিরক্ষর মানুষটি, যে ছোট থেকে একটাও বই দেখেনি। শোলো খুম্বুতে ইয়াক চরিয়েছে সতেরো বছর অবধি, এমনকী শেরপাদের নিজস্ব কোনও লিপি নেই, বর্ণমালা নেই। গোষ্ঠীগত পরিচয় খাংলা অর্থাৎ তুষার ঢাকা গিরিবর্ত। একটাই উত্তর সে দিয়েছিল, এভারেস্ট শীর্ষে মেয়ের দেওয়া লাল নীল পেন্সিল রাখার সময় যা বলেছিল উনত্রিশে মে শুক্রবার ১৯৫৩ সালে ‘’থুজি চে’ চোমোলোংমা’’… আমি ধন্য। আর কে উঠেছে? মানুষ!
দার্জিলিং। বসন্ত কাল। খাদের দিকে নেমে গেছে পাইনের দীর্ঘ ছায়া। চক বাজার থেকে হল্লা উঠে আসছে। কুয়াশা গলে আসা হালকা আলো এসে পড়েছে হিমালয়ান ইন্সটিটিউটের কাচের জানলায়। আমার অতিকায় মাথা নড়ছে কাচে। সামনে শো-কেসে তাকিয়ে থাকি। তেনজিং-এর বউয়ের হাতে বোনা কবেকার সেই ফুটিফাটা জীর্ণ মোজা। সুইস অভিযাত্রী বন্ধু ল্যাম্বার্টের দেওয়া ঐতিহাসিক লাল মাফলার। সুইসদের দেওয়া জুতো। ইংরেজদের দেওয়া জ্যাকেট, ডেনম্যানের ফেলে যাওয়া সেই হনুমান টুপি। কাচের বাতির তলায় শুয়ে আছে সেই আইস অ্যাক্স, যা দিয়ে তেনজিং বরফ খুঁড়েছিল। শিরশির করে মন, বহু দূর থেকে বরফ ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগে। ল্যাম্বার্টের ছবি দেখি ফ্রস্ট বাইটে অর্ধেক কাটা পা নিয়ে যে পাহাড়ি ছাগলের মত ওপরে চড়ত।
বিকেল নেমে আসে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ব্লিজার্ডের সাদা ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে। একরাশ রোদ এসে ঢেকে দিল পাইন বনের রোদেলা আকাশ। নিচে নামি। শিলিগুড়ি, কার্শিয়ং, গাড়ি হাঁকছে, তেনজিং রক থেকে তেনজিং দেখছে তার যৌবনের শহরকে, আলুবাড়ির মানবাহাদুর তামাংয়ের থেকে নেপালি শেখা, ছাং খেয়ে হাসাহাসির দিন।
সুমিতাদের নেপালের বাড়ির রান্নাঘরের জানলা দিয়ে এভারেস্ট দেখা যায়। এই বিশাল পর্বতশ্রেণির অজ্ঞাত দুর্গম গহীন সীমানার একটুখানি অংশ বহুদূর থেকে দৃশ্যমান, আমার জানলাতেও এসে দেখা দিয়ে যায়…।
এভারেস্ট ঘিরে এখন লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা। পৃথিবীর সব দেশের স্বপ্ন দেখা মানুষের পাখির চোখ। সিজনে লম্বা ট্র্যাফিক জ্যাম। শেরপাদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ। কম অক্সিজেন, অভিযাত্রীকে তারা বিপদে ফেলে পালায়। সময়মত অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় না, এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি দোষারোপ। আসলে কমার্স এলে কাঁচা রোমান্স উবে যায়। তেনজিংয়ের সময় আর নেই। প্রাণ হাতে করা একটা অভিযান থেকে যত বেশি অর্থ পাওয়া যায় ততই সংসারের সিকিউরিটি। পরিবার চায় না বার বার মৃত্যুর ভয়াল সম্ভাবনার দড়িতে ঝুলে টাকা আসুক। শেরপাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে চায়। চাকরি করতে চায়।
কোনও শেরপা গ্রামে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় যখন কারও বরফে খুঁজে পাওয়া টুপি, কিংবা একটা ছেঁড়া সোয়েটার ফিরে আসত, খুনখুনে কোনও বৃদ্ধ তা সনাক্ত করত। উদাস মুখ ঘুরিয়ে নিত প্রতিবেশী তাউ। ‘‘হ্যাঁ এ তো আমাদের ছেলে পাহাড়ে ঘুমোচ্ছে।’’ কচি ছেলেমেয়ের দল বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকত।
বিস্ময় কি মরে গেছে? ঘরে বসে রোমহর্ষ সবই তো সাপ্লাই হয় ইউটিউবে। গুগল আছে জেনে নেব, পাখির ডাক, বরফের তাপ, রেলগাড়ির দূর শব্দ, আমাজনে কোন ফুল ফুটে আছে।
কে জানে কবে শুনব চূড়ায় কে চপ-ফুলুরির দোকান দিয়েছে। অভিযাত্রীরা দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কচুরি খাচ্ছে। সম্ভব সবই।
পাহাড় আজও দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় পোকা থাকলে এসো। “আমি পারিনি তুমি যাও”। ধাপ কেটে এসেছি, দড়ি বেঁধে রেখেছি।