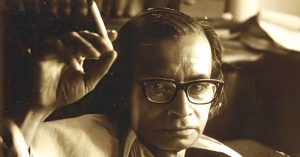বড়পিসিকে আমরা পিসিমণি বলতাম। তাঁর ছেলেমেয়েদের ডাকা হত বড়দা, ছোটদা, বড়দি আর ছোটদি বলে। কিছুদিন আগে ছোটদা মারা গেছেন, বছর-পঞ্চাশেক বয়সে। আজ ছোটদি ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই। ছোটদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পুরনো দিনের অনেক গল্প বাইরে এল আর সেই গল্পের অনেকখানি জুড়ে ছোটদার কথা। ছোটদা, বাংলার একসময়ের নামী ফুটবল খেলোয়াড় অলোক মুখার্জি। জন্মেছেন গত শতকের ষাটের দশকে। তাঁদের শৈশব-বাল্য-কৈশোর কাল আজকের মত একবারেই ছিল না। ছোটদার প্রসঙ্গ, ছোটদার ছোটবেলার গল্পে তাঁর সখা গোপীনাথ থাকবে না, তাই কি হয়? সেই গোপীনাথ বা গোপীদার দুষ্টুমি ও মজার গল্প বলতেই ধারাবাহিক ‘ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ’।
সপ্তম কিস্তি
আমরা প্রায়ই শিক্ষাব্যবস্থার ক্রম নিম্নগামী স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করি। লর্ড মেকলের দৌলতে, সেই যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার যাত্রা শুরু হল, তা আজও বহমান আছে। ইংরেজরা তখন ভারতে কব্জা জমিয়েছে, তাই নিজেদের ‘বেস্ট ইন্টারেস্ট’ তারা ভাববে সেটাই স্বাভাবিক। আর সেই জন্যেই লর্ড মেকলের মনে হয়েছিল, ভারতবাসীকে নিজেদের হিসেবে চালাতে হলে, নিজেদের দেশের অর্থাৎ ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাটা এদেশে লাগু করা দরকার। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বদলেছে। আমরা সেই কবেই স্বাধীন হয়েছি। আমাদের মনে হয়নি যে, ইংরেজ প্রদত্ত সেই শিক্ষাব্যবস্থারও এবার আমূল পরিবর্তন দরকার। সেই পরিবর্তনটাই আগামী দিনে ভারতবাসীর ‘স্ট্যান্ড’ তৈরি করবে। আসলে এই পরিবর্তনটা যে চাই, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা কার্যকরী করার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
না, না, তোমরা এত তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ো না! তোমাদের ‘বোর’ করার এতটুকুও ইচ্ছে আমার নেই। আসলে কী জানো, সুযোগ পেলেই একবার বিষয়টা নিয়ে আসি, যাতে চর্চাটা আবার করে এদিক-ওদিক পৌঁছয়। পরিবর্তনটা যে বড্ড জরুরি হয়ে পড়েছে। নইলে আমাদের ছেলেপুলেরাও সেই একধরনের ‘ক্লার্কি’ করেই জীবন কাটাবে। আমরা সব মোটা মাইনের চাকর হবার স্বপ্ন ছাড়া আর অন্য স্বপ্নের কথা ভাবতেও ভুলে গেছি। উঃ! আবার আমার কথাই বলে যাচ্ছি। সরি, সরি! এবার আমি চুপ করলাম। তোমাদের আদরের জনদের আনি!
তোমরা আজ যেমন সিস্টেমে পড়াশোনা করো, আমরাও তেমনই পড়াশোনা করেছি। তফাত শুধু এই যে, তখন অনলাইন ছিল না, মোবাইল ছিল না, গুগল ছিল না, তাই কপি-পেস্টও ছিল না! আমাদের কষ্ট করে, নড়েচড়ে, লাইব্রেরিতে যেতে হত, আর দু-পাঁচটা বইয়ের পাতা খুলে ইনফরমেশন বের করতে হত। প্রশ্ন-উত্তর লেখা, পড়া, তাকে পরীক্ষার খাতায় উতরোনো বা ওগলানো, সব প্রায় সেম টু সেম! আমি বলতাম, পেনস্থ, খাতাস্থ, মুখস্থ, মনস্থ আর ব্রেনস্থ— এই পর্যায়ে প্রসিড করতে হবে!
ষাটের দশক পেরিয়ে, সত্তরের দশক সত্বর শুরু হয়ে গেল। ‘পূর্ব রেলওয়ে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়’, এই স্কুলটাতেই ছোটদারা পড়েছে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। তারপর, সদলবলে বেলুড় স্কুলে শিফট। কারণ লিলুয়ার ওই রেলের স্কুল তখন ক্লাস সেভেন পর্যন্তই ছিল। ছোটদারা তখন সেভেনে পড়ে। মানে রেলের স্কুলে (চলিত কথায় রেলের স্কুলই বলা হত স্কুলটাকে) সেটাই ওদের লাস্ট ইয়ার। ছোটদারা, মানে ছোটদা, রাজা, পার্থ, রানা, গৌতম, পল্টু, অখিলেশ— এরা সব, আর ও হ্যাঁ, গোপীনাথও! এই দেখো, এইবার সব হাসি ফুটেছে! আছে বাবা, আছে! এই গল্পেও গোপীনাথ আছে।
স্কুলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা আসছে। এ বছর সব গোড়া থেকেই ভাল রেজাল্ট করার প্রেসার আছে। নইলে অন্য স্কুলে নেবে কী নেবে না তাতে একটা প্রশ্নচিহ্ন আসার চান্স! আর এ প্রশ্নচিহ্ন এলে, পিঠেও দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, সব চিহ্নের ছাপ বাড়ির লোকেরাই পিটিয়ে পিটিয়ে বসিয়ে দেবে। আর এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নচিহ্ন নেই!
অনেক বাচ্চাই তখন হাফ ইয়ারলি না বলে চলতি কথায় ‘হাপিয়ারলি’ বলত। গোপীনাথও তার ব্যতিক্রম ছিল না। পরীক্ষার আর মাত্র ক’দিন বাকি। গোপী বলল, ‘মাইরি এই হাপিয়ারলিটা সব হ্যাপিনেস আর্লি খতম করে দিচ্ছে! আর তো আর হাঁপিয়ে দিল হতচ্ছাড়া!’ বাকিরাও সুরে সুর মেলাল। গোপী বলল, ‘পড়াশোনা আবিষ্কার করল ঠিক আছে। মা সরস্বতীর আশীব্বাদ। কিন্তু এই পরীক্ষাটাকে, কে আবিষ্কার করেছে বল তো?’
ঝট করে পার্থ বলল, ‘হেনরি মিশেল, আমেরিকান।’
অ্যাঁ! সবারই এক এক্সপ্রেশন!
জবাব পার্থর, ‘‘ওই ‘জেনে নাও মনে রাখো’-তে পড়লাম।’’
গোপী একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, ‘দিস ম্যান, খতম করল আওয়ার লাইফ।’
পার্থ আবার বলল, ‘স্পয়েল্ট!’
‘কী?’, গোপীর প্রশ্ন।
রাজা বলল, ‘‘পার্থ বলছে, ‘দিস ম্যান স্পয়েল্ট দ্য জয় অফ আওয়ার লাইফ’।’’
পার্থ শোধরাল, ‘হ্যাজ স্পয়েল্ট, বললে পুরো কারেক্ট হবে।’
গোপীর জবাব, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিও তাই-ই বলেছি। এই রাজা, আগ বাড়িয়ে টপকে পড়াটা কবে তোর বন্ধ হবে রে? সবজান্তা এলেন!’
রাজা চুপ করে গেল। গোপী আবার বলল, ‘আম পর্যন্ত ফলাতে জানে কিনা সন্দেহ! অথচ নাম দেখ! আমেরিকা! জীবনটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিল, এই পরীক্ষা চালু করে।’
রানা জানাল, ‘ভাই, দুদিন আমি স্কুল আসব না ভাবছি। বইগুলো সবই নতুন লাগছে। এক-আধবার না ঝালালে পরীক্ষায় পুরো কেলো হওয়া সুনিশ্চিত।’
এবার পল্টুর পালা, ডাইরেক্ট রানাকে, ‘হ্যাঁ দুদিন পড়ে তুই উল্টে দিবি!’
গোপীনাথ বাধা দিল। ‘আঃ মেলা বকিস না। মন যদি মা সরস্বতীতে যায়, যাক না! তবে দুদিনে পুরো চেনাশোনা হওয়া অসম্ভব।’
ছোটদা বলল, ‘কার চেনাশোনা গোপী?’
গোপীনাথ জবাব দিল, ‘এটার মাথাটা গেছে! আরে বাবা, মা সরস্বতীর সঙ্গে চেনাশোনার কথা বলছি। রানা দু’দিনে মা বাগ্-দেবীকে কতটা বাগে আনতে পারবে, তাই ভাবছি।’
সবার নজর গেল পার্থর দিকে। পার্থ, অখিলেশ এরা সব ক্লাসের ভাল ছেলে। মানে, পড়াশোনায় ভাল এরা। গোপী বলল, ‘দেখো গুরু, সুযোগ পেলে দুর্দিনে একটু দেখো।’
রাজা বলল, ‘স্কুলের টিচার সব যা তা প্ল্যান করে! পরীক্ষার সিট নম্বর এমন হয় যে, অখিলেশ আর পার্থ একই ঘরে বসে।’
গোপীনাথ পুরোদমে সায় দিল, ‘ঠিক বলেছিস। একটু ফেলে-ছড়িয়ে সিট নম্বর করুন। পার্থ আর অখিলেশকে আলাদা ঘরে বসান, যাতে করে দু-দুটো রুমের গরিবদের উপকার হয়। আমি পড়াশোনায় গরিবদের কথা বলছি! তা নয়, দু-দুটো পাকা মাথাকে এক ঘরে বসিয়ে দেবে! আমাদেরও স্পিকটি নট্ বলবে! ঘেন্না ধরে গেল ভাই!’
চর্চা যতই চলুক, পরীক্ষা সময়েই চালু হল। মাঝে ছুটি বেশি নেই। শুধু অংক আর সংস্কৃতর আগে এক-এক দিন ছুটি। সায়েন্সের আগে ন্যাচারাল ছুটি এসেছে, মানে রবিবার পড়েছে। পরীক্ষার ক’টা দিন বই নিয়ে বসার কথা কাউকে তেমন বলতে হচ্ছে না। নিজেরাই মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই যে! দুদিনে আর কত হয়! মাথা-ফাথা সব গুলিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। যতই বলা হোক, ক্লাস টেন পর্যন্ত ‘হাতের পাঁচটা আঙুল সমান’ প্রবাদে বিশ্বাস করে, পড়ার সব সাবজেক্টকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে; এটা সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কেউ একটা বিষয় পছন্দ করে, তো অন্যজন আর একটা। আবার কেউ কেউ কোনওটাকেই নয়। এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই হয়তো ‘ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল, অংকেতে মাথা নেই, হয়েছি পাগল’ লাইনগুলো এসেছে!
জোর দমে পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার শেষে ছেলেপুলেদের আলোচনাগুলোও একই ধরনের লাগতে শুরু করেছে। এই যেমন, ‘আজ ধ্যাড়ালি, না ঠিকঠাক’, ‘আজ কড়া গার্ড পড়েছিল ভাই’, ‘আজ গুরু সব কমন এসেছিল’, ‘আজ ক’টা পাতা নিলি’ ইত্যাদি।
আজ ভূগোল পরীক্ষা। পরীক্ষার হল। খাতায় মাথা গুঁজে সব লিখছে। ভূগোল ব্যাপারটা একটু গোলমেলে লাগে গোপীনাথের। রাম, শ্যাম, যদুকে জিজ্ঞেস করে উত্তর লিখছে গোপী। রানা ফিসফিসিয়ে বলল, ‘গোপী, তুই কি কাল কিছুই পড়িসনি?’
গোপী জবাব দিতে পিছপা হল না। বলল, ‘জানি আমি সব। শুধু একটু কনফার্ম করে নিচ্ছি।’
একটা প্রশ্নে এসে কেমন যেন মাথাটা গুলিয়ে গেল গোপীনাথের। প্রশ্ন এসেছে, ‘পশ্চিম বাংলার কোথায় কয়লার খনি আছে?’ এদিকে গার্ড বদল হল। দত্ত স্যার গেলেন আর ফণীবাবু এলেন। ‘এই মেরেছে! এ ব্যাটা ঘাড় ঘোরাতেই দেবে না। কথা বলা তো দূরে থাক!’, ভাবল গোপী। কয়লার খনি কোথায় আছে? কোথায় আছে? কিছুতেই মাথায় আসছে না। গোপী বুঝে গেল, কয়লার খনি আর যেখানেই থাকুক, আপাতত সেটা মাথায় নেই! ‘প্রশ্নটা ছেড়ে দেব? না, না সেটা ঠিক হবে না’, মনে হল গোপীর। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, গোপী আরও একবার প্রশ্নটাকে ভাল করে পড়ল। ‘পশ্চিম বাংলার কোথায় কয়লা খনি আছে?’ তারপর সরসর করে খাতার পাতায় উত্তর লিখে দিল, ‘কানুদার গোলায়।’
কানুদার কয়লার গোলাটা ঠিক রেল কলোনির পাঁচিল পেরিয়েই। মানে পশ্চিম বাংলাতে পড়ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর বেলুড়, লিলুয়ার ঘরে ঘরে ওই কানুদার গোলার সাপ্লাই করা কয়লাতেই উনুন জ্বলে রোজ। অতএব এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর হতেই পারে না। নাঃ! এই প্রশ্নে আর বেশি সময় দেওয়া যাবে না। প্রশ্নপত্র পুরো শেষ করাতে মন দিল গোপী। ফণীবাবু গেলেন, কারণ দত্তবাবু আবার এসে পড়েছেন। কলম সব আরও গতি পাকড়েছে। শেষ ঘণ্টা বাজতে আর বেশি সময় নেই।
সময়ের সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত সখ্যতা। সে কেমন করে যায়, কেমন করে আসে, কখন যেন বসে, সব আমার নখদর্পণে! তাই আর বেশি না বলে, শুধু বলি, পরীক্ষা শেষ হয়ে বেশ ক’দিন কেটেও গেছে। গোপী, ছোটদা, রাজা, পল্টু তো ঠিকই করেছে সাত দিন আর বই ছোঁবে না। গোপী বলল, ‘মা সরস্বতী হাঁপিয়ে গেছেন। ক’টা দিন তাঁকে বিশ্রাম না দিলে মহা পাপ হবে।’
পার্থ একবার বলার চেষ্টা করেছিল, ‘ওরে গোপী, এটা সবে half-yearly…’, কিন্তু গোপী তাতে পাত্তা দেয়নি।
‘মা ছানাপোনাদের খেয়াল রেখেছেন। সাদা খাতা জমা করতে দেননি পরীক্ষায়। তাই ছানাপোনাদেরও উচিত মায়ের খেয়াল রাখা’, স্পষ্ট জবাব গোপীর। বলাই বাহুল্য, এই ব্যাপারে গোপীনাথের যুক্তির সাপোর্টারের অভাব হল না!
খাতা দেখানো চলছে। আজকালকার মত তখন এত প্যারেন্ট-টিচার মিটিংয়ের আধিক্য ছিল না। দাস স্যার ক্লাসে এলেন। দাস স্যারকে আমরাও দেখেছি। ঘন শ্যামবর্ণ। গোলগাল। মাথায় টাক। ইংরেজির আট মানে এইট-এর কথা মনে পড়ে যায়। না না, ছিঃ ছিঃ, এমন বলা মানে বডি শ্যামিং-কে প্রশ্রয় দেওয়া। এটা আমি কোনওদিনও সমর্থন করি না। বড় ভালমানুষ ছিলেন দাস স্যার। বকাঝকা মুখে যতই হোক, ফেয়ারওয়েলের দিন যখন বলেছিলেন, ‘সবই তোদের ভালর জন্য বলা’, জানি না কেন চোখে জল এসে গিয়েছিল।
যাইহোক, ক’দিন হল খাতা দেখানো শুরু হয়েছে। আজ ভূগোল খাতা দেখানো হবে। গোপীনাথের হাতে তখনও খাতা পৌঁছয়নি। গোপীনাথ শুরুতেই জিজ্ঞেস করে বসল, ‘স্যার, ভূগোলে আমি কত পেয়েছি?’
দাস স্যারের নজর গেল গোপীর দিকে। ‘তুই কত পেয়েছিস, সে আমি পরে বলছি। আগে তুই কি উত্তর লিখেছিস, সেটা পড়ে শোনাই।’
সবাই নিজেদের খাতা দেখা বন্ধ করে স্যারের দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন, গোপী কী এমন উত্তর লিখেছে যা স্যার পড়ে শোনাতে চান? ছোটদা সুনিশ্চিত, ‘গোপী নিশ্চয়ই একটা বড় ক্যাঁচাল করেছে!’
স্যার একটু সময় নিলেন। সড়সড় করে স্যারের আঙুল গোপীর খাতার এ পাতা থেকে ও পাতায় যাচ্ছে। তারপর একটা বিশেষ জায়গায় এসে ওঁর আঙুল থামল। উনি পড়তে শুরু করলেন, ‘পশ্চিম বাংলার অনেক জায়গাতেই কয়লার খনি আছে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, কানুদার গোলা।’ স্যার গোপীর পরীক্ষার খাতার পাতা থেকে চোখ তুললেন। পুরো ক্লাসকে শুধোলেন, ‘বল রে, বইতে আছে কয়লা খনি কানুদার গোলা?’ বেশিরভাগ ছাত্রই ফিক ফিক করে হাসছে।
গোপীর আত্মসম্মানে লাগল। সে স্যারের কাছ থেকে খাতা নিতে নিতে জোর দিয়ে বলল, ‘স্যার, আপনি সঙ্গে চলুন। গোলা আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। শুধু তা-ই নয়, সেখানে আপনাকে ঘরের মত বসিয়ে চা খাইয়ে দেব।’
স্যার বললেন, ‘আজ তুই চারটে পর্যন্ত বাইরে দাঁড়াবি গোপীনাথ। কাল তোর বাড়ি থেকে আমি গার্জেন ডেকে পাঠাব।’
গোপী মনে ভাবল, ‘বাড়ির লোককে আবার এর মধ্যে টানা কেন?’ আর মুখে বলল, ‘স্যার, আমরা যা জানি, যা আমরা চোখে দেখছি, তাই লিখেছি।’
দাস স্যার বললেন, ‘বাঁদর ছেলে, বেরো ক্লাস থেকে।’ গোপী চটপট বই গোছাতে শুরু করল।
ছোটদা জিজ্ঞেস করল, ‘এই গোপী, কী করছিস?’
গোপী বলল, ‘বই বেঁধে রাখছি। আজ আর কোনও ক্লাস করব না। বাইরে দাঁড়িয়ে দ্যাখ না কী করি!’ কথাগুলো বলতে বলতে খাতা থেকে বেশ ক’টা পাতা ছিঁড়ে পকেটে পুরল গোপী। স্যারকে ‘সরি’ বা ‘আজ ছেড়ে দিন না স্যার’, বললেই গোপীকে আর বাইরে যেতে হত না। কিন্তু গোপীর আজ আর ক্লাসে থাকার ইচ্ছে ছিল না। তাই স্যারের টেবিলে পরীক্ষার খাতা জমা করে, গটগট করে গোপী ক্লাসের বাইরে চলে গেল। স্যার দেখতে থাকলেন। বাকি ছেলেপুলেরা খাতা দেখছে। নম্বর বারবার যোগ করছে। ফাঁকফোকর দিয়ে একটু নম্বর বাড়ানো যায় কিনা সেই চেষ্টা করছে।
অখিলেশকে স্যার বললেন, ‘ওরে খাতাগুলো এবার জমা করে, আমায় দে।’ অখিলেশ কাজে লেগে গেল। ওদিকে গোপীনাথ বাইরে থেকে, ক্লাসে বসা বাকিদের লাগাতার কিল-চড়ের ইশারা করছে। স্যার না দেখলেই বসে পড়ছে। এখনও পর্যন্ত যে ক’টা খাতা দেখানো হয়েছে সেগুলোর নম্বরগুলো মনে মনে গুনল গোপী। নাঃ কোনক্রমে ছিটকে ওপারে উতরেছে! বাঁচা গেল! আরও একটা খাতা দেখানো বাকি আছে। ‘আমি পাশ’, ভাবামাত্র, নিশ্চিন্ত গোপী, পকেট থেকে দুটো ছেঁড়া খাতার পাতার গোলা বানাল। স্যারের নজর অন্যদিকে দেখেই, গোপী ওই কাগজের বল সিধে টার্গেট করল স্যারের টাকে। মাথায় না লেগে একটুর জন্য কাগজের ওই বল, স্যারের গা ঘেঁষে মাটিতে পড়ল।
স্যার বললেন, ‘এটা কোত্থেকে এল?’ বাকিরা সব চুপ। টাকে ডায়রেক্ট না লাগায় স্যারও আর কথা বাড়ালেন না। ঘণ্টা বাজল। স্যার খাতাপত্র নিয়ে ক্লাস থেকে বের হচ্ছেন। গোপীনাথ চুপচাপ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। স্যার যাবার সময় বললেন, ‘যা ভেতরে যা। কী যে করিস তুই গোপীনাথ! পড়াশোনায় একটু মন দে।’ গোপী ঘাড় নেড়ে ক্লাসের ভেতর ঢুকে গেল। আবার উদোম শুরু!
যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সে কথার খেই ধরে চট করে বলে ফেলি যে, আমি অনেকবার ভাবি, এমন তুখোড়, তেজ-তর্রাট ছেলেপুলে আমাদের দেশে। গুটিকতক ছাড়া, কেন বেশিরভাগেরই পড়াশোনাটাকে একটা বোঝা বলে মনে হয়? কেন ব্যাপারটাতে মন বসে না সহজে? কেন এটাকে দায় বলে মনে হয়? উত্তরটা একটা জায়গায় এসে আবার থমকায়। ভাই, এক্ষেত্রে যে গোড়ায় গলদ! শিক্ষাব্যবস্থার প্যাটার্নটাই এমন চলে আসছে যে, ‘রট্টামার’ পদ্ধতি বলতেও দ্বিধাবোধ হচ্ছে না। নইলে গোপীনাথের মত বুদ্ধিমান ছেলেদের পড়াশোনা মাথায় না থাকার অন্য কোনও কারণ খোঁজা বেশ দুর্ভর!
চারটে বাজল। স্কুল ছুটি। পিয়ার্স রোড পেরিয়ে, জেনিন্স রোডের রাস্তা ধরবে একদল। সেই চৌমাথা, যেখানে একটা রাস্তা গার্ডেন রোড আর স্ট্র্যাচি রোডের দিকে যাচ্ছে আর একটা জেনিন্স রোডের দিকে, বাকি দুটো দিকেই পিয়ার্স রোড, সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে ওদের। রাস্তার পাশের খেজুর গাছটায়, খেজুরগুলো এখনও কাঁচা। লক্ষ্মী দিদিমণির বাড়ির নিচের পলাশ গাছটায় ফুল ফোটার সময় নয় এখন। ছোটদা গোপীনাথকে জিজ্ঞেস করল, ‘গোপী, তুই পরীক্ষার খাতায় কানুদার গোলা লিখে এলি?’
গোপী বলল, ‘কানুদা লাগাতার কয়লা সাপ্লাই দিয়ে কত লোকের রোজ উপকার করছে। আমরা কি রানিগঞ্জ যাব কয়লা আনতে? আরে হ্যাঁ, একটু পা চালিয়ে চল।’
রাজা বলল, ‘কেন?’
গোপীনাথ জবাব দিল, ‘বাড়ি গিয়ে, খেয়েদেয়ে, খেলতে আসার পথে ভাবছি, কানুদার গোলাটা একবার ঘুরে আসব। কানুদাকে বলতে হবে তো, তার গোলা আমি ফেমাস করে দিয়েছি। বেশি দূর না হোক, বেলানগর পর্যন্ত গোলার নাম পৌঁছে গেছে।’
রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কী করে রে?’
গোপী জানাল, ‘ধুত্তোরি! তাও বুঝলি না? দাস স্যারের বাড়ি তো বেলানগরে!’
চিত্রণ: চিন্ময় মুখোপাধ্যায়
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: লিচু চুরি
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: চাঁদা আদায়
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: ঘুগনি সেল
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: লে হালুয়া
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: মুদিখানার প্রত্যাবর্তন