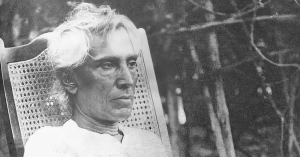নাগলিঙ্গম সুউচ্চ চিরসবুজ বৃক্ষ। বৈজ্ঞানিক নাম Couroupita guianensis, Lacythidaceae পরিবারের সদস্য। নাগলিঙ্গম আবিষ্কৃত হয় প্রায় তিন হাজার বছর আগে আমাজানের জঙ্গলে। ১৭৫৫ সালে ফ্রান্সের উদ্ভিদবিদ জে এফ আউব্লেট (Jean Baptiste Christophore Fusée Aublet) এর নামকরণ করেন Cannon ball. নাগলিঙ্গম নামটি সংস্কৃত হতে নেওয়া। তাই এর কোনও বাংলা নাম নেই। অনেক আগে থেকেই গাছটি ভারত উপমহাদেশে একটি পবিত্র উদ্ভিদ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিবমন্দিরে নাগলিঙ্গম গাছের বিশেষ কদর রয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শিব পূজায় নাগলিঙ্গম ফুল ব্যবহার করেন। এমনকি এ গাছকে ভারতে ‘শিব কামান’ নামে ডাকা হয়। বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে নাগলিঙ্গম যত্নে রোপণ করা হয়। এ কারণে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মিয়ানমারের বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে নাগলিঙ্গম গাছ বেশি দেখা যায়।
নাগলিঙ্গমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কাণ্ড থেকে বের হওয়া সাদা, লাল হলুদের মিশ্রণে উজ্জ্বল বড় বড় ফুল। ফুলটির রং, মিষ্টি গন্ধ, পাপড়ি বিন্যাস সবাইকে মুগ্ধ করার মতো। নাগের ফণার মতো বাঁকানো এর পরাগচক্র। ঠিক এমনটি আমাদের দেশের অন্য কোনও ফুলে নেই। পরাগদণ্ড সাদা কিংবা ম্লান গোলাপি ও মাংসল এবং প্রান্ত গর্ভমুণ্ডের ওপর উদ্যত। পাপড়ি ছয়টি ও পুরু। পরাগদণ্ডের শেষে অজস্র পুংকেশর রয়েছে। শুরুতে আরও অসংখ্য যেসব মৃদু হলুদ পুংকেশর আছে সেগুলো বন্ধ্যা। গাছে সারা বছর অনবরত ফুল ফোটে। তবে বসন্ত ও গ্রীষ্মে ফুল বেশি ফোটে। যেসব গাছে ফল হয় না সেসব গাছে সব সময়ই ফুল ফোটে। গ্রীষ্মকাল পাতা ঝরার সময়। কিন্তু বছরে কয়েকবারই পাতা ঝরে, পাতা গজায়। মঞ্জরীদণ্ডে একটির পর একটি ফুল ফুটতে থাকে। গাছের চারপাশে ঘিরে থাকে মৌমাছি, প্রজাপতি ও বিভিন্ন পতঙ্গ। ফল গোলাকৃতির, মাংসল, বড় ও বাদামি রঙের। ফল কামানের গোলার মত বড় হয় বলে এই উদ্ভিদকে ইংরেজিতে ‘Cannon ball tree’ বলে। প্রতিটি ফলে ২০০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত বীজ থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলে নাগলিঙ্গমের আদিনিবাস। বাংলাদেশের ঢাকার বলধা গার্ডেন, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের বাগানে, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নটরডেম কলেজে, কিশোরগঞ্জে আজিমুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে এবং ময়মনসিংহে শশীলজের দক্ষিণ পাশে পুকুরধারে দুটি এবং পশ্চিম পাশে দুটি নাগলিঙ্গম গাছ আছে। এছাড়া বরিশালের সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জলটঙ্গি পুকুর পাড়ে, গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং শ্রীমঙ্গলের বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিটিউটে এ বৃক্ষটি রয়েছে। ২০১২ সালে ভারতের কেরালার ত্রিবেন্দ্রাম চিড়িয়াখানায় নাগলিঙ্গম গাছ দেখেছি।
হাতির পেটের অসুখের প্রতিষেধক হিসেবে ওই গাছের কচিপাতা কার্যকর ভূমিকা রাখত বলে জানা যায়। গাছের কাণ্ডে ফুল ফোটে। ফলের গায়ের রং সফেদার মত। বাংলাদেশের অনেকেই গাছটির ফল সংগ্রহ করে এর বীজ থেকে চারা উৎপাদনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও চারা গজায়নি। ফলের ওজন হয় প্রায় ২ কেজি। দেখতে সুন্দর হলেও ফলের স্বাদ খুবই তিক্ত। পশু-পাখিও এই ফল খায় না। দুর্লভ নাগলিঙ্গম গাছের ব্যাপক ওষুধি গুণ রয়েছে।
নাগলিঙ্গম ফুলের কলি দিয়ে রস তৈরি করে খাওয়ালে প্রসূতির সন্তান প্রসব সহজ হয়। এর মাঝবয়সী পাতা দিয়ে তৈরি পেস্ট দাঁতের পাইরিয়া রোগ নিরাময়ে ব্যাপক কার্যকর। এ গাছের বাকল দিয়ে বহুমূত্র রোগের ওষুধ তৈরি করা হয়। এ গাছের কাঠও অত্যন্ত মজবুত। লালচে বাদামি রঙের এ কাঠ রেলের স্লিপারসহ ভারী কাজে লোহার পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও শুধু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এ দেশে নাগলিঙ্গম গাছের বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন হওয়ার কথা থাকলেও প্রচণ্ড উঞ্চ অঞ্চলের গাছ বলে এ গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম এ দেশে হয় না।
এ বৃক্ষের ফুল, পাতা ও বাকলের নির্যাস অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেটের পীড়া দূরীকরণে এর জুড়ি নেই। পাতা থেকে উৎপন্ন রস ত্বকের সমস্যা দূরীকরণে খুবই কার্যকর। চর্মরোগ এবং কাটা-ছেঁড়ায় এর রসে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া ফলের বীজ ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে বিশেষভাবে কার্যকর। এছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকায় এর পাতা ম্যালেরিয়া রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করে থাকে। ফলের শক্ত খোলস অলংকার বা বিভিন্ন দ্রব্য বহনে ব্যবহার করা হয়।
চিত্র : গুগল/ লেখক
প্রকৃতিপাঠ : বিলুপ্তপ্রায় কর্পূর গাছ
প্রকৃতিপাঠ: স্নিগ্ধ ছায়ার তমাল গাছ
প্রকৃতিপাঠ: খইয়ে বাবলা ফলের গাছ
প্রকৃতিপাঠ: চিনেবাদাম চিনে নিন
প্রকৃতিপাঠ: তাহার নামটি রঞ্জনা
প্রকৃতিপাঠ: বসন্তের শ্বেত শিমুল
প্রকৃতিপাঠ: পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় বৃক্ষ ছাতিম