কালী হিন্দুদের কাছে এক মাহাত্ম্যময়ী দেবী। অথর্ববেদ আর গৃহ্যসূত্রে কালীর কথা সর্বপ্রথম মেলে। ৯৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত ও ৯ হাজার শ্লোক-সম্বলিত অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্তর্গত ‘কালিকা পুরাণ’-এ এই দেবী সম্পর্কে বহু বিবরণ পাওয়া যায়। মহাকাল-এর ধারণার সঙ্গে একীভূত এই দেবী একদিকে তামসী শক্তির প্রতীক, অন্যদিকে অসুরনাশিনীরূপে খ্যাতা। পুরাণ ও তন্ত্র থেকে শুরু করে যুগযুগ ধরে বহু সাধকের বহু সাধনার মর্মমূলে কালীর ঐশী শক্তির পরিচয় মেলে। দক্ষিণ ভারতে, কেরালা ছাড়া, কালী তিমিরনাশিনী। মৃত্যু, সময়, সৃষ্টি, ধ্বংস ও শক্তির সমবায়িক রূপ এই কালী। কাল-পরিবর্তনের কারয়ত্রীরূপে কালীকে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বহুরূপ এই দেবীর, যা ধরা পড়েছে নিম্নলিখিত কালীপ্রশস্তিতে,—
ওঁ মঙ্গলা ভৈরবী দুর্গা কালিকা ত্রিদশেশ্বরী।
উমা হৈমবতীকন্যা কল্যাণী ভৈরবেশ্বরী।।
কালী ব্রাহ্মী চ মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী বাশলী চণ্ডী ত্বাং জগ্মুর্মুনয়ঃ তথা।।
কেরালায় লোকবিশ্বাস, দৈত্যনাশহেতু শিবের তৃতীয় নেত্র থেকে কালীর জন্ম। এজন্য সেখানে কালীকে বলা হয় ‘ভৈরবোপপত্নী মহাকালী’।
পুরাণে কালী ও দুর্গাকে সমার্থক ও পরিপূরকরূপে পাই। ষষ্ঠ শতকে কালীর আরাধনা সমাজে ব্যাপ্ত হয় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’-এর দেবীমাহাত্ম্যে (শ্রী শ্রী চণ্ডী) বিষ্ণুর শরীর থেকে যোগনিদ্রারূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি চণ্ডমুণ্ডকে বধ করে ‘চামুণ্ডা’ নামে পরিচিত হন। মহামায়ার রূপ ধরে তিনি বধ করেন ‘মধু’ ও ‘কৈটভ’-কে।
মধুকৈটভের অন্য এক কাহিনিমতে, প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছ থেকে এরা বেদ চুরি করে গভীর সমুদ্রে লুকিয়ে রাখে। হয়গ্রীব বিষ্ণু তখন তাদের বধ করে দুজনকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করে (দুই মাথা, দুই ধড়, চার হাত ও চার পা) পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেন।
আজকে বিজ্ঞানীরা যাকে ‘Continental Drift’ বলে থাকেন, তার সঙ্গে কেউ কেউ এই পুরাণোক্ত ঘটনার সমর্থন পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ১৯১২-তে জার্মান আবহবিদ আলফ্রেড ভাগনার এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। তিনি দেখিয়েছেন, মহাদেশগুলো বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও সমুদ্রের ব্যবধান সরালে তারা আশ্চর্যরকমভাবে জোড়া লেগে যায়। তিনি ভারত ও মাদাগাস্কারে প্রাপ্ত ফসিলের সাযুজ্যের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বকে,— প্যানজিয়া বা একীভূত মহাদেশ-তত্ত্বকে প্রমাণ করেন। একে ভিত্তি করেই ১৯৬৮-তে গড়ে উঠল ‘Plate Tectonics’, যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, পর্বতসৃষ্টি ও মহাদেশ-মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেন। সাতটি বড় ও আটটি ছোট টেকটনিক প্লেট (মোট পনেরো), আর মধুকৈটভের ছিন্নবিচ্ছিন্ন বারোটি দেহখণ্ড, এজন্য-ই এমন তুলনা। তবে এখানে কল্পনা-ই মুখ্য।
‘চণ্ডী’-তে পাই চণ্ডমুণ্ড, এই দুই অসুরের কথা। এরা দেবী দুর্গাকে আক্রমণ করলে ক্রোধে দুর্গার মুখাবয়ব কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। সেসময় দুর্গার কপাল থেকে কালীর জন্ম হয়। চেহারা গাঢ় নীল, দুটি চোখ নিমজ্জিত, পরনে বাঘের চামড়া (শিবের মতো কৃত্তিবাস!), গলায় অসুরের মুণ্ডমালা। এই কালীরূপী দেবী-ই চণ্ডমুণ্ড বধকারী।
আসলে, এসব প্রতীককে বিশ্লেষণ করলে দেখব, যুগে যুগে যে অশুভ শক্তি আমাদের চারপাশে আবির্ভূত হয়, তাকে দমন করে পৃথিবীতে শান্তির রাজত্ব নিয়ে আসতেই নারীশক্তির ভৃমিকা। অসুর আর সুর, মানুষের মাঝেই। এই সুরাসুরের দ্বন্দ্ব আবহমান কালের। এবং নারী যে পুরুষের চেয়ে অসুরনিধনে অধিকতর সমর্থ, তা স্বতঃসিদ্ধ, কেননা সাংখ্যদর্শন-মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। নারী-ই পুরুষকে ক্লীবত্ব থেকে মুক্ত করে তার শরীরে বলাধান করে। কথাটি বিজ্ঞানসম্মত-ও বটে। জীববিজ্ঞানে পুরুষ XY, আর নারী XX. প্রজননক্ষমতা তার এজন্যেই। জানি না সাংখ্যদর্শন বিজ্ঞান-আহৃত কিনা, তবে একথা নিশ্চিত, নিষ্ক্রিয়তা-সক্রিয়তায় পুরুষ যে নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভারতীয় দেবপূজায় তার সহজ প্রমাণ, লক্ষ্মী সরস্বতী কালী দুর্গা প্রমুখ পৌরাণিক দেবী আর মনসা শীতলা প্রমুখ লৌকিক দেবীরাই অনেক বেশি ক্ষমতাধর ও পুরুষ দেবতাদের তুলনায় অনেক সক্রিয়। ব্রহ্মাকে তো প্রায় অথর্ব-ই দেখতে পাই। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ কদাচ ক্রিয়াশীল, আর শিব সচরাচর শান্ত। কার্তিক-গণেশ ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর ভূমিকার মধ্যে আমূল প্রভেদ।
তাই দেখা যায়, সংকট উদ্ধারে বারেবারেই দুর্গা ও কালীর ভূমিকা। মহিষাসুরকে কী তীব্র সংঘর্ষের পর-ই না বধ করতে হয়েছে, যে নিহত হলেই অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। কালীকে তো আরও কঠিন কসরতে শুম্ভ-নিশুম্ভের সহচর রক্তবীজকে বধ করতে হয়েছে। রক্তবীজকে মেরে ফেললে যে রক্ত মাটিতে পড়ে, তা থেকে অযুত অসুর জন্ম নেয়। অতএব কেবল হত্যা করা নয়, অসুরের রক্ত যাতে মাটিতে পড়তে না পারে, সেজন্য দেহনিঃসৃত রক্ত পান করতে হচ্ছে দেবীকে। অবশেষে রক্তশূন্য হল অসুর, তার পরেই কেবল তাকে বধ করা সফল হল। আমাদের জীবনেও কি এমন রক্তবীজের অস্থিত্ব নেই?
কালীর নানা রূপ, নানা বর্ণ
ভক্তের বিচিত্র ভাব কালীকে করেছে নানারূপে রঞ্জিত। তাই একদিকে যেমন পাই লোলজিহ্ব, মুণ্ডমালা গলে, উলঙ্গ, চতুর্ভুজা কালীমূর্তি, অন্যদিকে অভয়প্রদা, বরাভয়রূপী কালী। আছেন দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, কৃষ্ণকালী, গুহ্যকালী, শ্রীরূপা কালী, চামুণ্ডা ও ভদ্রকালী, আছেন শ্মশানকালী-মহাকালী। অভিনবগুপ্তের ‘তন্ত্রলোক’ গ্রন্থে পাই স্রষ্টা ও স্থিতি কালী, সংহার ও যমকালী, মৃত্যুকালী ইত্যাদি। পরবর্তীতে পাই ব্রহ্মময়ী কালী, আনন্দময়ী কালী, শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধ্যা ‘ভবতারিণী’ কালী।
কালীর উপাসকরা শাক্ত। যে পাঁচজন দেবতা সবচেয়ে বেশি অর্চিত হন, বা একদা হতেন, তাঁরা হলেন শক্তি বা কালী, শিব, সূর্য, গণপতি (গণেশ) এবং বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ। এইসব দেবতাদের উপাসকরা যথাক্রমে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব নামে খ্যাত। এদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিরোধ। অথচ আশ্চর্য, স্বামী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শাক্ত-বৈষ্ণবে অভেদ দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকর বা শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে,— ‘যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ। যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ’। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, আর যিনি দুর্গা, তিনি-ই কৃষ্ণ। অতএব, কৃষ্ণ ও দুর্গা এক! এ-উপলব্ধি যথার্থ ঔদার্যের উপলব্ধি। পরবর্তীকালে যেমন সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন কালী-রূপে! পরাভক্তি ছাড়া এমন অচিন্ত্য অভেদ করে দেখা সম্ভব নয়। এক ভক্ত যেমন লিখেছিলেন,—
হৃদয়রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে,
একবার হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে সঙ্গে লয়ে।(নবীন ময়রা)
রটন্তী কালী
কালী ও কালা-র (শ্রীকৃষ্ণ) একাত্মতার কাহিনি রয়েছে রটন্তী কালীতে। রাধা একবার কৃষ্ণের অভিসারে এসেছেন। এদিকে রাধার ননদ জটিলা-কুটিলা গোপনে রাধাকে অনুসরণ করে এই ঘটনা চাক্ষুষ করে দ্রুত রাধার স্বামী আয়ান ঘোষকে বলায় আয়ান ছুটে আসেন কুঞ্জবনে। কালীভক্ত আয়ান দেখেন, রাধা সেখানে কালীকে (আসলে কৃষ্ণ-ই কালীরূপ ধরেছিলেন অবস্থা সামাল দিতে) পূজা করছেন। আপ্লুত আয়ান রাধার এহেন কালীপূজা চারদিকে রটিয়ে দিলেন।
ঘটনাটি নাকি মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ঘটে। তাই ওই তিথিতেই, অমাবস্যায় নয়, ব্যতিক্রমীভাবে চতুর্দশী তিথিতেই রটন্তী কালীপুজোর বিধান। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সমারোহ সহকারে প্রতিবছর রটন্তী কালীপুজো হয়।
দীপান্বিতা
এটি হয় কার্তিকী অমাবস্যায়। আলোকমালা দিয়ে প্রাঙ্গণ সাজানো হয়। দীক্ষিত পুরোহিত ছাড়া এ পুজো করা যায় না। এ পুজোয় জীববলি,— ছাগল, ভেড়া, এমনকি মোষবলিও দেওয়া হয়। ডাকাতদের কালীপুজোয় তো নরবলি পর্যন্ত হত। ‘বিশ্বসার তন্ত্র’-মতে গুহ্যকালীর প্রিয় হল গোধামাংস (গোসাপ)।
দীপান্বিতায় অলক্ষ্মীপূজা
অনেক গৃহস্থ বাড়িতে অলক্ষ্মীকে বিদায় জানিয়ে এইদিন লক্ষ্মীপুজো করেন। লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের চালগোলা পিটুলির মূর্তি লক্ষ্মীপুজোর জন্য। অন্যদিকে গোবরের একটি পুতুলকে কালো রঙের ভূত বানিয়ে বাঁহাতে অলক্ষ্মীর পুজো করতে হয়। তারপর কুলোর উল্টোপিঠে চাপিয়ে কাঁসর বাজাতে বাজাতে অলক্ষ্মীকে বিসর্জনের পর শুরু হয় লক্ষ্মীর আরাধনা।
ফলহারিণী কালীপুজো
দেবী কালী ভক্তের অশুভ কর্মের ফল হরণ করে তাকে পাপমুক্ত করেন এই পুজো করলে। জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় এই পুজোর বিধান। প্রসঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণ এই তিথিতেই সারদাদেবীকে পূজা নিবেদন করেছিলেন।
বঙ্গে কালীপূজা : ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিকতা
বঙ্গদেশ প্রাচীনকাল থেকেই তন্ত্রাচারী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশে তন্ত্র নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তান্ত্রিকদের মদ্যমাংস-সেবিত জীবনে কালীর আরাধনা ছিল, মূর্তি ছিল না। সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ‘তন্ত্রসার’ গ্রন্থের বিধান অনুযায়ী শান্ত কালীমূর্তি নির্মিত হয়, ‘দক্ষিণাকালী’। বঙ্গে তাহেরপুরের (রাজশাহী) রাজা কংসনারায়ণ যেমন দুর্গাপূজার প্রবর্তক, তেমনই নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীপূজার আহ্বায়ক।
নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর শাক্ত-অধ্যুষিত ছিল। এখানে আবার চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ ঘটে। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে রাস উৎসবের সূচনা করেন। এই দুইয়ের সংযোগে একদিকে বৈষ্ণবদের রাস, অন্যদিকে তার অনুকরণে শাক্তদের শাক্তরাস। যাতে রয়েছে তন্ত্রাচারের প্রতিফলন। শাক্তরাসের অঙ্গ পূজা, বলি, আড়ং (মেলা) ও বিসর্জন। নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের দারোগা (১৮৫০-৬০) গিরিশচন্দ্র বসু স্বপ্রণীত ‘সেকালের দারোগা’ (১৮৮৮) গ্রন্থে নবদ্বীপে শাক্তরাসের বর্ণনা দিয়েছেন।
আঠারো শতক থেকে বঙ্গে কালীপূজার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। রাজারাজড়ার পূজা থেকে সর্বজনীন পূজা ক্রমে বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শাক্তসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও ভবাপাগলার কালী-উপাসনা ও শ্যামাসঙ্গীত কালী-আরাধনাকে সাধারণের মধ্যে সাড়া জাগায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস কালীসাধনাকে আর এক তাৎপর্য দান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মাতৃসাধনায় স্বতন্ত্র। তিনি কালীকে নিয়ে যে কবিতা লেখেন, তা এক অসাধারণ দেবীস্তুতি! মূল রচনাটি ইংরেজিতে। শিরোনাম ‘Kali, the Mother’। শুরুর কয়েকটি পঙ্ক্তি,—
The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
তেমনই ঋষি অরবিন্দের দৃষ্টিতে কালী, ‘তিনিও মাতার স্নেহ, তাঁর ক্রোধের মতোই তীব্র, তাঁর কারুণ্য সুগভীর, আবেগ-আপ্লুত।’
ভগিনী নিবেদিতার ‘Kali the Mother’ গ্রন্থে মাকালীর আশ্চর্যসুন্দর ব্যাখ্যা পাই। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে কালী অন্যতর মাত্রা নিয়ে এমনভাবে পরাধীন ভারতীয় তথা বাঙালির মানসে আছড়ে পড়ে যে, সংখ্যাতীত দেশপ্রেমিক তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মবলিদানে এগিয়ে আসেন। বাংলায় ‘যুগান্তর’, ‘অনুশীলন’ ইত্যাদি দলের বিপ্লবীরা কালীর নামে শপথ নিতেন।
আজ কী পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায়, কী বাংলাদেশের, কালীর অজস্র মন্দির। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি, ঠনঠনিয়া, করুণাময়ী, চিত্তেশ্বরী (চিৎপুর) যেমন, তেমনই আছে তারাপীঠ, চামুণ্ডা (মন্তেশ্বর), সিঙ্গুরের ডাকাতকালী, গোবরডাঙার প্রসন্নময়ী, কালনা-কোচবিহার-রানাঘাট ও রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, শিবপুরের হাজার হস্ত-সম্বলিত কালীমন্দির। এন্টনি কবিয়ালের, চীনাদের কালীবাড়ি প্রমাণ করে, কালী তাঁদের কাছেও কতখানি আদৃত।
তেমনই বাংলাদেশের বিখ্যাত কালীমন্দিরের মধ্যে আছে সিদ্ধেশ্বরী, রমনা, চট্টেশ্বরী, যশোরেশ্বরী, কৃপাময়ী (গাজীপুর) ইত্যাদি। আছে মুকুন্দদাস প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির, বরিশালে। বরিশালেই আবার শ্মশানকালী বিখ্যাত। এখানকার শ্মশানটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বৃহত্তম, যেখানে ছ-হাজার মৃত ব্যক্তির মঠ রয়েছে, আর মঠের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন।
বাংলাদেশে ছ’টি মহাতীর্থ আছে, যেখানে দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আছে তেরোটি।






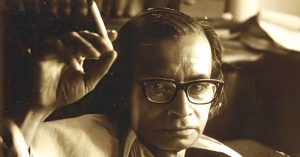








One Response
🙏