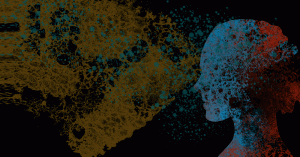১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল, ভোরের হাওয়াটুকু-ও সেদিন শীতল ছিল না। চারদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ, খরতাপে দগ্ধ বঙ্গদেশের গ্রাম-জনপদ, বিপর্যস্ত মহানগর কলকাতার নাগরিক জীবন। এমনই এক বোশেখের অগ্নিদগ্ধ দিনে আত্মহত্যা-তাড়িত হয়ে ঘুমের ওষুধ খেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ‘নতুন বউ’ কাদম্বরীদেবী (১৮৫৯-১৮৮৪)। ওষুধ খাওয়ার পর, জীবন-মৃত্যুর আলো-আঁধারির মধ্যে দুদিন বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রথমদিনে আসেন খ্যাতিমান চিকিৎসক ডি বি স্মিথ। এরপর আসেন বাঙালি ডাক্তার নীলমাধব হালদার ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তারপর আসেন ডাক্তার ভগবৎচন্দ্র রুদ্র। কিন্তু এঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে ১০ বৈশাখ ১২৯১ আঁধারের বৃন্ত থেকে ভোরের কুসুম ফোঁটার আগেই (২১ এপ্রিল ১৮৮৪) না-ফেরার দেশে যাত্রা করেন ঠাকুরবাড়ির এই চিরঅভিমানী বধূটি। এক গঙ্গা দুঃখ নিয়ে সবকিছু ছেড়ে যেন নিমেষে মিলিয়ে যান অনন্ত আঁধারে— ‘রবিহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে’।
‘কাদম্বরী দেবীর অকালপ্রয়াণের পর ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ কেন হয়েছিল তা-ও অপরিজ্ঞাত। তিনি প্রায় নীরবে এসে প্রায় সেইভাবেই বিদায় নিয়েছিলেন।’ (শ্রেয়সী পাল, পুনশ্চ কাদম্বরী, দেশ, শারদীয় ১৪২২)। কিছু সূত্র থেকে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নেমে এসেছিল গভীর শোক, বিষাদ ও নৈঃশব্দ্য। তবে এই মৃত্যুর জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল, কিন্তু তা নেয়া হয়নি। প্রবল প্রতাপশালী শ্বশুরমহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে বাড়িতেই তাঁর শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল, কিন্তু পোর্টমর্টেম রিপোর্টে কী ছিল তা আজ অব্দি জানা যায় না। কেবল জানা যায়, এক দাসী তাঁকে সেঁকো বিষ এনে দিয়েছিল— এইটুকুমাত্র। কাদম্বরীর মৃত্যু-রহস্যের জট এখনও উন্মোচিত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায়-নাটক-নিবন্ধে তাঁকে পাওয়া যায় নানাভাবে, নানারূপে। তিনি ঠাকুরবাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলেন শরৎ-হেমন্তের সংযোগস্থলে আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতায়— মিশে গেলেন তাঁর কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকর্মে কখনও আকুল হাহাকার হয়ে, কখনও অস্পষ্ট বেদনা হয়ে।
স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) ভালবাসা পেয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী, নিজেও স্বামীকে ভালবাসতেন। তাহলে কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন? কেন আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণসখা, প্রেরণাদাত্রী কাদম্বরী দেবী? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতার প্রেরণা এবং প্রথম শ্রোতা, অথচ তিনিই কিনা প্রিয় দেবর রবীন্দ্রনাথের বিয়ের মাত্র চারমাস পর আত্মহত্যা করলেন! রবীন্দ্রনাথ কি পারতেন না তাঁর প্রিয় নতুন বউঠানকে আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে? কারা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল? রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর রোম্যান্টিক সম্পর্ক, যাকে ইন্টেলেকচুয়াল রোম্যান্স বলা যায়, সে-ই রোম্যান্স কি তাঁকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিল? নাকি, স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাদর-অবহেলা? স্বামী জ্যোতিবাবু অভিনয় ও নাট্যকলাপ্রিয় ছিলেন। এমনও হয়েছে, গঙ্গার বুকে নাট্যজগতের নট-নটীদের নিয়ে ‘সরোজিনী’ জাহাজে আনন্দোৎসব চলেছে রাতভর, অথচ স্ত্রী কাদম্বরী সেই আনন্দোৎসবে নিমন্ত্রণ পাননি, খবর পেয়েও স্বভাবগুণে তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন।
সর্বক্ষেত্রেই তিনি থেকেছেন উপেক্ষিতা আর অনাদৃতা। এর ফলে তাঁর প্রাণের গভীরে সৃষ্টি হয়েছিল ক্ষত যা তাঁকে অস্থির, উদাস ও অভিমানী করে তুলেছিল। মনের গহনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল কাঠ-কয়লার তীব্র আগুন। এই অনাদর, এই অবহেলা, এই উপেক্ষাই তাঁর ভেতরে আত্মহননের বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। ঠাকুরবাড়ির নারীমহল, তারাও কি কাদম্বরীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী নয়? ঠাকুরবাড়ির নারীরা কোনওদিন তাঁকে ন্যূনতম সম্মান দিতে পারেননি। মেনে নিতে পারেননি। সত্যিই তো, তাঁকে মেনে নেয়া যা-ই বা কেমন করে! অভিজাত ঠাকুর পরিবারে তাঁর বিয়ে হলেও তাঁর জন্ম তো ১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই কলকাতার হাড়কাটা গলির এক দরিদ্র পরিবারে। বাবা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরবাড়ির একজন সামান্য বাজার সরকার। মাতা ত্রৈলোক্যসুন্দরীর কোনও পরিচয়-ই পাওয়া যায় না। আর তাঁর পিতামহ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দারোয়ান, যাঁর চিরস্থায়ী আসন পাতা ছিল ঠাকুরবাড়ির প্রধান গেটে, যদিও তিনি একজন গুণী সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে গানের-গলা তা পেয়েছিলেন মূলত কাদম্বরীর পিতামহের কাছ থেকে। অথচ বনেদি ঠাকুর পরিবার এই গুণী সঙ্গীতশিল্পীকে কোনওদিন সম্মান দেয়নি, এমনকি স্বীকৃতিও না।
মাত্র ন’বছর বয়সে কাদম্বরীর বিয়ে হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষষ্ঠ সন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে। প্রবল প্রতাপশালী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৌদ্দজন পুত্রকন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বে অনন্য, শারীরিকভাবে সুঠাম, রূপে-গুণে উজ্জ্বল। শিল্প-সাহিত্য, খেলাধুলা, অশ্বারোহণ ও শিকারে ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। তিনি বেহালা ও পিয়ানো বাজাতে জানতেন, গান রচনা করে তাতে সুর আরোপ করতে পারতেন। নাট্যকার হিসেবেও ছিলেন দারুণ সফল, কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক মঞ্চায়ন হত নিয়মিত। তার ‘অলীক বাবু’ নাট্য-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। কিংবদন্তিতুল্য অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী তাঁর নাটকে অভিনয় করেছেন। তখন বাংলার সারস্বত সমাজের সকলেরই দৃষ্টি ছিল ঠাকুরবাড়ির এই প্রতিভাধর তরুণটির দিকে, অনেকেরই ধারণা, তিনি ভবিষ্যতে বড় কিছু হবেন।
১৮৬৮ সালের ৫ জুলাই, কাদম্বরীর দশম জন্মদিনে ঊনিশ বছর বয়সী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনিবার্য আদেশে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনেকেই বিশেষ করে, দেবেন্দ্রনাথের মেজছেলে আইসিএস অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী এই বিয়ে মেনে নেননি কোনওদিন। মেজবউ জ্ঞানদা বলতেন, ‘বাবামহাশয়ের অন্যায় জেদের কারণে এ বিয়েটা হল। জ্যোতি মেনে নিল বটে, কোনও প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না কিন্তু এ বিয়েতে কারও মঙ্গল হবে না।’ দু’জনের মধ্যে ছিল যোজন যোজন দূরত্ব। এ দূরত্ব যেমন শিক্ষাদীক্ষা, বংশমর্যাদায় ছিল, তেমনই ছিল বয়সে। জ্ঞানদাদেবী তো প্রায়ই বলতেন, ‘নতুনের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কী যে একটা বিয়ে হল ওর। কোথায় নতুন আর কোথায় ওর বউ! এ বিয়েতে মনের মিল হওয়া সম্ভব নয়। স্ত্রী যদি শিক্ষাদীক্ষায় এতটাই নীচু হয়, সেই স্ত্রী নিয়ে ঘর করা যায় হয়তো, সুখী হওয়া যায় না। নতুন তো সারাক্ষণ আমার কাছেই পড়ে থাকে। গান বাজনা থিয়েটার নিয়ে আছে, তাই সংসারের দুঃখটা ভুলে আছে।’
মেজবউ জ্ঞানদাদেবী, জ্যোতিবাবুর বিয়ে ঠিক করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলেতফেরত মেয়ের সঙ্গে। কোথায় সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলেতফেরত মেয়ে, আর কোথায় বাজার সরকার শ্যামলাল গাঙ্গুলির মেয়ে! কেবল জ্ঞানদাদেবী নয়; ঠাকুরবাড়ির নারীমহলের প্রায় সবাই মনে করতেন, ঠাকুরবাড়ির রূপকুমার, রূপেগুণে অনন্য, সরস্বতীর বরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী হওয়ার কোনও যোগ্যতাই কাদম্বরীর নেই। তারপরও কেন যে জ্যোতিন্দ্রনাথের মত দেবোপম পুরুষের সঙ্গে সামান্যা কাদম্বরীর বিয়ে হল? বিয়ে হয়েছিল কেবলমাত্র কন্যা অর্থাৎ কাদম্বরীর সহজলভ্যতার কারণে, আর শুধুমাত্র কনে খোঁজার ভয়ে। হাতের কাছেই কাদম্বরীরা থাকতেন। তাছাড়া অভিজাত, কুলীন হিন্দুরা ঠাকুরবাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কারণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা দেব-দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন না; ছিলেন পৌত্তলিকতা-বিরোধী, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। যে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন হয়, সেই শালগ্রাম শিলাই ব্রাহ্মরা মানেন না! তার ওপর মুসলমানের হাতে জল খাওয়া পিরালি ব্রাহ্মণ!
হিন্দু ব্রাহ্মণরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের ব্রাহ্মণই মনে করতেন না। সুতরাং অভিজাত হিন্দুরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইতেন না। সেই কারণে সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী দেবী, ভবতারিণীর মতো অতি সাধারণ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের রূপেগুণে অসাধারণ সব ছেলের বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বিয়ে হয়েছে বনেদি পরিবারে। শরৎকুমারীর বিয়ে হয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মানিকতলার অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে। স্বর্ণকুমারীর বিয়ে হয় কৃষ্ণনগরের জমিদার জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে আর বর্ণকুমারীর হয় কুষ্টিয়ার গোস্বামী-দুর্গাপুরের জমিদার পরিবারের সন্তান সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথের মেজছেলের মেয়ে ইন্দিরাদেবীর বিয়ে হয় প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। কৃষ্ণনগরের অভিজাত পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা প্রমথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করার পর বিলেতে যান উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্যে। দেশে ফেরেন ব্যারিস্টারি পাশ করে। ঠাকুরবাড়ির জামাই হিসেবে ধনে-গুণে-মানে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অতুলনীয়। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বধূদের মধ্যে কেউ-ই তেমন উচ্চবংশীয়া ছিলেন না।
বংশ বা পিতৃপরিচয় যা-ই হোক, কাদম্বরী ছিলেন রূপে-গুণে অতুলনীয়। সাধারণ নারীদের তুলনায় লম্বা, গাঢ় ভুরু, বড় বড় অক্ষিপট, কৌতুকময় চক্ষু। দেখতে অনেকটা গ্রিক দেবীর মতো। তিনি যে যেনতেন মেয়ে ছিলেন না, তা প্রমাণ করেছেন তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভা দিয়ে। তারপরও এই নারীকে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই মানতে চাননি। অথচ মেজবউ জ্ঞানদাদেবীর মত তিনিও নিজেকে সামান্য থেকে অসামান্যে রূপান্তর করেছেন। কেবল রূপে-গুণে-রুচিতে নয়; লেখাপড়া, গানবাজনা, অভিনয়েও কাদম্বরী ছিলেন অতুলনীয়। তারপরও এই রুচিশীল নারীকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পরিশীলিত সাংস্কৃতিক আবহ ও বিনয় বচনের মধ্যেও তাঁকে সইতে হয়েছে নিন্দা বিদ্বেষ কুৎসার তীব্র আঘাত। এত লাঞ্ছনা, এত আঘাত, এত জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ রবীন্দ্রনাথকে যিনি সখা হিসেবে পেয়েছেন, তিনি কি কখনও মরতে চান! ঠাকুরবাড়িতে সব দুঃখ, সব বেদনা, সব অপমানের মাঝে কেবল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পরম আশ্রয়, একমাত্র পাওয়া।
ন’বছর বয়সে যেদিন তিনি ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে এলেন, সেদিন থেকে রবিই হয়ে ওঠেন তাঁর খেলার সাথি, প্রাণের দোসর। কৈশোরে রবি ছিলেন তাঁর একমাত্র বন্ধু। রবির হাতে হাত রেখেই তো ভাললাগার প্রথম আলো দেখা। রবির ভালবাসা পেয়ে নতুন বউঠানের মনে হয়েছিল, তাঁর প্রতি ঠাকুরবাড়ির সব লাঞ্ছনা, অবহেলা, অপমান, উপেক্ষা, ঘৃণা-কুৎসার যেন প্রতিশোধ নিলেন রবি! সারা ঠাকুরবাড়িতে কাদম্বরী একজনকেই প্রাণের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি তাঁর কষ্ট, দহন বুঝেছিলেন। সত্যিই তাই, নতুন বউঠানের ভেতরের দহন যদি কেউ বুঝে থাকেন তা কেবল রবীন্দ্রনাথ-ই বুঝেছিলেন। সে কারণে নতুন বউঠানের মন ভাল না থাকলে রবি বলতেন, ‘নতুন বউঠান, কী হবে ছোটখাটো দুঃখের কথা মনে রেখে? ভুলে যাও, সব ভুলে যাও।’ ঠাকুরবাড়ির নারীমহল তাঁকে সারাজীবন হেয় প্রতিপন্ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে; স্বামীর সোহাগ বলতে যা বোঝায় তাও তেমন পাননি। ষোল বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তানের মা হতে পারেননি। এত দুঃখ, এত হতাশার মাঝে রবিই ছিলেন তাঁর সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ, একমাত্র আশ্রয়। রবি যখন বলতেন, ‘নতুন বউঠান, ভুবন জুড়ে এত আনন্দ, সেই আনন্দধারাকে অন্তরে গ্রহণ করো, দেখবে ঝরাপাতার মতো পুরনো দুঃখ সেই আনন্দস্রোতে ভেসে গেছে’— তখন তাঁর যে কী ভাল লাগত তা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যাবে না।
আর, আকাশের রং ও বিভা কীভাবে দেখতে হয়, মর্ত্যের রূপ অরূপের লীলা কীভাবে উপভোগ করতে হয় তার শিক্ষা নতুন বউঠানের কাছ থেকে পেয়েছেন রবি। নতুন বউঠানের চোখের দিকে তাকিয়ে রবি একদিন রচনা করলেন এক কালজয়ী গান: ‘এ কী সুন্দর শোভা/ কী মুখ হেরি এ’। সেদিন ছিল জ্যোৎস্নারাত। আকাশে উঠেছে রুপোর থালার মত চাঁদ। গঙ্গার শান্ত জলের বুক চিরে ভেসে চলেছে তাঁদের নৌকো। আকাশে তখন রংয়ের ছড়াছড়ি, যেন মহাকাল মেতেছে হোলি উৎসবে। তিনজন মানুষ মহাভাবে বিভোর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজিয়ে চলেছেন একটার পর একটা রাগ-রাগিনী, রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন আর নতুন বউঠান সেই গানে যোগ দিচ্ছেন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। নতুনদার বেহাগের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন নিজের রচিত একটি গান গাইলেন: ‘‘সখী, ভাবনা কাহারে বলে/ সখী, যাতনা কাহারে বলে/ তোমরা যে বলো দিবস-রজনী,/ ‘ভালোবাসা’ ‘ভালোবাসা’।’’
নতুন বউঠানের কাছেই রবি শিখে নিয়েছেন ভালবাসার গাঢ় গহন গোপন ভুবনে ঢোকার মন্ত্র কখনও বৃষ্টিতে ভিজে, কখনও জ্যোৎস্নায় ছাদে দাঁড়িয়ে। তাই বিলেতে যাবার সময় কেবল একজনের কথা ভেবে রবি কষ্ট পেয়েছিলেন বেশি, তিনি নতুন বউঠান। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ভারতভূমির দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা যখন তার টনটন করে উঠেছিল তখন মনের খেরোখাতায় একটি গানের খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছায়ানট রাগিনীতে গানে গানে রবি তাঁর প্রিয় নতুন বউঠানকে হৃদয়ের কথা জানিয়ে লেখেন: ‘তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,/ এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।/ যেথা আমি যাই নাকো/ তুমি প্রকাশিত থাকো,/ আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা॥/ তব মুখ সদা মনে/ জাগিতেছে সংগোপনে,/ তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।’
একদিন এক গানের জলসায় স্বামী বিবেকানন্দ যখন গানটি গাইছিলেন তখন রবির বুকের ভেতরটা কেমন যেন টনটন করছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, এ গান তো কেবল তাঁদের দুজনের, সর্বসাধারণের জন্য নয়। নতুন বউঠানকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত গান, কত কবিতা এমনকি উপন্যাস রচনা করেছেন। ‘বউঠাকুরানির হাট’ উপন্যাসের পরিকল্পনা তিনি দুপুরবেলা বউঠানের পাশে বসে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে করেছিলেন। কোনওদিন কি কোনও মুগ্ধ পাঠক এ কথা জানতে পারবে! বউঠানকে সাজতে দেখে রবি একদিন রচনা করে ফেলেন অনবদ্য সব পঙ্ক্তি: ‘অশোক বসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে/ আপনার রূপের মাঝারে,/ রেখা রেখা হাসিগুলি আশেপাশে চমকিয়ে/ রূপেতেই লুকায় আবার।…’
‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতা রবি প্রথম শুনিয়েছিলেন নতুন বউঠানকেই। যেদিন এ কবিতা রচনা করেন সেদিন কবি দৈবদর্শনের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি কোনও কবিতা রচনা করছেন না, কবিতা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ভেতর থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে। ঋগ্বেদের ঋষিদের প্রকৃতি-দর্শনের আকস্মিক উদ্ভাসনে যে দশা হয়, তাঁরও সেই দশা হয়েছিল সেদিন। ভাষার জন্য তাঁকে চিন্তা করতে হচ্ছে না, চিন্তা যেন ভাষা ছন্দ কবিতা হয়ে হৃদয়ের গহন গভীর থেকে বেরিয়ে আসছে। কয়েক পঙ্ক্তি লিখে তা একা একা আবৃত্তি করে নিজেই বিস্মিত হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, এ কার কবিতা— কে লিখেছে? রবি যখন কবিতাটি গর্জন করে আবৃত্তি করছিলেন, ‘জাগিয়া উঠেছে প্রাণ/ ওরে উথলি উঠেছে বারি/ ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ/ রুধিয়া রাখিতে নারি।’— তখন কাদম্বরী রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে যখন তিনি বলছেন, তোমার কী হয়েছে, তুমি যা পড়ছ তা কী কবিতা, না অন্য কিছু? সেদিনের তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতাকে বললেন, ‘নতুন বউঠান, আমার ঘোর লেগেছে, এই প্রভাতের রবির আলোয় আমার প্রাণ জেগে উঠেছে, আমি আমার ভেতরের মহাসমুদ্রের গর্জন শুনতে পেয়েছি। কীসের ঘোরে আমি আচ্ছন্ন তা জানি না, তবে আমি যেন আমার মধ্যে নেই।’ ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবির আত্মজাগৃতি ও চৈতন্যের বোধনকালের সূচনাবিন্দু। কবিতাটি লেখার সময় তিনি ছিলেন নতুনদার সঙ্গে জাদুঘরের কাছে ১০ নম্বর সদর স্ট্রিটের এক বাসায়। সেখানে একদিন ‘এক অভূতপূর্ব আনন্দ-আবেগ’ তাঁর চেতনায় নতুন সুর সঞ্চার করে দেয়। সদর স্ট্রিটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এক দৈবমুহূর্তে তিনি লিখে ফেলেন ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’।
১৮৭৮ থেকে ১৮৮০ সাল দু’বছর কাদম্বরীর জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর দহনকাল, এই দুটি বছরের প্রতিটি প্রহর কেটেছে বিরহ-বেদনায়। এ দু’বছর রবীন্দ্রনাথ বিলেতে ছিলেন। বিলেত থেকে যখন ফিরলেন তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে ঘিরে সূচিত হল গান-বাজনা, নাটক-থিয়েটার, সৃজন-মননচর্চার এক নতুন অধ্যায়, নতুন কালপর্ব। ১৮৮২ সালের মধ্যে ঠাকুরবাড়িতে ঘটে বঙ্গ সংস্কৃতির নবজাগরণ। বাংলার সারস্বত সমাজের দৃষ্টি তখন রবীন্দ্রনাথের দিকে। তিনি তখন গানে প্রাণে, সুরে ছন্দে, নাটকে সারা বাংলাকে মাতিয়ে তুলেছেন। তিনি হয়ে উঠলেন বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ আর তাঁর ‘মক্ষীরাণী’ হলেন কাদম্বরীদেবী। এর মধ্যে ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: ‘সেই জানালার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের/ গাছগুলি মনে পড়ে সেই অশ্রুজলে সিক্ত/ আমার প্রাণের ভাবনাগুলিকে মনে পড়ে।/ আর একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল,/ তাহাকে মনে পড়ে।’
লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে মুসৌরিতে তলব করলেন এবং বিয়ে করার আদেশ দিলেন। বাবার অমোঘ আদেশে ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর খুলনার দক্ষিণডিহির বেণী রায়ের ন’বছরের কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হল। ঠাকুরবাড়িতে ভবতারিণীর নাম দেয়া হল মৃণালিনী। বিয়ের পর মৃণালিনীকে নিয়ে রবি মেজ বউঠানের কাছেই থাকতে লাগলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির যে ঘরটিতে রবি থাকতেন সেটি পরিষ্কার করতে গিয়ে কাদম্বরী একদিন আবিষ্কার করলেন একটি অসমাপ্ত কবিতার দুটি পঙ্ক্তি। পঙ্ক্তিদুটি পড়ে ভেতরে তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ— তাঁর প্রিয় রবি লিখেছে: ‘হেথা হতে যাও পুরাতন!/ হেথায় নতুনের খেলা আরম্ভ হয়েছে…’। তিনি প্রচণ্ডভাবে কষ্ট পেলেন; তারপরও তাঁর মনে হল, এটাই জগতের নির্মম সত্য। নতুনের জন্য পুরাতনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, আর এটাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তিনি পুরাতন হয়ে গেছেন, তাই তাকেও স্থান ছেড়ে দিতে হবে। তারপর খুব বেশিদিন আর ঠাকুরবাড়িতে থাকলেন না তিনি। একদিন ঘুমের ওষুধ খেয়ে, কেউ বলেন আফিম খেয়ে গহন গভীর ঘুমের দেশে চলে গেলেন, আর ফিরে আসলেন না।
যে-নারী স্বামীর সাহচর্য পান না, সন্তানের মা হতে পারেন না— তিনি কী নিয়ে বেঁচে থাকবেন? অন্য একজনকে নিয়ে তিনি সুখী হতে চেয়েছিলেন, সেও যখন জীবনসাথি যোগাড় করে নিয়েছে তখন বেঁচে থাকার কোনও অর্থই থাকে না! তারপর নিরর্থক জীবনের মায়া ছেড়ে, নতুনের জন্য স্থান করে আঁধারে মিলে গেলেন ঠাকুরবাড়ির চিরঅভিমানী বধূটি। তাঁর মৃত্যুসংবাদ কলকাতার কোনও দৈনিক কিংবা সাময়িকপত্রে ছাপা হয়নি। ঋষিতুল্য পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে কাদম্বরীর আত্মহত্যা সংক্রান্ত প্রমাণাদি কৌশলে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, পাছে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ হয়ে যায়। পুরোহিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে আনা হয়েছিল শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করতে। প্রচুর চন্দন কাঠ, গব্য ঘৃত, ধূপ ধুনো সংগ্রহ করা হয় দাহের জন্য। শাস্ত্র মতে, পুত্রহীনার মুখাগ্নি করার কথা স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। কিন্তু তিনি এতই ভেঙে পড়েছিলেন যে, স্ত্রীর শেষ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। স্ত্রীর আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বিপর্যস্ত ও শোকার্ত হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেননি, শোকে স্তব্ধ হয়ে বিছানায় মুখ গুজে শুয়েছিলেন, স্ত্রীর শেষ মুখখানিও তাঁর দেখা হয়নি। অবশেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে দিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজটি সম্পন্ন করেন। নিমতলার শ্মশানে চিতার আগুনে যখন কাদম্বরীর নিথর দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপটে কত ছবিই না ভেসে উঠছিল! কাদম্বরীর যখন মৃত্যু হল, তখন রবীন্দ্রনাথের নতুন গ্রন্থ ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’-এর কাজ চলছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল নতুন বউঠান থাকলে নাটকের মধ্যের ‘মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে’ গানটির সুর নিয়ে কিংবা দু’একটা শব্দ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলা যেতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়! কাদম্বরীর আত্মহত্যার পর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল সমগ্র জগৎ যেন আত্মহত্যা করেছে। তারপরও শোক-দুঃখ, বিরহ-মৃত্যু কোনও কিছুই তাঁকে জগতের আনন্দযজ্ঞ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি, মর্ত্য-মানবের প্রেমে ব্যাকুল এই কবি এই বিশ্বনিখিলকেই সত্য বলে জেনেছেন। তাই সৃজন আনন্দের পথ থেকে কখনও ছিটকে যাননি।
১৮৩৮ সালে পিতামহী অলকাদেবীর মৃত্যু ‘বিলাসের আমোদে’ ডুবে থাকা একুশ বছর বয়সী দেবেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন পালটে দিয়েছিল। ধনের মত্ততা ত্যাগ করে তিনি প্রবেশ করেছিলেন ধর্মের সিংহদ্বারে। যিনি ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন পূজা-অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন, তিনি কিনা হয়ে উঠলেন অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক। একটি মৃত্যুই সারাজীবনের জন্য ক্রমেই তাঁকে করে তুলল এক সাধক মহা-ঋষি-পুরুষে। একটি মৃত্যু তাঁর বিগত জীবনের সব বিশ্বাস ও ধারণার ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়ে দিল। হয়ে উঠলেন সংসারউদাসী, প্রত্যক্ষ কর্মময় জীবন থেকে দূরবর্তী, ধ্যানযোগী, সত্যনিষ্ঠ এক মহান ধর্মাশ্রয়ী নেতা। কিন্তু কাদম্বরীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে জীবন থেকে দূরবর্তী করতে পারল না। তিনি গভীরতর অর্থেই জীবনলগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু জীবনের প্রভাতবেলায় যে-নারীকে প্রথম দিনের সূর্য হিসেবে পেয়েছিলেন, তাঁকে সারাজীবন ভুলতে পারলেন না। তাঁর সাহিত্য-সমুদ্রে বারবার ভেসে উঠতে লাগল নতুন বউঠানের মুখচ্ছবি। কখনও বালিকা হয়ে, কখনও কিশোরী, কখনও বা যুবতী হয়ে। তাঁর কবিতা, নাটক, ছোটগল্প সর্বত্রই যেন কাদম্বরী তথা নারীশক্তির জয়জয়কার। কখনও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, কখনও আত্মবিশ্বাসী, কখনও বা রহস্যময়ী। নতুন বউঠান যেন বারবার নব নবরূপে ফিরে এসেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। এজন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথের একটি গানে পাওয়া যায়: ‘আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়॥/ যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে ভালোবাসে আড়াল থেকে,/ আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়॥’
মৃত্যুর পর এত বছর পার হয়েছে, কিন্তু বাঙালির স্মৃতিপট থেকে মুছে যাননি কাদম্বরী দেবী, বরং ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। দিন যতই যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেমন আমাদের আগ্রহ বাড়ছে, তেমনই কৌতূহল বাড়ছে রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর সম্পর্ক নিয়ে। তাঁদের দু’জনের সম্পর্ক নিয়ে ইতিমধ্যে বাঙালিদের মধ্যে একটা মিথ তৈরি হয়ে গেছে। প্রায় সবাই বলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো দেবতুল্য মানুষও প্রেম করতেন! তাও কী-না আবার বউদির সঙ্গে! কবির বিয়ের মাত্র চারমাসের মধ্যে কাদম্বরী আত্মহত্যা করেছিলেন! এই প্রশ্নটা আজও সবার মধ্যে ঘুরপাক খায়, কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন? এর জন্য কে দায়ী? তাঁর মৃত্যুর জন্য যে-ই দায়ী হোন, আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম যতদিন থাকবে, তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে কাদম্বরীর নামটাও মুছবে যাবে না।