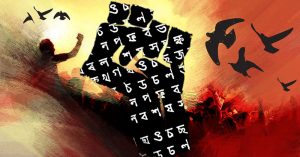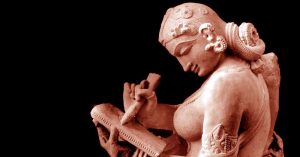মুঘল চিত্রসাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট আকবর। যদিও বাবর, হুমায়ুনকে নিয়ে দিল্লির তখত্-এ তিনি তৃতীয় মুঘল নরপতি। তাঁর আমলের দরবারি চিত্রের সংখ্যা কত কে জানে! তবে এই তসবির-নির্মাতাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই শ’খানেক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জানতে ইচ্ছে করে, এই ছবি আঁকিয়েদের গুণগ্রাহী বাদশা নিজে কি কোনওদিন তসবির কলায় মন সঁপে ছিলেন? রঙের পাত্রে ডুবিয়েছিলেন নিজের কোনও তুলি?
সে কথা ভাবলে মনে পড়ে যায় ১৫৫১ সালের এক অলস মধ্যাহ্নের কথা। দুই রাজকুমার প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবি আঁকছেন, তাঁদের একজন আকবর। বয়সটি তখন তার বছর নয় হবে। সম্ভবত ঘটনাটি ঘটেছিল কাবুলে। সে সময় তার বাবা হুমায়ুন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় পরবাসে কোনওক্রমে দিন কাটাচ্ছেন কষ্টেসৃষ্টে।
আকবর বাদশার এর পরের চিত্র-চর্চাটি ১৫৫৬ সালের। হুমায়ুন দিল্লির মসনদে পুনরাধিকার কায়েম করেছেন। তেরো বছরের বালক আকবর উদ্যানবাটিকায় দৌড়ে এসেছে বাবাকে ছবি দেখাতে! এই যে চিত্রকলায় আকবরের বাল্যলীলা তার সচিত্র প্রমাণ ধরা আছে আবদুস সামাদের আঁকা দুটি বিখ্যাত ছবিতে। একটি তাঁর জাহাঙ্গীরের গুলশান অ্যালবামের অন্তর্গত ছিল কোনওকালে। তারপর সেটি যায় তেহেরানের গুলিস্তা মিউজিয়ামের সংগ্রহে।
খাজা আবদুস সামাদ এবং মীর সঈদ আলি নামে দুই ইরানি শিল্পীর আশ্রয়ে আকবরের শিল্পশিক্ষার ভার দিয়েছিলেন পিতা হুমায়ুন। পারস্যের এই মহান দুই চিত্রশিল্পীকে আরও কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে হুমায়ুন এদেশে এনেছিলেন পারস্যরাজ শাহ তাহমাম্প-এর রাজসভা থেকে। ইরানি এই শাহের সঙ্গে হুমায়ুনের প্রথম দেখা ১৫৪৪-এর জুলাই মাসের এক নতুন গড়ে ওঠা চিত্রশালায়। এই আবদুস সামাদ, মীর সঈদ আলিদের প্রথম যুগলবন্দীতে ভরে উঠল মুঘল চিত্রকলার অভিনব তসবিরখানা।

আবদুস সামাদের সেই ছবির কথা বললাম যার বিষয় কিশোর আকবরের ছবি আঁকা। এখন দেখা যাক, এ বিষয়ে ‘আকবরনামা’-তে আবুল ফজল নিজে কী বলেন? ‘‘শাহনশা বাদশার (আকবরের) আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সেদিনের সেই ব্যাপারটি যেদিন বাদশা জাহানবানি জিন্নত আশিয়ানি (হুমায়ুন) সিকন্দরকে যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লিতে এলেন আর আকবর তাঁর (হুমায়ুনের) এক উজ্জ্বল ব্যঞ্জনাময় ছবি এঁকে ফেললেন। শিল্পচর্চার অতুলনীয় দুই কুশলী ব্যক্তি মীর সঈদ আলি এবং খাজা আবদুস সামাদ ‘শিরিন কলম’ তাঁকে (আকবরকে) শিল্পশিক্ষার পাঠ দিতেন।’’
তাব্রিজ শহরের চিত্রকর মীর মনসুরের ছেলে মীর সঈদ আলি মাইকেলেঞ্জেলো কিংবা রোসেটির মত একাধারে ছিলেন কবি ও শিল্পী। তাঁরই সমসাময়িক সিরাজ নগরীর খাজা আবদুস সামাদ খ্যাত হয়েছিলেন চিত্রকর ও অলঙ্কৃত লিপির কুশলী বিশারদ হিসেবে। বলতে গেলে হুমায়ুনের আগ্রহে এবং আকবরের আনুকূল্যে মুঘল চিত্রকলার গোড়াপত্তন করেন এঁরাই। ছেলেবেলায় নানা কারণে প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয়নি আকবরের। কিন্তু ছবির জগৎকে তিনি গড়ে নিয়েছিলেন শিক্ষার বাহন হিসেবে। আকবরের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনও রাজাবাদশা চিত্রকলাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে মনে করেননি বোধ হয়।
‘আইন-ই-আকবরী’-র লেখক আবুল ফজল সম্রাটের এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন— ‘বাদশা তাঁর খুব ছোটবেলা থেকেই চিত্রকলার প্রতি বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন আর এ ব্যাপারে তিনি অন্যদের উৎসাহও যোগাতেন অনেকখানি। কেননা তিনি মনে করতেন ছবি বা তসবির হল একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ। তাই শিল্পচর্চার বেশ প্রসার হল তাঁর সাম্রাজ্যে। অনেক শিল্পী খ্যাতিও অর্জন করলেন। দরবারের রাজকর্মচারী ও করণিকেরা সম্রাটের কাছে প্রতি সপ্তাহে নানা ধরনের ছবি হাজির করতেন। বাদশা সেই ছবির কারুকুশলতার উৎকর্ষ তারিফ করে পুরস্কারও দিতেন শিল্পীদের। কারও বা মাসিক তনখা বাড়িয়ে দিতেন খুশি মনে।’
শিল্প ও শিল্পী উভয়কেই আকবর লালন করেছেন সযত্নে। ধর্মীয় অনুশাসনের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করেছেন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে। আকবর জানতেন ইসলামের কট্টরপন্থীরা চিত্রকলা চর্চার বিপক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে একবার তিনি ব্যক্তিগত বন্ধুদের আসরে মন্তব্য করেছিলেন, ‘এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা ছবি আঁকাকে ছোট চোখে দেখেন। আমি তাঁদের অপছন্দ করি। আমার তো মনে হয় চিত্রশিল্পী তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করে থাকেন। শিল্পী যখন কোনও প্রাণীর ছবি আঁকেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একে একে রূপায়িত করতে থাকেন তখন অবশ্যই তাঁর মনে হয় যে তিনি ওই চরিত্রটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারছেন না। আর তখনই তাঁকে বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় সেই পরমেশ্বরের কথা যিনিই কেবল জীবন দিতে পারেন। এভাবেই সেই অপারগ শিল্পীদের ঈশ্বর জ্ঞানের চোখ খুলে যায়।’
দুই
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই জীবনের প্রথম দিকে ইরানের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পকলা আকবরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বেশ বুঝেছিলেন তাঁর সমধর্মী পূর্বসূরিরা ভারত শাসনের রাজদণ্ডটি ভাল করে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এদেশের মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির অভাবে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সূত্রে তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল মোগল সাম্রাজ্যকে সুস্থিত করতে হলে ভারতের মূল অধিবাসী হিন্দুদেরও আস্থা অর্জন করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে দৃঢ করে ন্যায় ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই হয়ে উঠল সম্রাট আকবরের স্বপ্ন।
এক সুসংগঠিত সাম্রাজ্য তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে একটি মুক্ত উদার সমাজব্যবস্থা কায়েম করার প্রচেষ্টা ছিল আকবরের। তাঁর পূর্বপুরুষের ফেলে আসা ভিটেমাটির সাংস্কৃতিক গন্ধটি তিনি এদেশের বাতাসেও ঘুরেফিরে ভাসতে দিয়েছেন। দক্ষিণ-মধ্য এশিয়া, ইরান এবং কিছুটা পরোক্ষভাবে চিন ও মঙ্গোলিয়ার শিল্পভাবনার সূত্রগুলো আকবরের আগের মুসলিম জমানায় এদেশের স্থানীয় শিল্পচেতনার সঙ্গে সবে মিশতে শুরু করেছিল। আকবর সেই মিশ্রণে প্রয়োজনীয় গতিসঞ্চার করলেন। ফলে পশ্চিম ভারতীয় শিল্পরীতি, সুলতানি আমলের চিত্র-প্রক্রিয়া ও হিমালয়ের ওপার উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ থেকে আমদানি করা শিল্পের এক নতুন ঢং মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল আকবরি আমলের শিল্পকলায়।
সাম্রাজ্যগঠনে যেমন তাঁর এক ব্যাপক সামগ্রিক দর্শন ও পরিকল্পনা ছিল তেমনই তাঁর সময়কার চিত্রচর্চা, সঙ্গীতসাধনা, কারুকলা এমনকি ধর্মচর্চার মধ্যেও তিনি আনতে চেয়েছিলেন তাঁর সেই ‘টোটাল ভিশনের’ ছায়া। তিনি বুঝেছিলেন একটি সাংস্কৃতিক নতুন নগরী গড়ে তোলা দরকার। তাই ১৫৬৮ থেকে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ফতেপুর সিক্রিতে স্থাপন করলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা রাজধানী, যেখানে জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, কারিগর, ধর্মালোচক সকলেরই নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দেওয়া হল ঢালাওভাবে। এখানে আসতে শুরু করলেন পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জ্ঞানপিপাসু মানুষ। এই ফতেপুর সিক্রির ইবাদতখানায় সম্রাটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে চলত নানা আলোচনা। সেই মন্থনে তৈরি হল সকল সমন্বয়ের এক নিকষিত হেম ‘দীন-ই-ইলাহী’, যার মূলমন্ত্র ছিল ‘সুলহ-ই-কুল’ বা সবার তরে শান্তি।
বিবিধের মাঝে মিলন, অনৈক্যের মাঝে ঐক্য; আকবরের জীবনে এই ছিল সত্যের পথে যাত্রার পাথেয়। ভারতের বিভিন্ন জীবনধারণের উপাদানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শ্ৰেষ্ঠ, তা খুঁজে বার করতে আকবর বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, বাস্তুবিদ্যায় বা চিত্রকলায় আকবরের নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চলত সবসময়। তাঁর তৈমুরীয় পূর্বপুরুষেরা যেভাবে বুখারা, সমরকন্দ ও অক্সাসের বড় বড় শহর নির্মাণ করে সাজিয়ে তুলেছিলেন, তেমনই আকবরও চেয়েছিলেন তাঁর সাধের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিকে গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, উপাসনাগৃহ, শিল্পশালা দিয়ে সাজিয়ে দিতে। হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন ফতেপুর সিক্রি। তাঁর সেই আদর্শ নগরীর বুলন্দ দরওয়াজা, দিওয়ানি খাস, পাঁচমহল, সেলিম চিস্তির সমাধি সে যুগের স্থপতিদের প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর বহন করে আসছে।

ফতেপুর সিক্রিতে যোধাবাই-এর মহল এবং আকবরের প্রাসাদে আঁকা হয়েছিল বেশ কিছু মুর্যাল। এর কোনও ছবি হিন্দু শিল্পীর আঁকা; কোনও কোনও ছবি একেবারে পারসিক। ধরে নিলে ভুল হবে না যে, রাজকার্যের নানা ব্যস্ততার মধ্যেও আকবর নিজে এসে ছবি আঁকার তদারকি করতেন। আর স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রকলার যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে সে কথা আকবর বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর এই পরিকল্পনা মারফত। রাজপ্রাসাদের এই মুঘল মুর্যালগুলো আঁকার সময় বোধ হয় ১৫৭৫। পার্সি ব্রাউনের মতে, ফতেপুর সিক্রির দেওয়াল অলঙ্করণের সূত্রেই আকবরের আকাঙ্ক্ষা জাগে মুঘল চিত্রকলার সুসংহত শৈলীর এক বিশাল সম্ভার গড়ে তোলার।
শিল্পের নানা শাখায় আকবরের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। মুসলমান লেখক-শিল্পীরা কলমকারিকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নত করেছিলেন যুগে যুগে। দরবারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল তো চিত্রকলা থেকে ক্যালিগ্রাফিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আকবরও এই লেখনী-শৈলীর কদর করেছিলেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে। দক্ষ ক্যালিগ্রাফার হিসেবে কাশ্মীরের মুহম্মদ হোসেনকে ‘জরিন কলম’ বা স্বর্ণ কলম উপাধিতে ভূষিতও করেছিলেন। আকবরের এই শিল্পচেতনা যে নানা ধারায় প্রবাহিত হত তার আর একটি উদাহরণ তাঁর আমলের স্বর্ণমুদ্রার অলঙ্করণে। শিল্পী আবদুস সামাদকে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ‘মাস্টার অব দি মিন্ট’ নিযুক্ত করেছিলেন আকবর হয়তো এই ভেবেই যে ছবির পাতার মতই মুদ্রার ধাতুর পাতটি চিত্রের সৌন্দর্যে মনোহারী হয়ে উঠবে। আসিরগড় দুর্গজয়ের পর তাঁর মুদ্রায় ফুটে ওঠে ফুললতাপাতার কারুকাজের মধ্যে এক বাজপাখি। আগ্রা থেকে প্রচারিত মুদ্রায় সেই একই ধরনের কারুকাজের মাঝে ভেসে বেড়ায় একটি হাঁস আর সেই যুগপুরুষ রাম এবং সীতাকে নিয়ে তাঁর সেই অর্ধ মোহরখানা যেন। মিনি সাইজের সোনার পাতে এক অপূর্ব মিনিয়েচার।
কারুশিল্পেও বাদশাহি অনুরাগ ছিল দেখার মত। অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোসন, তাঁবু, গালচে, জ্যামিতিক জাফরির কাজ— আকবরি যুগের সবেতেই ছিল শিল্পরুচির ছোঁয়া। মুঘল বাদশারা ফুল ভালবাসতেন তাই ফুলে ফুলে ভরে যেত তাঁদের সাজানো বাগান। মণিমুক্তোর মধ্যে আকবরের বিশেষ পছন্দ ছিল পান্না। দরবারের শিল্পী কারিগরেরা এই পান্নাকে মণির জগৎ থেকে তুলে এনেছিল শিল্পের পর্যায়ে নানা কারুকাজে খচিত করে। রবীন্দ্রনাথের মত আকবরও হয়তো ভাবতেন তাঁর চেতনার রঙে পান্না হয়েছিল সবুজ। এই পান্না-পসন্দ সম্রাটের কাছে রত্নটি ছিল আনন্দ, অধ্যাত্মচেতনা ও যাদুমন্ত্রের প্রতীক।
শিল্পসংস্কৃতির আর এক শাখা সঙ্গীতেও আকবরের অধিকার ছিল যথেষ্ট। নিজে তিনি হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীত শিখেছিলেন লাল কলাবন্তের কাছে। নাকাড়াও বাজাতে পারতেন তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে। আবুল ফজল লিখেছেন, জনা ছত্রিশ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন আকবরের রাজসভায় আর তানসেন তো আবুলের মতে সেই বিরল প্রতিভা যাঁর মত শিল্পী ভারতবর্ষে হাজার বছরের মধ্যে জন্মাননি। আর ছিলেন বাবা রামদাস। রাজদরবারে মিঞা তানসেনের পরেই ছিল তাঁর খ্যাতি। ইরানি, তুরানি, কাশ্মীরি পুরুষ-মহিলা নানা ধরনের শিল্পীরা আলো করেছিলেন আকবরের সঙ্গীতসভা।
স্থাপত্য, সঙ্গীত, উদ্যানকলা, বয়নশিল্প, কারুকলা শিল্পের সবক্ষেত্রেই আকবর ছিলেন পরম এক রসিক। আকবর-সভার জৈন পণ্ডিত সিদ্ধিচন্দ্ৰ উপাধ্যায় সংস্কৃত একটি শ্লোকে বাদশার গুণকীর্তন করেছেন: ‘ন সা কলা ন তদ্ জ্ঞানম্, নতদ্ বৈর্যং, ন তদ বলং। সহীন, যুবরাজেন যএ নৈবোদ্যমঃ কৃত৷’ এমন কোনও কলা নেই, এমন কোনও জ্ঞানের শাখা নেই, এমন কোনও ধৈর্য বা সাহসের বিষয় নেই, সে ব্যাপারে যুবরাজ উদ্যম দেখাননি।