মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি যুগসন্ধির নাম। উনিশ শতকীয় আলোর প্রবল বিচ্ছুরণ। যখন ইংরেজ শাসন ১৭৫৭-র পর বাংলা জুড়ে বসল তখন আমাদের প্রচলিত সংস্কৃতি ও সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধ যেমন ক্ষয় পেতে লাগল তেমনই সমাজের বহুকালের কুপ্রথাগুলি লোকসম্মুখে যেন লজ্জা ও ঘৃণা নিয়ে এসে দাঁড়াল। পশ্চিমের ধার করা আলো কিনা এই নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক পণ্ডিতের টোলকে ধ্বনিগর্ভ করে তুলল। কিন্তু সত্য যা তা দিনের মতোই স্পষ্ট। তা হল, তথাকথিত হিন্দুসমাজে জাতপাতের অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচার। ব্রিটিশ শাসনে যেমন অর্থনৈতিকভাবে আমরা দেউলিয়া হতে শুরু করলাম তেমনই শিক্ষার নতুন আলোয় আমরা নিজেদের মুখ আয়নায় দেখতে শিখলাম। এ আলোর প্রথম ধারক রাজা রামমোহন রায়। তাঁর অবদান বিস্মরণের অতীত। তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আমরা বহু সমাজ-সংস্কারকের দেখা পাই। ধর্মের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেইসব মনীষী উনিশ শতকের বাংলাকে এমন আলোকিত করল যে, তার প্রভাবে পাশ্চাত্য পর্যন্ত দুলে উঠেছিল। সম্ভবত কলকাতা তখন ব্রিটিশ শাসকদের রাজধানী ছিল বলে এমন করে নগর কলকাতা বিদ্যায় বিভবে সেজে উঠতে পেরেছিল।
এই আলোয় আমাদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে ফিরে দেখার নাম মধুসূদন দত্ত।
১৮২৪ সালে জন্ম তাঁর। যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রাম থেকে কলকাতা শহরের খিদিরপুর অঞ্চলে আসেন নিতান্ত বালক বয়সে। পিতা রাজনারায়ণ বিত্তশালী ছিলেন। মধুসূদনকে তিনি সেকালে বিখ্যাত ক্যালকাটা গ্রামার স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন তখন দেখা যায় তিনি ল্যাটিনসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী। হিন্দু কলেজ তখন বিত্তবান যুবসমাজের বিচরণক্ষেত্র। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে যেমন-তেমনই বিলাসে-ব্যসনে এঁরা সর্বাগ্রগণ্য। উনবিংশ শতকের বাবু কালচারে কলকাতা তখন বিশেষ অভ্যস্ত। পায়রা ওড়ানো, বাইনাচের আসর বসানো, ইংরেজি মদ্যপান, ইংরেজ বাবুবিবিদের দুর্গাপুজোয় নিমন্ত্রণ করা, ইত্যাদি নানাভাবে বিত্তপ্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলত। এর মধ্যেই রামমোহন তাঁর সংগ্রাম চালিয়েছেন। শাস্ত্র থেকেই যুক্তি এনে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাশ হচ্ছে। অন্য দিকে একদল শিক্ষিত নবযুবক হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে যা কিছু প্রথা সব যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করছেন। তাঁরা কিছুতেই প্রচলিত বলেই সবকিছু গ্রহণ করছেন না। বাঙালির মানস-জগতে অবিরাম সংগ্রাম চলছে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের। বিত্তবান শিক্ষিত এই বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই এই বিপ্লবী বাঙালির উদ্ভব। মধুসূদন সেই বৈপ্লবিক আলোর অন্যতম নাম।
কীভাবে তাঁর এই নবচেতনার উন্মেষ হল যদি দেখতে হয় তাহলে তাঁর গড়ে ওঠাটা ফিরে দেখব। এখানে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। এই যে তিনি যশোরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এলেন, এর ফলস্বরূপ তিনি কলকাতার অন্যতম ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন। এলিয়েনেটেড। এই এলিয়েনেশন তাঁর সাহিত্যে ফল্গুধারার মতো বহমান। অথচ দেখতে গেলে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বহু বহু মনীষী কলকাতায় এসেছেন। এখানকার আদি বাসিন্দা তাঁরাও ছিলেন না। বিদ্যাসাগর তো সেই কোন পাড়াগাঁ বীরসিংহ থেকে কলকাতা এলেন। তাঁর জন্ম মধুসূদনের থেকে মাত্র চার বছর আগে। কিন্তু দুজনের ভাগ্যই বিড়ম্বিত। দু’রকমে। ঈশ্বরচন্দ্র দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমাজে সংস্কার এনেছেন। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছেন। সমাজের সঙ্গে, বা বলা ভাল, অত্যাচারিতের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ঘটেছিল। বিরোধিতার সঙ্গে সম্মানও পেয়েছেন তিনি। কিন্তু মধুসূদনের ভাগ্যবিড়ম্বনা পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। যে সংস্কার তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে এনেছিলেন তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা সমাজের সর্বস্তরে ছিল না।
উনিশ বছর বয়সে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে তিনি খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম না নিয়ে কেন খ্রিস্ট ধর্ম নিলেন সেই যুক্তি তিনি নিজে দেননি। তাই অন্তর্নিহিত কারণ জানা যাচ্ছে না। তবে পরিবার থেকে বিয়ের কথা উঠতে মধুসূদন ধর্মান্তরিত হন এটি জানা। অপরিচিত অশিক্ষিত বালিকাবয়সী কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন না, তাই অন্য ধর্ম নিলেন এবং ত্যাজ্যপুত্র হলেন। তাঁর এই পরিবার-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তেইশ বছর পর্যন্ত তিনি পিতার থেকে মাসিক ভাতা পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ভাতা বন্ধ হয়। তখনও মধুসূদনের সাহিত্যিক সত্ত্বার জন্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ, তাও ইংরেজিতে লেখা, এই ছিল তাঁর ঝুলিতে।
এরপর মাদ্রাজ পর্ব, বিবাহ ও বিচ্ছেদ পর্ব। চরম দারিদ্র ও অসম্মানের মধ্য দিয়ে জীবন কেটেছে তাঁর।
ফিরে যাই আর একবার। তিনি তের বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সন ১৮৩৭। ঠিক একবছর আগে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ রামমোহন রায়ের প্রবল উপস্থিতি তখন নাগরিক মানুষকে উদ্বেল করছে। তাঁর এই তথাকথিত সনাতনী কৌলীন্য প্রথাকে উৎখাত করার ফলে সকলেই যে খুব সুখী হয়েছিলেন তা তো নয়। অনেক অনেক হিন্দু পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন সে আমরা জানি। সমাজে তাঁর দুরকম প্রভাবই ছিল। পক্ষে ও বিরুদ্ধে, দুদিকেই মানুষ ছিলেন। মধুসূদনের মনে তাঁর অনুকূল প্রভাব পড়েছিল বলেই আমরা জানি। তের/ চোদ্দ বছরের বালক বলে ভাবা একালের বাঙালি সেকালের মানসিকতা বুঝবেন আশা করা যায় না। সে সময় তের কিংবা চোদ্দ বছরে তারুণ্য আসত। স্বাধীন চিন্তার পথিক নব্যশিক্ষিত যুবক ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। বিলাসে অভ্যস্ত আর সব বিত্তবান বাঙালি যুবকের মতো মদ্যপানে অভ্যস্ত আসেন কলেজে।
১৮১৮ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠার পর মাত্র উনিশ বছর পর এখানে আসেন তিনি। তার মধ্যেই ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। হিন্দু কলেজের তিন স্মরণীয় শিক্ষকের নাম, ডেভিড ড্রামন্ড, ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন। যদিও মধুসূদন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওকে শিক্ষক হিসেবে পাননি, কারণ তিনি তখন ইহজগতের মায়া কাটিয়েছেন, তবু তাঁর শিষ্যবর্গ, ইয়ং বেঙ্গলের বাকিরা তাঁকে যেন তাঁর স্মৃতির মধ্যে অনুসারী ধারণার মধ্যে সদাজাগ্রত রেখেছিলেন। শারীরিক উপস্থিতির চেয়ে এই উপস্থিতি কম নয়। মাইকেল সেই ইয়ং বেঙ্গলের অনুসারী। এই সোসাইটির মূল লক্ষই ছিল তথাকথিত সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলে আঘাত।
অন্তর্মুখ মধুসূদন ভাল ছাত্র হলেও অনেক নম্বর পেতেন এমনটা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারছি তাঁর বিরল মনীষার কথা।
কলকাতায় ফিরে এসে পরিণত বয়সে মধুসূদন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। ‘রত্নাবলী’ নাটকের প্রদর্শন দেখে আহত মধুসূদন তাঁর প্রিয় বাল্যসখা গৌরদাস বসাকের কাছে হতাশা ব্যক্ত করেন। একে কি নাটক বলে? গৌরদাস হেসেছিলেন। এর চেয়ে ভাল কিছু বাংলায় কি আশা করো? কে লিখবে বাংলায়? মধুসূদন লিখে ফেলেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক। গ্রিক মহাকাব্য থেকে শেক্সপিয়র পর্যন্ত যাঁর গতি তিনিই তো যোগ্য ব্যক্তি! শোনা যায়, পাথুরেঘাটার রাজা ও পাইকপাড়ার রাজবাড়ির দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় মাইকেল শুনেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা অসম্ভব। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই তিনি অমিত্রাক্ষর বা মুক্ত পয়ারে কবিতা লিখে দেখিয়ে দেন, সম্ভব। বাংলার কাব্যভাষা নতুন শক্তি পায়। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যের আলোচনায় লিখছেন,— “বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে তাহা মিত্রাক্ষর। কোনো প্রগাঢ় বিষয়ের আলোচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক অথবা অভ্যাসের দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। …এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে”। স্পষ্টতই সেই সময়ের নবচেতনাপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানুষের উচ্চারণ। আরও গূঢ় আরও গভীর আত্মানুসন্ধানে মানুষ সাহিত্যের আশ্রয় চাইছে।
ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, এসবই একটি বৃহৎ ও কালজয়ী সৃষ্টির পূর্বপট মাত্র। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। মধুসূদনকে যে জন্য আমরা প্রণাম জানাব তা হল ভারতবর্ষের প্রথম মহাকাব্যের বিনির্মাণ তাঁর হাত ধরেই হয়। ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত তাঁর অবদান ছন্দ ও বিষয়, রচনারীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেই পারেন কারণ এখনও সেই প্রাসঙ্গিকতা আছে, কিন্তু রামায়ণকে বিষয় করে বেছে নেওয়ার মধ্যে তাঁর যে সাহসী ও বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। এর আগে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গিতে রামায়ণ লেখা হয়েছে। কিন্তু মূল ভাব ও চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়নি। মধুসূদন দত্ত প্রথম রামায়ণের বিনির্মাণ করেন।
তিনি যখন রামায়ণের বিনির্মাণ করছেন তখন আমাদের মনে পড়বে যে তিনি বহু পূর্বেই স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। অন্তত সমাজ তাঁর ধর্মত্যাগের কথা সোচ্চারে প্রকাশ করেছে। তাঁকে যত দূর সম্ভব টেনে নামিয়েছে। কিন্তু আসলে তাঁর মনোজগতে হিন্দু ধর্মের নানান কুসংস্কার ও অত্যাচার তাঁকে বিরক্ত করেছে। সাজসজ্জায় চলাফেরায় তিনি সারাক্ষণ প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। কিন্তু শুরুতেই রামমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। দুজনেই মেধার দিক থেকে দানবিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এগারোটি ভাষা জানা মধুসূদন যে রামমোহনের ভাবধারায় প্রভাবিত নন সেকথা অবিশ্বাস্য। প্রসঙ্গত, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। অতএব এই সঙ্গ তাঁকে আরও নিবিড়ভাবে রামমোহনের অন্তর্জগতে প্রবেশে সাহায্য করেছে। এর সঙ্গে উল্লেখ্য বিদ্যাসাগরের প্রভাব। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করেননি বটে কিন্তু আস্তিক্য নিয়ে বা ধর্মের বাড়াবাড়ি যে তাঁর ছিল না সে জানাই যায়। বরং হিন্দু সমাজে মেয়েদের অবস্থান তাঁকে বিচলিত করেছে। মাইকেল তাঁর অপরিমিত স্নেহ পেয়েছেন। এবং আজীবন ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড হিসেবে বিদ্যাসাগরকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করেছেন। অথচ বিদ্যাসাগর তাঁর চেয়ে মাত্র চার বছরের বড় ছিলেন।
এইটুকু পারিপার্শ্বিকতার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। আর একটি কথার উল্লেখ বড় প্রয়োজন। মধুসূদন যে সময় মদ্যপ বলে দুর্নাম কুড়িয়েছেন খোঁজ করলে দেখা যাবে তখন প্রায় সমস্ত আলোকপ্রাপ্ত নগরবাসী মদ খান। তফাত এই যে মধুসূদন প্রকাশ্যে করতেন। এমনকি বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বসেও। বাকিরা লুকিয়েচুরিয়ে। কিন্তু সব সত্য গোপন থাকে না। মনীষীদের মদ্যপান সম্পর্কিত ইতিহাসে সেকথা নিশ্চয় কেউ না কেউ লিখবেন।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের কাছে যাতায়াত সম্ভবত তাঁকে খ্রিস্ট ধর্মে আকৃষ্ট করেছিল সত্য কিন্তু এরপরেও কিন্তু কোনও খ্রিস্টীয় বিষয় তাঁর সাহিত্যের বিষয় নয়। দেশ ও ভাষা যে তাঁর কতখানি ভালবাসার বস্তু তা তাঁর বিষয় নির্বাচনেই স্পষ্ট। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা তাঁর হৃদয়ের বস্তু।
তিনি ভারতাত্মার প্রতীক দুটি মহাকাব্যের একটিকে বেছে নিলেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ থেকেই তুলে ধরলেন একটি বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ। কোথাও মহৎ চরিত্রের কুৎসা নেই। বরং মহান অবতার বলে বর্ণিত চরিত্রও যে আদতে মানুষ এবং মানবিক দুর্বলতা যে তাঁরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাই তুলে ধরলেন। আমাদের ধারণায় যখনই কোনও মানুষকে আমরা দেবতার আসনে বসাই তখনই তাঁর সমস্ত মানবিক দুর্বলতাকে উচ্ছেদ করে ফেলি। মধুসূদন নিজের চরিত্রের সেই দুর্বলতা জানতেন। একই সঙ্গে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই বাল্মীকির কথা বলতে গিয়ে বন্দনাকালে বলছেন, “নরাধম আছিল যে নর নরকুলে চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়…”। সরস্বতীর প্রসাদে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হলেন। বিদ্যার আলো বিনা চেতনার মুক্তি নেই, এই আপ্তবাক্য মধুসূদন নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন। জানালেন, জগতে তাঁর কাজ নিন্দিত হলেও বিদ্যার আলো পেলে সে অন্য মানুষ হয়।
তিনি লিখলেন মেঘনাদবধ কাব্য।
আমরা একটু দেখে নেব, বিনির্মাণ বলতে কী বোঝায়। প্রচলিত কাহিনি ও সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা প্রধান নায়ক চরিত্রের দুর্বলতাগুলিকে আলোয় আনা। যে সব দুষ্ট চরিত্র আঁকা হয়েছে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সৎ গুণগুলি তুলে ধরা। এর ফলে নায়ক প্রতিনায়কে পর্যবসিত হচ্ছেন, প্রতিনায়ক নায়কে। এবং কথা হচ্ছে, এটি করতে গিয়ে লেখক কিন্তু মূল মহাকাব্যের কাহিনি থেকে সরছেন না। বেদব্যাস যেমন মহাভারত মহাকাব্যে ‘ব্যাসকূট’ রেখেছেন প্রতি পদে, যে রহস্যের উন্মোচনে আদিকবির বক্তব্যকে নতুন আলোয় চেনা যায়, ঠিক তেমনই রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনির আড়ালে লুকিয়ে কূটরহস্য উদ্ঘাটন করে চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দেবোপম চরিত্রগুলির দুর্বলতা চোখের সামনে আনলেন মধুসূদন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। প্রমীলাসুন্দরী লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে চলেছেন। সঙ্গে সখীদল। পবনপুত্র হনুমান প্রহরায় আছেন। তিনি প্রবেশে বাধা দিলেন। উত্তরে প্রমীলা তাকে জানালেন, তিনি রামের সঙ্গে কথা বলতে চান, নরেতর বানরের সঙ্গে নয়। রাম প্রমীলাকে বিনা বাধায় লঙ্কায় প্রবেশ করতে দিলেন। প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাম আড়ালে হনুমানকে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? প্রমীলার সঙ্গে রণে আমার জয় আশা করো? অবতারের মুখে এমন কথা শুনিয়েছেন মধুসূদন। লক্ষ্মণ যখন মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করছেন, লঙ্কাপুরীর স্বর্ণশোভা তাঁকে মুগ্ধ করছে। তিনি লোভের বশে বিভীষণকে সেই কথা বলছেন। নিরস্ত্র মেঘনাদকে যে লক্ষ্মণ আক্রমণ করছেন এটি মূল রামায়ণে আছে। অথচ ক্ষত্রিয়ের ধর্মে নিরস্ত্রকে যুদ্ধে আহবান করা ধর্মবিরুদ্ধ। মধুসূদন এই একটি অন্যায়কেই তুলে ধরলেন জনসমক্ষে। দেখিয়ে দিলেন, যুদ্ধজয়ের জন্য মহামান্য অবতারও এমন অন্যায় আশ্রয় করছেন। কেন এই ছল? অবশ্যই মেঘনাদ প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রবল ছিলেন। সম্মুখসমরে তাঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব। অবতার একনিমেষে দেবতা থেকে মানুষ হলেন। অন্যদিকে যিনি রাক্ষস, তিনি ক্ষাত্রধর্ম মেনে প্রজাপালন থেকে যুদ্ধ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে দেবগুণ আছে। মেঘনাদ চরিত্রে যে পরিমাণ পিতৃভক্তি আছে স্বয়ং রামচন্দ্রও ততটা দাবি করতে পারেন না।
যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্যবীজ মূল রামায়ণেই নিহিত তাই কেউই এর যাথার্থ অস্বীকার করতে পারেন না।
মধুসূদন প্রথম আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, বাল্মীকি রামায়ণ আসলে এক সম্পন্ন প্রজাপ্রিয় সমরকুশল সম্রাটের অন্যায় যুদ্ধে পরাজয়ের কাহিনি। এই পরাজয় আসলে তাঁর নৈতিক জয়ের কথা বলে। পার্থিব বিলাস বৈভব, মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত শোক, প্রকৃতপক্ষে কোনও পরাজয়ই নয়। প্রকৃত পরাজয় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’, এইভাবে পরের সম্পদ হস্তগত করা। মিথ্যাকে কোনও ঋষির প্রবচনই সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।
কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখছেন, দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার নায়কগণ এমনই যথাযোগ্য গুণে বিভূষিত যে, তাহাতে রামায়ণ প্রচারয়িতা বাল্মীকিকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে।
এমন করে রাবণ চরিত্র আঁকলেন কেন মধুসূদন? মনে হয় রাবণ যেমন শক্তিশালী হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বিত, এক নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকার, চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি প্রজাপ্রিয় স্নেহময় পিতা ও স্বামী, মধুসূদন নিজেকে রাবণ চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন। রাবণ তাঁর কাছে ‘গ্র্যান্ড ফেলো’, যাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি সিংহহৃদয় এবং জগতে পরাজিত এক মহান সম্রাট। কিন্তু মেঘনাদ? রাবণের প্রিয়তম সন্তান? তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক কই? শুচিশুভ্র চরিত্র তাঁর। ক্ষাত্রধর্ম পালন থেকে প্রেমিক ইন্দ্রজিৎ, মাতাপিতার প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি তাঁকে যেন সবরকম জাগতিক কালিমার ঊর্ধ্বে রাখে। মেঘনাদ তাই মধুসূদনের মানসসন্তান। এই মনোভাবের পরিচয় পাই যখন তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠিতে মাই ফেভারিট ইন্দ্রজিৎ বলে সম্বোধন করেন।
উল্লেখ করব, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের রচনা ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য’ থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি কথা।
“জীবনে যে সব কথা অনুচ্চারিত বা অর্ধোচ্চারিত, সাহিত্যে তার জন্য আসন পাতা থাকে। মেঘনাদবধ কাব্যে আনন্দের সঙ্গে বেদনার যুগপৎ অবস্থান থাকল। ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবনের বৈপরীত্য দুই খাতে বইছিল। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ, ইন্দ্রজিত, মন্দোদরী, ও প্রমীলা সকল জটিলতা অকাতরে একসঙ্গে ধারণ করে আছে। যেমন মানুষের দুর্মদ আশার প্রতীক, তেমন আশাভঙ্গেরও। এ কাব্যের নায়ক সর্ববিধ সুস্থতার প্রতীক। সে দক্ষ সেনানী, প্রেমময় স্বামী, স্নেহকাতর পিতা, জনপ্রিয় শাসক, এবং সুতনু নর। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে যা কিছু অভিপ্রেত সে সকল সদগুণের অধিকারী। রাবণ শক্তিশালী পুরুষ। তাঁর প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্য কম্পমান, কিন্তু রাজ্যচ্যুত বনচর সামান্য দুই যুবক আর তাদের তদধিক অকিঞ্চিতকর রাবণের সুরক্ষিত পুরী ও সুসজ্জিত সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। তবে কি শক্তি শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়? বীর্য নয় বীর্যশালিতার ভিত্তি?”
মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য কোনও ভিত্তিহীন রচনা নয়। মহাকাব্যকে নতুন যুগের আলোয় রেখে দেখা। এই দর্শন মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে জীবনে তিনি শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বহুতর অপমান অসম্মান ও অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর শক্তি শক্তিমত্তার পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি। সমাজের বাধা প্রতিপদে তাঁকে নায়ক থেকে প্রতিনায়কে পর্যবসিত করেছে। সেই অভিজ্ঞতা প্রতিভার আশ্রয়ে এসে জন্ম দিয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যের।
আমাদের বিদ্যাবিমুখ মন মাত্র দেড়শ বছর আগের বাংলা ভাষার রচনা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্র আর অনুকূল নয়। যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা হচ্ছে (সন ১৮৬১) তখন আমাদের দেশ পরাধীন। এক বহিঃশত্রু দেশ অধিকার করেছে। আর এখন আমরা দেশের মধ্যেই সেই শত্রুর আস্ফালন দেখতে পাচ্ছি। আবারও তাই মধুসূদনকে ফিরে পড়ার সময়। তাঁকে ছাড়া তাঁর সাহিত্য ছাড়া বাঙালির মনন বাঙালি মেধাচর্চা অসম্পূর্ণ।
“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;— তা সবে অবোধ আমি! অবহেলা করি, পরধনলোভে মত্ত…”। একথাটি আধুনিক বঙ্গেও প্রাসঙ্গিক।






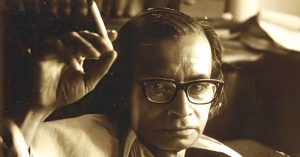








One Response
অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি লেখা। লেখিকাকে অভিনন্দন।