আমরা এই শহরের মধ্যে একটা লুকোচুরি খেলছি। আমরা, মানে পাঁচজন বন্ধু। যাদের পরিচয় হয়েছিল অর্থনীতি পড়ার টিউশনে। তিনজন ছেলে, দুজন মেয়ে। আমরা যখন বললাম, বোঝা গেল এই তিনজন ছেলের মধ্যে একজন আমি।
আমার নাম দীপ। দীপ নামটি আমি চিরকাল দীপ লিখেছি। দ্বীপ লিখিনি। দ্বীপ লিখতে ইচ্ছে হত। আইল্যান্ড শব্দটি আমার পছন্দ ছিল। কারণ প্রথম দ্বীপ আমি দেখেছিলাম টেলিভিশনের পর্দায়। সাদা বালি, চারিদিকে নীল জলরাশি। মাঝে হারিয়ে যাওয়া দুজন তরুণ-তরুণী। তারা উদ্দাম যৌনক্রীড়া করছে। দ্বীপ আমি লিখতে পারিনি, কারণ আমার নাম দীপ। একটা ক্ষীণ আলো। উৎসবের দিনে উঠোনে জ্বলে থাকে। তারপর কখন নিভে যায়, কেউ জানতে পারে না।
অপর দুই বন্ধুর নাম অর্ণব এবং জয়। তাদের নাম নিয়ে বিশেষ কোনও বক্তব্য নেই আমার, এখানে।
দুজন মেয়ের নাম— ডলি এবং সুপর্ণা। ডলি নামটি আশ্চর্য খারাপ। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি এটাই ওর প্রকৃত নাম। মনে হয়েছিল, বাড়ির নামটিই অবশেষে স্কুলের নামের খাতায় চলে এসেছে। কিন্তু একথা সত্যি নয়। ওর দিদির নাম মলি। সেই নাম মিলিয়ে বোনের এই নাম দেওয়া হয়েছে। টিউশন ব্যাচের কোনও এক অশ্লীল সহপাঠী ওর বড় বড় দুটো বুকের দিকে তাকিয়ে ডলি-মলি শব্দটা ব্যবহার করে। অথচ ছেলেটি জানত না ডলির দিদির নাম সত্যিই মলি। সুপর্ণার নাম এতদিনে কোনও বিখ্যাত কবির বইয়ের নামকরণের বিষয় হয়ে ওঠেনি।
যে শিক্ষকের কাছে আমরা অর্থনীতির পাঠ নিই, তিনি নিজেই অর্থনৈতিকভাবে খুব বিপর্যস্ত। ফলে, বেশি কিছু আশা আমরা কেউই তার থেকে আশা করি না। প্রতিদিন উনি নির্দিষ্ট সময়ের এক থেকে দেড় ঘণ্টা পরে আসেন। আসেন, একদিনও বলেন না যে পড়াবেন না। ফলে আমাদের দুঘণ্টার টিউশন ব্যাচ এক থেকে দেড় ঘণ্টারই হয়। হতাশ একজন লোক, যার সারা মাথা ভর্তি টাক। এসেই দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন কিছুক্ষণ। তার পোশাকে মাঝেমাঝেই লেগে থাকে অবাঞ্ছিত ঘাস ও মাটি। মনে হয়, এখুনি কোনও মাঠ থেকে গড়াগড়ি খেয়ে এলেন। আমাদের কোনও প্রশ্নেরই তিনি উত্তর দেন না। নিজের মত করে পড়ান, চলে যান। মাইনের বিষয়েও অত্যন্ত উদাসীন। আমরা তার মাইনে মেরে দিয়ে নিজেদের শখ আহ্লাদ পূরণ করি। জয়ের বেজির বাচ্চাটি তিনি সহ্য করতে পারেন না। যদিও জয় তাকে ছাড়া কিছুতেই টিউশনে আসতে চায় না। জামার ভেতর ঢুকিয়ে এনে প্রতিদিন জয় ছেড়ে দেয় টিউশন ঘরে।
শুধু স্যারকে নয়, এই বিষয়টি বিরক্ত করে অর্ণব এবং ডলিকেও। সুপর্ণার ন্যাকা বন্ধুরা চেঁচামেচি করে। তবে স্যারের সেই ক্ষমতা নেই, জয়কে এ বিষয়ে নিষেধ করেন। কারণ আমাদের অর্থনীতির স্যারের কোনও নাম নেই। তাকে কোনও নাম দিতে চাননি অভিভাবকরা। একজন নামহীন শিশু হিসেবেই তিনি বড় হয়েছেন। অবশেষে সকলের কাছে পরিচিত হন অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে। ফলে একজন নামবিহীন শিক্ষকের একজন নামযুক্ত ছাত্রকে এটুকু বলারও সাহস হয় না। এটি বলার সাহস আছে কেবল আমার ও ডলির। আমি বলব না, কারণ সত্যি বলতে, বেজির বাচ্চাটিকে আমার ভালই লাগে। বিশেষত হতাশাগ্রস্ত স্যারের পক্ষে যখন তা যন্ত্রণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা আমাকে এক পৈশাচিক আনন্দ দেয়।
আমার আকর্ষণ সুপর্ণাকে নিয়ে। যদিও ব্যাচের অধিকাংশ ছেলের মত তা যৌন আকর্ষণ নয়। প্রতিদিন আমরা যেভাবে বসি, তাতে করে মেয়েদের সীমানা হল সুপর্ণা এবং ছেলেদের সীমানা হলাম আমি। অধিকাংশ দিন সুপর্ণার হাঁটু থাকে আমার হাঁটুর ওপরে। এতে করে আমার শরীর যে খুব বেশি জেগে ওঠে এমন নয়। কারণ সুপর্ণার শরীরের থেকেও ওর গল্পের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি। সুপর্ণার আশ্চর্য সব গল্প। বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ওর রাতের অন্ধকারে যৌনক্রীড়া, বাংলা পড়ার ব্যাচে ইচ্ছে করে প্যান্টি পরে না যাওয়া, ইতিহাসের স্যারের গভীর রাতে পাঠানো মেসেজসমূহ, দুপুরবেলা বাথরুমে স্নানরত অবস্থায় ভূত দেখা, নিজেকে মাঝে মাঝেই কবরের ভেতর আবিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সুপর্ণার চমৎকার শরীরের থেকেও ওর এইসব গল্প বেশি আকর্ষণ করে আমাকে। বিশেষত, পড়া থেকে বেরিয়ে ও আমার হাতের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাঁটে। সেটি বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বের ওম আমিও অনুভব করতে পারি। যদিও সকলেরই ধারণা, সুপর্ণা নিয়মিত আমার সঙ্গেই শুচ্ছে। তাই ছেলেদের বসার সীমানাটা দখল করার কথা কারুর মনেই হয় না। সকলেই আশ্চর্য হীনম্মন্যতায় ভোগে।
ডলিকে তোলার একটা ছক কষেছে জয়। যদিও ছকটি দুর্বল। কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রেমটা ওভাবে কান্নাকাটি, আবেদন-নিবেদন করে হয় না। নিজের চরিত্রের বাইরে গিয়ে তো আরও হয় না। বেজির বাচ্চা পোষা জয় এমনিতে যতই ডাকাবুকো হোক না কেন, ডলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নরম। ফলে, জয়কে আলাদা করে কোনওদিন দেখার সুযোগ পায় না ডলি। জয়ের সমস্ত ক্ষেত্রে এই ডাকাবুকো স্বভাব এবং নিজের ক্ষেত্রে এই নরম শিশুটি হয়ে থাকা মনে মনে ও ঘৃণা করে। ঠিক যতটা ঘৃণা করে জয়ের বেজির বাচ্চাটিকে। আমাকে একাধিকবার চিঠি লিখে একথা জানিয়েছে ও। যদিও আমাদের চিঠির বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়াশুনো এবং তত্ত্বচর্চা। সেসব সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই যদিও। কিন্তু ডলির কাছ থেকে কিছু খুচরো যৌনতা পাওয়ার আশা আছে। ওর বুকদুটো আমাকে আকর্ষণ করে খুব বেশি। এছাড়া সামান্যতম আকর্ষণ আমি ডলির প্রতি অনুভব করি না। বাইরে বাইরে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, ওকে নিংড়ে নিলেও সামান্য উত্তেজক কোনও গল্প বেরোবে না। ওর জীবনটা এতটাই সাধারণ এবং নিয়মবদ্ধ।
তবে আমার আকর্ষণের কেন্দ্র অন্য একজন। অর্ণবের কাকার মেয়ে মায়া। ওদের বাড়িতেই থাকে। ওকে যত আড়াল আবডাল দিয়ে দেখছি, ততই প্রেমে পড়ছি। ছিপছিপে তরুণী, নিয়মিত সাঁতার কাটে। পড়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। আমাদের একেবারেই পাত্তা দেয় না। এই বিষয়টাই আমাকে তাতিয়ে দেয় আরও। বাংলা মাধ্যমের মেয়েরা আমার পক্ষে সহজ হয়ে গেছে। তবে অর্ণব একটি জলজ্যান্ত মৃতদেহ। সারাদিন গান ও ছবি নিয়ে পড়ে থাকে। কোনওটা করার ক্ষেত্রেই ওর কোনও উত্তেজনা নেই। কারুর প্রতিই ও কোনও আকর্ষণ অনুভব করে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ও এক অনন্ত ঘুমের ভেতর আছে। আমি ও জয় একদিন ওর প্যান্ট খুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, সত্যিই দাঁড়ায় কি না। তবে অর্ণবের এসব বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। ওর পেট থেকে কথা বের করাও অত্যন্ত কঠিন। আমাদের আড্ডা ঘরের অ্যাকোরিয়ামের রঙিন মাছ মনে হয় ওকে। সাঁতার কাটছে আর প্যাকেটের খাবার খেয়েই চলেছে। এক একদিন কেঁচো। ফলে, ওর মাধ্যমে বোনকে হাত করার কোনও সুযোগই আমি পাচ্ছি না।
অর্ণবের বাড়িটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যখন-তখন সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের দুই সৈনিক, অর্ণবের বাবা এবং মা। সহিংস যুদ্ধ। যুদ্ধাস্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে যায়। অর্ণবের ঘরের ছিটকিনিটি ছিল দুর্বল। ফলে, আমাদের প্রাণ এক একদিন বেশ দুরুদুরু করে। তবে সে সময়ে আমার মন পড়ে থাকে আরও বেশি মায়ার চিন্তায়। তবে দেখেছি মায়া সেই সময়টা বাড়িতে কোথাও লুকিয়ে থাকে। ওর বাবা মা, অর্থাৎ অর্ণবের কাকা ও কাকিমা দুজনেই স্কুলে চলে যান। জয়ের সঙ্গে মায়ার যতটা সুসম্পর্ক ততটাও আমি করতে পারিনি কখনও। এই ব্যর্থতাবোধ আমাকে কুরে কুরে খায়। প্রচণ্ড রাগ হয় অর্ণবের ওপরে। ওকে এক একদিন রঙিন অ্যাকোরিয়ামের ভেতর ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।
২
অর্থনীতি পড়ার শেষে আমরা পাঁচজন প্রতিদিন যাই এক সস্তার রেস্তোরাঁয়। সন্ধের প্রবল খিদেকে বাগে আনবার একমাত্র আশ্রয় এই রেস্তোরাঁ। স্টেশনের ধারে একটা টিনের চালওয়ালা দোকান। দেওয়াল পাকা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য এই, রাস্তা থেকে কিছুটা বাগানের পথ অতিক্রম করে এই দোকানের কাউন্টারে পৌঁছতে হয়। বাগানটা দোকানের মালিকেরই করা। বাগানে কিছু সস্তা ফুলের গাছ। অধিকাংশটাই আগাছা। তবে সেটুকু বাগান শহরের আর কোনও দোকানে নেই। তেমন সস্তার খাবারও থাকে না কোথাও। কোনও এক অজানা কারণেই শহরের ছেলেমেয়েদের এই দোকানটি পছন্দের নয়। তারা বড় বড় রেস্তোরাঁয় যায়। যেখানে খুব সহজেই তাদের পকেট ফাঁকা হয়ে আসে। এইটেই তাদের কাছে একপ্রকার সুখের ধারণা।
তবে যাই হোক, রেস্তোরাঁটির কিছু সমস্যা আছে। প্রথমত, কোনও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত, খাওয়ার জায়গাটিতে আলো তেমন নেই বললেই চলে। একজনই ওয়েটার। চূড়ান্ত ঘুষখোর এক ব্যাঙ্ক কর্মচারী ছিল সে। লাথি খেয়ে এসেছে এখানে ওয়েটার হতে। সেই জানিয়েছিল, মালিকের আলো বিষয়টা একদম পছন্দের নয়। ওয়েটারের পুরোনো স্বভাব যায়নি। টিপ বিষয়টাও সে টেবিলের তলা দিয়ে নেয়। তবে এই রেস্তোরাঁর সবচেয়ে সমস্যার বিষয় হল, মাংসের কিছু নিলে তা অধিকাংশ সময়েই কিছুটা কাঁচা থাকে। আমার বিশেষ সমস্যা এতে হয় না। অর্ণবের কিছুতেই কিছু যায় আসে না। জয় চিৎকার করে। মুখেই তুলতে পারে না ডলি এবং সুপর্ণা। তাই মাংসের কিছুই তারা কখনও অর্ডার করে না। মাঝে মাঝে এই চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে নিজেদের রেস্তোরাঁকে বাঁচানোর জন্য ওয়েটার আমাদের কিছু ঘুষ দেয়। ব্যাস, মুখ বন্ধ।
বর্ষার একদিন আমরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে অর্ডার করেছি টম্যাটো স্যুপ এবং মৌরলা মাছ ভাজা। ডলি এসব খায় না। তার জন্য অল্প কিছু সেঁকা পাঁউরুটি এবং মাখন নেওয়া হয়েছে। জয় নিজের আলুভাজা থেকে কিছু তুলে দিয়েছে ডলির প্লেটে। সুপর্ণা আমার পাশে, তখন ওর বিখ্যাত গল্পটি শোনাচ্ছিল। যে গল্পটি এর আগে আমি নয় নয় করে সাতাশবার শুনেছি। তবুও শুনতে একইরকম উত্তেজনা হয়। ও বলছিল, কীভাবে স্কুলের জীবনবিজ্ঞান স্যারকে ওর জামার ভেতরে হাত ঢোকাতে দিয়ে সে বছর ফেল করা থেকে বেঁচেছিল। আমি প্রতিবার আরও খুঁটিয়ে প্রশ্ন করি। কোন দিকে প্রথমে? বাম, নাকি ডান। সুপর্ণা নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়। আমি প্রশ্ন করে যাই, স্কার্টের ভেতরেও কি হাত ঢোকানোর অনুমতি দিয়েছিল সুপর্ণা? সুপর্ণা দুষ্টু এক হাসি হেসে বলে— অল্প। কিন্তু কতটা অল্প, সেটা বলতে চায় না। এমন সময়ে ডলি, আলুভাজা খেতে খেতে হঠাৎ এক দার্শনিক প্রশ্ন করল।
—তোরা কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস?
যা উত্তর এল, তাতে করে বোঝা গেল, আমি ছাড়া সবাই মোটামুটি করে। যদিও জয়ের উত্তর নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত প্রচুর আড্ডায় জয় আমাকে জানিয়েছে, ঈশ্বর নামক কোনওকিছুতেই ওর বিশ্বাস নেই। এখানে পাল্টি খাওয়ার পেছনে কারণটা বোঝা গেল। ডলি আবার প্রশ্ন করল— তোদের কাছে ঈশ্বর মানে কী?
অর্ণব প্রথম কথা বলবে, সেটা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। অথচ প্রথম ওর ব্যাখ্যাই শোনা গেল। অর্ণব বলল— ঈশ্বর মানে এক নির্লিপ্তি। যা কিছু আমাকে ব্যস্ত করে না, শান্তি দেয়, তাই হল ঈশ্বর। এরপর কথা বলে উঠল সুপর্ণা। বলল, ঈশ্বর মানে চূড়ান্ত সুখানুভূতি। যা কোনও কিছু ন্যায়-অন্যায়ের বোধের বাইরে গিয়ে আমাদের সুখ দেয়, তাই হল ঈশ্বর। জয়, কিছু একটা বানিয়ে বলতে চাইল। কিছুই হল না। ওর ফাঁকিবাজিটা ওখানেই ধরা পড়ে গেল। জামার ভেতর থেকে বেজির বাচ্চাটা কুটকুট করে খেতে লাগল আলুভাজা। এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠল ডলি। তারপর নিজেকে শান্ত করে বলল— আমার কাছে ঈশ্বর মানে এক বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসই আমার গুরু। তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করে যাওয়া। লোভ, পাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। অন্যায়কে যেকোনও মূল্যেই ত্যাগ করা।
একথাটি শুনে আমি একটু গম্ভীর হয়ে গেলাম। বলা ভাল, আশাহত হলাম।
রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর পথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। বাড়ি ফেরার পথে ডলি একটা চিঠি ধরিয়ে দিল আমার হাতের ভেতরে। এমনিতেই আশাহত হয়েছি, অবাক হলাম কিছুটা।
বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিই মানুষকে অনেকটা ভিজিয়ে দিতে পারে। জামাকাপড় ছেড়ে চিলেকোঠায় গিয়ে খুলে বসলাম ডলির চিঠিটা। সংক্ষিপ্ত চিঠি।
‘দীপ, সুপর্ণা তোকে কিচ্ছু দিতে পারবে না।’
৩
শরৎকালের একদিন পড়ার শেষে আমরা আবার সেই রেস্তোরাঁয়। এবার আমাদের টেবিলে স্প্যাগেটি এবং মাংসের ছোট ছোট বল। সুপর্ণা খাচ্ছে না সেসব। ওর জন্য আনানো হয়েছে পোলাও। ডলি ওর পাঁউরুটি এবং মাখন থেকে বেরোতে পারেনি। জয় ডলির প্লেটে তুলে দেয়নি আলুভাজা। ওর কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে। বারবার বেশ কড়া চোখে তাকাচ্ছে আমার এবং ডলির দিকে।
আজকের প্রশ্নকর্তা জয়ই। ওর প্রশ্নও দর্শনমূলক।
—তোরা প্রেমে বিশ্বাস করিস?
আবারও দেখা গেল, আমি ছাড়া প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে। সুপর্ণা প্রথমে শুরু করল— প্রেম আমার কাছে জীবনের সমস্তকিছু। বারবার বারবার প্রেমে পড়া। প্রতিবার নিজের সমস্তটা দিয়ে দেওয়া। এই পৃথিবীতে একটা দিনও আমি প্রেমবিহীন থাকতে চাই না। অর্ণব বলল— ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রেমকে গ্রহণ না করলেও, প্রেমের ধারণাকে বিশ্বাস করে। তবে তা কেবলই এক ধারণামাত্র। এই ধারণার প্রয়োগ হতে ও কোথাও দেখেনি। এবার এল ডলির পালা। আমার চোখ চলে যাচ্ছে ওর বুক ও ঠোঁটের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল— প্রেম ওর কাছে কোনও ধারণামাত্র নয়। বরং, একজন মানুষ। যে মানুষকে সহজে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বারবার ছুঁয়েও মনে হয়, কিছুতেই ছুঁয়ে নেওয়া হল না। প্রেম আমার কাছে এক সীমাহীন যাত্রা।
চোখাচখি হল আমার ও জয়ের। ওর চোখের ভেতর আগুন ঝরছে। তীব্র ঈর্ষার আগুন। এতক্ষণ যা বলবে বলে ও ঠিক করেছিল কিছুই না বলে উঠে গেল। যাওয়ার আগে আমার চোখে চোখে রেখে বলল— প্রেম কিছুই না, এক অপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া।
৪
শীতকালে সেই রেস্তোরাঁয় আমাদের টেবিলে ছিল দক্ষিণ ভারতীয় কিছু খাবার। তবে ডলির খাবারের কিছুই পরিবর্তন হয়নি। শীতকালের সেই দিনটির আগে আমি ডলিকে ছুঁয়েছি বেশ কয়েকবার। ওর ওই আকর্ষণীয় বুক আমি মুঠোর মধ্যে নিয়েছি। জিভের ভেতর জিভ বুলিয়ে নিয়েছি। ইতিমধ্যে সুপর্ণা আমাকে ছুঁয়েছে একবার। আচমকা একদিন টিউশন ব্যাচে লোডশেডিং হলে আমার পুরুষাঙ্গ চেপে ধরেছে। আলো আসার পর ওর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে কিছু হয়েছে। কেবল একটা খেলাই ওর কাছে এসব। সুপর্ণার ক্ষেত্রে আমি একটুও এগোতে চাই না। কারণ আমি জানি, এই গল্পটাই হয়তো ও বেশ নির্লিপ্তভাবে বলবে অন্য কাউকে। গল্পের মধ্যে আমিই একমাত্র লেখক। অন্য কারুর গল্পের চরিত্র হতে চাই না। জয় এবং আমার সম্পর্কটা প্রায় না থাকার মতই। ওর বেজিটাও আমাকে সহ্য করতে পারে না আজকাল। যৌনঈর্ষা যে কতবড় ঈর্ষা, তা আমি বুঝি। ফলে জয়কে দোষ দিই না। ওর কাছে প্রেমের পবিত্রতাই মিথ্যে হয়ে গেছে। প্রেমের পবিত্রতা! ভাবলেই হাসি পায়।
আজকের প্রশ্নটি তুলল অর্ণব।
—তোরা কি বিশ্বাস করিস, দুটি মানুষের ভালবেসে একসঙ্গে থাকা উচিত?
এটা এখন নিয়ম হয়ে গেছে, আমি ছাড়া সবাই বিশ্বাস করবে! আমিই হলাম সবচেয়ে বড় অবিশ্বাসী। জয় শুরু করল— প্রেম আর বিশ্বাস। এই দুটো থাকলে জন্মের পর জন্ম দুজন একসঙ্গে থাকতে পারে। ওর এই জন্মের পর জন্ম কথাটি শুনে খুব হাসি পেল। হাসলাম না। গম্ভীর হয়ে রইলাম। ডলি কিছু তত্ত্ব দিল না। শুধু বলল, ও বিশ্বাস করে। শুধু এইটুকু কথাতে ও প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেল। একটা দীর্ঘ বিরক্তিকর ভাষণ দিল সুপর্ণা। সেখানেও শোনা গেল, এই জন্মের পর জন্ম শব্দটি। অবশেষে কথা বলল অর্ণব— উচিত, এমনই ভেবেছিলাম। বাবা-মাকে জন্তুর মত লড়তে লড়তেও দেখেছি, কেন উচিত, কীভাবে উচিত। তোরা জানিস না, দুজনে একাধিকবার আত্মহত্যা করতে গেছে। কিন্তু প্রতিবারই ঘরের ছিটকিনিটা দেয়নি। তারপর যখন গলায় ফাঁস লাগিয়ে নীচের টুলটা সরিয়ে দিতে যাবে, তখুনি দরজা দিয়ে ঢুকেছে অপর পক্ষ। নামিয়ে এনেছে। এটা যেন একটা খেলা। আত্মহত্যা আত্মহত্যা খেলা। তারপর কয়েকদিন কত খুশি, কত আনন্দ আমাদের বাড়িতে। আত্মীয়-স্বজনেরা আসছে, রান্না হচ্ছে ভাল ভাল খাবার, সবাই যেন এক ফুর্তিতে মেতে থাকছে। সবাই চলে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে শুরু হচ্ছে আবার সেই ঝামেলা। আবার সেই আত্মহত্যার খেলাটি। স্টান্ট।
হয়তো এই প্রথম অর্ণবকে এতটা কথা বলতে শুনলাম।
একটু থেমে অর্ণব আবার বলতে শুরু করল—
ভালবেসে দুটি মানুষের একসঙ্গে থাকা উচিত নয়, যদি সেই থাকার মধ্যে তারা আরও অন্য অন্য ভালবাসা খুঁজে না পায়। অন্য ভালবাসা, অন্য মানুষ। যৌনঈর্ষাই একটি সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখে হয়তো।
৫
আমাদের পরীক্ষার ঠিক মাস দুই আগে, ভরা বসন্তে একদিন খবর এল আমাদের অর্থনীতির শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন। তবে ঘটনাটি তেমন তীব্রভাবে আমাদের ভেতর আঘাত করল না। এই পৃথিবীতে ওঁর বেঁচে থাকাই যেন এক বাহুল্য ছিল। এছাড়াও আমাদের সিলেবাস শেষ করে দিয়ে গেছেন তিনি। শেষ একটি ক্লাস হওয়ার ছিল, হল না। তবে আত্মহত্যার পদ্ধতিটি আমাদের বিস্মিত করেছে। ওর জন্য গলায় ফাঁস বা মেট্রোতে ঝাঁপ যথেষ্ট ছিল।
নদীতে ডুবে মরাটা একটু বেশিই রোমান্টিক।
আমাদের শেষ রেস্তোরাঁর দিন। টিউশন ব্যাচটা শেষ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল। এরপর পাঁচজন কোথায় কোনদিকে ছিটকে চলে যাব ঠিক নেই। ইতিমধ্যে জয় এবং ডলির মধ্যে কোনও এক সেতুবন্ধন হয়েছে। দুজনেই এখন ঘৃণা করে আমাকে। এই ঘৃণার মাঝেও একদিন ডলির বুক ছুঁয়েছি আমি। একটি চিঠিও দিয়েছে ও আমাকে। যদিও এখন সেসব আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। বুঝি একজনের প্রতি ভিন্ন ঘৃণা, দুজনকে কাছে আনতে পারে।
সুপর্ণার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পরীক্ষা পাশের পর-পরই। সুপর্ণার সমস্ত গল্প অনেকবার করে শুনেও যেন বাকি থেকে যায়। বিয়ের পর কি সেসব গল্প এমনি নির্লিপ্তভাবে বরকে শোনাতে পারবে? ওর জন্য কষ্ট হয়।
ইতিমধ্যে আমাদের টিউশন ব্যাচে কয়েকবার লোডশেডিং হয়েছে। এবার শুধুমাত্র সুপর্ণা নয়, আমার হাতটিও সচল হয়েছে। তারপর বুঝেছি, কত বড় ভুল হয়ে গেল। অর্ণব, সেদিনের পর একটু বেশি কথা বলছে। আমাকে একদিন সুপর্ণার বিয়ের ব্যাপারে জানতে চায় ও। এও জানতে চায় যে, সুপর্ণা ঠিক কতজনের সঙ্গে শুয়েছে। তারপর একমনে অ্যাকোরিয়ামের রঙিন মাছেদের মধ্যে ডুবে যায়।
এমনই এক বসন্তের দিনে আমাদের টেবিলে কাঁকড়া, স্যালাড এবং মাছের কয়েকটা পদ। ডলি ও জয় একই খাবার নিয়েছে। ডলির পাঁউরুটি ও মাখনের দিন কি অতিক্রম করে গেল? আজ আমার মেনুটা একটু অন্য। আমি নিয়েছি একটা পায়রার মাংস। খুব বাসি মাংস। ঠিক করে রান্না করা হয়নি। তবে আমার খেতে কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।
আমিই সেই বিপজ্জনক প্রশ্নটি করে ফেললাম এবার। জানি না কীভাবে এত দার্শনিক মন আমার ভেতরে লুকিয়ে ছিল।
—তোদের কি মনে হয় না, আমরা সকলেই লিবিডো দ্বারা পরিচালিত? বাকি সব মিথ্যে, সবটা।
খেয়াল করলাম প্রশ্নটির মধ্যেই আমার সম্মতি লুকিয়ে আছে। অথচ আজ সকলেই চুপ।
জয় কিছু বলতে পারল না।
ডলি কিছু বলতে পারল না।
সুপর্ণা একটু হাসল। কিছু বুঝল না।
কিছু বলল না অর্ণব।
আমি হাসলাম কিছুটা। বেশ শব্দ করেই। তারপর খাওয়া শেষ করলাম নিজের। আমার মন আজ এক অজানা আনন্দে ভরে উঠেছে। পৃথিবীর এক সূত্র যেন আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি আজ। রেস্তোরাঁর বিল সকলেরটা আমিই মিটিয়ে দিলাম। জড়িয়ে ধরার সময় দেখা গেল, সকলেই আড়ষ্ট। এমনকী সুপর্ণাও। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার সময় অর্ণব ডাকল আমাকে। একটু আড়ালে নিয়ে গেল। ঘামছে ও। বহুক্ষণ চুপ করে রইল।
তারপর প্রায় এক কুখ্যাত অপরাধীর মত হিসহিস করে বলল— দীপ, তোকেই শুধু আজ একথাটি বলতে পারব।
আরও ঘামছে অর্ণব। ওকে অসুস্থ অথচ জীবন্ত মনে হচ্ছে।
—বিগত দেড় বছর বাবা-মায়ের প্রবল ঝগড়ার দিনে রঙিন মাছেদের অ্যাকোরিয়ামের সামনে, মায়াকে বারবার, বারবার ধর্ষণ করে গেছি।






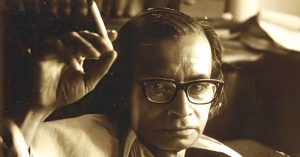








2 Responses
সার্থক ছোটগল্প। অনেক দিন মাথার মধ্যে থেকে যাবে। অদ্ভুত গল্প। লেখককে শুভেচ্ছা জানাই।
বাস্তব মনে হলো।