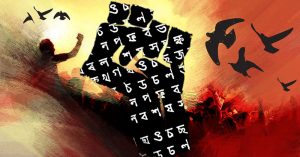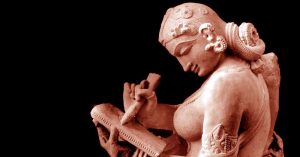১৯৪৭-’৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্তানে নাটক রচনা এগিয়েছিল সামগ্রিকভাবে সেদেশের কবিতা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্য রচনার সমান্তরালভাবে না হলেও পাশাপাশি। এই সময়কালে সেখানে কবিতাচর্চার ব্যাপ্তি ও সিদ্ধি ছিল সর্বাধিক। প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেখানকার কবিরা নিজ নিজ জেলা থেকে কবিতাচর্চা করেই দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছেন। তাই দেখি, আজিজুল হক যশোরে, দিলওয়ার হোসেন সিলেটে, আবুল হোসেন চট্টগ্রামে বসেই কবিখ্যাতি পাচ্ছেন তাঁদের কবিকৃতির দরুন। কবিতার সেরা শিরোপা ‘বাঙলা একাডেমী’ পুরস্কার পর্যন্ত পাচ্ছেন তাঁরা জেলায় বসে। পাঁচ ও ছয়ের দশক এপার ওপার দু-বাংলাতেই অবিরাম সোনা ফলিয়েছে কবিতায়, বিস্ময়কর সত্য এটি।
উপন্যাস বা নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সাফল্য এ-সময় আসেনি। এই পর্যায়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখা হয়েছে ঠিকই, যেমন আবু ইশহাকের ‘সূর্যদীঘলবাড়ি’ (১৯৫৫), সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের ‘লালসালু’ (১৯৪৯), আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘কর্ণফুলী’ (১৯৬২), শওকত ওসমানের ‘জননী’ (১৯৫৮), শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘কাশবনের কন্যা’ (১৯৫৪), শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংশপ্তক’ (১৯৬৫), রশীদ করিমের ‘উত্তম পুরুষ’ (১৯৬১), সত্যেন সেনের ‘আলবেরুণী’ (১৯৬৯), জাহির রায়হানের ‘আরেক ফাল্গুন’ (১৯৬৯) যথার্থ গুরুত্ব দাবি করতে পারে। উল্লেখিত উপন্যাসগুলি একদিকে পাঠকনন্দিত, অন্যদিকে স্থায়িত্বের স্বাক্ষরও রাখতে পেরেছে, তদুপরি পুরস্কারধন্য। কিন্তু এ-সময়ে ভাল নাটক, নাট্যকারের সংখ্যা দুঃখদায়কভাবেই মুষ্টিমেয়।
 ‘৪৭-’৭১ পর্বের নাটকাবলির দিকে বিহঙ্গাবলোকনে দেখব, কী মঞ্চসাফল্যের বিচারে, কী শিল্পের নিরিখে উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। নাট্যকারের সন্ধান নিলে দেখা যাবে, তালিকাটি নিতান্ত হ্রস্ব নয়। নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, কল্যাণ মিত্র, ইব্রাহিম খাঁ, আনিস চৌধুরী, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আকবরউদ্দীন, ওবায়দুল হক, সিকানদার আবু জাফর, ইব্রাহিম খলিল, আলী মনসুর, আবদুর রহমান, ইন্দু সাহা, জিয়া হায়দার, মোজহারুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন ও অন্যান্য। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় সম্ভ্রান্ত নাম, আবার নাটকও লিখেছেন এক বা একাধিক, তাঁদের মধ্যে স্মরণযোগ্যরা হলেন আবুল ফজল (‘কায়েদে আজম’ ১৯৪৭), আলাউদ্দীন আল আজাদ (‘ইহুদীর মেয়ে’ ১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (‘বহিপীর’ ১৯৬০), নীলিমা ইব্রাহীম (‘দু’য়ে দু’য়ে চার’ ১৯৬৪), জসীমউদ্দীন (‘মধুমালা’), মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান (‘অচেনা প্রহর’ ১৯৬৮), বন্দে আলী মিয়া (‘জোয়ার ভাটা’ ১৯৫৫) প্রমুখ।
‘৪৭-’৭১ পর্বের নাটকাবলির দিকে বিহঙ্গাবলোকনে দেখব, কী মঞ্চসাফল্যের বিচারে, কী শিল্পের নিরিখে উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। নাট্যকারের সন্ধান নিলে দেখা যাবে, তালিকাটি নিতান্ত হ্রস্ব নয়। নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, কল্যাণ মিত্র, ইব্রাহিম খাঁ, আনিস চৌধুরী, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আকবরউদ্দীন, ওবায়দুল হক, সিকানদার আবু জাফর, ইব্রাহিম খলিল, আলী মনসুর, আবদুর রহমান, ইন্দু সাহা, জিয়া হায়দার, মোজহারুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন ও অন্যান্য। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় সম্ভ্রান্ত নাম, আবার নাটকও লিখেছেন এক বা একাধিক, তাঁদের মধ্যে স্মরণযোগ্যরা হলেন আবুল ফজল (‘কায়েদে আজম’ ১৯৪৭), আলাউদ্দীন আল আজাদ (‘ইহুদীর মেয়ে’ ১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (‘বহিপীর’ ১৯৬০), নীলিমা ইব্রাহীম (‘দু’য়ে দু’য়ে চার’ ১৯৬৪), জসীমউদ্দীন (‘মধুমালা’), মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান (‘অচেনা প্রহর’ ১৯৬৮), বন্দে আলী মিয়া (‘জোয়ার ভাটা’ ১৯৫৫) প্রমুখ।
নাটকের অনুবাদ-ও থেমে থাকেনি এ-সময়। নাটকের অনুবাদ হয়েছে, বিদেশি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমটির উদাহরণ আবু শাহরিয়ার অনূদিত শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’ প্রকাশিত হয় ১৯৬০-এ। কবীর চৌধুরী অনুবাদ করেন বেশ কিছু বিদেশি নাটক, আবু সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদে আমরা পাই সোফোক্লেসের ‘ঈডিপাস’ (১৯৬২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক-গবেষক নরেন বিশ্বাস নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কির সুবিখ্যাত উপন্যাস ‘মা’-এর। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট জুড়ে নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্লাবন এবং বাংলা নাটকের জোয়ারের সময়টিতে আমরা উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক (এক ডজনের ওপর নাটক লিখে গিয়েছেন তিনি), বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ দিকপালদের নাম পাচ্ছি। এমনকি শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়রা অভিনয় আর নাটক পরিচালনা করার পাশাপাশি নাটক রচনাও করে গিয়েছেন। নাটক বাবদ দুই বঙ্গের এই ফারাক কেন?
কারণ, ১৮৭২ থেকে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় যে পেশাদারিত্বের সূচনা করল বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে, পরবর্তী একশো বছরে তা বিচিত্রভাবে ফলেফুলে ঐশ্বর্যান্বিত হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাট্যশালায় আগমন, নটী বিনোদিনীর অভিনয় দেখা এবং ‘থিয়েটারেও লোকশিক্ষা হয়’ জাতীয় নাটক সম্পর্কে প্রশংসাত্মক উক্তি নাট্যদর্শকদের নাটক দেখায় উৎসাহিত করেছিল নিঃসন্দেহে। গোটা একটি শতক জুড়ে অমৃতলাল বসু, দানীবাবু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্য-অভিনেতার (এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে বেশ কিছু অভিনেত্রীর নাম— সুকুমারী বিনোদিনী, আঙুরবালা, কঙ্কাবতী, সরযূদেবী, আশ্চর্যময়ী, ইন্দুবালা প্রমুখ) অভিনয়দীপ্তির সমান্তরাল ওপার বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও পশ্চিমবঙ্গের নাট্য-ঐতিহ্য ওপার বাংলার ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের সমান ও ন্যায্য দাবিদার। মধুসূদন-মন্মথ রায়-বিজন ভট্টাচার্য-তুলসী লাহিড়ীর মত নাট্যকার বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-উৎপল দত্ত-তৃপ্তি মিত্র-মনোজ মিত্র প্রমুখ অভিনেতাদের শিকড় তো আসলে পূর্ব বাংলায়।

তাই বলে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ একেবারেই যে নাটকহীন ছিল, তা বলা যাবে না। ঢাকায় একটি নাট্যমঞ্চের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি।’ উনিশ শতকের ছয়ের দশকে নাটমঞ্চটি তৈরি হয়েছিল অনুমান, যদিও রঙ্গমঞ্চটি ঠিক কবে নির্মিত হয়, সে-বিষয়ে যথার্থ তথ্যের অভাব। ঢাকার বিখ্যাত সাময়িকপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’ অনুযায়ী ১৮৬৫-তে জানা যায়, নাট্যমঞ্চটি সংস্কার করা হয়েছে। অতএব নাট্যমঞ্চটি প্রাক-১৮৬৫-র কথা বলা চলে। নয়ের দশকে এটির নাম পাল্টে হয় ‘ক্রাউন থিয়েটার’। এর আগেই ঢাকায় অন্যত্র অভিনীত হয়েছে ‘নীলদর্পণ’। তাছাড়া ১৮৫৭-তে সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে কোম্পানি ঢাকায় যে নৌসেনার সমাবেশ করেছিল, তারাও একাধিক নাটক অভিনয় করে বলে জানা যায়।
ঢাকা ছাড়া এ-সময় বরিশাল, পাবনা, কুষ্টিয়া এবং বিশেষ করে কুমারখালি থেকে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পাদিত ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ বেরোত কুমারখালি থেকে। ১৮৭০-এ পত্রিকাটি জানাচ্ছে, কেবল কুমারখালিতেই নয়, পার্শ্ববর্তী মহিষবাগান, মেখলা গ্রামেও নাটকের আসর বসেছিল। অন্যদিকে ১৮৬৯-এ বরিশালে অভিনীত হচ্ছে ‘স্বর্ণশৃঙ্খল’ নাটক। যে নাটকের নায়ক সেজেছিলেন রাজকুমার দত্ত। ‘ঢাকা প্রকাশ’ নাটকটি সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছে। এক, ‘অধিক গোল হইবে বলিয়া আহূত ব্যক্তিদিগের জন্যে টিকেট করা হইয়াছিল।’ আর দুই, সম্ভবত বরিশালে এই সর্বপ্রথম নাটক অভিনীত হল। কেননা ‘ঢাকা প্রকাশ’ লিখছে, ‘বরিশালেও যে নাটকাভিনয় হইবে ইহা আমরা একদিনের জন্যও মনে করি নাই।’ বরিশালে নাটকের সর্বজনগ্রাহ্য জনপ্রিয়তার প্রমাণ, একমাত্র চাঁদসী গ্রামেই চার-চারটে নাট্যদলের সন্ধান মেলে— বিষহরি নাট্য সমিতি, দশমহাবিদ্যা নাট্য সমিতি, সিদ্ধেশ্বরী নাট্য সমিতি ও চাঁদসী আর্ট প্রোডিউসার্স। চাঁদসীর মধু শেখ হরবোলা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। পরবর্তীকালের রবি ঘোষ, জহর রায় চলচ্চিত্র এবং মঞ্চে অভিনয় করে স্বনামধন্য, যাঁরা এই বরিশালেরই ভূমিপুত্র।
বরিশালের মত পাবনার নাট্য-ঐতিহ্যকেও স্মরণ করতে হয়। তাছাড়া ফরিদপুর, রংপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থান থেকে নিয়মিত অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। খুলনার ‘নাট্যনিকেতন’ শতবর্ষজীবী নাট্যমঞ্চ, যেখানে এখনও পর্যন্ত শতাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ঢাকা যে ‘ক্রাউন থিয়েটার’ প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, তারা কলকাতা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী আনত। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর মত প্রখ্যাত অভিনেতাও কিছুকাল এখানে অভিনয় করে গিয়েছেন। যে নাটকগুলি ক্রাউন-এ অভিনীত হয়েছে, তার তালিকা দেখলে তখনকার দর্শকরুচির খানিক পরিচয় পাওয়া যাবে— চৈতন্যলীলা, নলদময়ন্তী, কেদার রায়, আনারকলি, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, এসব নাটকের নাট্যকার বা নাট্যরূপদাতার নাম এখন আর জানা যায় না, পাওয়া যায় না অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশদ তালিকা, অভিনয় রজনীর সংখ্যা।

ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও জেলাশহরে পেশাদারী নাট্যদল ছিল। ক্রাউন পেশাদারী নাটমঞ্চ হিসেবেই পরিচালিত হত, যেখানে প্রতি সোম, বুধ ও শনিবার নাটকের অভিনয় হত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে একমাত্র এখানেই বাংলা নাটকে অভিনেত্রী হিসেবে স্থানীয় মহিলারা অভিনয় করতেন। কনক সরোজিনী ও সরলা এমনই দুই অভিনেত্রী। স্থানীয় মহিলা, তবে ‘ভদ্রঘরের’ অবশ্যই নয়। এই নিয়ে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ কম উত্তেজিত হয়নি। সেসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। আজকে যাকে গ্রুপ থিয়েটার বলা হয়ে থাকে, পেশাদারিত্বের বাইরে শখের থিয়েটার নামে যাকে প্রায়শ সংজ্ঞায়িত করা হত, তারও কিন্তু অস্তিত্ব ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে ছিল। ১৮৭১-এর এরকমই একটি গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, যার নাম ছিল ‘প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার’। ঢাকার বিভিন্ন আর বিচিত্র পেশাজীবী মানুষ, যেমন শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী এবং পরেশনাথ ঘোষ ছিলেন পালোয়ান, রাজেশ্বর চক্রবর্তীর মত ডাক্তার, দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর মত স্কুল রেকটর আর আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁর মত ব্যবসায়ী। এঁদের অভিনয়স্থল ছিল ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’। বিভিন্ন সময়ে এই দল ‘শরৎ সরোজিনী’, ‘মেঘনাদবধ’ ইত্যাদি নাটক অভিনয় করে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখতে হত।
স্থায়িত্ব আরও বেশি ছিল ঢাকার অন্য একটি দল— ‘নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানি’-র। এদের উদ্যোগেই কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকটি বাংলায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছিল, ১৮৭১ সালে। প্রসঙ্গত, ঢাকায় অভিনীত হবার প্রায় চোদ্দো বছর আগে ১৮৫৭-র সরস্বতী পুজোর রাতে সাতুবাবুর বাড়িতে (সাতুবাবু বা ছাতুবাবু, অর্থাৎ সেকালের কোটিপতি রামদুলাল দেবসরকারের দুই ছেলে আশুতোষ ও প্রমথনাথ-দের প্রথমজন) কালিদাসের এই নাটকটিই অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন নন্দকুমার রায়।
এছাড়া ঢাকায় ‘ইলিশিয়াম থিয়েটার’, এরাও ‘শকুন্তলা’ মঞ্চস্থ করে। তাছাড়া এদের উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনার মধ্যে রয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘বিল্বমঙ্গল’ এবং দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’। শেষোক্ত নাটকটি অভিনয়ের জন্য সরকারি আপত্তি ওঠায় নাটকটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর ‘ইলিশিয়াম’ দলটিই ভেঙে যায়।
এছাড়া ‘সনাতন নাট্যসমাজ’, ‘অলিম্পিয়ান থিয়েটার’ (কৌতূহলের বিষয়, এই দলের সদস্যরা তখনকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় ব্যবসায় সূত্রে আসা বণিক সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত ছিল) ইত্যাদি কিছু নাট্যদলও ঢাকায় বেশ কিছুকাল অভিনয় চালিয়ে গিয়েছে।


সেই সঙ্গে ঢাকার উর্দু নাটক নিয়েও কিছু বলা দরকার। ‘ফের হাত আবজা’ নামে একটি দলের কথা জানা যায়, যারা উনিশ শতকের শেষ দশকে সেসময়কার বিখ্যাত উর্দু নাট্যকার আলি নফিসের অন্তত তিরিশটি নাটক মঞ্চস্থ করে। এ-সব নাটকে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করানো হত স্থানীয় বারবণিতা দিয়ে। বারবণিতারা, মজার ব্যাপার, বহু পুরুষ চরিত্রেও অভিনয় করতেন। অন্যদিকে সাতুবাবুদের নাটকে শকুন্তলা সেজেছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে অবিনাশচন্দ্র ও ভুবনমোহন। স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষদের ভূমিকার ইতিহাস তো আজকের নয়, সোফোক্লেসের ‘ঈডিপাস’ নাটকে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ইয়োকাস্তে-র ভূমিকায়, বা সাড়ে চারশো বছর আগে শেকসপিয়রের ওথেলো, হ্যামলেট অথবা টেম্পেস্ট নাটকে যথাক্রমে ডেসডিমোনা, ওফেলিয়া এবং মিরান্দা সাজতেন তো পুরুষরাই।
তবে এর মধ্যেই বিস্ময়কর তথ্য, মহিলাদের দ্বারা ব্যবস্থাপিত, মেয়েদেরই অভিনয়ঋদ্ধ নাটক কলকাতা নয়, উপহার দিয়েছিল ঢাকা। ১৮৮০-তে গুণুবাঈ, আনুবাঈ এবং নয়াবন নামে ভগিনীত্রয় ‘ইন্দ্রসভা’ নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। এ-নাটক টিকিট কেটে দেখতে হত দর্শককে। অভিনীত হয়েছিল ‘পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি’ মঞ্চে। শুধুমাত্র মহিলাদের উদ্যোগে নাটক বাংলায় এই প্রথম। এঁদের অপর আর এক প্রযোজনা ‘যাদুনগর’। এ ঘটনার বহু দশক পরে কলকাতায় কেবলমাত্র মেয়েদের নিয়ে নাট্যদল গড়ে উঠেছিল অভিনেত্রী মঞ্জু দে-র অধ্যক্ষতায়। এই একটি ব্যাপারে কলকাতাকে পিছিয়ে রেখেছে ঢাকা।
সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ঢাকা এবং বৃহত্তর অর্থে পূর্ববঙ্গ কলকাতার তুলনায় নাটকের দিক দিয়ে যথার্থ প্রতিতুলনায় আসতে না পারার যোগ্য কারণ আছে একাধিক। কলকাতা যেহেতু সেসময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, স্বাভাবিকভাবেই শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই হবে। পূর্ববঙ্গের বাঙালি, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা নাটকের প্রচার-প্রসারে বাধা দিয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় বঙ্গেই যাত্রা, কথকতা, কবিগান, রয়ানি, তরজা ইত্যাদি অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল, যা নাট্যচর্চা ও নাটমঞ্চের প্রসারে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় যাত্রার অভিনয়ধারা, পৌরাণিক বিষয়কে নিয়ে নাটক লেখা ইত্যাদি প্রভাব নাটকের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা নাটকে সাধারণভাবে এবং পূর্ববঙ্গের নাটকে বিশেষভাবে যাত্রার কাছে বহুভাবে নাটকের অধমর্ণতা লক্ষ্য করি আমরা। একটি সংবাদে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বরিশালের যাত্রাওয়ালারা প্রত্যেক বছর পৌষ থেকে চৈত্র, এই চার মাস ‘অক্রুর সংবাদ’, ‘রাম বনবাস’, ‘মানভঞ্জন’ ইত্যাদি যাত্রাপালা পরিবেশন করে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। মনস্বী কৃষ্ণকুমার মিত্র (ব্রাহ্ম নেতা, ‘সঞ্জীবনী’ সম্পাদক এবং উনিশ শতকের এক অন্যতম পুরোধা মনীষী) তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘‘বরিশালের এক নট প্রতি বৎসরই ময়মনসিংহ আসিয়া (কৃষ্ণকুমার মিত্রের দেশ) বহু টাকা লইয়া যাইত। সে ঢাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত প্রথমে ‘স্বপ্নবিলাস’, তাহার পর ‘রাই উন্মাদিনী’ যাত্রাগান করিয়া সমস্ত সহর মাতাইয়া তুলিত। লোকে যশোদার খেদোক্তি ও রাধিকার প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত।’’ যাত্রার এহেন জনপ্রিয়তার কাছে নাটককে অসম প্রতিযোগিতাতে পড়তে হয়েছিল সেদিন। ময়মনসিংহই নয় কেবল, ঢাকা বা ফরিদপুরকেও যাত্রা কম মাতায়নি। প্রসঙ্গত, যাত্রাদলে সমধিক বিখ্যাত ‘নট্ট কোম্পানি’-র সূতিকাগার ছিল বরিশাল।

এই সালতামামির পরে ’৪৭-পরবর্তী নাটকের অভ্যুদয় সূচিত হয়েছিল কীভাবে, তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অনেকটাই আলোচনা করেছি। পৌরাণিক নাটক ক্রমে এ-সময়কার নাট্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক কাহিনিকেও নাটকে আনা হচ্ছে। যেমন ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নিয়ে লেখা আসকার ইবনে শাইখের নাটক ‘অনেক তারার হাতছানি’ (১৯৬৫), ‘তীতুমীর’ (১৯৬৯), ‘লালন ফকির’ (১৯৬৯)। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর ‘মানুষ’ নাটকে (১৯৪৭)। এ-নাটকে মুনীর যেমন শিল্পী হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক দায় পালন করেছেন, তেমনই এখানে তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন আবিষ্কার করি। যখন নাটকটিতে তাঁকে মানুষকে সব সংকীর্ণতার ওপরে মানুষরূপে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম মহাভারতে যে মানুষ সম্পর্কে চিরায়ত উক্তিটি করেছেন তারই সমান্তরালতায়— ‘ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ’।
ইতিহাসকে নতুন ব্যাখ্যায় প্রসার দিতে এ-বঙ্গ ও-বঙ্গ দু-বঙ্গই ’৪৭-পরবর্তীকালে সমরেখভাবে এগিয়ে গিয়েছে, কৌতূহলের সঙ্গে তা লক্ষ্যযোগ্য। অথচ এমন নয় যে দুই বঙ্গে খুব একটা সংস্কৃতির আদানপ্রদান চলছিল তখন। কলকাতার নাটক দৈবাৎ দেখার সুযোগ মিলত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের, যদিও ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতার সিনেমা একই সঙ্গে ঢাকা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ৬৫-তে ঢাকার ‘বলাকা’ প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিৎ রায়ের ‘মহানগর’ ছবির মুক্তিতে দর্শকের যে তুমুল ভিড় হয়, তাতে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল।
’৪৭-’৭১ পর্বে একমাত্র কলকাতার ‘বহুরূপী’ ঢাকায় নাট্য প্রদর্শন করে। স্বভাবতই এর ক্ষণস্থায়ী কিছু প্রভাব সেসময়ের নাট্যচর্চাকারীদের ওপর পড়ে থাকবে। কিন্তু কলকাতার নাটকের প্রথম প্রভাব ঢাকা বা সমগ্র বাংলাদেশের ওপরই পড়েছিল ’৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর কালপর্বে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে জড়িত মানুষ কলকাতায় সাময়িক আশ্রয় নেন। তাঁদের এই ক’মাসের কলকাতায় অবস্থানের সময় তাঁরা কলকাতার নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন এবং এখানকার নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, কলাকৌশল, অভিনয়রীতি দেখা ও পর্যালোচনার সুযোগ পান। দেশ স্বাধীন হবার পর মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে নাট্যকর্মীরা তাঁদের কলকাতায় দেখা নাটকের প্রভাবে এবং প্রায়শ তার বাইরে গিয়েও নিজস্ব নাট্যরীতি গড়ে তোলেন, যার বহুমুখী ধারা আজকের সময় পর্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে প্রবহমান। ’৭১-পূর্ববর্তীতে যেখানে কবিতাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম, ’৭১-পরবর্তীকালে সেদেশে তার স্থান নিয়েছে নাটক। জেলায় জেলায় সেখানে রয়েছে অসংখ্য নাট্যদল। কেবল ঢাকা শহরের কথাই যদি ধরা যায়, সেখানে শতাধিক নাটকের দল নিয়মিত ঢাকা, বাংলাদেশের অন্যত্র এবং বিদেশেও নিয়মিত তাদের অভিনয় চালিয়ে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বহু নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে এই চার দশকে— মামুনুর রশীদ, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, সোলায়মান, আবদুল্লাহ্ আল মামুন, আলী যাকের, সৈয়দ শামসুল হক এবং সর্বোপরি সেলিম আলদীন। নাটকের বিখ্যাত দলগুলির মধ্যে রয়েছে আরণ্যক, থিয়েটার, বহুবচন, ঢাকা থিয়েটার, আরও বহু। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে স্পার্ক জেনারেশন, অরিন্দম বা তির্যক, গাইবান্ধার ‘পদক্ষেপ’, নাটোরের ‘সাকাম’, এরকম অজস্রাজস্র নাট্যস্নায়ু বাংলাদেশের অবয়বকে সচল রেখেছে। উভয় বঙ্গই এই অর্জন নিয়ে নিঃসন্দেহে গর্ব অনুভব করতে পারে। আমরা সেলিম আলদীন-এ আসি।

’৪৭-’৭১ কালপর্বে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার যেমন মুনীর চৌধুরী, ’৭১-পরবর্তী, অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার নাটকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সেলিম আলদীনেরই প্রাপ্য। মুনীর চৌধুরীর মতই নোয়াখলির জাতক তিনি, তাঁরই মত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, দেশি-বিদেশি সাহিত্যে সু-অধীত। এবং হ্যাঁ, মুনীর যেমন, সেলিম আলদীনও অকালপ্রয়াত। তফাত এই, মুনীর শহিদ হন মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে (১৯২৫-১৯৭১), আর সেলিমকে শহিদ হতে হয়নি, উনষাট বছর বয়সে আকস্মিক মৃত্যু হয় তাঁর। সেলিম আলদীন নাট্যকার হিসেবে এতটাই সম্ভ্রম আদায় করেছেন যে, অনেক সমালোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথের পরেই নাট্যকার সেলিম আলদীনকে গণ্য করতে হবে।
কিন্তু কবে শেষ হল পূর্ববঙ্গের নাটক, শুরু হল বাংলাদেশের? সন্ধিলগ্নটিও নাটকীয়। নাটক ও মহানাটক মিলে গিয়েছিল যেদিন। ’৭১-এর ১৫ মার্চ লক্ষ দর্শকের সামনে উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল মমতাজউদ্দীন আহমেদ (ইনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয়, মালদহে জন্ম, পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান দেশভাগের পর) রচিত ‘এবারের সংগ্রাম’ নাটকটি। ২৪ মার্চ মমতাজউদ্দীন রচিত আর একটি নাটক ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ অভিনীত হল চট্টগ্রামেরই প্যারেড মাঠে। এখানে দর্শকসংখ্যা আশি হাজার। নাটক চলছে, এমন সময় শোনা গেল, চট্টগ্রাম বন্দরে ‘সোয়াত’ জাহাজ থেকে জনসাধারণ পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র নামাতে বাধা দিচ্ছে বলে সৈন্যরা (হ্যাঁ, পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য, যারা পরদিন অর্থাৎ পঁচিশে মার্চ থেকে সুদীর্ঘ ন’মাস এই ভূখণ্ডে নরহত্যায় মাতবে, যাতে মৃত্যু হবে তিরিশ লক্ষ মানুষের) গুলি চালাচ্ছে। প্যারেড মাঠের নাটকের দর্শক এই সংবাদ শুনেই ঝটিতি ছুটে যায় শহর থেকে সাত মাইল দূরে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিতে। এখানেই পূর্ব পাকিস্তানের নাটকের নাটকীয় যবনিকা। সেলিম আলদীন এখন মুক্তিযুদ্ধে যাবেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হাজারো কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বলবেন, ‘অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি’।