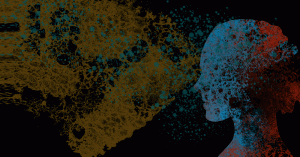আমাদের ছোটবেলায় প্রচুর পোস্টকার্ড আসত। মাসি-পিসি, মামা-কাকা ছাড়াও নানারকম পরিচিত লোকেরা চিঠি লিখত। এমনও হয়েছে কেউ মারা গেছে, সেই সংবাদ পৌঁছাতে পৌঁছাতে অশৌচ বা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের দিন চলে যেত। আমাদের বাড়িতে বাবার এক কাকিমা থাকতেন। তাকেই আমরা ঠাকুমা বলে ডাকতাম। শুনেছি বাবার খুব ছোটবেলায় আমাদের ঠাকুমা মারা যান। তারপর থেকে এই কাকিমাই বাবাকে মানুষ করেছিলেন। বাবাও খুব শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুমা লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু পড়তে পারতেন না। কারণ চোখে ছানি পড়েছিল। তাকে বহুবার সাধা হয়েছিল ছানিটা অপারেশন করে নাও। তিনি চোখে অস্ত্র করবেন না। মা তাই ঠাকুমাকে রান্নাঘরে যেতে দিতেন না। রান্না করতে গিয়ে যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়। ঠাকুমা সকালে স্নান আহ্নিক সেরে বারান্দার এক পাশে ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। পিওন আমাদের বাড়িতে রোজই আসত। উনিই চিঠিগুলো হাত পেতে নিতেন। তখন তো এ অঞ্চলে এত লোকজন ছিল না। পিওনরা দাশগুপ্ত পদবি দেখলেই আমাদের বাড়িতে দিয়ে যেত। ঠাকুমা চোখে খুব কম দেখতেন বলে মিলিয়ে নিতে পারতেন না। ভুল চিঠি দিলে পরদিন হাতে নিয়ে বসে থাকতেন অন্য লোকের চিঠিটা ফেরত দেওয়ার জন্য। যদি কোনও কারণে পিওন না আসত, তাহলে অনেক নতুন নতুন শব্দ শোনা যেত, যেমন আলপ্পেয়ের দল, হস্তিমুর্খ ঠিকানাটা পড়েও দেখে না। মানুষটার কী সংবাদ আছে কে জানে। গর্দভগুলার জন্য দুইডা দিন পিছাইয়া গেল।
ঠাকুমার দুই মেয়ে ছিল। তাদের আমরা বড়পিসি আর ছোটপিসি বলে ডাকতাম। তারাও চিঠি লিখত। চিঠিটা আসত ঠাকুমার নামে, দুর্গাকন্যা দাশগুপ্ত, কিন্তু চিঠিটা লিখত ‘শ্রীচরণেষু বৌদি’ বলে। ঠাকুমা নিজের নামে চিঠি আসলে খুব আনন্দ পেতেন। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে শোনাতে হত। প্রথম প্রথম আমরা ‘শ্রীচরণেষু বৌদি’ পড়ে ফেলতাম। ঠাকুমা তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাদের বলেছিলেন, ‘শ্রীচরণেষু বৌদি’ এই লাইনটা বাদ দিয়ে পড়তে। সরাসরি চিঠিতে চলে যেতে। ঠাকুমা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন, কার চিঠি। আমরা বলতাম, বড়পিসি বা ছোটপিসি। তিনি আদেশ দিতেন, ‘পড়’। আমরা যখন চিঠি পড়তাম ঠাকুমা নিজের কর গুনতেন, কতবার তার নাম আছে বা কতবার আমাদের মা’র নাম আছে।
বাবা একবার অফিসের কাজে দিল্লি গেছিলেন। প্রায়ই চিঠি লিখতেন। চিঠিগুলো আসত মায়ের নামে। ঠাকুমার একটাই জিজ্ঞাস্য ছিল, ও বৌমা, আমার নামটা লেখছে?
চিঠির শেষে লেখা থাকত, কাকিমাকে প্রণাম দিও। একটা পোস্টকার্ডে একবার মাত্র ঠাকুমার নাম থাকায় তিনি আনন্দ পেতেন না। একটু হতাশ হতেন। বাবা বাড়ি ফেরার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাসুরপো, তুমি কি আমারে ভুইল্যা গেছিলা?
কেন ভুলব কেন?
চিঠিতে একবারও আমার নাম লেখো নাই।
তোমাকে প্রণাম জানাইনি?
জানি না।
তোমায় পড়ে শোনায়নি?
হ। শোনাইছে। আছে হয়তো, ভুইল্লা গেছি।
প্রতি চিঠিতেই তোমার নাম আছে।
চিঠি তো বৌমার নামে।
এই ঘটনার পর থেকে বাবা বাইরে গেলে ঠাকুমার নামেই চিঠি লিখতেন।
সব চিঠি ঠাকুমার ঘরে একটা টেকো ফাইলে থাকত। নববর্ষ ও বিজয়াতে প্রচুর চিঠি আসত। ঠাকুমা সেগুলো আলাদা রাখতেন। নববর্ষ বা বিজয়ার পর ঠাকুমা মিলিয়ে দেখতেন, কার কার চিঠি আসেনি। তারপর দিদি বা আমি বসতাম ঠাকুমার মুখোমুখি। সেইসব আত্মীয়-পরিজনদের বিজয়া বা নববর্ষের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য ঠাকুমা চিঠি লিখতেন। অনেকেই ঠাকুমাকে রিপ্লাই পোস্টকার্ড পাঠাত। সেগুলোয় আর ঠিকানা লিখতে হত না। বাকিগুলোয় আগে ঠিকানা লিখে তারপর চিঠি লিখতে হত। ঠাকুমার একটা ছোট ডায়েরি ছিল, তাতেই ঠিকানাগুলো লেখা থাকত। চিঠিতে লেখা হত, ‘তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্বাদ নিবা।’ বা ‘নববর্ষে তোমরা সবাই আশীর্বাদ জানিও।’ ইতি দুর্গাকন্যা দেবী। দাশগুপ্ত লেখা যাবে না। দেবীই লিখতে হবে।
আমি লিখলে দিদিকে দিয়ে দেখিয়ে নিতেন। আমি একটু বড় বড় করে লিখতাম, যাতে বেশি কথা লিখতে না হয়। তখন তো ঝর্নাকলমে লেখা। যদি কখনও পোস্টকার্ডে কালি পড়ে যেত, তিনি যা বলতেন, সব বুঝতেও পারতাম না।
একবার একটা চিঠি এসেছিল—
প্রীতিভাজনেষু,
আপনার একটা চিঠি পাব প্রত্যাশা করে অনেকদিন কেটে গেল। আশা করি এর মধ্যে ভ্রমণপর্ব চুকেছে, এবং আপনিও কাজের ঘূর্ণিতে নেমে পড়েছেন। এর মধ্যেই একদিন সময় করে জানান— আমরা কোথায়, কখন এবং কবে দেখা করছি।
অশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।
ইতি— সরস
চিঠিটা এসেছিল বিষ্ণু দাশগুপ্তের নামে, অবধায়িকা দুর্গাকন্যা দাশগুপ্ত। ঠাকুমা যখন অবধায়িকা, তখন আমাদের বাড়ির চিঠিই হবে। পিওন কোনও ভুল করেনি। যিনি পাঠিয়েছেন, তার কোনও ঠিকানা নেই। অথচ আমাদের বাড়িতে বিষ্ণু নামে কেউ নেই। ঠাকুমা সেই চিঠি কাউকে দেবেন না। নিজের কাছে রেখেছেন। আমাকে আর দিদিকে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, সরস কে? যত বলি ওই নামে কাউকে চিনি না, ঠাকুমা বিশ্বাস করতে চান না। দিদি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, আমি কলেজে। দিদির ওপর সন্দেহ প্রবল। কিছু একটা ঘটছে তলায় তলায়, চিঠি পড়লেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। কয়েকবার আমাকে দিয়ে পড়িয়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন। মাস ছয়েক আগে শীতের ছুটিতে দিদি আর আমি বড়পিসির বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঠাকুমা সেটাও হিসেবের মধ্যে আনছেন। দিদির প্রতি প্রবল সন্দেহ, সারাদিন বাড়ি মাথায়, ‘যত বলি বেশি পড়ানোর দরকার নেই, বিএ তামাত পড়ছে, এবার বিয়া দাও। আমার কথা কেডা শোনে, মাইয়ারে বিদ্যালঙ্কার বানাবা। বানাও, কোন দিন সকালে উইঠা দেখবা মাইয়া চইলা গেছে। একটু ভাবো।’ মা কোনও কথা বলেন না। ঠাকুমা সেদিন আমাদের কাউকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেন না। বাবা অফিস থেকে আসলে বিচার হবে। তারপর সবাই স্বাভাবিক জীবন পাবে।
বাবা অফিস থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে ঠাকুমার ঘরে বসতেন। আমরাও যেতাম। বাবা ওখানে বসেই চা-জলখাবার খেতেন। ঠাকুমা তখন সারাদিনের ফিরিস্তি দেওয়ার চেষ্টা করতেন।
বাবা রোজকার মত ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করেন, কাকিমা কেমন আছ?
খুব খারাপ।
কেন, কী হয়েছে।
আতঙ্কে হাত-পা ঠান্ডা হয়া গেছে।
কী হয়েছে একটু খুলে বলো।
তোমার বাড়িতে বেনামে চিঠি আসছে।
চিঠিটা কই?
ঠাকুমা পোস্টকার্ডটা এগিয়ে দেন।
বাবা হাতে নিয়ে পড়েন, প্রাপক ও প্রেরক দুজনের নামও দেখেন। বেশ কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে হোহো করে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন আর কী! ঠাকুমাও অবাক হয়ে যান। বাবা হাসতে হাসতে দম নিয়ে বলেন, সরস সান্যাল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। প্রথমদিন আলাপের পর বলেছিল, নারায়ণ নামটা শুনলে কীরকম ভগবান ভগবান মনে হয়। তোকে আমি বিষ্ণু বলে ডাকব। তুই আপত্তি করিস না। আমি আপত্তি করিনি কখনও। ও মাঝে মাঝেই বলত, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন অবতার আছেন। একটু থেমে বলেছিলেন, ও মনে হয় দেশে ফিরেছে।
অপামাসির পোস্টকার্ড ব্যবহারের কথা না বললেই নয়। আট থেকে আশি কেউ মাসি-পিসি, দিদিমা-ঠাকুমা বা অন্য কিছু বলে সম্বোধন করে না। সবাই বলে অপা। অপা আমাদের ছোটমাসি, বড়জ্যেঠিমার ছোটবোন। আমার মায়ের সঙ্গে এমন ভাব ছিল, মনেই হত না অপা আমাদের দিদিমার মেয়ে নয়। বাল্যবিধবা অপার অনেক বাড়ি। যার যখন লোকের দরকার সে অপাকে ডেকে নিত। হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। নিজস্ব প্রয়োজন কিছু ছিল বলে মনে হত না বা কোনও জিনিস আর-একটু দাও, এই চাহিদাও ছিল না।
তাই অপার নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা ছিল না। আমাদের বাড়ির ঠিকানায় অপার একটা বিধবাভাতা হয়েছিল। প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা পেত। আমাদের ছোটবেলায় পঁচিশ টাকা অনেক। বিধবাভাতা পাওয়ার পর অপা একটু চনমনে হলেও, পুরনো স্বভাব পাল্টায়নি। যে ডাকে তার বাড়িতেই যায়। মা বুদ্ধি দিয়েছিল। সেই অনুসারে অপা একটাকা দিয়ে দশটা পোস্টকার্ড কিনে, আমাকে দিয়ে দশটা পোস্টকার্ডেই আমাদের বাড়ির ঠিকানা লিখিয়ে নিয়েছিল। অপার পেন নেই, পেন কিনলে কালি কিনতে হবে। কালি আবার শুকিয়ে যায়। বহন করতে গেলে সাদা কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক ভাবনাচিন্তা করে অপা আমার ছোটবেলার ক্রেয়নের বক্সটা চাইল। তাতে বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট টুকরো ছিল। অপাই গুছিয়ে রেখেছিল। কোনও কিছু ফেলত না, সবকিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখত। অপরের সংসারে কয়েকদিনের জন্য থেকেও সব গুছিয়ে দিত। টিনের সেই ক্রেয়নের বাক্সটা অপা নিয়ে গেল। যখন বিরাটী যেত, পোস্টকার্ডে বড় বড় করে লিখত ‘বিরাটী’। ওখান থেকে টালিগঞ্জ গেলে গোটা গোটা অক্ষরে লিখত ‘টালিগঞ্জ’। বিরাটী লাল, টালিগঞ্জ সবুজ, বেহালা হলুদ বা হরিদেবপুর খয়েরি রঙে সেজে আমাদের কাছে আসত। জায়গাগুলো রঙিন হত আর আমাদের জানা থাকত, টাকা এলে কোথায় খবর দিতে হবে।
ঠাকুমার এক ভাই ছিলেন, আমরা তাকে ধনদা বলতাম। বারাসতে থাকতেন। ছোটখাটো চেহারা। বারাসত স্টেশন থেকে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে ধনদা বাড়ি পৌঁছতেন। ওর স্ত্রীকে আমরা বৌদি বলতাম। প্রথমজীবনে ধনদা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে গিয়ে এন্ট্রান্স (তখনকার মাধ্যমিক) পরীক্ষাও দিতে পারেননি। পরীক্ষার সময়ে তিনি জেলে ছিলেন। দেশভাগ হওয়ার পর এদেশে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে একটা চাকরি চেয়েছিলেন। সব শুনে ডাক্তার রায় বলেছিলেন, ‘মূর্খ লোক দিয়ে দেশসেবা হয় না। তুমি সাতদিন পরে এসো।’ সাতদিন পরে ধনদা গিয়েছিলেন। উনি ধনদাকে পাঁচ বিঘা জমি দিয়ে বলেছিলেন, ‘যাও চাষ করে খাও গিয়ে।’ ধনদা তো অবাক, চোদ্দপুরুষে কেউ চাষ-আবাদ করেননি। কী করে করবেন? কিছুই তো জানেন না। বলেছিলেন, স্যার…
বদ্যির ছেলে চাষ করতে পারবে না। এই তোমাদের দেশপ্রেম?
ধনদা আর কোনও কথা না বলে চলে এসেছিলেন। বারাসত স্টেশন থেকে প্রায় আধঘণ্টা হাঁটতে হয়। তারপর সেই পাঁচবিঘা জমি। জমির এক পাশে বাড়ি করে ধনদা থাকেন আর চাষ-আবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন।
ধনদা প্রচুর চিঠি লিখতেন। সব চিঠিই পোস্টকার্ডে লিখতেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তার একটা পোস্টকার্ড আসত।
প্রতিটি পোস্টকার্ডের মাথায় লেখা থাকত, ‘বন্দে মাতরম’। ধনদা বলতেন, দেশমাতৃকাই আমার দেবতা, তাই তাঁকে স্মরণ করি।
তিনি তার দিদিকে একবার লিখলেন, ‘পুবের দিঘে প্রচুর লঙ্কা ফলিয়াছে। তোমাদিগের জন্য লইয়া যাইব। গতযাত্রায় দেখিলাম শ্রীমান নারায়ণ বাজার হইতে লঙ্কা আনিয়াছে, তাহাতে তিন প্রকার লঙ্কা ছিল, মৃত, অর্ধমৃত আর জ্যান্ত। বধূমাতার খুবই কষ্ট, সেই লঙ্কা বাছিয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। দ্বিতীয়ত যত টাকার লঙ্কা আনিয়াছিল, তাহার অর্ধেক বাতিল হইল। অর্থাৎ মূল্য দ্বিগুণ হইল। আমার ইচ্ছা মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য কিছু টাটকা সব্জি পাঠাই।’
ধনদার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল, ছোট ছোট অক্ষরে পুরো পোস্টকার্ড জুড়ে লিখতেন। তার চিঠির প্রথম দুটো লাইন আমরা পড়তাম না। তাতে লেখা থাকত, শ্রীচরণেষু দিদি, তুমি আমার প্রণাম নিও। শ্রীমান শ্রীমতীদের আমার আশীর্বাদ দিও। পরের অংশ থেকে আমরা পড়তাম। এত কথা লিখতেন, পোস্টকার্ডে জায়গা থাকত না। কয়েকবার দেখেছি, ঠিকানার মাথায় উল্টো করে লেখা— প্রণাম নিও, ভাই।
একবার লিখলেন, ‘দিদি, সংবাদে তোমার আনন্দ হইবে, ‘মা অজ চারটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। তিনটি কন্যা একটি পুত্র। হিসেব করিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীকালীমাতার চরণে নিবেদন করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না।’ ঠাকুমাকে যত জিজ্ঞাসা করি, মা অজ কে? ঠাকুমা মিটিমিটি হাসেন, উত্তর করেন না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, তোর মত। আমার মত তো ধনদার বাড়িতে কেউ নেই। দিদিকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, ছাগলের বাচ্চা হয়েছে।
সম্ভবত আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। ধনদার চিঠি এল। সেদিন দুটো চিঠি এল। একটা বাবার নামে, অন্যটা ঠাকুমার নামে। বাবাকে তিনি লিখেছিলেন, ‘স্নেহের নারায়ণ, তোমার কথামত ইষ্টমন্ত্র লইয়াছি। শ্রীশ্রী গুরুদেবের বাড়ি গিয়া আমি ও তোমার মামীমা মন্ত্র লইয়া গুরুগৃহে প্রসাদ পাইয়া ফিরিয়াছি। আজ তিনদিন হইল তিনবেলা নাম জপিতেছি। আমাদের খুব আনন্দ হইতেছে। তোমার সুপরামর্শে আনন্দে অবগাহন করিতেছি। সপরিবারে আশীর্বাদ নিও।’ চিঠিটা সবার পড়া হয়ে গেলে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম।
ধনদা প্রতিমাসে তৃতীয় শনিবার আসতেন। রাতে থেকে রবিবার ভোরবেলা চলে যেতেন। অনেক সময়ে আমরা তার যাওয়া জানতেই পারতাম না। ঠাকুমাই জানতেন। পরে ঠাকুমার কাছে জানতাম ধনদা চলে গেছেন। তৃতীয় শনিবার আসার কারণ, বাবা ওইদিন সাপ্তাহিক রবিবার ছুটির সঙ্গে একটা ছুটি পেতেন। ধনদা বাবার সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করতেন। মামা-ভাগ্নে প্রচুর কথা হত। বলতে গেলে আমরা বাবাকে পেতামই না। সেই রাতে ধনদা আর বাবা একসাথে শুতেন, মা আমাদের ঘরে চলে আসতেন। এটাও একটা আনন্দের রাত, দিদি আর আমার মধ্যে মা থাকতেন।
চিঠি আসার পর ধনদা এলেন। আমাদের জন্য প্রচুর শাক-সব্জি, ফল এনেছিলেন। সবই তার বাগানের। সন্ধেবেলা ধনদা ঠাকুরঘর থেকে আহ্নিক করে এলেন, বাবার খুব আনন্দ, মামা মন্ত্র নিয়েছেন। সবাই যখন একজায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দাদু, তুমি কী মন্ত্র নিয়েছ?
ইষ্টমন্ত্র। সে তুমি বুঝবে না।
তুমি তো চিঠিতে তা লেখোনি।
কী লিখেছি?
নিজেই দেখো।
চিঠিটা ধনদার হাতে দিলাম।
ধনদা বার বার দেখছেন। ঝর্নাকলমে লেখা। এরকম ভুল হবার তো কথা নয়। বাবার হাতে দিয়ে বললেন, দেখো তো কী লেখা আছে। বাবা পড়লেন, ‘স্নেহের নারায়ণ, তোমার কথামত দুষ্টমন্ত্র লইয়াছি’। বাবার কপাল ভাঁজ হল। বললেন, ‘আমার পরিষ্কার মনে আছে ইষ্টমন্ত্রই দেখা ছিল, দুষ্টমন্ত্র হল কী করে?’ তারপরেই বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি সময় নষ্ট না করে ঠাকুমার কাছে চলে গেছিলাম। ওটাই তখন আমার নিরাপদ জায়গা।