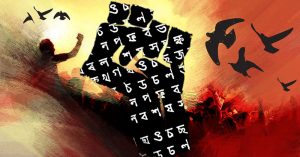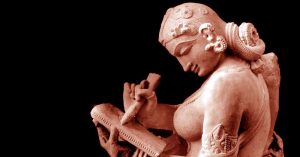আমাদের শৈশব-কৈশোরে প্রতিবছর তেইশে জানুয়ারি ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিময়। খুব ভোরে উঠে স্কুলে যেতে হত। সেখানে জড়ো হতাম ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারপর বিশাল লাইন করে আমাদের গেম টিচার সন্তোষস্যারের নেতৃত্বে শুরু হত পদযাত্রা। প্রায় একঘণ্টা ধরে। অতি ভাগ্যবতী জনৈক ছাত্রী নেতাজির একটি বাঁধানো ছবি দুই হাতে তার বুকে আগলে নিয়ে মিছিলের পুরোভাগে থাকত। তাকে কেবল এ দিনটিতেই নয়, সারাবছর ধরেই ঈর্ষা করতাম।
মিছিলে একটাই স্লোগান, ‘নেতাজি! ফিরে এসো!’ সে-বয়সে নেতাজি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না। তিনি কোথায় গেছেন, ফিরে আসবেনই বা কেন, সেসবও বুঝতাম না। আমাদের কাজ ছিল মিছিলে সামিল হওয়া, স্লোগানে প্রতিধ্বনি তোলা আর মিছিল শেষ হলে স্কুল থেকে দেওয়া ইয়া বড় আস্ত একটি কমলালেবু নিয়ে বাড়ি ফেরা। নেতাজির চেয়ে ওই কমলালেবুটিই সেসময় বেশি গুরুত্ব পেত, বলতে দ্বিধা নেই।
সকালের পর দুপুর। তখন আমাদের পাড়ায়, প্রতি পাড়ায় যেমন, ঠিক সওয়া বারোটার সময় বেজে উঠতো শাঁখ। পরিবেশিত হত জাতীয় সঙ্গীত। ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হত। দুপুর সওয়া বারোটা কেন? ১৯৯৭-এর ২৩-এ জানুয়ারি ওইসময়েই নেতাজি জন্মেছিলেন, সেজন্য। বয়স যত বেড়েছে, নেতাজি সম্পর্কে ততই বেশি করে জেনেছি। মহান দেশপ্রেমিক সশস্ত্র সংগ্রামী নেতারূপে তাঁকে ভালবেসেছি এবং বারবার শ্রদ্ধাবনত হয়েছি সব ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর সমদর্শী ও উদার মনোভাবে।
নেতাজির অনন্যতা কোথায়? ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হিউ টয় থেকে নেতাজি সম্পর্কে সাম্প্রতিক মারাঠি গবেষক বিশ্বাস পাতিল— সকলেই বলেছেন, নেতাজির স্বপ্নময়তা, যার বাস্তব প্রয়োগ তিনি ঘটাতে পেরেছিলেন অনেকটাই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নেতৃবৃন্দ আত্মনিয়োগ করেন— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, শেরে বাংলা ফজলুল হক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জওহরলাল, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, রাজেন্দ্রপ্রসাদ— কেউই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পর যে ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, সেই ভারতবর্ষের কেউ অস্ত্র হাতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, এটা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু নেতাজি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যুদ্ধ বিনা ভিক্ষা করে কখনও দেশকে স্বাধীন করা যাবে না।
নেতাজির পূর্বেও অনেক দেশপ্রেমিকের এমন উপলব্ধি হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস যে তার আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি নিয়ে সফল হতে পারবে না, তাতে নির্দ্বিধ হয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত তো কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে বলেই ফেললেন, এসব বাৎসরিক সর্বভারতীয় তিনদিনের সভা ও রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে ‘Three day’s mockery’, অর্থাৎ তিনদিনের তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেসের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল। এরই ফলশ্রুতিতে মুম্বাইতে বিদ্রোহী হলেন তিন চাপেকর ভাই— দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব। ১৮৯৭-এর ২২-এ জুন তাঁরা ব্রিটিশ প্লেগ কমিশনার রান্ডকে হত্যা করার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ভারতে সর্বপ্রথম সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা হয়।
সেই থেকে শুরু। তারপর একে একে দেখতে পাব, ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামের পিস্তল গর্জে ওঠা, ১৯১৫-তে বুড়িবালামের যুদ্ধে বিপ্লবী বীর বাঘাযতীনের মৃত্যুবরণ, একের পর এক ম্যাজিস্ট্রেট-হত্যা, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ, এরকম ধারাবাহিক ঘটে যাওয়া সশস্ত্রতা। বিপ্লবীরা জানতেন, একজন-দুজন ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিকে হত্যার মাধ্যমে এইভাবে স্বাধীনতা আসবে না। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও যে অস্ত্র ধরা যায়, সেটা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের। এবং এ-কাজে বীণা ঘোষ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের মত নারীরাও হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।
নেতাজি এই সশস্ত্র সংগ্রামকেই বৃহত্তর আকার দিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের মাধ্যমে। বিদেশের মাটিতে স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মতো দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কাজটি এককথায় মনে হবে অলীক ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইতিহাসে বাঙালি এমনই এক জাতি, যে-জাতি অবিশ্বাস্য বহু ঘটনা ঘটিয়েছে বারবার। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। রুশ বিপ্লবের উদ্গাতা লেনিনের ‘April Thesis’-এর সংশোধনী আনেন বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। বাংলা মুলুক থেকে সুদূর ব্রাজিলে গিয়ে সেনাবাহিনীতে কর্নেল হন সুরেশ বিশ্বাস। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অলৌকিক ক্ষমতা ও দক্ষতায় জন্ম হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু নেতাজিকে অপার শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজীবনীতে অকুণ্ঠচিত্তে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-তে নেতাজি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা এইরকম: ‘‘মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হতো, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার ওপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হলো। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নেই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সঙ্গেই মেলামেশা করতাম।’’
আত্মজীবনীর অন্যত্র নেতাজির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতীতি এই: ‘‘আমাদেরও ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা জাত ক্রোধ ছিল। হিটলারের ফ্যাসিস্ট নীতি আমরা সমর্থন করতাম না, তথাপি যেন ইংরেজের পরাজিত হওয়ার খবর পেলেই একটু আনন্দ লাগত। এই সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের দলে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। মনে হতো, ইংরেজের থেকে জাপানই বোধ হয় আপন। আবার ভাবতাম, ইংরেজ গিয়ে জাপান আসলে স্বাধীনতা কোনদিনই দেবে না। জাপানের চীন আক্রমণ আমাদের ব্যথাই দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষ বাবুর বক্তৃতা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতাম। মনে হতো, সুভাষ বাবু একবার বাংলাদেশে আসতে পারলে ইংরেজকে তাড়ানো সহজ হবে। আবার মনে হতো, সুভাষ বাবু আসলে তো পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তান না হলে দশ কোটি মুসলমানের কি হবে? আবার মনে হতো, যে নেতা দেশত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন তিনি কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। মনে মনে সুভাষ বাবুকে তাই শ্রদ্ধা করতাম।’’
নেতাজিকে নিয়ে লাখ কথা বললেও তাঁকে নিয়ে বলা শেষ হয় না, বলার সূচনা হয় মাত্র। তবে আজকের এই ঘোর সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার দিনে নেতাজির অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া জরুরি। নেতাজির এই মানসিকতা এসেছে প্রধানত তাঁর রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন দাশের মাধ্যমে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ‘Bengal Pact’-এর মাধ্যমে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোটা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠে হিন্দু-মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ভবিষ্যতে সমতা আসতে পারে। গান্ধির বিরোধিতায় তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। নেতাজির যাত্রা শুরু এখান থেকেই।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের Bengal Pact ব্যর্থ হলেও, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়ে সাধ্যমত সেখানে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করেন নেতাজি। পরবর্তীকালে তিনি যখন স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে নামলেন, তাঁর সহকারীদের অনেকেই ছিলেন মুসলিম। কর্নেল আবিদ হাসান সাফরানি, হাবিবুর রহমান, ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, লোকমান খান শেরওয়ানি তাঁদের অন্যতম। আজাদ হিন্দ ফৌজে মুসলমান সেনানীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। নেতাজির কথায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফৌজের সকলেই জাতপাত বিসর্জন দিয়ে একত্র আহার করতেন, নেতাজির প্রতি ছিল তাঁদের এমনই নিঃসংশয় আনুগত্য। সিঙ্গাপুরে ভারতের প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী সরকার আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত লেখার দায়িত্ব মুমতাজ হুসেনকে দিয়েছিলেন নেতাজি। মুমতাজ আবিদ হাসানের সঙ্গে মিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার আধারে রচনা করেছিলেন ‘শুভ সুখ চ্যান কি বরখা বরসে’। আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে ‘জয় হিন্দ’ স্লোগান, তার উদ্গাতাও আবিদ হাসান সাফরানি। তাঁর স্বপ্নের ভারতকেও এইরকম সাম্প্রদায়িকতারহিত রূপে গড়তে চেয়েছিলেন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।