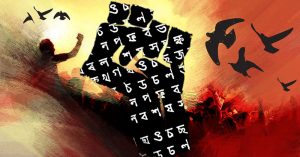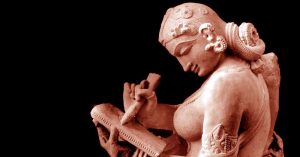অশনি রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল— ধরা পড়িবার ভয়ে নহে, ধরা পড়িবার পর। খবরের কাগজে সে, উদ্ধারণপুরের শৈলমূলে নবনির্ম্মিত একটি টুরিষ্টস্ রেষ্ট হাউসের সন্ধান পাইয়াছিল— সেইদিকে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। স্থানটি নূতন, সুতরাং দৃশ্যও নূতন; হোটেলটাও নূতন; এখনো সেখানে লোকসমাগম হয় নাই মনে করিয়া সেই নির্জ্জনতার দিকে, যেন কারাগৃহের প্রাচীর টপকাইয়া, আর, তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রহরারত পৃথিবীর চক্ষে ধূলা দিয়া, অশনি রায় প্রাণপণে ধাবিত হইল।
টুরিষ্টস্ রেষ্ট হাউসের বাড়ীটা নূতন; তার কোণে কোণে মাকড়সা এখনও জাল পাতে নাই, এবং দেয়ালে দেয়ালে পানের পিকের দাগ এখনো পড়ে নাই মনে করিয়া প্রধাবিত অশনির উৎসাহ আর আনন্দ আরো বাড়িয়া গেল।
অশনি রায় সাহিত্যিক—
অশনি রায়ের গল্পের বই ‘নয়নে নয়ন’ প্রকাশিত হইবার পরই পাঠকসমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল— নূতন জিনিষ আসিয়াছে! পাঠকের আনন্দ আর লেখকের খ্যাতি দ্রুতগতি ছড়াইতে আরম্ভ করিল….
কিন্তু নির্জ্জলা দুধের মতো অবিমিশ্র খ্যাতিও দুর্লভ—
উত্কৃষ্ট সমালোচনা হইতে কে একজন বক্রচক্ষু সমালোচক বিস্তৃত সমালোচনার পর লিখিলেন : ‘‘এই বয়সেই”?
কিন্তু তাঁর ঐ প্রশ্নের মানে বুঝা যায় নাই। ‘এই বয়সেই’ এমন চতুর, কি এমন অভিজ্ঞ, কি এমন লোলুপ, কি এমন দক্ষ, কি এমন দৃষ্টি, কি মোটের উপর এমন সুন্দর, ইহার ভিতর কোনটা সেই সমালোচকের জিজ্ঞাস্য তা’ তিনিই জানেন…
কিন্তু ‘নয়নে নয়ন’ পুস্তকের গল্পগুলিতে টেকনিকের অপরূপ নিজস্বতা, আর, প্রকাশভঙ্গীতে অনিন্দ্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাগরীয় গভীরতা আর বায়বীয় লঘুতার অসামান্য সমাবেশ থাকিলেও ছোট গল্পই যে অশনি রায়ের প্রতিভার পরম আর চরম অবদান নহে তাহা বুঝা গেল তার উপন্যাস ‘সুন্দরী’ বাহির হইলে। লোকে অবাক্ হইয়া গেল….
দেহের মারফৎ আত্মা, আত্মার মারফৎ প্রকৃতি, প্রকৃতির মারফৎ বিশ্ব, এবং বিশ্বের মারফৎ বিশ্বপতি, মাত্র দু’টি ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ যৌন-অনুভূতির, ভিতর দিয়া এমন সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ন, সজীব, আর, প্রবহমান হইয়া উঠিয়াছে যে, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল; অশনি রায়ের নাম জানিতে কাহারো বাকি রহিল না— সদর মফঃস্বল একই তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিল…
লোকে বলিল :
১। “বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, অভাবিতপূর্ব্ব’’।
২। ‘‘জ্ঞানের গভীরতা, সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমা, বচন-বিন্যাসকৌশল, ভাষা, ভাব, প্রেরণাগত স্বাতন্ত্র্য, কল্পনার মৌলিকতা ও সরস সরলতা, আমাদিগকে বিস্মিত আর মুগ্ধ করিয়াছে”।
৩। ‘‘রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঝড়ের মতো দ্রুত গতিতে একটানা পড়েই যেতে হয়— থামবার উপায় নেই; পড়বার সময় ভাবের কিম্বা অর্থের দিক্ দিয়ে বিচার করবার কথা মনেও ওঠে না; এমন নিপুণতা অন্যত্র দেখেছি বলে’ মনে পড়ে না”।
৪। ‘‘নরনারী অর্দ্ধ-বাস্তব ও অর্দ্ধ-কাল্পনিক; স্বপ্প ও জাগরণ পরিমিত মাত্রায়, আর সূক্ষ্মতম একটি সীমারেখা বজায় রেখে’ মিলিত হয়েছে। যে-বস্তু অশনি রায় বাংলাকে দিয়েছেন বিশ্বে তার তুলনা নাই’’।
ইত্যাদি আরো কত!
এবং তারপর ছ’মাসের মধ্যেই দেখা দিল ‘গভীর হইতে গভীরে’…
‘গভীর হইতে গভীরে’, এক কথায় মানুষকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল; প্রতিভার দুরন্ত জাগরণ; দুর্ব্বার জ্বলন্ত হইয়া সে দেখা দিয়াছে— যাদুকর অশনি, অদ্বিতীয় অশনি… সমালোচকগণ বিরুদ্ধে কলম তুলিতে পারিলেন না—
যিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : ‘এই বয়সেই’? —শুনা গেল, তিনি অত্যন্ত অধোবদনে অন্য পথে দেশত্যাগ করিয়াছেন। আত্মার নরক-ভোগের যে প্রগাঢ় মিষ্টিক ব্যাখ্যা ‘গভীর হইতে গভীরে’ অশনি রায় আবিষ্কার করিয়াছে তাহা চরম…. অনেকেই ভয় পাইয়া অনেক বদ্-অভ্যাস ত্যাগ করিল— বালিগঞ্জ ও টালিগঞ্জ লেকের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অন্য কথা পাড়িতে লাগিল….
হল্লা উঠিল বেজায়—
‘প্রতিভা’ অশনি রায়ের ‘দর্শন’ চাই; কলিকাতার হলদিঘাটা লেনের ২৭।৩ নম্বরের বাড়ী জনতা আক্রমণ করিল— দর্শন চাই, বাণী চাই, উপদেশ চাই, স্বাক্ষর চাই, অনুজ্ঞা চাই, অনুগ্রহ চাই….
সুতরাং অতিষ্ঠ হইয়া অশনি রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।
শৈলমূলস্থ উদ্ধারণপুর অত্যন্ত নির্জন স্থান; পাখীই কম। ‘রেসট্ হাউস’ বাড়ীটা অত্যন্ত সুন্দর— লাল রঙের বাড়ীটা সুবৃহৎ; দেড় শত ভ্রাম্যমাণ আমেরিকানের স্থান অক্লেশেই হইতে পারে। বান্দোবস্তও বেশ। নীচেকার হলঘরে এত চেয়ার টেবিল রাখা হইয়াছে যে, দেড়শত স্ত্রী-পুরুষ অভ্যাগত ব্যক্তি সেখানে বসিয়া ‘চা বিস্কুট’ খাইতে পারে।
কান্তিযুক্ত ম্যানেজার একখানা বিপুলাকার বাঁধানো খাতায় আগন্তুক অশনি রায়ের নামধাম লিখিয়া লইলেন। অশনির প্রকৃত নামধামই তিনি পাইলেন; কারণ, অশনি রায় আধুনিক হইলেও অদ্ভুত নয়; সে নাম-ঠিকানা গোপন করিল না, কিন্তু নিজের নামটি উচ্চারণ করিবার সময় সে একবার শিহরিয়া উঠিল….
আর নিস্তার নাই— লোকের ভিড় জমিল আর কি! কত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহারা ভক্তির বান ডাকাইবে তাহার ঠিক নাই। দাও ‘দর্শন’….
তিনখানি বই লিখিয়া এত সংকটে পড়িতে হইবে জানিলে বই সে লিখিত না। আর কি লেখক বাংলায় নাই— অই ত’ মুরলীধর সেন রহিয়াছেন, দময়ন্তীনাথ দে রহিয়াছেন, কুসুমিত লাহিড়ী রহিয়াছেন! যা-না বাপু তাদের কাছে! বাঙালীর একেবারে মাথা নাই বলিয়া একা তাহাকেই এই দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে।
নাম লিখিয়া লইবার সময় ফ্যাসনেবল্ ম্যানেজার বাবু চমকিয়া উঠিলেন না— সে যে অপর কোন অশনি রায় নয়, ‘সেই অশনি রায়’ তাহা তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। লোকটা ব্যবসাদার বই ত’ নয়! খাতাপত্র আর তরকারির হিসাব লইয়াই সে মত্ত। বাঙালীকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়া নেতাগণ বাঙালীর ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিতেছেন। চা’ল ডা’ল ঘুঁটে কয়লার বাজার-দর যাচাই করিতে করিতে মানুষের অন্য দিকে ঔৎসুক্য, অর্থাৎ জীবনের চারুতা আর রস, আর থাকে না; উদর-সর্বস্বতায় ক্রমে মানুষের মনে হিংসা জাগে, আর, তার কাণ্ডজ্ঞানই নষ্ট হইয়া যায়, ইহা নেতারা বুঝেন না।
কিন্তু ম্যানেজার অশনিকে হঠাৎ চমকাইয়া দিলেন; বলিলেন— আপনার নাম ত’ লিখলাম, কিন্তু একটা ধোঁকায় পড়লাম যে!
অশনির সন্দেহ রহিল না যে, ম্যানেজার এইবার জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি সেই সুবিখ্যাত অশনি রায়? অশনি এক সঙ্গেই উন্মুখ আর বিনীত হইয়া উঠিল।
কিন্তু ম্যানেজার তা’ জিজ্ঞাসা করিলেন না; বলিলেন,— বাল্যকালে ভাষা পড়েছিলাম; সকল শব্দের অর্থ মনে নেই। কিছু মনে করবেন না দয়া করে’; জানতে চাই, অশনি মানে বজ্র না বিদ্যুৎ?— বলিয়া তিনি অশনির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন, যেন তাঁর এই শব্দার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অশনির পক্ষেও একটা মজার কথা!
অপ্রত্যাশিতভাবে কথার মোড় ঘুরিয়া যাওয়ায় অশনি হতাশ হইল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু অশনি তা’ নিজের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়; স্বীকার করিতে প্রস্তুত সে ইহাই যে, সে যেন একটা দুর্ভাবনার হাত হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছে; বলিল,— অশনি মানে বজ্র বিদ্যুৎ দুই-ই হয়।
শুনিয়া ম্যানেজার বলিলেন,— আজ্ঞে তা’ হবে। ভাষার মা’রপ্যাচ্ আমরা কিছুই বুঝিনে। আমরা এই নিয়েই আছি। ….বড়ো ‘স্ল্যাক্ সীজন্’ চলেছে, মশায়। দু’টি পরিবার আছেন, আর আপনি এলেন। বৃহৎ পরিবারের একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে থাকার বন্দোবস্তও এখানে আছে।
অশনি বলিল,— মনোরম ব্যবস্থা।
শৈলমূলস্থ এই উদ্ধারণপুরে, এই রেষ্ট হাউসে, জনতা হইতে দূরে, আর, মনোরম ব্যবস্থার ভিতর, দেড়টি দিন অশনি রায়ের একেবারে অকুতোভয়ে, অপরিসীম শান্তিতে এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কাটিল। ম্যানেজার নেহাৎ ব্যবসাদার— পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য, আর, বনানীর নিবিড়তা তাঁহাকে স্পর্শ করে না; তবু তিনি আছেন ভালো…
অশনির মনে হয় এই নির্জনতা আর নীরবতা ভূগর্ভস্থ কবর নহে, আকাশময় নির্লিপ্ততা; বায়ুহীন শূন্যে এই আবাস নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানেরই আত্মনিমগ্নতা, চিরস্থিরতা, আর ইথারীয় একটা স্থির দীপ্তি দিয়া, আর, নিঃসঙ্গ ধ্যানের একটা গরিমায় মণ্ডিত করিয়া কে বা কাহারা যেন ইহাকে উদ্ধারণপুরের শৈলমূলে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়াছে। তাজমহলের মতো এটাও একটা নিখুঁত কবিতা…
অশনি রায়ের লোভ হয়, কবিতার প্রাণদ সেই স্বত্ত্বাধিকারীর করমর্দ্দন সে করে।
বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে কাহার রচনার ঊর্দ্ধতম আয়ু পঁচিশ বৎসর, অশনি রায় অধুনা তাহাই চিন্তাপূর্ব্বক নির্ণয় করিতেছে।
নিজের সম্বন্ধে তার ভয় নাই— এক শতাব্দী রাজত্ব সে করিবেই; কিন্তু তাহার মতো, সে যেমন করিতেছে তেমনি করিয়া, অন্তরের উত্তাপ আর অকপটতা, আর হৃদয়লীন মানবপ্রেম ওতঃপ্রোতভাবে বিকিরণ করিয়া যাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন না, কেবল প্রজ্ঞার প্রখরতা দেখাইতেই আগ্রহবান্, তাঁহাদের আশা নাই— তাঁহাদের জীবনকাল খুবই কম— বিশ-পঁচিশও নয়; কারণ, সাহিত্যে বুদ্ধি থাকে নিষ্ফলা হইয়া; প্রসাদ এবং প্রভাব বিতরণ দ্বারা যে নিজেকে ক্রমাগত স্ফুটতর করিয়া উদ্ভূত করিতে থাকে সে হইতেছে হৃদয়। বুদ্ধি বোনে তর্কের জাল, হৃদয় পান করায় রস। হৃষীকেশ হৃদয়েই বাস করেন, মস্তিষ্কে নয়—
ভাবিয়া অশনি রায় নির্ভয় হইয়া গেছে— তার মতো দীর্ঘজীবী গণপতি ঘোষালও নয়; গণপতির হৃদয় শক্তিহীন— সে মাথা খাটাইয়া কেবল সমস্যা আর দুর্গতের অবতারণা করিতেছে।
কিন্তু অশনির ও-সব চিন্তা অবান্তর— বিশ্রামের পোষাক…
আদত কাজেও সে এই সুযোগে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে— সেটা হইতেছে আর একখানি উপন্যাস, যাহা অধিকতর যুগান্তকারী হইবে। উপন্যাসের অঙ্কুর এবং পুষ্প, অর্থাৎ তার শুরু আর তার শেষ, সে হৃদয়স্থ হৃষীকেশের আবহাওয়ায় উত্তাপ আর প্রেম দিয়া মনোজগতে নির্ম্মাণ করিতেছে….
এখনো কলম ধরে নাই— প্রেরণার বেগে কলম ধরিবার অধিকার-লাভের সাধনায় সে যখন বিহ্বল তখন একদিন সহসা তার সাধনায় এমন একটা বিঘ্ন ঘটিয়া গেল যার তুল্য পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না।
স্থান নিস্তব্ধ ছিল— উপন্যাসের প্রসব-গৃহ ঠিক্ এম্নি নির্জ্জন, আর, পবিত্রভাবে শান্তিপূর্ণ হওয়াই দরকার; কিন্তু তেমনটি একদিন রহিল না— প্রবল শব্দে ঝড় উঠিল যেন বায়ুমণ্ডল এক নিমিষেই আলোড়িত হইয়া কাজ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল…. ভয়ে অশনির প্রাণ এতটুকু হইয়া গেল— অঙ্কুর এবং পুষ্প একই সঙ্গে নির্জ্জীব হইয়া উঠিল….
বেলা তখন তিনটা— অশনি চোখ বুজিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল; ভাবিতেছিল, বেশ আছি… এমন সময় ঐ রেষ্ট হাউসেরই সম্মুখে নরনারীর কলরব শুনিয়া অশনি চোখ খুলিল… তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ধারে যাইয়া দাঁড়াইল; এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ভয়ে মুখ তখনই টানিয়া লইল— দেখা গেল, বিপুল একটা জনতা নীচেকার হলে প্রবেশ করিতেছে।
অশনির সন্দেহ রহিল না যে, ভক্তবৃন্দ তার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া তার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। এ কি কঠিন বিধাতা! তাহাকে কি বিশ্রামসুখ ভোগ করিবার আর নিভৃতে চিস্তা করিবার অবসর তিনি দিবেন না! বিখ্যাত হওয়ায় এ কি বিড়ম্বনা!
দম্ লইতে অশনি রায়কে চেয়ারে বসিতে হইল….
নীচে হইতে হাস্যস্রোত উপরে ছুটিয়া আসিতেছে…. তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করে কি না শুনিবার জন্য অশনি উৎকর্ণ হইয়া রহিল… মনস্থ করিল যদি ওরা কেহ তা’ করে তবে জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া সে পলায়ন করিবে। কিন্তু ওরা সবাই উচ্চৈস্বরে কথা কহিতেছে— যেন হাটের গোল! তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করিয়া থাকিলেও শোনা গেল না।
সওয়া চারিটায় চা—
ঘণ্টা পড়িল—
চায়ের টেবিলে যাইবার পূর্ব্বে অশনি ঘরের ভিতর জোরে জোরে কয়েকবার পায়চারি করিয়া লইল। উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তার গা ঠাণ্ডা হইয়া আসে যেন।
সিঁড়ির অর্দ্ধেক নামিয়াই মোড় হইতে অশনির চোখে পড়িল, যেন ফোটা ফুলের বাজার বসিয়াছে!

চট্ করিয়া ঘুরিয়া অন্য সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া সে ম্যানেজারের অফিসে গেল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এঁরা সবাই ‘মহানট ছায়াবীথি’ লিমিটেডের শিল্পী প্রভৃতি; ‘মায়াবী মদনের’ শুটিং শেষ হইবার পর মাত্র সাত দিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন অবসর যাপন করিতে…
এই সংবাদ দিয়া সুর একটু তরল করিয়া ম্যানেজার জানিতে চাহিলেন;— দেখ বার মতো, নয় কি?
ম্যানেজারের প্রশ্নের জবাব অশনি দিল না, দিতে পারিল না; তার বুক তখন আরো দুরুদুরু করিতেছে। প্রত্যক্ষ ভক্ত এঁরা নন্; কিন্তু তাতে কি আসে যায়! শিল্পী এঁরা ত’ বটেই! শিল্পীশ্রেষ্ঠের প্রতি শিল্পীর যে আকর্ষণ তা’ বাস্তবিকই প্রচুর— আর, তা’ কোন বাধা মানে না; আত্মনিক্ষেপ করিবেই।
অশনির আরো মনে হইল, স্বনামধন্যের কোনোদিকেই পা বাড়াইবার পথ নাই— সহিষ্ণুতার পরীক্ষা তাহাকে পদে পদে দিতে হয়।
কিন্তু চা খাইতেই হইবে—
নিতান্ত ভীরুর মতো হলে প্রবেশ করিয়া অশনি একখানা চেয়ারে বসিল; প্রথমতঃ সে মুখ নামাইয়া রহিল; তারপর ছায়াচিত্রের অনুকরণে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে শিল্পীগণের দিকে নেত্রপাত করিল….
অশনি জানে, চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক রকম শিল্পীর প্রয়োজন আছে; যথা : প্রচার-শিল্পী, প্রাচীর-শিল্পী, প্রয়োগ-শিল্পী, নাট্য-শিল্পী, সঙ্গীত-শিল্পী, শব্দ-শিল্পী, পট-শিল্পী, চিত্র-শিল্পী, রসায়ন-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, পরিকল্পনা-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, প্রসাধন-শিল্পী, মঞ্চ-শিল্পী, রূপায়ন-শিল্পী, ইত্যাদি…. এই সমুদয় শিল্পীদের আবার সহকারী ও সহযোগী শিল্পী থাকেন, এবং থাকেন নক্ষত্র, অগণিত নক্ষত্র। এঁরা তারাই।
পর্দ্দার বাহিরে সুন্দরতর কায়াময় সজীবতার অভ্যন্তরে ইঁহাদের দেখিয়া অশনি রায় মুগ্ধ হইয়া গেল; নরনারীর একত্র সমাবেশের দ্বারা স্ফূর্ত্ত জীবনের এই চাকচিক্যময় অভিব্যক্তি, আর, প্রাণের এই অনর্গল নির্গমশীলতা তাহার বড় ভালো লাগিল….
নীরবতা আর নির্জনতা ভালোই, কিন্তু এ-ও বেশ, যদি তাহাকে নাড়া না দেয়।
—মশায় একা বসে’ আছেন, এদিকে আসুন না!
অশনিকে নাড়া দিয়া জনৈক শিল্পী আহ্বান করিলেন।
অশনি ঐ দিকেই তাকাইয়া ছিল; এই আহ্বানে কেবল আহ্বান-কারীকে নয়, ওঁদের সবাইকে সে যেন আরো স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল; বেশভূষায়, আর, দেহের আপাদমস্তকে, আর কথোপকথনে, এমন কি বঙ্কিমভঙ্গিম মৃদু হাসিটিতেও, এমন নিঃসন্দিগ্ধ মসৃণতা অশনি আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। একেবারে কাছে ঘেঁষিয়া গেলে যদি মায়া নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া অশনি নড়িল না; বলিল,— আমি এখানেই থাকি। আপনাদের সঙ্গেই ত’ আমি আছি!
—বেশ। আপনার নামটি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ধৃষ্টতা মাফ ক’রবেন। একা তরুণ আপনি এই নির্জ্জনবাসে এসেছেন দেখে’ জিজ্ঞাসা করছি।
শুনিয়া অশনির মনে হইল, লোকটা ভারী চতুর; কি-কারণে উহাকে চতুর মনে হইল তাহা অশনি জানে না; কিন্তু ব্যক্তিটিকে চতুর মনে করিয়া সে একটু সঙ্কুচিত হইল…
এবং তারপর, টানিয়া-বুনিয়া নয়, অত্যন্ত সোজা স্বাভাবিকতারই সহিত তার মনে হইল, এমনও হইতে পারে যে, তাহারই একটি গল্পের কথা-রূপকে ছায়া-রূপ দিবার পরিকল্পনা চলিতেছে; সত্ত্বাধিকারী একেবারে নাছোড়বান্দা— তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন : “অশনি রায়ের গল্পকে পর্দ্দায় ফেলতে পারলে তোমরা ধন্য হ’য়ে যাবে; টাকা রাখার ঠাঁই পাবো না।”
এতগুলি লোক— পুরুষ এবং নারী— সহসা সেই অশনি রায়কে সম্মুখে পাইয়া প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে, তারপর প্রচণ্ড আনন্দে সবাই কলরব করিয়া উঠিবে; তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আর চেষ্টা পূর্ব্বাপর ওঁদের যে কতো ছিল তাহাই ওঁরা আগে আর সবেগে বলিবার প্রতিযোগিতাসহ প্রত্যেকেই বলিবেন— মহিলারাও বলিবেন….
চলচ্চিত্র-শিল্পী আর কথা-শিল্পীর প্রেরণার উৎস একই না বিভিন্ন, ইহাই লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে চাহিবেন….
বলিল,— আমার নাম অশনি রায়।
—অশনি?
অতর্কিত দর্শন-ব্যাপারের প্রবলতম বিস্ময় আর চমৎকারিত্ব সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি ওদিক্ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর, সে-চীৎকার অশনির বুকে পড়িল মুগুরের মত— আঘাত হিসাবে নয়, ওজন হিসাবে তা’ বেজায়। অশনি মূঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল….
কিন্তু ব্যাপার তা’ মোটেই নয়— অশনি যা’ ভাবিয়াছে তা’ নয়; সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত নয়। যিনি অশনি বলিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, চীৎকারের পর তিনিই বলিলেন অন্য কথা; বলিলেন,— না, সে-অশনি নয়। আমাদের সঙ্গে এক অশনি পড়ত’ পাঠশালায়। অশনি কোন্ ‘শ’?
অশনির হুঁশ ফিরিতে দেরী হইল—
একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল,— যা’ শাস্ত্রসম্মত— তালব্য শ।
—কিন্তু আমাদের সেই অশনি লিখত’ অশাস্ত্রীয় দন্ত্য স দিয়ে। পণ্ডিতের এত মা’র খেয়েছে তবু সে দন্ত্য স ছাড়েনি’!
শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল…
অশনি লক্ষ্য করিল যে, শিল্পীগণের হাসি মামুলী ধরণের নহে, অর্থাৎ প্রবল হইলেও যথেচ্ছাচারিতার সহিত বিস্তৃত নহে; একটা আর্টসম্মত পরিধি এবং পরিমিতির ভিতরেই সুষ্ঠু লালিত্য আর সৌকুমার্য্যের সহিত তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে— কান পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।
অশনিও হাসিল—
শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত একগুঁয়ে যে সহপাঠী তালব্য শ-এর স্থানে কেবলি দন্ত্য স বসাইতে পারে তাহার কথায় না হাসিয়া উপায় নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে অশনির ইহাও মনে হইল যে, ইহাদের হাসির তুলনায় তাহার হাসি নিতান্তই স্থূল, অনভিজাত, আর গ্রাম্য।
তৃতীয় ব্যক্তি একটি সুন্দরী মহিলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,— মিস্ ভার্জ্জিন, তোমার গার্হস্থ্য নাম ত’ সুবসনী— কোন্ শ?— বলিয়া তিনি দৃষ্টি শ্লথ করিয়া রাখিলেন— মহিলার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে সটান্ তাকাইয়া থাকা মার্জ্জিত-অবয়ব শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়।
সুবসনা বলিলেন,— সোয়ামীতে যে স, সেই স।
—সোয়ামীর কথা আর বলো’ না, লক্ষ্মী! আমাদের গুরুলোক হলিউডের আচরণে সোয়ামী কথাটার ওপরেই ঘেন্না ধরে’ গেছে।
ওঁদেরই সমীপস্থ আর-একজন বলিলেন,— স্বামী আর স্ত্রী, দুই-ই দন্ত্য স। কিন্তু পর-পর ঐ দন্ত্য স প্রয়োগের ফল হয়েছে এই যে, দুনিয়ার স্বামীস্ত্রীতে বনিবনাও হ’চ্ছে না।
শুনিয়া একটি সুন্দরী বড় আহতা হইলেন; ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন,— অবাক্ করলেন, কামিনী-বাবু। তার মানে?
কামিনীবাবুর নাম প্রাচীরগাত্রে রঙ্গিন অক্ষরে কবে যেন দেখিয়াছে বলিয়া অশনির মনে হইল।
কামিনীবাবু বলিলেন,— মানে এই যে, দন্ত্য স-এর ঐ অপরিমিত ব্যবহারের দরুণ স্বামী দেখায় দন্ত, আর স্ত্রী আসে দন্ত মেলে’ কামড়া’তে।
দন্তপ্রশস্তি শুনিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিল, পূর্ব্বোক্তরূপে আর্টের আইন লঙ্ঘন না করিয়াই।
তারপর একজন বলিলেন,— যে যা’-ই বলো, মিস্ রঙ্গিলা না এলে কিছুই ভাল লাগবে না। বলিয়া তিনি অরুচির অপরূপ একটি ভঙ্গী এমনি করিয়া মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন যে, অশনির মনে হইল অভিনয় সার্থক হইয়াছে।
দক্ষিণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া একজন সে কথাব জবাব দিলেন; বলিলেন,— সে আসবে শ্রীমান প্রেমেশের সঙ্গে।
…কথার উপর কথা আছড়াইয়া পড়িয়া আর ফেনায়িত হইয়া হাস্য-পরিহাস চলিতে লাগিল। সবাই খুব চঞ্চল, কাঠবিড়ালীর চাইতেও চঞ্চল, প্রজাপতির চাইতেও চঞ্চল…. মালঞ্চের সবগুলি ফুল সবগুলি দল মেলিয়া শোভার আর সুখের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল।
অশনির মনে হইতে লাগিল, সে-ই কেবল অচঞ্চল, অপ্রস্ফুটিত— তার ঔজ্জ্বল্য নাই… সে, জলজ্যান্ত মানুষ একটা, যে এখানে বসিয়া আছে তা’ যেন ওদের চোখেই পড়িতেছে না!
চা-পান শেষ হইল এতক্ষণে—
অশনি উঠিয়া দাঁড়াইল; বাহিরে যাইবার দরজার কাছে গেল; সেখানে দাঁড়াইয়া তার একটি সিগারেট ধরাইবার ইচ্ছা হইল; সিগারেট একটি প্যাকেট্ হইতে বাহির করিয়া সে দুই ঠোঁটের ভিতর গুঁজিয়া দিল খুব আলগাভাবে; কিন্তু তখনই সিগারেট ধরানো তার বরাতে ছিল না—
দিয়াশলাইয়ের কাঠি টানিয়া বাহির করিবার সময়টিতেই ঘটিল এক ব্যাপার— ব্যাপারটি রূঢ়, সন্দেহ নাই….
ঠোঁটে সিগারেট, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, বাঁ হাতে দিয়াশলাইয়ের বাক্স, বাক্স খানিকটা খুলিয়া সে কাঠি টানিয়া লইতেছে, হঠাৎ পিছন্ হইতে একটা ঠ্যালা খাইয়া সে সর্ব্বাঙ্গে নড়িয়া গেল…
অপর যে ব্যক্তি ঐ পথেই আসিয়াছে এবং যাহার গায়ের ধাক্কায় অশনির ঠোঁটের ভিতরকার সিগারেট টুপ করিয়া মাটিতে পড়িল চটিয়া গেল সে-ই— চটিয়া সে বলিল, ‘‘ধ্যাৎ’’….
বলিয়া ভারি চঞ্চলতার সহিত সে বাহির হইয়া গেল….
ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধমক্ খাইয়া অশনির কিছুই মনে হইল না, ইহা বলা চলে না— কিছু মনে তার হইলই; তার উপরে সে অনুভব করিল, চারিদিকটা যেন বাষ্পাবরণে মলিন হইয়া উঠিয়াছে; এবং আরো ঘটিল ইহাই যে, সে শুনিতে লাগিল, কে যেন তার কানের কাছে দাঁড়াইয়া অতিশয় তাচ্ছিল্যের সহিত পুনঃপুনঃ বলিতেছে : ‘‘ধ্যাৎ”।
[গল্পটি ‘মেঘাবৃত অশনি’ (প্রকাশ: পৌষ, ১৩৫৪) গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া। বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত।]