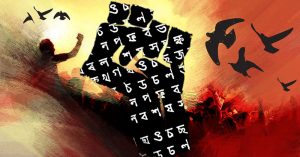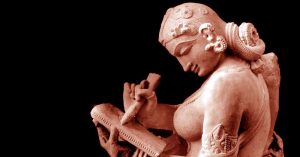বড়পিসিকে আমরা পিসিমণি বলতাম। তাঁর ছেলেমেয়েদের ডাকা হত বড়দা, ছোটদা, বড়দি আর ছোটদি বলে। কিছুদিন আগে ছোটদা মারা গেছেন, বছর-পঞ্চাশেক বয়সে। আজ ছোটদি ছাড়া আর কেউই বেঁচে নেই। ছোটদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পুরনো দিনের অনেক গল্প বাইরে এল আর সেই গল্পের অনেকখানি জুড়ে ছোটদার কথা। ছোটদা, বাংলার একসময়ের নামী ফুটবল খেলোয়াড় অলোক মুখার্জি। জন্মেছেন গত শতকের ষাটের দশকে। তাঁদের শৈশব-বাল্য-কৈশোর কাল আজকের মত একবারেই ছিল না। ছোটদার প্রসঙ্গ, ছোটদার ছোটবেলার গল্পে তাঁর সখা গোপীনাথ থাকবে না, তাই কি হয়? সেই গোপীনাথ বা গোপীদার দুষ্টুমি ও মজার গল্প বলতেই ধারাবাহিক ‘ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ’।
চতুর্থ কিস্তি
আমরা যখন আজ ধাপে ধাপে বয়সের সিঁড়ি চড়ছি তখন সত্যিই মনে হচ্ছে পুরনো দিনগুলো গল্পের দুনিয়াই ছিল। আমাদের ছেলেপুলেরা এমনতর ছোটবেলা পেল না। হয়তো শহরের কোনও বাচ্চাই আজ আর তা পায় না। এই গল্পগুলোর অছিলায় তবুও তো একবার উঁকি মারা যাচ্ছে ওই দিনগুলোয়!
বছর বাইশ হল আমি পশ্চিম বাংলার বাইরে। তবু আজও আমি সেদিনকার লিলুয়া রেল কলোনির অবিকল বর্ণনা দিতে পারি। প্রতিটা বাড়ি, প্রতিটা রাস্তা, প্রতিটা গাছ, মাঠ— সব আমাদের একান্ত আপন ছিল। আসলে কী জানো, তখন ম্যাপ (Map) আমাদের মনে ছিল, ফোনে (Phone) ছিল না।
এবারের গল্পটাও গোপীনাথ আর ছোটদা-দের ছেলেবেলা নিয়ে। ষাটের দশকের গল্প। শোনো সেই গল্প।
রেল কলোনির পাঁচিল যেখানে শেষ, ঠিক তার পরেই একটা গুরদুয়ারা ছিল। সেখানে, প্রতি রবিবার শিখদের জমায়েত হত, ‘প্রসাদ’ বিতরণ চলত। একবার, গোপীনাথের ওই প্রসাদ খাবার খুব ইচ্ছে হল। একেবারে নিজস্ব কায়দায় সে বলল, ‘মাইরি! রবিবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে আসা দায় হয়েছে। এত সুন্দর দেশি ঘিয়ের সুজির গন্ধ! ওই সুজি… খবর নিয়েছি, শিখরা ওটাকে ‘হালওয়া’ বলেন। ও ‘হালওয়া’ আমাকে টানছে।’
ছোটদার চোখেমুখে প্রশ্ন, ‘‘সুজিকে ‘হালওয়া’ বলে?’’ (এখানে তোমাদের বলে রাখি, ওদের ছোটবেলায়, মানে এই ধরো ষাটের দশকে, ঘরে টিভিই ছিল না, মোবাইল ফোনের কথা তো ভুলেই যাও। কাজেই, সবাই যে সব হিন্দি জানে, এমনটা যেন ভেবে বোসো না।) গোপীনাথ সেদিকে দৃকপাত না করে বলল, ‘নামে কী আসে যায়? আমরা লিলুয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নয় হালুয়া বলব! ওই হালুয়া হল গিয়ে চুম্বক; এই আসছে রবিবার আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।’
গোপীনাথ ছোটদাকে সাবধান করল, ‘আসছে রবিবার ট্রায়াল অভিযান। তাই ভিড় বাড়ানোর দরকার নেই। শুধু গুরু তুমি আর আমি— আমরা দুজনেই ট্রিপ মারব। পরে গতিক দেখে বাকিদেরও নিয়ে যাওয়া যাবে।’ সারা সপ্তাহ রবিবারের অপেক্ষায় কাটল অথচ গোপীনাথ একবারও হালুয়া নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। ছোটদা ভাবল, ‘কে জানে গোপীর মনে আছে কিনা!’
রবিবার। সকাল দশটার আগেই গোপীনাথ হাজির। ‘সত্যি গোপী কথার খেলাপ করে না’, মনে মনে বলল ছোটদা। তুবড়ি-তেজে গোপীনাথ বলল, ‘গুরু, একটা রুমাল নিয়ে নাও। চলো আজ হালুয়া খেয়ে আসি।’ এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, গোপীনাথ ছোটদাকে প্রায়ই ‘গুরু’ বলে সম্বোধন করত। ছোটদা ফুটবলটা বরাবরই দুর্দান্ত খেলত। এই একটা জায়গায় গোপীনাথ, ছোটদাকে তার গুরু স্বীকার করে নিয়েছিল। আর আমরা বড় হয়ে, যখন ছোটদাকে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে খেলতে দেখেছি, তখন মনে হয়েছিল সেই ছোট বয়সেও গোপীনাথের চোখ প্রতিভা চিনতে ভুল করেনি।
সে যাহোক, ছোটদা রুমাল তো সঙ্গে নিল কিন্তু হালুয়ায় উৎসাহ দেখাল না। ‘দ্যাখ গোপী, তুই যা। আমি বাইরে দাঁড়াব।’ গোপীনাথ এতটুকুও আপত্তি না করে বলল, ‘গুরু তাই হবে। তবে মনে রেখো, ওখানে নিশ্চিন্তে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। ও হালুয়ার গন্ধ হল চুম্বক, ও ঠিক তোমাকেও ভেতরে টানবে ওরা গুরুদুয়ারার পথে পা বাড়াল।
গুরুদুয়ারায় বেশ ভিড়। কোনও উৎসবের দিন মনে হচ্ছে। রবিবারকে ধর্মকর্মের জন্য ব্যবহার করছে সব। সারা সপ্তাহ যা কাজের চাপ! নিশ্বাস নেবার সময় থাকে না। গোপীনাথ মাথায় রুমাল বেঁধে নিল। হালুয়ার গন্ধ ততক্ষণে ছোটদাকেও তার চুম্বকত্ব দেখানো শুরু করেছে। ছোটদাও কিন্তু কিন্তু করতে করতে মাথায় রুমাল বাঁধল। গুরুদুয়ারায় ঢুকল ওরা। হালুয়ার গন্ধকে দিক-নির্ণায়ক মেনে গোপীনাথ এগিয়ে চলেছে। ছোটদা ইতঃস্তত করে আওয়াজ দিল, ‘এই গোপী, অমন হনহন করে যাচ্ছিস কেন?’ অযথা প্রশ্নে খুবই বিরক্ত হল গোপীনাথ। শুধু বলল, ‘ফলো মি।’ দু-চারজন সর্দারজি ওদের সামনে দিয়ে আসছেন। নজর তাদের দিকে পড়তেই হঠাৎ গোপীনাথ তালি বাজিয়ে বলতে শুরু করল, ‘গুরু নানকো, জন্মদিনোকো…’। সর্দারজিরা বিস্ময়সূচক দৃকপাত করে নিজেদের দিশায় এগিয়ে গেলেন। গতি বাড়াল গোপীনাথ। হালুয়ার দেশি ঘিয়ের গন্ধ তীব্র হয়েছে। গন্তব্য আর গোপীনাথ বেশি দূরে নেই। অবশেষে পৌঁছে গেল হালুয়া বিতরণস্থলে। শালপাতার বাটি ভরে ভরে সবাইকে হালুয়া দেওয়া হচ্ছে। ঘি চুপচুপে হালুয়ার সে কী চমক! খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে গোপীনাথ হালুয়া নিল। ছোটদার হাতেও পৌঁছল বাটি। তারপর দুজনে গুরদুয়ারা থেকে বেরোনোর রাস্তা ধরল। হালুয়ার বাটি এমনভাবে সাফ হল যে ওই বাটিতে আবার অন্যদের হালুয়া দেওয়া যায়!
ছোটদাই প্রথম মুখ খুলল। ‘হ্যাঁ রে গোপী, তুই ওসব কী বলে চ্যাঁচাতে শুরু করলি? ওটার কী দরকার ছিল?’ হাজির জবাব গোপীনাথ বলল, ওটা গুরদুয়ারার মন্ত্র বলতে পারিস। ওই মন্ত্রের জোরেই ওরা আমাদের শিখ ভেবে হালুয়া দিল।’
‘মোটেও না। এমনিও ওরা যে আসছিল, সবাইকেই হালুয়া দিচ্ছিল। ওমন পাগলামো করার কোনও দরকার ছিল না’, বলল ছোটদা। গোপীনাথ, বিইং (being) গোপীনাথ, ছোটদার কথায় একটুও পাত্তা দিল না। বলল, ‘বাজে কথা রাখ তো। আসল কথাটা শুনে রাখ, এবার থেকে রবিবার আর হালুয়ার গন্ধ মানেই গুরুদুয়ারা ফিক্স। যাতায়াতের পথে আমি ঠিক হালুয়া ডে (day) ট্রাক (track) করতে থাকব।’ ছোটদার তো মাথায় হাত। গোপীনাথ বলল, ‘‘মাথায় হাত দিয়ে বুদ্ধিটাকে ভাল করে ঘষে নে আর মন্ত্রটা শিখে রাখ। ‘গুরু নানকো, জন্মদিনকো’।’’ ছোটদা বলল, ‘তা না হয় হল। কিন্তু প্রতি রবিবার তো আর গুরু নানকের জন্মদিন থাকবে না। তখন?’ উত্তরে গোপী বিজ্ঞের মতো নাক উঁচু করে বলল, ‘লে হালুয়া! বড্ড জ্বালাস। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। কপাকপ হালুয়া খেলি কিনা বল? আর জেনে রাখ, জন্মদিন হোক বা না হোক আমি ঠিক হালুয়া ম্যানেজ করব। গোপী হালুয়াকে আর হালুয়া গোপীকে ঠিক খুঁজে নেবে। চল এবার খেলতে চল। হালুয়া হজমও তো করতে হবে!’
ওরা চলতে থাকল আমতলা মাঠের দিকে। ওই মাঠে আমরাও ছেলেবেলায় খেলেছি। আমতলা মাঠ মনের মধ্যে আজও তেমনি সবুজ হয়ে আছে।
চিত্র : গুগল
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: লিচু চুরি
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: চাঁদা আদায়
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: ঘুগনি সেল

ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: মুদিখানার প্রত্যাবর্তন
ইনস্টলমেন্টে গোপীনাথ: আচার অভিযান