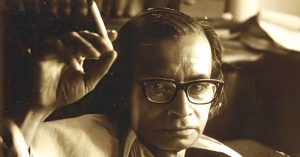দীনবন্ধু মিত্রের লেখা বিখ্যাত নাটক ‘নীলদর্পণ’; উনিশ শতকে ঘটে যাওয়া নীলবিদ্রোহের এক মর্মন্তুদ নাট্যরূপ। আজও বাংলার বিভিন্ন স্থানের মত কাটোয়ার গ্রামেগঞ্জে ভাঙচোরা, বিলীয়মান নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। শোনা যায়, কত রাইচরণ তোরাপ ক্ষেত্রমণি গোলক বসুদের ব্যথাবেদনার লোককাহিনি। দাঁইহাট দেওয়ানগঞ্জ থেকে অগ্রদ্বীপ পাটুলি, চাণ্ডুলি থেকে ওকড়সা, সুদপুর হয়ে গাঁফুলিয়া-পঞ্চাননতলা, মঙ্গলকোট থানার শ্যামবাজার থেকে কাটোয়ার গোয়াই— এমন কত জনপদে আজও দেখা যায় নীলচাষের স্মৃতিস্বরূপ ডাঙা, পুকুর মাঠ ঘাট আর নীলকুঠির ধংসাবশেষ। হারিয়ে গেছে তাদের ইতিহাস। বিস্মৃতির পলিতে চাপা পড়ে গেছে সেইসব দুর্দান্ত অত্যাচারী ইংরেজ নীলকর বা দেশীয় জমিদারের নাম। ব্যতিক্রম সবসময় থাকে। যেমন শাঁখাই-এর এডিস সাহেব; এঁর কথা আজও শোনা যায়, জানা যায়। শুধু এডিস সাহেব নন; তাঁর আগে থেকেই শাঁখাই নীলকুঠির ইংরেজ নীলকরদের নাম পাওয়া গেছে। জানা গেছে, মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত শাঁখাইয়ের নীলকরদের অজানা কাহিনি। সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হল যে, শাঁখাইয়ের নীলকুঠিতে একদা অর্থলগ্নি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
ভারতে নীলচাষের ইতিহাস বহু প্রাচীন। প্লিনির মতে, ভারত থেকেই নীলচাষ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। সতেরো-আঠারো শতকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ও আমেরিকায় ব্যাপকমাত্রায় নীলচাষ হত। চাষে তেমন লাভ না থাকায় এবং কৃষকদের ব্যাপক লোকসানের ফলে নীল উৎপাদন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জার্মানরা নীলকে বলত, ‘‘The Devil’s dye’’, অর্থাৎ,শয়তানের রং। তারাও একসময় নীলচাষ নিষিদ্ধ করেছিল। ফলে নীলকরেরা ক্রমশ বিকল্প স্থান খুঁজতে থাকে।
ইতিমধ্যে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। ইংল্যান্ডে ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মেটাতে নীলচাষ তখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। অনুকূল জলবায়ু, সহজলভ্য শ্রমশক্তি ও পর্যাপ্ত ঊর্বর জমির জন্য বাংলাকে নীলচাষের জন্য পাখির চোখ করেন ইউরোপীয়রা নীলকরেরা। এদিকে কোম্পানিও বেহাল অর্থর্নীতি চাঙ্গা করতে নীলচাষকে বাংলায় স্বাগত জানায়।
চন্দননগরে বসবাসকারী ফরাসি নাগরিক ক্যারেল ব্লিউম নামে এক নীলকর বাংলায় নীলচাষ শুরু করেন ১৭৮৯ সালে। বীরভূম জেলায় ডেভিড আর্স্কাইন জন চিপ সাহেবের উদ্যোগে নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলায় নীলচাষ ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল এ সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলেও জেমস লংয়ের লেখা ‘দি ব্যাংক অব দি ভাগীরথী’ প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, দাঁইহাট দেওয়ানগঞ্জে মোটামুটি ১৭৯৩ সাল নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল, যদিও সেখানকার নীলকরের নাম জানা যায়নি। আরও জানা যায়— দেওয়ানগঞ্জে হাড়ি বাগদি বুনো পোদ ধাঙর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহিরাগত মানুষজন এই নীলকুঠির সঙ্গে যুক্ত ছিল। লং সাহেবের মতে, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে তখন ২৯টি নীলকুঠি ছিল।
নীলচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে যে, তখন বছরে দুবার নীলের চাষ হত; বসন্ত ও হেমন্তকালে। মার্চ মাসে বৃষ্টির পর নীল বোনার কাজ শুরু হত। আর নীল কাটা হত জুন মাসে। হৈমন্তী নীল বোনা হত অক্টোবর মাসে এবং কাটা হত এপ্রিল বা মে মাসে। বাসন্তী নীল হত পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং এটি ছিল গুণমানে উত্তম। শহর কাটোয়ায় একজন বাঙালি নীলকর ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। কাটোয়ার মিশনারি জুনিয়র কেরিসাহেব মি. অ্যালবার্ট নামে জনৈক নীলকর্মচারীকে ব্যাপটাইজড করেছিলেন। ইনি ছিলেন কাটোয়ার নীলকুঠির কর্মচারী।
হান্টার সাহেবের লেখা ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, বার্ডওয়ান’ গ্রন্থে উল্লিখিত ১৮৭১ সালের কালেক্টর প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে বর্ধমান জেলায় তখন ইউরোপীয় নীলকুঠি টিকে ছিল মাত্র তিনটি। দুটি কালনায় এবং একটি শাঁখাইগ্রামে। কালনার নীলকুঠি চলত আর্স্কাইন অ্যান্ড কোম্পানির তত্ত্বাবধানে। কালনার একটি নীলকুঠিতে ১৬ জন দেশীয় কর্মচারী কাজ করতেন। শাঁখাই নীলকুঠির মালিক ছিলেন এডিস সাহেব। তবে সে কারখানা তখন বন্ধ হওয়ার মুখে। ইতিমধ্যে বাংলাতে নীলবিদ্রোহের ফলে নীল কমিশন বসে। কৃত্রিম নীল রং আবিষ্কৃত হয়। ফলত, একের পর এক নীলকরেরা পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হন। নিবারণচন্দ্র তাঁর ‘কাটোয়ার ইতিহাস’-এ লিখেছেন— ‘কাটোয়া দুর্গের সন্নিকটে যে ইষ্টকস্তূপ সমন্বিত উচ্চভূমি দৃষ্টি গোচর হয়, উহা মিস্টার এডিস নামক জনৈক ইউরোপিয়ানের নীলকুঠি ছিল। বর্গির হাঙ্গামার সমতূল্য না হউক কুঠিয়ালের অত্যাচার বড় কম ছিল না। অত্যাচার নিবারণের জন্য স্থানীয় জমিদারের সহিত এডিস সাহেবের প্রথমে মতান্তর হয়, তারপর পাইক সর্দার লাঠিয়ালের লাঠালাঠি তারপরে তুমুল মোকর্দমা। এই যন্ত্রের পেষণে নীলকুঠিও অধঃপাতে গেল, জমিদার ও তাহার অনুগামী হইলে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই নীলকুঠির অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া বর্তমান ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে।’

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ‘বসুমতী’ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীহরিহর শেঠের ‘শ্রীগৌরাঙ্গ তীর্থে দুই দিন’ শীর্ষক রচনায় এডিস সাহেবের নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপের ছবি ছাপা হয়েছিল। অনেকেই দাবি করেন, বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭) তাঁর যৌবন বয়সে এডিস সাহেবের নীলকুঠিতে চাকরি করতেন। এই তথ্যটি সর্বাংশে সত্য নয়। দাশরথির যৌবনকাল যদি ১৮২৫ থেকে ১৮৩৫ সাল ধরা যায় তাহলে শাঁখাই নীলকুঠির মালিক তখন এডিস সাহেব নন; প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোম্পানি কিংবা মি. রোজ নামে জনৈক ইংরেজ নীলকরের।
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে (১৭৯৪-১৮৪৬) আমরা শুধুই মাত্র রবীন্দ্রনাথের পিতামহ বলেই জানি। দ্বারকানাথ যে সমকালীন ভারতবর্ষে একজন সফল ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী পুরুষ ছিলেন সে তথ্য প্রখর রবি-প্রতিভার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। জাহাজ ব্যবসা, বিমা, ব্যাঙ্কিং, কয়লাখনি, নিউজ পেপার, জমিদারি, স্টিমার চালানো এবং নীলের ব্যবসাও করতেন। ১৮৩০ সালে কার (William Carr) সাহেবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ‘কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি’ খুলেছিলেন। ১৮৩৫ সালের আগেই শাঁখাই নীলকুঠিতে অর্থলগ্নি করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তথা ‘কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি’।
‘ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮৩৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের মামলার একটি রায়দান থেকে শাঁখাই নীলকুঠি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে। মামলাটির যাবতীয় তথ্যাবলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৬ সালে ‘The Calcutta Monthly Journal, July’ সংখ্যায়। মামলার বাদী ছিলেন যশোরের নীলকর যোশেফ টুম্যান আর অভিযুক্ত ছিলেন টি পি মোরেল। এই মোরেল সাহেব তখন শাঁখাইয়ের নীলকুঠির নীলকর। এঁর আগে শাঁখাইর নীলকর ছিলেন মি. রোজ সাহেব। এই রোজ সাহেব ‘কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি’-র কাছ থেকে শাঁখাই নীলকুঠি হস্তান্তর করেছিলেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘The plaintiff, in this case is a grower of indigo seed in the district of Jessore, and the defendants are proprietors of the Shakia indigo factory, near Cutwa, on the Bhuggaruttee. In 1834 this factory was in the possession of Mr. Rose, who held it with Carr, Tagore and Co., and who previously to disposing of it…’।
বোঝাই যায়, শাঁখাই নীলকুঠির মালিকানার অংশ ছিল ‘কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি’-রও। শুধু নীলকুঠি নয়; ১৮৪০ সালেও গঙ্গায় যে পাঁচটি প্রাইভেট স্টিমার কলকাতা থেকে চলাচল করত এরমধ্যে ‘কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি’ চালাত তিনটি, যার স্টেশন ছিল কাটোয়াতেও। যাইহোক, এই মামলাটি থেকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যায়, যেমন মি. টুম্যানের কাছ থেকে শাঁখাই নীলকুঠির মালিক রোজ সাহেব দুশো মণ নীলবীজ কেনার চুক্তি করেন। প্রতি মণের দাম ধার্য হয়েছিল বারো টাকা। ইতিমধ্যে মোরেল সাহেবকে শাঁখাই নীলকুঠি বিক্রি করে দেন রোজ সাহেব। শর্তানুসারে এই চুক্তিপত্রটি কিনে নিতে বাধ্য হন মোরেল সাহেব। মোরেল বীজের গুণমান ভাল নয় বলে দশ টাকা হারে মণ প্রতি দাম দিতে গেলে টুম্যান নিতে অস্বীকৃত হন। ফলে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। এই মামলায় শেষপর্যন্ত টুম্যান জয়ী হয়েছিলেন এবং সুদ সমেত ১২৪৩ টাকা মেটাতে বাধ্য হয়েছিলেন শাঁখাইয়ের তৎকালীন নীলকর মি. টি পি মোরেল সাহেব।
তবে সব নীলকরই যে শোষক এবং অত্যাচারী ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ‘দি ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত (THE CALCUTTA REVIEW, VOL. XIX., JANUARY—JUNE 1853, page no-148) কাটোয়ার অনতিদূরে গঙ্গাতীরবর্তী এক গ্রামের মনোজ্ঞ বিবরণ-সহ নীলচাষের বর্ননা রয়েছে। সেখানকার জমিদার ছিলেন বাঙালি নীলকর। এ বিষয়ে জনৈক মিশনারি পর্যটক লিখেছেন— কাটোয়ার বিপরীতে অবস্থিত এক জনপদের নীলকর জমিদার ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি। সেই গ্রামের রাস্তাঘাট বাড়িঘর ছিল দেখার মতো। নীলকর জমিদার শাসিত এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ছিল নীলচাষ আর রেশম উৎপাদন করা।
লেখকের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে এই নীলকুঠি সম্ভবত নগর ইন্দ্রাণীর বারো ঘাট তেরো হাটের মধ্যে কোনও এক জনপদে অবস্থিত ছিল।
দাঁইহাট স্টেশনের কাছে একটি চকমিলানো তিনতলা একটি জমিদার বাড়ি আছে। মটুবাবু ওরফে জমিদার শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ শতকের প্রথম দশকে পরিত্যক্ত নীলকুঠির ভিতের ওপর এই বাড়িটি নির্মাণ করেন। নীলকুঠিটি কেনা হয়েছিল উনিশ শতকের আটের দশকে। পরবর্তীতে বাড়ির একাংশের মালিক সোমনাথ চ্যাটার্জি জানিয়েছিলেন যে, বাড়ির দাওয়াটি নীলকুঠির চেম্বারগুলি বুজিয়ে তৈরি করা। নীলকুঠির ভিত ছিল প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া। জমিদার বাড়িটির ১৬টি ঘর নীলকুঠির ভিতের ওপর গড়ে উঠেছে।
দাঁইহাট গার্লস স্কুলের পিছনে যে পুরাতন বাড়ির ধ্বংসস্তূপটি দেখা যায়, সেটি অনেকের মতে জনৈক ইংরেজ বণিকের বাসগৃহ ছিল। এই ইংরেজ বণিক দাঁইহাট ভাউসিং-এ চিনির কল চালাতেন। এখনও সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে চিনির কুঠি বলে। এ বিষয়ে ১৮৪২ সালে প্রকাশিত ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, ‘European sugar manufactories have been erected, on an extensive scale, at Doba and Bowsingh, between Culna and Cutwa.’ (পৃষ্ঠা-৪২৫)।