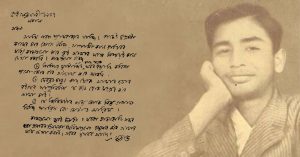পুরুলিয়া গিয়েছি ছো (ছৌ) নিয়ে কাজ করব বলে। বছর দশ আগের কথা। এই কাজে বুঁদ হওয়ায় আড়ালে চলে গিয়েছে একটা বিষয়— আলপনা। পুরুলিয়া জংশন থেকে কুদলুং গ্রাম যেতে গিয়ে জেনেছি অনতিদূরে ভাগাবাঁধ, বনবহাল, বালিগারা, মাকরাবেরা, আনাই, জামবাদ ইত্যাদি জায়গার নাম। যেতে যেতে চোখে পড়ছিল মাটির দেওয়ালে আঁকা আলপনা শিল্প। বড় আদরে বানানো। তবে কেবল পুরুলিয়া নয়, গ্রামের বাড়ির দেওয়ালকে আলপনার অলংকার দিয়ে সাজাতে দেখেছি পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়াতেও। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় তো ছোট্ট কুড়ের দেওয়ালে লোকচিত্র অবাক করে দেয়। যে বা যাঁরা এই আলপনা কর্মে পটু, তাঁদের আঙুলে জাদু। দক্ষতাও নিখুঁত। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, এই শিল্প সারল্যের ফসল। আমাদের শহরবাসীর কাছে বিরল এই ‘সারল্য’। জেনেছি যে, সাঁওতালদের উপজাতীয় গোষ্ঠীর পাশাপাশি সাদাক এবং মাহাতো সম্প্রদায়ের গ্রামগুলিতেও দেখা যায় আলপনা চিত্র। কৃষিবউ, কামার, কুমোর, মেথররাও এই শিল্পে পারদর্শী।
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প এবং তারাপদ সাঁতরার শিল্পী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত ছবি নিয়ে একটি নিবন্ধ এই বিষয়টা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে। গেটবেঙ্গল ডটকমে প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়ে জেনেছি, তপশিলি জাতি বা মিশ্র হিন্দু বংশোদ্ভূত মানুষদের মধ্যে প্রতি বছর দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর আগে এই দেওয়ালচিত্রের কাজ শুরু হয়। দেওয়াল আঁকার জন্য ব্যবহৃত রংগুলি কিন্তু অন্যতম আকর্ষণের। যা তৈরি করা হয় গাঁয়ের ঘরের ঘরেই। লাল ওচর, সাদা চক, কালি ইত্যাদি রং তৈরির কাঁচামাল। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার নয়ায় দেখেছি খয়ের, চুন, সুপারি গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে লাল রং তৈরি হতে। কখনও বা লটকান গাছের ফলের বীজও ব্যবহার করা হচ্ছে লাল রং তৈরিতে। নীল রং তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে অপরাজিতা ফুল। দেখেছি, সাপকঞ্চা নামে একটি গাছের পাকা ফল গুঁড়ো বা থেঁতো করে সেই রসের সঙ্গে বেল আঠা মিশিয়ে রোদে শুকোতে দিতে। পরে প্রয়োজনমতো জল মেশালেই তা থেকে তৈরি হয়ে যাবে নীল রং। আবার কাঁচা হলুদ গুঁড়ো করে বেল আঠা মেশালে এবং বনকুদরি (সম্ভবত তেলাকচু) গাছের পাতা চটকে যে রস, তার সঙ্গে ওই একইভাবে বেল আঠা মেশালে তৈরি হবে হলুদ ও সবুজ রং। এ ছাড়াও লম্ফের শিখা থেকে ভুসা কালি, এটেল মাটির ঘুসুম পুড়িয়ে সাদা রং থেকে পাকা পুঁইমিটুলির রসজাত বেগুনি রং তৈরি হওয়া দেখেছি অবাকদৃষ্টিতে। অন্যদিকে, যাঁরা আলপনা আঁকেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি, পাট দিয়ে তৈরি ব্রাশ দেওয়ালে রং লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দেখেছি, কোনও শিল্পী তাঁর আঙুলের চারপাশে মুড়ে রেখেছেন একটি ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। আলপনা সৃষ্টিতে তিনি মশগুল। প্রথমে সাদা খড়ির প্রলেপ দেওয়া হয় দেওয়ালে। ওটাই নাকি ভিত্তি। প্রতিমা তৈরিতে প্রথমে যেমন খড়ের কাঠাম বানানো হয়, এও তেমন কাঠাম। মূল এই ভিত্তি-র উপর নকশা আঁকা হয়। লতা, পাতা, ফুল, গাছ, পাখি নিয়ে তৈরি আলপনাগুলি যেন অদ্ভুত অপার রূপকথা। তবে আরও একটা জিনিস চোখে পড়েছে। তা হল রেখাচিত্র। এরমধ্যে একটা অঙ্ক আছে বুঝি। বলা ভালো জ্যামিতিক নিদর্শনও কিন্তু আলপনা শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। পুরুলিয়ার এক অঁজপাড়া কুদলুংয়ে ছো দেখব। ডুমুরডি গ্রামে আমরা যাচ্ছিলাম আমরা। গ্রামটি গরজয়পুর পোস্ট অফিসের লাগোয়া। ওখানে মুখোশশিল্পী কাঞ্চন রায়ের বাড়ি। তিনি মুখোশ তৈরিতে মশগুল। ওখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয় ছো-শিল্পী মাগারাম মাহাতোর সঙ্গে। তাঁর কাছেই বায়না ধরি। ‘ছো দেখব’। শীতের দুপুর। সমবেত রোল উঠল। ঢোলক, মাদলভেরি, ঝাঁঝ, সানাই, ধামসা, করতাল জাগাল গোটা গাঁ-কে। ছো শেষে একলাই বেরিয়েছি পাড়া ঘুরতে। বিকেল। সূর্যের পাটে যাওয়া তখনও বাকি। মনে তখন বাজছে— “তার থেকে মহাবীর/ ক্রোধে কাঁপে থরথর/ আসিছেন মহাবীর ময়ূর বাহন/ মাতা যার পার্বতী, পিতা মহেশ্বর/ শুনো শুনো সভাজন…” কার্তিক আসার পালা। হঠাৎই থমকে গেলাম। একটা মাটির বাড়ি। তার সদরের সামনে বসার ঠান। সেখানে বসে ইন্দিরা ঠাকরুন— এক বৃদ্ধা। সামনে সবজির ঝুড়ি। আর বাড়ির দেওয়ালে উড়ে যাচ্ছে পাখি, পাহাড়, অরণ্য, সঙ্গে অজস্র মোটিফ এবং নকশাও। এ যেন একপলকে দৃশ্যান্তর। একদিকে অভাবের জীবন্ত চিত্র। একইসঙ্গে প্রকৃতির অমন মায়া দেওয়ালে চিত্রিত। কিন্তু এমন মোটিফ, এমন নকশা তো ছবিতে দেখেছি আগেই। আলপনা তৈরির এই মোটিফ, নকশাগুলি হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর হাঁড়ি এবং ফুলদানিতে দেখা মোটিফগুলির মতই। এই চিত্র সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই যে প্রতিফলিত করে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঁচ হাজার বছর ধরে নদীর মত ভেসে এই শিল্প যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ সমাজকে যেন ‘অমরত্ব’ শিখিয়ে এসেছে।
“অহিরে-জাগহো লক্ষ্মী, জাগহো ভগবতী/ জাগে ত অমবস্যার রাত রে-বাবু-হো,/ জাগে-ত পতিফল, দেবে গো মা লছুমন,/ পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাইয়-রে।” সুনীপা চক্রবর্তীর লেখা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম এই গান। সংবাদ প্রতিদিন-এর ১২ মে, ২০১৮-র মুর্শিদাবাদ পৃষ্ঠায় তাঁর ‘বাঁদনার আগমনী গান আজ অতীত’ নামক লেখায় রয়েছে এ-গানের উল্লেখ। এই বাঁদনা পরব কালীপুজোর পরদিন পালিত হয়। পরবে যে গান গাওয়া হয়, তাকে বলে অহিরা। কেউ বলেন ঐহিরা। যদিও এখন পরবের রূপ বদলেছে। ‘সভ্যতা’-র হাওয়া লেগেছে। তাই ধামসা-মাদল সহযোগে ঘরে ঘরে গো-বন্দনা বা গো-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা গরু বা কাড়াকে সারারাত ধরে জাগানোর গান অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। কিন্তু ঘটনা হল, সাঁওতাল উপজাতি আলপনা শিল্পের বিকাশে বড় ভূমিকা পালন করে। এই পরব উদ্যাপন করার জন্য তাঁরা দেওয়ালে নতুন ছবি আঁকেন। পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুরের যেসমস্ত এলাকায় সাঁওতালদের বাস, সেজে ওঠে রঙিন আলপনায়। অতীত প্রজন্মের দেওয়া এই শিল্পের প্রতি সাঁওতাল উপজাতির মানুষ দায়বদ্ধ। কিন্তু, এই বাঁদনা পরব সশরীরে উপস্থিত থেকে দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। তবে, দুর্গাপুজোর সময় বেশ কয়েকবার বোলপুরে কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে। প্রকৃতি তীর্থের কাছে শিল্পী বাঁধন দাসের পুজো এখন বিখ্যাত। বিদেশিরাও ভিড় করে। এখন এই পুজো দেখে অনেকেরই মনে হবে কলকাতার থিম নির্ভর পুজোর মতই। কিন্তু ২০০২ নাগাদ, উচ্চমাধ্যমিক তখনও পাশ করিনি, প্রকৃতি তীর্থের পুজো ছিল গাঁয়ের কণ্ঠস্বর। কলকাতা পেরিয়ে সেখানে টাটকা নিশ্বাস নেওয়া যেত। ক্যানালের পাশ দিয়ে ছিল দীর্ঘ লম্বা লাল মাটির পথ (এখন পিচের রাস্তা)। ডানদিকে সোনাঝুরির জঙ্গল থাকত পথের সাথি হয়ে। দুর্গা দালানে আলপনা দিতেন গাঁয়ের সাঁওতালি বধূ। মেয়েরা খড়ি ভিজিয়ে নিয়ে আসতেন। ইয়া তাগড়াই গোঁফওলা পেটাই চেহারার কোনও দেহাতি পুরুষ তাঁর ধামসা নিয়ে নিকোনো উঠোনটার কাছে রাখতেন। রাতে বাজনা হবে। লাচ হবে। খুশির মাদল তালে ঘুম ভাঙানিয়া রাত কাটবে একসঙ্গে। এমনই ছিল তখন। এই সোনাঝুরি জঙ্গলের পাশে বনেরপুকুর আদিবাসী গ্রাম। এর মাত্র এক মিনিট হাঁটা পথ দূরত্বে রয়েছে মারাংবুরু মন্দির। এই গ্রামে রয়েছে সাঁওতালদের টিপটপ মাটির ঘর। খড়ের ছাউনি। টিনের চাল। কারোর ঘরের দেওয়ালে পোড়া মাটির মোটিফ। দেওয়াল চিত্রে ধান নিরোচ্ছেন কৃষিনারীরা। কখনও চোখে পড়ছে জঙ্গলে তির ধনুক নিয়ে শিকারের চিত্র। কখনও বা ধিতাং বোলে গান-বাজনা-নাচের ছবি। দেওয়ালে তো আলপনা রয়েইছে। কিংবা তাঁদের হাতের কাজ এবং আলপনার পরিচয় পেতে সৃজনী শিল্পগ্রামেও ঘুরে আসতে পারেন। একটু কমার্শিয়াল হলেও এক ছাতার নীচে এই আয়োজন এখনকার প্রজন্মের বেশ ভালই লাগবে।
কর্মসূত্রে নদিয়া গিয়ে আলপনা নিয়ে অদ্ভুত কথা শুনেছি। সেখানকার বধূরা চর্মরোগ থেকে মুক্তির আশায় পালন করেন একরকমের ব্রত (নাম মনে নেই)। তাঁরা আলপনা দেন রোগমুক্তির আশায়। এই আচার ফাল্গুনে পালন করা হয়। ওই সময়টায় অনেকেরই পক্স বা হামের মত রোগ হয়। বৈশাখে হয় পূর্ণিপুকুর ব্রত আলপনা। ইংরেজির এপ্রিল-মে-তে এই ব্রত পালন করেন অবিবাহিত মেয়েরা। তাঁরা দেবীকে আহ্বান জানান। বিশ্বাস, এতে বারোমাস জলে ভরা থাকবে পুকুর। মাটিও থাকবে উর্বর। উপাচার হিসাবে পান সুপারি ব্যবহার করা হয়। মেঠো আঙিনা বা শানের মেঝেতে আল কাটা হয় এই ব্রত পালনের সময়। পুকুরপাড়ে বা বাগানেও এই ব্রত করা হয়। দেখেছি সেঁজুতি ব্রত। একবার তো এই ব্রতর আলপনার ব্যাখ্যা চেয়ে জানতে চেয়ে অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। তারপর অন্য সূত্রে জেনেছি, ব্রতের আলপনা ও ছড়া কুমারী মনের আয়নার মত। চাঁদ, সূর্য, গাছ, নদী, বাসগৃহ, রান্নাঘর, নাড়ু, কীটপতঙ্গ, গৃহপালিত পশুপাখি, শিবমূর্তি, গৃহকর্তা, তৈজসপত্রাদি ও গয়না, দশপুতুল ইত্যাদি জল দিয়ে চটকানো চালবাটা দিয়ে আঁকেন কুমারীরা। আর আঁকেন ‘হাতে পো কাঁখে পো’। অনেকে বলেন, কোলে পো কাঁখে পো। এই ছবিতে দেখা যায়, নারীর কোলে সন্তানের খেলা করার ছবি। যদিও ষষ্ঠীর আলপনাতেও এমন রেখাচিত্র আঁকা থাকতে দেখেছি। রঙের চূর্ণ দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন ষষ্ঠীদেবীর চারিদিকে ‘রক্ষভূতিরেখা’ দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। যাই হোক, এমন বাহান্নটি রেখাচিত্র দিয়ে আঁকা হয় আলপনা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এই ব্রত। অবন ঠাকুর বলছেন, “ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখানি। এই-সব ছড়ায় নানা রসের সমাবেশ দেখা যায়, শুধু কামনাটুকু জানানো এই-সব ছড়ার উদ্দেশ্যও নয়। দুই রকমের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একশ্রেণীর ছড়া কামনাকে স্বর দিচ্ছে, সুর দিচ্ছে না, কিংবা মনের আবেগের অনুরণনও তার মধ্যে নেই। এই ভাবের ছড়া দিয়ে মেয়েদের এই সেঁজুতি ব্রতটি গাঁথা হয়েছে। সেঁজুতি খুব একটি বড়ো ব্রত। “সকল ব্ৰত করলেন ধনী, বাকি রইল সাঁজ-সুজনী।” এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিস আলপনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধ’রে, এক একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো-টুকরো কেবল কামনা জানানো ছাড়া আর কিছু পাই নে, যেমন— সাঁজপূজন সেঁজুতি/ ষোলো ঘরে ষোলো ব্ৰতী;/ তার এক ঘরে আমি ব্ৰতী/ ব্রতী হয়ে মাগলাম বর— ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর/ দোলার ফুল ধ’রে/ বাপের বাড়ির দোলাখানি/ আসতে-যেতে দুই জনে/ শ্বশুরবাড়ি যায়/ ঘৃত মধু খায়।” স্বচক্ষে না দেখলেও শুনেছি সুবচনীর ব্রতকথা। এই ব্রতেরও প্রতিরূপ চিত্র। রাজার পুকুরে অনেক হাঁস এবং তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এক খোঁড়া হাঁস।
বর্ধমানের এক গ্রামের পুকুরপাড়ের গল্প। সেই পুকুরে একজোড়া হাঁস ভাসে। প্রতিদিন। সেই হংসীর সাত-সাতটা ছানাপোনা। যদিও তাদের মধ্যে একটি ‘খোঁড়া’। জল থেকে উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাসার পথ ধরত ছোট্ট হাঁসটি। প্রথমে মা, তারপর খোঁড়া হাঁস, তারপর তার ছয় ভাইবোন। এভাবেই কাটল বেশ কিছুদিন। এরপর কী হল জানেন, খোঁড়া হাঁসটিকে দেখে দেখে বাকি ছয় হাঁসও খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের মায়ের সঙ্গে বাসায় ফিরত প্রতি গোধূলিতে। যে খোঁড়া, সে এমন দেখে ভাবল, বাহ তাহলে আমার শরীরে বোধহয় কোনও ত্রুটি নেই, আমার ভাইবোনেরাও যে অমনভবে হাঁটে… এভাবেই তারা কাটিয়ে দিল বাকি জীবন। এখন সেই খোঁড়া হাঁস পাঁচ সন্তানের মা। সে যে খোঁড়া, এখন তা জানে। তবে সব জেনেবুঝেও ভারি খুশিতে আছে সে! এই গল্পটা হঠাৎই মনে এল। মেয়েলি এই সুবচনীর ব্রতের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে কোনও মিল না থাকলেও মনে হল, এই সেই খোঁড়া হাঁস, যে কিনা রাজার পুকুরের অসংখ্য হাঁসকে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাছাড়াও লক্ষ্মী ব্রতের কথা তো প্রায় সকলেই জানেন। “দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ/ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস।।/ লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ/ করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন।।” এখন হয়তো গোবর মাটিতে নিকানো উঠোন গ্রামে ঘুরলে দেখা মিলবে হাতে গোনা কয়েকটি। কিন্তু তা বলে ফিবছর ধরে চলে আসা লক্ষ্মীর আরাধনা এবং লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে ঘরের উঠোন, গোলাঘর, গোয়ালঘর কিংবা মূল ফটকের সামনে আলপনা দেওয়া হবে না, তেমনটা কিন্তু নয়। দেবীকে আলপনা এঁকে সম্ভাষণ জানানো হয় ভক্তিভরে। অভিধান অনুসারে, ‘পিটুলীদ্বারা দেবস্থান, গৃহদ্বারাদি লেপন বা চিত্রকরণ।’ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিবায়ণ’ কাব্যের উল্লেখ পাই ‘দ্বারদেশে আলিপনা দিয়ে।’ এসবই রূপগত দিক থেকে মেয়েলি ব্রত অনুষ্ঠানের খাঁটি আলপনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। সেক্ষেত্রে তাকে শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের যুগলমূর্তি বলা যেতে পারে। অবন ঠাকুর বলেছিলেন, ‘সব আলপনাই সখীপনা’। নদী ভরা ঢেউয়ের মতো এর আহরণ আছে, কামনার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্য আছে, পুকুর কাটা আছে, প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা আছে— নেই পূজারি অথবা তন্ত্রমন্ত্রের কোনও জায়গা। আছে কেবল গাঁ-জীবনের কথাকলি। “মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের ফোঁটা!/ মা যেন বিয়োর চাঁদপানা বেটা!/ গুয়ো গাছ! কাকুনি গাছ!/ মুঠে ধরি মাজা। বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর,/ ভাই হয়েছেন রাজা/ শর, শর, শর!/ আমার ভাই গাঁয়ের বর।/ বেণী, বেণী, বেণা!/ আমার ভাই চাদের কোণা।/ আম-কাঁঠালের পিড়িখানি/ তেল-কুচকুচ করে, আমার ভাই অমুক যে/ সেই বসতে পারে। বাঁশের কোড়া। শালের কোড়া!/ কোড়ার মাথায় ঢালি ঘি/ আমি যেন হই রাজার ঝি।/ কোড়ার মাথায় ঢালি মউ,/ আমি যেন হই রাজার বউ/ কোড়ার মাথায় ঢালি পানি,/ আমি যেন হই রাজার রানি।” সেঁজুতি ব্রতর ছড়া। যা পেয়েছি অবন ঠাকুরেরই লেখায়। এখন তো আলপনার স্টিকারও কিনতে পাওয়া যায়। সেসব কতটা সময়োপযোগী, সেটা অন্য আলোচনা। ভাবুন কেবল, “পাখি, পাখি, পাখি!/ সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে ছাদে উঠে দেখি।” বানানটা লক্ষ করুন, ‘সতিন মাগি’। অর্থাৎ একসঙ্গে তিন নারী। অথবা বানানভেদে তা ‘সতীন’-ও হতে পারে। তাই তাঁকে বা তাঁদের প্রাণ দিয়ে কুমারীরা উচ্চারণ করেন— “চড়া রে, চড়ি রে, এবার বড়ো বান,/ উঁচু করে বাঁধব মাচা,/ বসে দেখব ধান/ ওই আসছে টাকার ছালা,/ তাই গুণতে গেল বেলা।/ ওই আসছে ধানের ছালা,/ তাই মাপতে গেল বেলা।” এমন সুর, এমন ছন্দ, এমন মহাজীবন, এমন সরল নরম হাতের আলপনা দেখে সহস্র বেলা গড়িয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। এসো গাঁ-জীবন, তোমাকে প্রণাম করি।
চিত্রণ: চিন্ময় মুখোপাধ্যায়