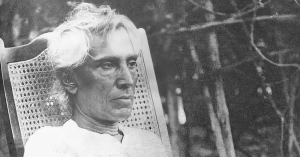সু ত প ন চ ট্টো পা ধ্যা য়
বৈবাহিক সূত্রে আমি বাংলাদেশের সম্পর্কে জামাই হলেও আমি বা আমার স্ত্রী কোনওদিন বাংলাদেশ যাইনি। আমার স্ত্রীর বাপ-ঠাকুরদার দেশ বরিশাল কিন্তু সে জন্মেছে দক্ষিণ কলকাতায়। আমার জন্মস্থান হুগলী জেলায়, আমাদের তিন কুলের কাউকে দেশ ছাড়তে হয়নি। তাই আমার সঙ্গে বাংলাদেশের সেই অর্থে সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। আমার স্ত্রী শিশুকালে তার দাদুর কাছে বরিশালের গল্প শুনে বড় হয়েছে। তার মাথার মধ্যে বাংলাদেশের বরিশালের নদনদীবহুল ভূখণ্ডের এক সুচিত্রিত ছবি আঁকা আছে, তা টের পেতাম বিয়ের পর থেকে। যতবার নানান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা উঠেছে, সে অনুরোধ করেছে, ‘একবার বাংলাদেশে নিয়ে যাবে? আমি বরিশাল যেতে চাই। আমাদের জমিদারির অংশ ছিল, দাদু বলেছে। বরিশালের বাজার ছিল আমাদের। লোকে খাজনা দিত। এমনই নানান গল্প।’
আমি এপারে জন্মেছি। জ্ঞান ইস্তক পড়েছি ওপারের বহু কৃতি মানুষের কথা। সে গানে, সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায় ও প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল মাধ্যমে। মনের ভিতরে এক প্রবল আগ্রহ জেগে ছিল, কী আছে ওই ভূখণ্ডে যে, এত গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে? সুযোগ পেলে আমি ওই ভূখণ্ড নিজের চোখে দেখতে চাই। যেহেতু আমি অক্ষরশ্রমিক ও বাংলা ভাষার চর্চা করি সেই কারণে আগ্রহ আরও তীব্র ছিল। এত বিখ্যাত সাহিত্যিকের দেশ, না দেখলে বা ঘুরলে একটা বড় কাজ অপূর্ণ রয়ে যাবে। বিয়ের পর আমার স্ত্রীর ইচ্ছেটি যুক্ত হয়ে ভ্রমণের ইচ্ছেটি ফণা তুলে রইল।
অনিন্দিতা, আমার স্ত্রী কোভিড লকডাউনে ঘরে বসে বসে প্রায় আন্তর্জাতিক নাগরিক। বাচিক-শিল্পের দৌলতে সে অনলাইন কানাডা, আমেরিকা, ইউকে, বাংলাদেশ, ফ্রান্স এইসব দেশের বাঙালি সংগঠন আয়োজিত নানা অনুস্ঠানে অংশগ্রহণ করে বাচিকশিল্পী হিসেবে কিছু খ্যাতি পেয়েছে। বাংলাদেশেও তার গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম নয়। আমার দু-একজন পরিচিত আছেন কিন্তু কাউকেই সরাসরি চিনি না। একটি দেশে যাব, সাক্ষাৎ পরিচিতি না থাকলে নিজেকে পর্যটক মনে হয়। পর্যটকের চোখে দেশ দেখা আর দেশকে অন্যভাবে দেখা, সেখানের মানুষজনকে জানা, শিল্পসংস্কৃতি জানা অন্য বিষয়। এর মধ্যে একদিন আমার বন্ধু-লেখক গৌতম দে আমাকে একটি ই-মেল পাঠিয়ে বলল, কোভিড নিয়ে আমার একটা গল্প বাংলাদেশে পাঠাতে। লেখা তৈরি ছিল। একদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম। এই আমার লেখা বিদেশের পত্রিকায় প্রথম পাঠানো।
বিদেশ? হ্যাঁ, বিদেশই তো, আমরা যতই এক ভাষা, এক খাদ্য, এক জীবনযাত্রা, এক সংস্কৃতি, এক রবীন্দ্রনাথ, এক নজরুল বলি। কাঁটাতারের বেড়া তো পড়ে আছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। কেউ তো তুলতে পারেনি? তা আর উঠবেও না। তাই মনে ভাবি, চিনি না, জানি না, ছাপবে তো লেখাটা? কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন একটি খবর এল আমার ফোনে। ‘‘আপনার বাড়ির ঠিকানাটা পাঠান। আমি নাহিদা আশরাফী। ‘রুদ্ধদিনের গল্প সংকলন’-টি আপনাকে পৌঁছে দিতে চাই।’’ সঙ্গে রুদ্ধদিনের একশোটি গল্পের সংকলন করার কারণ ব্যাখ্যা করে একটি ছোট্ট প্রতিবেদন। আমি হতবাক। কোভিড-কালের দুই বাংলার একশো লেখকের গল্প নিয়ে একটি বিশাল সংকলনের সম্পাদিকা নাহিদার মেসেজ পেয়ে ঠিকানা পাঠালাম। মাথার মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন বার বার ঘুরে আসছিল। কেন নাহিদা এই সংকলন করার কথা ভাবল? ভাবলই যদি তো ওপারের লেখকদের নিয়েই করতে পারত। দুই পারের লেখকদের নিয়ে কেন? ওপারের লেখকদের নিয়ে করলে তাকে এপারের লেখকদের কাছে পৌঁছে দেবার কোনও দায় থাকত না।
প্রতিবেদনটি পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরই লিখেছে নাহিদা। আমি তার মতো এইভাবে কাউকে লিখতে বা ভাবতে দেখিনি। একথা আর অজানা নয় যে, আমাদের জীবৎকালে কোভিডের মতো মহামারী, সারা পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুমিছিল, অগণিত শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষের প্রাণহানি মানবসভ্যতা কোনওদিন দেখেনি। দুবছর ধরে জীবনবলির কষ্ট-যন্ত্রণা, বাংলা ভাগ, জার্মানি ভাগ, কোরিয়া ভাগের চেয়ে অনেক বড় মানবিক বিপর্যয়। সেই ধরিত্রীর যন্ত্রণাকে ভাষার অক্ষরে চিরকালীন ধরে রাখার, এই ইতিহাসকে রক্ষা করার অগ্রণী ভূমিকা নাহিদা নিয়েছে। এই একটি কাজ মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখবে।
‘আপনার বাড়ির ডিরেকশনটা? সল্টলেকে থেকে কতক্ষণ লাগবে?’
ডিরেকশন বলে জানালাম, ‘প্রায় দু’ঘণ্টা।’
‘নো প্রবলেম। আমি আসছি।’ বলে ফোনটি কেটে দিল নাহিদা।
সন্ধের মুখে নীল জিন্স আর উপরে সাদা টপ পরে একটি মেয়ে এসে হাজির হল আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, ‘আমি যদিও ঢাকায় থাকি, অরিজিনাল বরিশালের মেয়ে।’
‘বরিশাল?’ বাড়ির মধ্যে যেন বোমা পড়ল! ‘তাই নাকি? আমারও তো বাবার দেশ বরিশাল।’ বলে উল্লাসে ফেটে পড়ল অনিন্দিতা।
আমার মনে হল, বাড়ি থেকে না বেরতেই বাংলাদেশ ভ্রমণ শুরু। কথাটা মিথ্যে নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে নাহিদাকে মনে হল, সে আমাদের দীর্ঘ দিন চেনে। অনিন্দিতাকে মনে হচ্ছে, সে বরিশালের মানচিত্র বুকে নিয়ে হেঁটে চলেছে নাহিদার পাশাপাশি বরিশালের জমির আলে আলে, ভেসে চলেছে কীর্তনখোলা নদী ধরে আরিয়াল খান নদীর দিকে। নৌকায়। অনেক গল্প হল, নাহিদা তার কত ব্যক্তিগত গল্প করল অবলীলায়। কোথায় যেন দেশের মাটির সুঘ্রাণ রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে। এ দেশের যোগ না থাকলে সম্ভব নয়। আর বার বার মনে হচ্ছিল, আমরা তো এপারের মানুষ, এত তাড়াতাড়ি অকপট হতে শিখিনি। হইও না। নাহিদা যখন ব্যাগ থেকে প্রায় দু’কিলো ওজনের সংকলনটি বের করে টেবিলের উপর রাখল, বিস্ময়ে বললাম, ‘তুমি এই বই ঘাড়ে করে বয়ে এনেছ বাংলাদেশ থেকে!’
আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে নাহিদা বলল, ‘সাহিত্যের ভার সবাই মনে আর মাথায় বয়, আমি না হয় একটু ঘাড়ে বহন করলাম, দাদা?’
সেদিন এই জেদী, স্পষ্টবাদী, নিরহংকারী ও পরিশ্রমী নাহিদাকে কুর্নিশ করেছিলাম এই ভেবে যে, নাহিদা তো শুধু ‘জলধি প্রকাশনা’-র প্রধান নয়, সে একাধারে কবি, গল্পকার ও পত্রিকার সম্পাদক। নাহিদা যে শুধু এই অমূল্য ও রুচিশীল সংকলনের জন্য প্রশংসা দাবি করে তাই না, তার এই মহৎ কাজ বাংলা সাহিত্যের একটি কঠিন কালের ইতিহাস।
আমাদের বাড়িতে যে বাংলাদেশ এসে ঢুকে গেছিল, সেই বাংলাদেশের গল্প অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই দিনের মতো শেষ করতে হল। কেন না নাহিদাকে ফিরতে হবে সল্টলেক। নাহিদার ভিতর দিয়ে আমরা বাংলাদেশের অন্তর ও বাহির দেখতে পেলাম। প্রায় তিন ঘণ্টার কথোপকথনে। যাবার আগে নাহিদা বলল, ‘এসো দাদা। ঢাকায় আমি আছি। কোনও প্রবলেম হলে আমি রইলাম। এই ভেবেই একদিন বেড়িয়ে পড়ো।’
বললাম, ‘আমি একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান দেখিনি। খুব দেখার ইচ্ছে ‘
‘চলে এসো দাদা। তবে মনে রেখো, রাতে যদি দেখতে যেতে চাও তো সন্ধে থেকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। পারবে তো?’
আমাদের এখানে আপাতত এমন কোনও অনুষ্ঠান নেই, যেখানে সন্ধে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে মধ্যরাতে পুষ্প অর্পণ করার নজির আছে। বললাম, ‘এত বড় লাইন দিতে পারব না।’
নাহিদা বলল, ‘তাহলে পরের দিন দুপুরে যেয়ো।’
‘দুপুর?’
নাহিদা বলল, ‘হ্যাঁ, দুপুর। একুশের রাত বারোটা এক মিনিট থেকে পরের দিন বিকেল ছ’টাতেও শেষ হয় না। এসে এবার দেখে যাও। দেখার জিনিস।’
আমি অনিন্দিতার দিকে তাকাতেই নাহিদা বলল, ‘তারপর না হয় বরিশাল ঘুরে এসো। আমি ফ্রি থাকলে আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।’
অনিন্দিতা বলল, ‘তাহলে তো খুব ভাল হয়।’
সেই আমাদের বাংলাদেশ যাওয়ার বীজবপন। সেটা নভেম্বর মাস।
||২||
মাসখানেক পরে একদিন অনিন্দিতা বলল, ‘কাল আমাদের বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে দুজন আসবে। খাবে।’
আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, ‘এবার কে?’
‘রাজিয়া পিঙ্কি ও তার বন্ধু। কলকাতায় এসেছে। আমি তার সঙ্গে অনলাইনে প্রোগ্রাম করেছি। ফোন করেছে। বলেছে, আমাদের বাড়ি আসবে।’
‘তা আমাকে কী আনতে হবে?’
‘দু’রকমের মাছ নিয়ে এসো।’ বলে সে ঘরে চলে গেল।
দুদিন পর রাজিয়া ও তার বন্ধু ড. নাঈমা খানুম আমাদের বাড়িতে এল। রাজিয়া আবৃতিকার, টেলিভিশন অ্যাঙ্কর ও সভাসঞ্চালক। আর নাঈমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক। একজন তারুণ্যে টগবগ করছে আর একজন শান্ত, স্বল্পভাষী, কোমলকণ্ঠী মানুষ। কথার মাঝেমাঝে আমাদের নিবিড় চোখে দেখছে আর আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আমাদের বাড়ির টেরাকোটা টালির ব্যবহার, দেওয়াল চিত্রণ, সাবেকী আসবাব। একসময় বলেই বসল, ‘আপনারা ঠিক আধুনিক মানুষের মতো নন; প্রাচীন ইতিহাস, আভিজাত্য, দেশজ শিল্পকলা ধরে রাখতে চান। কি ঠিক বলেছি, দাদা?’
তার এই অকপট কথা আমি আশা করিনি। বললাম, ‘তোমার সব দেখে যদি তাই মনে হয়, তো তাই ঠিক।’
রাজিয়া বলল, ‘ঠিক বলেছ। দেখো টেরাকোটা দিয়ে বাড়ি সাজানো সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেক দিন পর টেরাকোটার দশবতার দেখলাম।’
নাঈমা বলল, ‘এখানে কোথায় টেরাকোটার টালি পাওয়া যায় দিদি? আমি পারলে নিয়ে যাব।’
রাজিয়া এবার নাঈমার আরও কাজের পরিচয় দিল। সে কবি, সমাজসেবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংগঠনের সহ-সভাপতি। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে নানান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে।
আবার সেই একই পরিবেশ। ছোট্ট বাংলাদেশ। অনিন্দিতা নানা রান্না করে প্রায় ওদের অবাক করে দিয়েছে। খেতে খেতে আমি বললাম, ‘আমরা ঢাকা যাইনি কোনওদিন। বাংলাদেশ দেখিনি। খুব দেখার ইছে আছে।’
নাঈমা বলল, ‘চলে আসুন দাদা। আমি আমাদের গেস্টহাউসে ব্যবস্থা করে দেব। আমাদের কাছেই থাকবেন। খুব ভাল লাগবে।’ রাজিয়া বলল, ‘হ্যাঁ দাদা, বইমেলার সময় আসুন। আমাদের বইমেলা খুব বড়। সারা পৃথিবী থেকে বাংলাদেশিরা চলে আসে ঢাকায়। থাকার জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। নাঈমা আপু যদি করে দেয়, তো জবাব নেই।’
নাঈমা বলল, ‘করে দেব।’
রাজিয়া বলল, ‘আমার দুটো বই বেরবে দাদা, নাঈমা আপুরও বই বেরবে বইমেলায়।’
‘কী বই?’
দুজনেই একবাক্যে বলল, ‘কবিতার।’
‘তোমরা দু’জনেই কবি, বলোনি তো? তাহলে আমি ছোট্ট করে জানাই, আমিও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত, ছ’টা বই আছে আমার।’
নাঈমা বলল, ‘আপনার একটা বই চাই।’ কী সুন্দর যোগাযোগ, আলাপচারিতা, সম্পর্ক লেখালেখি নিয়ে। অনিন্দিতার সঙ্গে ওরা গল্পে মেতে উঠেছে, তার মধ্যেই রাজিয়া বলল, ‘‘দিদি, তুমি কি ‘দিদি নম্বর ১’ হয়েছ? ফলক দেখছি যে টেবিলে?’’
অনিন্দিতা বলল, ‘হ্যাঁ। বছর-তিনেক আগে।’
রাজিয়া বলল, ‘আমিও পার্টিসিপেট করতে চাই। তুমি হেল্প করো।’
অনিন্দিতা মন দিয়ে রাজিয়াকে এই অনুষ্ঠানের নিয়মাবলি বোঝাতে লাগল। আমি আর নাঈমা গল্প করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেক বিখ্যাত মনীষী একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন বা যুক্ত ছিলেন। তখন কলকাতা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই ভূখণ্ডের দুটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান। নাঈমা বলল, ‘জানেন দাদা, আমার আব্বা ঢাকা ইউনিভারসিটিতে পড়াতেন। আমি ওই চত্বরে বড় হয়েছি। আবার এখন চাকরি সূত্রে এই ক্যাম্পাসেই ঘোরাফেরা। বাড়ি ধানমন্ডিতে।’
সেদিন সন্ধ্যায় রাজিয়া ও নাঈমার সঙ্গে দারুণ গল্প করে কাটালাম। গল্পের মাঝেমাঝেই আমাদের বাংলাদেশ যাবার প্রসঙ্গ শুশুকের মতো ভেসে ভেসে উঠছিল। অনিন্দিতা বলল, ‘আমি নতুন ঢাকার চেয়ে পুরনো ঢাকা দেখতে চাই। সেই বিখ্যাত রিকশা আছে এখন?’
রাজিয়া বলল, ‘সব দেখাব। রিকশাই তো ঢাকার প্রাণ।’
এই শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে রিকশা যে কোনও শহরের প্রাণ হতে পারে, এ কথা কল্পনার অতীত। তবে কি ঢাকা খুব ধীর, স্লথ, প্রাণহীন শহর? না। বাংলাদেশের নানান ক্ষেত্রে যে উন্নতির ঘনঘটা, তাতে কোনও দেশ বা তার রাজধানী পিছিয়ে পড়তে পারে না। আজকের বিশ্বে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে এগিয়ে আছে, ব্যবসার নিরিখে, শিক্ষার নিরিখে, গবেষণার কাজে। অর্থনৈতিক যে মডেল ব্যবহার করে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে, সেটাও খুব সহজলভ্য নয়। বাংলাদেশ তা হাতেনাতে করে পৃথিবীকে দেখিয়েছে। রাজিয়া ও নাঈমাকে বলে দিলাম, ‘আমাদের এক বন্ধু আছে তোমাদের দেশে। নাহিদা।’ ওরা দুজনেই বলল, ‘অহ, নাহিদা আপা?’
‘তোমরা চেনো নাকি?’
‘চিনব না। খুব ভাল করে চিনি।’ নাঈমা বলল।
‘বাঃ তাহলে তো ভালই হল।’
আমার যুগল উপন্যাস দিলাম দুজনকে।
বাংলাদেশ যাবার আগেই সেই দেশের কবি, সম্পাদক, সঞ্চালকদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল নিজগৃহে, এর চেয়ে মনোমুগ্ধকর আর কী হতে পারে?
||৩||
একদিন সল্টলেক সেক্টর ফাইভে বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে ভিসার জন্য ফর্ম জমা করে দিয়ে এলাম দুজনে। এমনই সুব্যবস্থা যে নিরক্ষর ব্যক্তিটিও ভিসার জন্য আবেদন করতে পারে এবং সব ব্যবস্থা আছে। ফোন নম্বর থেকে আধার কার্ডের কপি বের করার সুবিধা আছে, আছে সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলার ব্যবস্থা। জমা দেবার সময় ছেলেটি জালঘেরা চেম্বারের ভিতর থেকে বললেন, ‘পনেরোটি ওয়ার্কিং ডে-র পরে পাসপোর্ট নিতে আসবেন। মেসেজ চলে যাবে আপনার মোবাইলে।’
অনিন্দিতা বলল, ‘দশ দিনে করা যাবে না? আমরা স্পেশাল চার্জ দিতে রাজি আছি।’
ছেলেটি হেসে বললেন, ‘না, ম্যাডাম। এমন কোনও চার্জ নেই। তবে উপর লেবেলে কেউ চেনা থাকলে অনেক সময় আগেও হয়। মানে সোর্স। আচ্ছা বলুন, এসে নিয়ে যাবেন, না আমরা কুরিয়ারে পাঠাব? কুরিয়ারের চার্জ লাগবে। সুবিধা এই যে, যেদিন ভিসা ইস্যু হবে তার পর দিন বাড়িতে বসে পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন। এখানে আসতে হবে না। আপনারা কোথায় থাকেন?’
‘বেহালায়।’
‘ও হো, অনেক দূরে। দেখুন কী করবেন। আমি সেইমতো ফাইল ছেড়ে দেব।’
বললাম, ‘কুরিয়ারে পাঠান।’
ছেলেটি ভিসা ফি ও চার্জ লিখে আমাকে ইনভয়েসটি ধরিয়ে দিলেন হাতে। তাহলে বাংলাদেশ যাত্রার প্রথম ধাপ শেষ হল!
যথা সময়ে ভিসা সমেত পাসপোর্ট হাতে এল। ভিসার দিকে তাকিয়ে দেখি, একবছরের মাল্টিপল ভিসা দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার বাহাদুর। তার মানে, একবছরের মধ্যে যত বার খুশি আমরা বাংলাদেশ যেতে পারি। ঘুরতে পারি। কেউ আমাদের আটকাবেন না। এর চেয়ে খুশির অভ্যর্থনা কোন দেশ করতে পারে? মনে মনে বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে অনিন্দিতাকে বলতেই সে বলল, ‘তাহলে এক একবার প্ল্যান করব। একবার বরিশাল, পরের বার চট্টগ্রাম, তার পরের বার ময়মনসিং, রংপুর, খুলনা। এমনি করে ঘুরে বেড়াব।’
বললাম, ‘সেটা করাই যায়।’
এবার টিকিট। ভিসার আগে তো টিকিট কেউ দেবে না। বাসে, ট্রেনে কিংবা বিমানে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে বিমানে বাংলাদেশ যাব না। কেউ বিমানের টিকিট দিলে অন্য কথা। তার একটি কারণ, আমি সারা জীবনে এত লম্বা লম্বা বিমানযাত্রা করেছি, এই আধঘণ্টার বিমানযাত্রার কোনও মানে হয় না। বিমানে ওঠার আগে ও পরে যে অপেক্ষা, কাস্টমস, সিক্যুরিটি— আধঘণ্টার বিমানযাত্রার পক্ষে খুবই বিরক্তিজনক। তার চেয়ে মৈত্রী এক্সপ্রেস ধরে যাব। সকালে উঠব কলকাতা স্টেশন থেকে, বিকেল চারটেয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নামিয়ে দেবে। সারাদিন ট্রেনের জানালা দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদনদী, বনাঞ্চল দেখতে দেখতে যাব। দুচোখভরে দেখব এই শ্যামলিমা। অনিন্দিতা এককথায় রাজি হয়ে গেল। আমরা টিকিট কাটার জন্য শ্যামবাজারের কাছে, আর জি কর হাসপাতালের উল্টো দিকে ‘কলকাতা’ স্টেশনে টিকিটের জন্য ফর্ম ফিলাপ করলাম। কাউন্টারের লোকটি ভিসা দেখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ‘প্রথম বার?’
বললাম, ‘হ্যাঁ। আগে যাইনি।’
ভেবেছিলাম এই প্রশ্নটি টিকিট দেবার প্রসঙ্গে একটি জরুরি জিজ্ঞাসা। পরে বুঝেছি সে ধারণা ভিত্তিহীন।
টিকিটদুটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘বেড়াতে যাচ্ছেন?’
আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’
‘কোথায় যাবেন?’
‘বরিশাল।’
‘আমাদেরও দেশ বরিশাল। কতবার ইচ্ছে করছে দেশটা একবার দেখে আসি। আজও হল না।’
আমার চোখটা ভদ্রলোকের চকচকে টাকে গিয়ে পড়েছে। জিজ্ঞেস করি, ‘এত বয়স অবধি যাননি কেন?’
‘কোথায় যাব? কেউ তো নেই ওপারে। আর এপারে যাঁরা এসেছিল আমাদের নিয়ে, তাঁরাও তো চলে গেছে উপরে। থাকলে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, তারও উপায় নেই। এখন কি চিনতে পারব আমার দাদু, বাবু, মার কাছে শোনা আমাদের পুণ্য পিতৃভূমি?’
খালি ছিল। এর মধ্যে একজন এসে ফর্ম জমা দিতেই তিনি আমাকে বিদায় করে তার ফর্মটি নিয়ে নিলেন। টিকিট কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমার মনে হল, সত্যি তো, অনিন্দিতার পূর্বপুরুষদের কেউ তো বেঁচে নেই? যাঁরা একসময় বরিশালকে নিজের দেশ মনে করতেন, তাঁরা তো দু-একবার ঘুরে এসেছিলেন দেশভাগের আগে। তাহলে অনিন্দিতাকে কে চিনিয়ে দেবে তাদের পৈতৃক বাসস্থা্ন? তাদের ঘরবাড়ি কি আজও আছে? যে দেশের টানে সে বরিশাল যেতে চায়, সেই ছবি যদি না মেলে? তাহলে তো আশাভঙ্গ হবে? তাহলে বাংলাদেশ যাবার উদ্দেশ্যই বৃথা। এতদিনে হয়তো তাদের গ্রাম স্বরূপকাঠীর ভূগোল বদলে গেছে। মহকুমা বদলে গেছে, নতুন জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের বাড়ি যারা দখল নিয়েছিল তারা বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছে। আর তখনই মনে পড়ল নাহিদা, রাজিয়া, নাঈমাদের মুখ। তাদের আন্তরিকতা, সাবলীল মেলামেশা, প্রাণের টান। কী দিয়ে অনিন্দিতা তাহলে মানুষদের সঙ্গে যোগসূত্র টানবে? ভাষা। তার সাবলীল বরিশালের ভাষা তাকে চিনিয়ে দেবে তার জন্মসূত্র। শুধু মানুষের জন্যই তাহলে বাংলাদেশ যাওয়ার তাৎপর্য। এখনও ফুরোয়নি। ফুরাবে না কোনওদিন। কিন্তু ভাষা থেকে গেছে। ভাষার মৃত্যু হয় না যে!
||৪||
ইমিগ্রেশনের সামনে এসে দুজনে দুটি লাইনে ভাগ হয়ে গেছি। সময় বাঁচানোর একমাত্র পন্থা হিসেবে। আমি যে লাইন দিয়েছি সেখানে চারজন আগে। আনিন্দিতা যে লাইনে তার সামনে একজন। একটু পরেই অনিন্দিতার গলা কানে এল। ইমিগ্রেশন অফিসার তাকে প্রশ্ন করছেন, ‘কোথায় উঠবেন? হোটেলে?’
অনিন্দিতা বলছে, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে।’
‘কেন যাচ্ছেন?’
‘বেড়াতে।’
‘একা?’
‘না, হাসবেন্ড আছে।’
‘আপনার হাসবেন্ড কী করেন?
‘রিটায়ার করেছেন।’
‘পেনশন পান?’
‘না।’
‘কী চাকরি করতেন?’
অনিন্দিতা আমাকে দেখিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, ‘আমি জানি, উনি একটি বিজনেস চেম্বারের চাকরি করতেন। বাকি ওকে প্রশ্ন করুন।’ বলে আমাকে দেখিয়ে দিল। ইমিগ্রেশন অফিসারটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা নিচু করতেই অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি যে প্রশ্নগুলো করলেন, সেগুলো কি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন?’
লোকটি বললেন, ‘হ্যাঁ।’
অনিন্দিতা এবার বলল, ‘আমি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি, এমন প্রশ্ন কেউ কোনও দিন করেনি।’ বলে পাসপোর্টটি নিতে নিতে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’
গজগজ করতে করতে অনিন্দিতা হাঁটছে। ‘লোকটি কেন বলো তো ওইসব উদ্ভট প্রশ্ন করছিল? কি স্টুপিড না?’
বললাম, ‘তুমি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে আসবে। ওদের তো কিছু করতে হবে। শুধু স্ট্যাম্প আর দিনে কত বার দেবে? ঠিক না হয় বেঠিক প্রশ্ন করবে। আজ তোমার পালা পড়েছিল। তুমি শুনলে। অন্য কেউও হতে পারত।’
ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। টিকিট অনুযায়ী চেয়ারকারের মাঝামাঝি একটি সারিতে বসে পড়লাম। পাশের সিটে আমীর। তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ বেড়াতে এসেছিলেন। কলকাতায় ছিলেন সাত দিন। ঢাকায় সে রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করেন।
জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন লাগল কলকাতা? কোথায় গিয়েছেন?’
মেয়েটি খুব সপ্রতিভ। মুখ কালো বোরকায় ঢাকা, উজ্জ্বল দুটোচোখ চশমার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে। তিনি বললেন, ‘ভিক্টোরিয়া, জোড়াসাঁকো, জৈন মন্দির, প্লানেটোরিয়াম, বোটানিকাল গার্ডেন আর নতুন হুগলী সেতু। আর বাকি কেনাকাটা করেছি। সব ঠিক ছিল, কেনাকাটা করেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম।’
‘ঝামেলা?’ অনিন্দিতা জিজ্ঞাসা করে।
আমির বললেন, ‘আপনাদের সব ভাল, ইমিগ্রেশনের লোকজন খুব খারাপ। আসার সময় আমাদের যা টাকা বেঁচে ছিল, মানে ডলার, সব নিয়ে নিল।’
‘নিয়ে নিল মানে?’
‘‘হ্যাঁ, একটা ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বলল, এত জিনিস কিনেছেন কেন? পাঁচ হাজার টাকার বেশি কেনকাটা যায় না। জানেন না?’ আমি বলেছিলাম, ‘না, জানি না। এমন নিয়ম তো কেউ বলেনি?’’
লোকটি বলল, ‘আপনারা সব কেনাকাটার রসিদ দিন, না হলে যা টাকা আছে এখানে জমা দিতে হবে।’
মেয়েটি বললেন, ‘সব কেনার কি রসিদ থাকে বলুন?’
আমির বললেন, ‘আমার কাছে তিন হাজার ডলার ছিল, সব নিয়ে নিল।’
অনিন্দিতা বলল, ‘আপনি কমপ্লেন করেননি?’
আমির বললেন, ‘কেউ আমাদের কথা শুনল না। মনে হল একটা র্যাকেট। আমাদের খুব হ্যারাস হতে হয়েছে। এত খারাপ লাগছে কী বলব!’
অনিন্দিতা তখন আমাকে বলল, ‘তাহলে তো নাঈমা ঠিকই বলেছিল। আমাদের বাড়িতে গল্প করতে করতে বলেছিল, তার কাছ থেকেও একবার এমনি করে ডলার নিয়েছিল।’ এর পর অনিন্দিতার সাংবাদিক সত্তার উন্মেষ। ‘আমি ফিরেই এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখব।’
আমির বললেন, ‘আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না। ডলার নিয়ে তো আপনাদের দেশে খরচ করছি। তাতে তো আপনাদের লাভ। এটা কেউ বুঝল না। পরে বুঝেছি, পাঁচ হাজারের গল্পটা বানানো। টাকা নেবার অছিলা মাত্র।’
মেয়েটি বললেন, ‘উনি খুব শান্ত মানুষ। প্রতিবাদ করতে পারেন না। ঢাকা হলে আমি একবারে হুলুসস্থুলুস করে দিতাম।’
ট্রেন ছেড়ে দিল। দমদম, শ্যামনগর, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়ার মতো জনবহুল স্টেশন পেরিয়ে গেলে জনপদ ক্রমাগত ক্ষীণ হতে লাগল। চোখের ভিতর দিয়ে উলটো দিকে ছুটে যেতে লাগল সবুজ প্রকৃতি, গাছপালা, ধানের খেত আর ধূ ধূ মাঠ। সকালের রোদে মাঠে মাঠে কৃষকদের মুখ। ছোট ছোট জনপদ। মাটির বাড়ি। এই ট্রেন থামবে দর্শনায়। তাই এর গতি সতত দ্রুতগামী। হঠাৎ আস্তে হল গতি। মনে হল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঢুকছি। তাই এই সতর্কতা। না তেমন কিছু নেই। আমির বললেন, ‘এটা ইচ্ছে করে করে যাতে মানুষ বুঝতে পারে ট্রেনটি বাংলাদেশে ঢুকছে।’ কিছুক্ষণ পরেই আবার সমান গতি প্রাপ্ত হল। একসময় ট্রেনটি এসে থামল দর্শনায়।
এই নামটি বড় মিষ্টি। আমাদের দেশদর্শনের প্রবেশমুখের নাম দর্শনা, ভাবতেই উৎফুল্ল হই। কে যে এই নাম রেখেছিল? এমনিতে গ্রামের নামের শেষে পুর, গ্রাম— এমনই সব স্টেশনের নাম হয়। দর্শনা এই কাব্যিক নামটি রাখার জন্য এই নামকরণের মানুষটিকে মনে মনে অভিনন্দন না দিয়ে উপায় রইল না। অনিন্দিত বলল, ‘এখানেই ইঞ্জিন, রেলের স্টাফ পরিবর্তন হবে। এবার আমাদের রক্ষা করবে বাংলাদেশের রেলপুলিশ। এখানে বাংলাদেশি টাকা চলবে। কিছু পকেটে বের করে রাখো। ইচ্ছে হলে কিছু কিনতে পারবে।’ ঠিক সেই সময় আমার পিছনের যাত্রীটি রেলের ক্যান্টিনের ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, ‘কী খাবার পাওয়া যাবে?’
ছেলেটি বললেন, ‘মোরগ বিরিয়ানি।’ আমার কানে বাংলাদেশে এই প্রথম একটি নতুন শব্দ সজোরে ধাক্কা মারল। আমরা আজীবন শুনে এসেছি বা বলে এসেছি, চিকেন বিরিয়ানি। রেস্তোরাঁয় খাবার অর্ডার দেবার সময় চিকেন কিংবা মাটন বিরিয়ানি বলতে অভ্যস্ত। কোনও দিন ‘মোরগ বিরিয়ানি’ বলিনি। তবে কি আমরা এমন একটি দেশে ঢুকছি, যেখানে প্রতিটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দে কথা বলতে হবে? আমরা তো যথেচ্ছ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। একটি টিভি চ্যানেলের দৌলতে এই সঙ্গে বাংলা ও ইংরাজি শব্দের ককটেল করে বাক্য বলি। রাস্তাঘাটে কলকাতায় হিন্দিতেও কথা শোনা যায়। কখনও অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে আহ্লাদ করে দু-চারটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিই, আমি আসলে বাঙালি। ইংরেজিটা বলতে পারি, তাই আমি একটু উচ্চমার্গের। এখানে সব ইংরেজির বাংলা প্রতিশব্দ বলতে পারব তো?
আমাদের পিছনে দুই হিন্দিভাষী মানুষ হিন্দিতে কথা বলছিলেন এবং তাদের একজন বাংলাদেশের একজন মানুষের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলায় আলোচনা করছিলেন, বাংলাদেশের আলুর দাম ওঠানামার গল্প। অনিন্দিতা ঘুমিয়ে ট্রেনের দোলায়। হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। ট্রেনটি বিশাল জলমণ্ডলের উপর দিয়ে আসতে চলতে আরম্ভ করেছে। আমির বললেন, ‘সাড়ে সাত কিলোমিটারের ব্রিজ। পদ্মার উপর। দেখতে থাকুন।’ অনিন্দিতা আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে এই প্রথম তার পিতৃভূমির সুবৃহৎ নদীটির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। এই জলরাশি, এই বিস্তার, এই পদ্মার কথা অনেক লেখায় পড়েছি, গানে শুনেছি, চোখে দেখিনি। মনে হচ্ছিল এ এক অন্য দেশ, আমার ছোটবেলার হাজার কেদারমতি নদী মেলালেও এই জলরাশি সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এটা নদী নয়। জলদৈত্য। এক কূল থেকে অন্য কূল চোখে পড়ে না। আমরা জল আর আকাশের মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে ভেসে চলেছি। একসময় মনে হচ্ছে ভেসে যাচ্ছি কোন অজানার উদ্দেশে। একসময় ট্রেনটি মাটির কাছাকাছি পৌঁছলে দূরে তিনটি চিমনি চোখে পড়ল। জল থেকে স্থলের ওপর এসে গেলে চোখে পড়ল বিশাল জনপদ। বিশাল বিশাল তিনটি সাইলো। আমির বললেন, ‘দেখেন এখানে অ্যাটোমিক পাওয়ার তৈরি হচ্ছে। রাশিয়ার সহযোগিতায়। ওই যে কলোনি দেখছেন, ওখানে রাশিয়ানরা থাকে। ওরা তৈরি করে বাংলাদেশের হাতে দিয়ে যাবে। বিরাট কর্মযজ্ঞ।’ আমি এই অ্যাটোমিক পাওয়ার স্টেশন দেখেছি চেন্নাইয়ের কাছে। চিনতে অসুবিধা হয়নি। আমরা বাংলাদেশকে যতই ছোট্ট দেশ ভাবি না কেন, তলে তলে বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না তারা পদ্মার উপর যে গাড়িচলার ব্রিজটি সম্প্রতি তৈরি করেছে বিনা বিদেশি সাহায্যে, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশ, জনসংখ্যা প্রতুল দেশ, কৃষিবহুল দেশ কীভাবে এতবড় একটি ব্রিজ বানানোর অর্থ যোগাড় করেছে নিজের চেষ্টায়, তা না দেখলে কল্পনা করা যেত না। এই একটি সেতুই বাংলাদেশকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে, একথা প্রায় সকলের কাছে জানা। আমিরের স্ত্রী বললেন, ‘জানেন দাদা, আপনাদের কলকাতায় আমার কী ভাল লেগেছে?’
‘কী?’
‘ভিক্টোরিয়া আর হুগলী সেতু।’
‘কেন?’
‘দুই অভিনব আর্কিটেক্ট। পুরাতন ও নতুন। ভিক্টোরিয়া দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।’
আমির বললেন, ‘ও তো আসতেই চাইছিল না। আসলে ও তো পেশায় আর্কিটেক্ট।’
অনিন্দিতা বলল, ‘তাই নাকি? তাহলে তো আপনার ভালই হয়েছে। আপনার বিজনেসে খুব হেল্প করতে পারে।’
‘করে তো। আমার সব প্রোজেক্টে ওর আর্কিটেকচার।’
অনিন্দিতা এবার সরাসরি প্রশ্ন করল, ‘আপনি এত শিক্ষিত, আপনি এখনও বোরকা পরেন কেন? ভাল লাগে?’
মেয়েটি মুখ থেকে কালো কাপড়টি সরিয়ে দিতে আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমিরের স্ত্রী অপরূপ সুন্দরী। টানা টানা চোখ, ধনুক ভুরু, টুকটুকে লিপ্সটিকে আঁকা দুটো সরু ঠোঁট।
অনিন্দিতা আবার বলল, ‘আপনাকে এত সুন্দর দেখতে, আপনি মুখটাই ঢেকে রাখেন?’
আমির বললেন, ‘আমি কিন্তু কোনওদিন বোরকা পরতে বলিনি। নিজেই পরে।’
এবার হাল্কা হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, ‘আমার কাছে এই পোশাকটি খুব স্বাস্থ্যসম্মত। এই পোশাকের মধ্যে একটি অসীম মহত্ব লুকিয়ে আছে। আমি কিছু দেখতে চাইলে দেখব, না হলে চোখ বন্ধ করে রাখব। কিন্তু অন্য কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। এর চেয়ে নিরাপদ পোশাক আর কী হতে পারে?’
বললাম, ‘এটা খুব সত্যি।’
তিনি বললেন, ‘আরও অনেক সুবিধা। সারা শরীরে ধুলোবালি পড়ে না, মাথায় বায়ুমণ্ডলের নোংরা পড়ে না, চুল খুব ভাল থাকে। আমার চুল দেখলে অবাক হবেন। মাথা থেকে পায়ের গোছা অব্দি লম্বা। বাঁধতে গিয়ে দম বেরিয়ে যায়।’
অনিন্দিতা বলল, ‘তাই নাকি? আপনার মতো চুল থাকলে তো লোককে দেখানোর জন্য পাগল হয় মেয়েরা। আপনার বাড়িতে বোরকা পরার চল আছে?’
‘না। আমার মা মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন, ভীষণ তেজী মহিলা। কোনও দিন বোরকা পরেননি। আমি বোরকা পরি শরীরের নিরাপত্তার কারণে।’
‘পড়াশোনা?’
‘ইংল্যান্ডে। ওদের দেশ ঠান্ডার দেশ, ধুলোবালি নেই, ওখানে না পরলে খুব একটা ক্ষতি নেই।’
আমার মনে পড়ল সারা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে পুরুষেরাও সাদা রঙের জোব্বা পরে, ভিন্ন প্রকরণে বানানো জোব্বা। এই পোশাক কি তাদের দেশের আবহাওয়াকে মনে রেখে পরিধান করে? মরুভূমির দেশ, ধুলোঝড়ের দেশ, বাতাসে শুষ্ক বালুকণার দেশ, প্রবল তাপের দেশ বলেই কি ছেলেরা সারা শরীর ঢাকা, গোড়ালিসমান জোব্বা পরে? আমীরশাহী, কাতার, কুয়েত, সৌদির জোব্বা দেখতে আলাদা কিন্তু কারণটি সম্ভবত একই।
||৫||
ট্রেনটি দুলকি চালে চলছে না। মাঠ-ময়দান, বন-বনাঞ্চল, জনবসতি দুপাশে রেখে সবুজ বাংলাদেশের রাজধানীর উদ্দেশে ছুটে যাচ্ছে। উল্টো দিকে যে মানুষটি বসে তার দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ‘আপনারা কলকাতা থেকে?’
বললাম, ‘হ্যাঁ। আপনি?’
‘বাঙ্গালোর।’
‘বাঙ্গালোর? এখানে কে থাকে?’
‘আমার ছেলে। একটা এমএনসি-তে চাকরি করে। বড় পজিশনে আছে। আপনারা?’
‘বেড়াতে। তা ছেলে থাকে কোথায়?’
‘গুলশান বলে একটা জায়গায়। আমি চিনি না। আসবে স্টেশনে নিতে। আলাপ করিয়ে দেব।’
‘আচ্ছা।’ বলে ভাবতে থাকি, এই দুই দেশের মধ্যে এত যাতায়াত, যোগাযোগ, তবে ওই তারের বেড়াটা কেন? দেখতে দেখতে ট্রেনটির গতি স্লথ হল। বাইরে তাকিয়ে দেখি ধীরে ধীরে পার হয়ে যাচ্ছে ‘গাজীপুর’ স্টেশন। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সদাহাস্যমুখ বাঙালি লেখক। একাধারে লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, নাট্যকার, সঙ্গীতকার, রসায়নের অধ্যাপক হুমায়ূন আহমেদ। বাংলা ভাষার সর্বকালের জনপ্রিয় লেখক শায়িত আছেন নুহাশ পল্লীতে, এই গাজীপুরে। সম্ভ্রমে মাথা নিচু হয়ে এল। বাংলাদেশ এতটাই ভাগ্যবান যে, তাঁর মতো একজন প্রতিভা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই শতাব্দীর শিল্প-সাহিত্যকে নানা দিকে থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরই তৈরি ও পছন্দের জমির নিচে চিরঘুমে শুয়ে আছেন সেই মহান মানুষটি। তাঁর মতো বাঙালির হৃদয় ও মন কে বুঝতে পেরেছে? এপারের শরৎচন্দ্র আর ওপারের হুমায়ূন আহমেদ, যাঁরা অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে দিয়েছেন ফেলে আসা সময়ের বাঙালির মন ও মনন। আবার সেই ভুল করে বসলাম। আবার এপার ও ওপার বলে ফেললাম। তার তো পড়ে আছে মাটিতে সীমান্ত বরাবর। মনের মধ্যে বেড়া কোথায়। তাই চলেছি এক ভাগ বাংলা থেকে অন্য এক ভাগ বাংলার দিকে।
এক সময় ট্রেনটির গতি বদলে গেল। কামরার লোকজন চঞ্চল হয়ে জিনিস নামাতে শুরু করল। কে একজন বলে উঠল, ‘ক্যান্ট এসে গেছে। আর পাঁচ মিনিট।’
আমি উঠে মাথার উপর থেকে স্যুটকেস নামাতে অনিন্দিতা বলল, ‘তাড়া কীসের? ফিরদৌস তো গাড়ি পাঠাবে বলেছে। গাড়ির নাম্বারও দিয়ে দিয়েছে। ধীরেসুস্থে নামব।’
বললাম, ‘সেটা ঠিক। তবে তৈরি থাকতে তো কোনও অসুবিধে নেই?’
‘না।’ বলে ব্যাগ খুলে, ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিল। ট্রেনটি থামল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। ঠিক চারটে তখন।
অনিন্দিতা বলল, ‘ফিরদৌস মেসেজ করেছে। ড্রাইভার স্টেশনে অপেক্ষা করছে। লাল রঙের গাড়ি।’ নিশ্চিন্ত হলাম। বেরিয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। ইমিগ্রেশনে যেটুকু সময়। প্রথমবার, একটু ঝামেলা হতেও পারে। ট্রেন থেকে নেমে দেখি বেশ লম্বা লাইন পড়েছে। যারা বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাদের আলাদা লাইন। সেখানেই বড় লাইন। অনেক লোক বেড়াতে এসেছে নাকি? কলকাতা স্টেশনে যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, তার বিন্দুমাত্র নেই এখানে। যেভাবে অতিথিকে বাড়িতে আপ্যায়ন করে মানুষ, আমাদের তেমনই হাসিমুখে যেন ডেকে নিল বাংলাদেশ। অনিন্দিতা বলল, ‘দেখো, বাংলাদেশের যে অতিথি আপ্যায়নের খ্যাতি বিশ্বজোড়া তার প্রমাণ এই প্রবেশ কালে। ভাবতে পারো, পৃথিবীর কোন দেশে এসেছ? তোমরা বাঙালদের এমনি গালমন্দ করো। বাঙালরা, খেতে ও খাওয়াতে যেমন পারে, কেউ পারে না। জীবনে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নটাই যে আসল, সেটা বোঝার চেষ্টা করো।’ বলে সে বেশ জোরে নিশ্বাস নিল। যেন সে ঢাকা না পৌঁছেই বরিশালের মাটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।
আমি বললাম, ‘ঠিক, প্রায় কিছুই জিজ্ঞেস করল না। শুধু কেন, আর কোন হোটেলে উঠছি, জিজ্ঞেস করেই বাংলাদেশে প্রবেশ।’ মহিদুল বেরনোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, একগাল হেসে বলল, ‘আমি আপনাদের দূর থেকে চিনতে পেরেছি।’
‘চিনতে পেরেছ? কী করে? তুমি তো আমাদের কোনওদিন দেখোনি?’
হাসল মহিদুল। বলল, ‘স্যার তো আমাকে নাম দিয়ে দিয়েছে। আমি আপনাদের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি দেখে নিয়েছি। চিনতে কোনও সমস্যা হয় নাই।’
অনিন্দিতা আমার দিকে তাকাল। আমি মনে মনে বললাম, কত এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। আর ঠিক তখনি মনে পড়ল, আরে, টেলিভিশন, কম্পিউটার ভারতের অনেক আগে প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশে। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ অনেক দিন আগেই শুরু হয়ে গেছে এখানে। খবরে দেখেছি, বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ছেয়ে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুনাম হয়েছে বিদেশে। এখন বাংলাদেশের নতুন স্লোগান, স্মার্ট বাংলাদেশ। এই স্মার্ট বাংলাদেশ বস্তুটি কী? সেটা একবার জানতে হবে ফিরদৌসের কাছে।
||৬||

কাঁকরাইল এলাকায় একটি হোটেল আমাদের জন্য বুক করা আছে। শুনেছি ঢাকায় খুব ট্রাফিক জ্যাম হয়। ফিরদৌস আমাদের কমপ্লেক্স-এ থাকত, কলকাতায়। বিয়ে করে বছরখানেকের মধ্যেই ঢাকায় চাকরি নিয়ে চলে এসেছে। সেও বছর পাঁচেক। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তার বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন অনেক দিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। আমি মহিদুলকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখান থেকে হোটেলের এলাকা কত দূর?’
মহিদুল স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বলল, ‘মিনিট পনেরোর পথ, এবার দেখুন কত ঘণ্টা লাগে। জায়গাটা আমি চিনি, আপনার চিন্তা নেই। ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। স্যার বলেছে, আপনাদের কমফর্টেবল দেখে তবে ফিরতে।’
অনিন্দিতা বলল, ‘দেখেছ, কী ভাল ছেলে ফিরদৌস?’
বলি, ‘হ্যাঁ। ব্রিলিয়ান্ট। তাই এই বয়সে ভাল চাকরি করছে। ওর মতো ছেলে কি বাংলাদেশে নেই? নিশ্চয় আছে, তবে ওর মতো হয়তো স্কিল সেটস নেই।’
অনিন্দিতা বলল, ‘মহিদুল, তোমার বাড়ি কোথায়?’
‘ফরিদপুর।’
‘কে কে আছে দেশে?’
‘দেশ তো আমাদের একটাই ম্যাডাম।’
অনিন্দিতা সংশোধন করে নিল নিজেকে। বলল, ‘সরি, আমি বলতে চেয়েছি তোমার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে?’
‘বাবা, মা আর এক বোন।’
‘জানো মহিদুল, আমিও এই দেশের মেয়ে। আমাদের বাড়ি বরিশাল। যাওয়া হয়নি কোনওদিন। এবার যাব।’
‘তাই নাকি? তাহলে তো আপনি আমাদের অতিথি নন। ঘরের মানুষ। বরিশাল খুব ভাল জায়গা। অনেক বিখ্যাত মানুষ জন্মেছেন। আমরা ইস্কুলে পড়েছি।’
‘কোন ক্লাস অবধি পড়েছ?’
‘মাট্রিকটা দিতে পারিনি। চাকরির সন্ধানে ঢাকায় চলে এসেছিলাম।’
ফরিদপুরের ছেলে মহিদুল নিজের পায়ে দাঁড়াতে অনেক যুদ্ধ করেছিল। চাকরি তো পায়নি, লোকের বাড়ি চাকরের কাজ করেছে অনেক দিন। ততদিনে সে বুঝেছিল, এই শহরে দুধরনের মানুষের বাস। ধনী আর গরিব। সে গাড়ি চালানো শিখে প্রথমেই আবেদন করেছিল বড় বড় কোম্পানিতে। একদিন তার কপালে লেগে গেল এই কোম্পানির চাকরি। ফিরদৌস জয়েন করার পর কোম্পানি তাকে ফিরদৌসের ড্রাইভারের কাজ দিয়েছে। সে একলপ্তে দুটো পাখি মেরে দিয়েছে। সে মাকে চিঠি লিখেছিল, ‘আমার দুই মালিক। এক এই লাল রঙের বিদেশি গাড়ি আর তার ফিরদৌস সাব। মানুষটি খুব ভাল। লোকের দুঃখ খুব বোঝে।’
অনিন্দিতা বলল, ‘ঠিক, ফিরদৌসের দুঃখটা কেউ বুঝল না।’
‘না ম্যাডাম। স্যার কিন্তু খুব হাসিখুশি।’
কোন উত্তর দিল না অনিন্দিতা। শুধু প্রশ্ন করল, ‘আর কত দূর মহিদুল?’
‘কোথায় যাব ম্যাডাম, প্রায় কুড়ি মিনিট জ্যামে আটকে আছি। একটুও আগাতে পারিনি।’ বাইরে তাকিয়ে দেখি, গাড়িটা একটা সিগনালে আটকে আছে। অনেকক্ষণ।
আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। মহিদুল বলল, ‘কত দিনের প্রোগ্রাম ম্যাডাম?’
‘দিন দশেকের। বাড়তেও পারে।’
‘একুশে ফেব্রুয়ারিতে যাবেন। আমাদের ভাষার দিবস। আমি প্রতি বছর যাই। সন্ধ্যায় লাইন দিই, মধ্যরাতে ফুল দিতে পারি। খালি লোক দেখবেন।’
‘এতক্ষণ লাইন দিতে হয়?’
‘দিতে হবে না! এত লোক সবাই লাইন দিয়ে শহিদের বেদিতে মালা দেয়।’
হঠাৎ গাড়িটা বিকট শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। মহিদুল বলল, ‘ঘাবড়াবেন না। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। যেভাবে যে গাড়ি চালায়? কোনও হিসেব রাখে না। আপনাদের দেশে রাফ ড্রাইভিং করে?’
‘করে মানে, কলকাতায় তো কেউ রাস্তার নিয়ম মানে না। যে যেমন পারে চালায়।’ অনিন্দিতা না বলে থাকতে পারল না।
মহিদুল বলল, ‘তবে এখানে ট্রাফিক এত স্লো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় না বললেই চলে।’
গাড়িটি চলতে আরম্ভ করল। আমি জানালা দিয়ে এক নতুন দেশ দেখতে দেখতে চলেছি। প্রায় একই চেহারার মানুষ, রাস্তার গড়ন এক, যানবাহনের চেহারাও কলকাতার মতো, শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে রিকশা এসে মনে হচ্ছে শহরের গতি রুদ্ধ করে দিচ্ছে। বললাম, ‘মহিদুল, রিকশা এত চললে তোমরা গাড়ি চালাও কী করে?’
মহিদুল একগাল হেসে বলল, ‘ঢাকার এটাই সৌন্দর্য, বলে না, যত দূর ঢাকা যায় তত দূর রিকশা যায়। রিকশা ছাড়া এই শহরকে ঠিক মানায় না।’
‘শুনেছি রিকশাওয়ালারা খুব রসিক হন।’
‘খুবই। ওদের সঙ্গে কথায় পারবেন না। আপনাকে কথায় বিশ্ব ঘুরায় দেবে।’
বলতে বলতে মহিদুল একটি রাস্তার ডান দিকে ঘুরে গেল। বলল, ‘ওই দেখেন স্যার, আপনাদের হোটেল।’
আমি হোটেলের নামটি পড়তে পারলাম না, তবে ইন্টারন্যাশনাল শব্দটি বেশ বড় হরফে লেখা চোখে পড়ল।
মহিদুল বলল, ‘আগের থেকে বুক করেছিলেন বলে পেয়েছেন। এই সময় ঢাকায় পা ফেলবার জায়গা নেই। দুনিয়ার মানুষ ঢাকায় এসে হাজির হয়। এই জায়গাটা বলতে পারেন অফিস পাড়া। সব কিছু হাতের কাছে পাবেন।’
||৭||

গাড়িটি থামল একটি বাড়ির সামনে। দশতলা বাড়ি। হোটেলটি ছয়তলা থেকে দশতলা। একতলা থেকে ছয়তলার নিচে নানান কোম্পানির অফিস। হোটেলে যাব বলে সাততলার বোতাম টিপতেই লিফট পৌঁছে গেল রিসেপশনে। অনিন্দিতার সঙ্গে কথা হয়েছিল হোটেল ম্যানেজারের। আমাদের দেখেই সরবত এগিয়ে দিল একটি ছেলে, ‘বলল, বসুন, ম্যানেজার আসছে। নামাজ পড়তে গেছে।’
আমাদের থাকার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হলে, কিন্তু সেটা চার দিন পর থেকে পাওযা যাবে। তাই এই আপৎকালীন ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে খুব কম সময়ে। এ সময় হোটেলে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে অনিন্দিতা পেয়েছে। আমরা বসে আছি একটি সোফায়। উল্টো দিকের সোফায় বসে কথা বলছে তিন মধ্যবয়সী মানুষ, একজনের মাথায় ফেজ টুপি, অন্য দুজন শার্ট-প্যান্ট পরিহিত। তাদের আলোচনার শব্দ কানে আসছে। আমরা যে বসে আছি, তাতে তাদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। একজন বলছে, ‘এই মহকুমায় আমার প্রতিপত্তি এত প্রবল, আমাকে ছাড়া কেউ ভোট করতে পারবে না। পারলে আমি রাজনীতি ছাড়েই দিব।’ অন্যজন ঘাড় নেড়ে সমর্থন দিলেও লোকটি থামল না। সামনের জনের হাতে হাত রেখে বলল, ‘আপনি সালেম সাহেবকে একবার বলেন, আমাকে যেন টিকিট অস্বীকার না করেন। আমি ওনার সব মূল্য বুঝাইয়া দিব।’
যার উদ্দেশে কথা, সে ঘন ঘন ঘাড় ঘোরাচ্ছে। সম্মতি আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এমন সময় ফোন এল। মাঝের লোকটি ফোন ধরে বললেন, ‘জি, রাজি আছে মনে হচ্ছে। কত দেবে এখনও ফয়সালা হয়নি।’
‘তবে যা দেবে তার চার গুণ তুলে নেবার ক্ষমতা আছে মনে হচ্ছে।’
আমার যেন মনে হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন সম্মুখে, বসে আছে পার্টির নেতারা। গোপন নিরিবিলি রেস্তোরাঁয়। টিকিট পাওয়ার জন্য দর কষাকষি হচ্ছে। একবার হয়ে গেলেই ওই অঞ্চলের নেতা বানানো শেষ। তারপর শুধু প্ল্যাকার্ড, দেওয়াল লিখন, হোর্ডিংয়ে নেতার ছবি আর তার উপরে দলনেতা বা নেত্রীর ছবি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কি ধীরে ধীরে এই একই পথে ঘুরে যাচ্ছে? নেতা আর তৈরি হয় না, কেবল বানানো হয়? যেমন বানানো হয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য!
মানেজার এসে অনিন্দিতাকে বলল, ‘এমন জায়গায় এসেছেন দিদি, হাত বাড়ালেই বন্ধু। খাবার, রিকশা, সিএনজি, সারাদিন সারারাত, মানি এক্সচেঞ্জ, কমলাপুর স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, সব পাবেন।’ অনিন্দিতা বলল, ‘আগে ঘরটা দেখান, তার পর শুনব। সারাদিন ট্রেন জার্নি করে এসেছি।’
সাততলায় একটি ঘর আমাদের দেখিয়ে দিল একটি ছেলে। ঘরের সব দেখানোর পর বলল, ‘আমি মাস্টারদা সূর্য সেনের দেশের লোক। যা চাইবেন এনে দিব। লজ্জা করবেন না দিদি। সত্য কথা কই। দরকার হলে বাইরে থেকেও এনে দিব।’
ছেলেটি চলে গেলে আমি বললাম, ‘আসলে এটা একটা বিজনেস হোটেল, এখানে খাবার পাবে না। এই ছেলেটির ওপর নির্ভর করতে হবে।’
অনিন্দিতা বলল, ‘তা কেন, আমরা বাইরে খেয়ে নেব।’
হোয়াটসঅ্যাপ কল করলাম নাহিদাকে। বললাম, ‘পৌঁছে তো গেছি কিন্তু বাংলাদেশের সিম কোথায় পাব? একজনের সঙ্গে দেখা হল, সে বলেছে বাংলাদেশের সিম নিতে গেলে রেফারেন্স চাই, তার ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে।’
নাহিদা বলল, ‘ছাড়ো তো দাদাভাই। আজ আমি একটু বিজি আছি, কাল সকালে আমি তোমাকে হোটেলে একটা সিম দিয়ে আসব। ওটাই হবে বাংলাদেশে তোমার সিম।’
সিমের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত, চান করে পোশাক বদলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সন্ধের ঢাকা। কাছের কোনও গাছ থেকে পাখির ডাক, যানবাহনের ক্রমাগত কমে আসা আওয়াজ, তার মধ্যে আবছা ধোঁয়ার কুণ্ডলী সমাহিত ঢাকার আকাশ। মনে হচ্ছে, এ তো উত্তর কলকাতার ছাদ থেকে কলকাতার দিকেই তাকিয়ে আছি।
তাই তো হবে। এই দুটি শহরের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ হয়। একই মানুষের যাতায়াত, একই ভাষায় কথা। কেউ এসে আলাদা করে দিলেই কি আলাদা হয়? আজকের দিনে মোবাইলের সিমের কোম্পানির নাম বদল হয়, কিন্তু সেই তারহীন পথে শব্দ একদিক থেকে অন্য দিকে চলাচল করে তো বর্ণপরিচয় ধরেই। এক ভাষা। চেষ্টা তো কম করেনি। পেরেছে? পারেনি। তবেই তো ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা ভাষার নবজন্ম। মাতৃভাষা দিবসের মাস।
হোটেলটির উল্টোদিকে একটি রেস্তোরাঁ। পরিশ্রান্ত শরীরে দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এই হোটেলের মেনু দেখে খুব একটা খাবার ইচ্ছে হচ্ছে না। মামুলি মেনু। ঢাকায় এসেছি নতুন কিছু খাব না? অনিন্দিতা বলল, ‘নিচের কোনও রেস্তোরাঁ থেকে কিনে আনো। দেখে কিনবে। নতুন জায়গা।’
নিচে নেমে রাস্তা পার হয়ে রেস্তোরাঁর কাউন্টারে দাঁড়াতেই একজন তাকিয়ে বলল, ‘কলকাতা থেকে নাকি?’
একটু অবাক হলাম, দেখে কোথাকার লোক চেনা যায় নাকি! বললাম, ‘হ্যাঁ, তা বুঝলেন কী করে?’
‘মুখ। মুখ দেখে। আমার এই রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন কলকাতার লোক আসে। তাদের মুখ আর চলার ধরন দেখে বুঝতে পারি দাদা। বলেন, কী খাবেন?’
‘রাতের খাবার চাই। কী পাওয়া যাবে?’
‘যা লেখা আছে সব।’ বলে মেনুটি এগিয়ে দিলে দেখি হুবহু হোটেলের মেনুর মতো দেখতে। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে তফাত চোখে পড়বে না। শুধু ঠিকানাটা আলাদা। পদগুলি আগেপিছে সাজানো।
আমি দুবার মেনুবুকে চোখ বোলালাম। তারপর বললাম, ‘আমাদের হোটেলের মেনু বুকেও তো সব এই খাবার।’
লোকটি মুচকি হেসে বলল, ‘হবেই তো। ওর তো কিচেন নেই। আমার এখানে অর্ডার দিয়ে করিয়ে নেয়। হোটেল থেকে বিল করে। যাই হোক, সোজা এখানে চলে আসবেন, খরচা কম হবে।’
আমি সম্মতি জানালে সে বলল, ‘বলুন কী নেবেন?’
‘আপনার মতে যেটা বেস্ট।’
‘মোরগ বিরিয়ানি। নিয়ে যান, খেয়ে দেখেন, বুঝতে পারবেন। জিভে লেগে থাকবে। আর একটা কথা, আমি কিন্তু আপনাকে কিছু বলিনি। আপনি নিজেই কিনেছেন।’
‘হুম।’
‘আপনাদের ধুলাগড়ে আমার ছোট ভাই থাকে। নানা থাকে হালিসহরে। এক খালাতো ভাই থাকে শিয়াখালায়। আমাদের সব ওইদিকে থাকে। আমরা জানি কোথাকার জিনিসের কী টেস্ট।’
বিরিয়ানির এই মাধুর্য কী করে যে দুই বাংলায় এমনভাবে সংক্রমিত হয়েছে, এটি একটি গবেষণার বিষয়। কলকাতায় সম্প্রতি গলি, তস্য গলি, রাস্তার ধারে ছেয়ে গেছে বিরিয়ানির দোকানে। যে কোনও এলাকায় বিরিয়ানির বিক্রি দেখলে অবাক হতে হয়। বিস্ময়ের কথা, বিরিয়ানি বাংলার মানুষের খাবার ছিল না। উত্তর ভারতে মুঘল রাজত্বকালে এই খাবারটির উৎপত্তি বলেই বিশারদরা মনে করেন। অনেকে এমনও বলেন, বাবরের আগেও এই খাবারটির চল ছিল ভারতে। দক্ষিণ ভারতে এই বিরিয়ানির চল বহুদিনের। ভেজ ও ননভেজ বিরিয়ানির পাশাপাশি চলন দক্ষিণ ভারতে খুব প্রচলিত। তা বলে বাংলা দখল করল কবে?
ঠিক সাল তারিখ লিপিবদ্ধ করা নেই হয়তো, তবে আন্দাজ করা যায়, বাঙালির চাকরি করা, মেয়েদের চাকরির প্রয়োজনে বাইরে অনেক সময় কাটানো আর বিশেষত, একবারে চাল, মাংস, আলু দিয়ে রান্নার যে সহজ প্রণালী, সেটাই এই ভূখণ্ডের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। না হলে এই সময়ের যে কোনও ছেলেমেয়েকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে, বিরিয়ানিই তাদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার, যেমন বাচ্চাদের ম্যাগি।
সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নববর্ষ। রাস্তার একদিকের ফুলের দোকান থেকে ফুলের মুকুট পরে মেয়েরা দলে দলে জড়ো হচ্ছে প্রাঙ্গণে। সেখানে বসে ছিল নাঈমা ও তার স্বামী। তাদের পাশে বসে দেখি মুক্তমঞ্চে এক একটি দল নাচ ও গান পরিবেশন করছে। একটি গাছের তলায় মুক্তমঞ্চ। কী অপূর্ব নিয়মানুবর্তিতা। আলাপ হল নাঈমার বিচারক স্বামীর সঙ্গে। প্রথম আলাপেই মনে হল মানুষটি খুব আন্তরিক। এখানেই আলাপ হল বাংলাদেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, আবৃতিকার এবং একুশে পদক-প্রাপ্ত ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমার বন্ধু আশিস চক্রবর্তীর স্ত্রী পাপিয়ার বন্ধু। আলাপের সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বললেন, ‘ছায়ানটে অনুষ্ঠান আছে, চলে আসুন। কত দিন আছেন?’
বললাম, ‘দিন সাতেক।’
তাহলে একদিন আড্ডা মারা যাবে সময় করে। নববর্ষের এই অনুষ্ঠান অনেকটাই শান্তিনিকেতনের আদলে তৈরি। মানুষের ভালবাসায় ও আন্তরিকতায় সম্পৃক্ত এই জনজীবন। চারিদিকে ফুলের রং, মানুষের রং, আনন্দের হাসি হিল্লোল মিলনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে ঢাকার সকাল যেন নতুন উৎসাহে ভরে উঠেছে এই মহামিলনে। এখানেই আলাপ হল কবি লিলি হকের সঙ্গে। বিভিন্ন গাছের নিচে শান্ত ছায়ায় গোল করে বসে গান, আবৃতি, এ এমন উদযাপন এক প্রাণবন্ত সকালের দান। ঘুরে ঘুরে আমাদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। ছবি উঠল গ্যালারি-বন্দি করে।
||৮||

ফিরদৌস বলেছিল, ‘যেদিন আসতে পারবে জানাও, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। সকালে ফোন কোরো, তাহলে আমার পক্ষে সুবিধে।’
এ যেন হাতের মধ্যে তাস, যখন ইচ্ছে ফেলতে পারব। পরের দিন আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে অনিন্দিতার আবৃত্তি। হলটি আমাদের হোটেলের খুব কাছে। হেঁটে যাওয়া যায়। নতুন বলে রিকশা চল্লিশ টাকা নিয়ে পৌঁছে দিল। বিশাল অডিটোরিযাম, অনুষ্ঠানের অনেক বাকি তবুও হল কানায় কানায় ভর্তি। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এসে জানালেন, ‘শিক্ষামন্ত্রী ব্যস্ত, এখনও আসেননি। এলেই শুরু করে দেবেন।’ আমরা সামনের সিটে বসে তাকিয়ে দেখি ডায়াসে তিন-চারজন বসে আছেন। একজনকে চিনতে পারলাম, ডক্টর নূর-উন নবী ও তাঁর স্ত্রী, আর একজন হুমায়ূন আহমেদের ভাই ডক্টর মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন ঘন ঘন। একবার হলের মধ্যে তাকিয়ে দেখি গোটা হল প্রচুর কচিকাঁচায় ভর্তি। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, বাংলাদেশের অনেক স্কুল থেকে প্রচুর ছেলেমেয়ে এসেছে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তারাই ভরে দিয়েছে সারা হল।
সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, মন্ত্রীর দেখা নেই। একসময় অনুষ্ঠান শুরু হল। শুরু হবার পর জানা গেল এই অনুষ্ঠানটি একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং নূর-উন নবী সাহেবের পুস্তক প্রকাশ। এখানে বিশেষভাবে নূর-উন নবী সাহেবের কথার উল্লেখ করাটা দরকার। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং প্রায় তিন দশক আমেরিকা প্রবাসী নবী সাহেব ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করেছেন। দীর্ঘদিন আমেরিকার বাংলাদেশি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। একসময় চাকরি ছেড়ে বই লিখতে শুরু করেন। মানুষের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৌঁছে দেবার ব্রত গ্রহণ করেন। পর পর বাইশটি বই লিখেছেন তিনি। তার মধ্যে তিনটি বইয়ের আজ মোড়ক উন্মোচন। আর সেই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের স্কুলে বিনা পয়সায় তাঁর বই পাঠিয়েছেন, যাতে আগামী প্রজন্ম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে জানে ও মনে রাখে। বক্তৃতা দিতে উঠে নবী সাহেব বললেন, তাঁর মুক্তিযুদ্ধের দিনের কথা। কীভাবে তিনি আগরতলার কাছে পার্বত্য অঞ্চল থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাড় করতেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আবার বলতে বলতে তিনি কীভাবে আমেরিকায় বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা করে চলেছেন। দীর্ঘ বক্তৃতার পর জাফর ইকবাল সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাঁর সহযোগিতার ও বিদেশে তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার কথা বললেন। আর এর মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপুমণি এসে হাজির।
মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি অন্য চেহারা নিল, কেন না মন্ত্রী প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন। দেরি হয়েছে। চেয়ারে বসলেন আর তার পরেই অনিন্দিতার আবৃত্তি শুরু হল। সে দুটো কবিতা কোলাজ করে নিবেদন করলে দীপুমণি ডেকে বললেন, ‘খুব ভাল হয়েছে। মন দিয়ে শুনেছি। কীভাবে দুটো কবিতা মেলালেন? আমি বুঝতেই পারিনি।’ এতে অনিন্দিতা খুশি। এরপর যেটি অপেক্ষা করেছিল, যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।
বাংলাদেশের স্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যারা প্রাইজ পেয়েছে, সেইসব ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েরা মঞ্চে স্তব্ধ করে দিয়েছে হলভর্তি দর্শকদের। মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম এই মাপের আবৃত্তি গভীর চর্চা ও অধ্যায়ন না হলে সম্ভব নয়। কেউ কেউ আধুনিক কবিতাও উচ্চারণ করছে অনায়াসে। চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিং, রংপুর, বাগুড়া, পাবনার স্কুল থেকে এই কচিকাঁচারা যে ভাষাকে ভালবেসে কবিতা চর্চা করে, দেখে গর্বে বুক ভরে যায়। দীপুমণি একে একে পুরস্কার দিলেন। বুকের কাছে এই আগামী প্রজন্মকে টেনে এনে এমন পুরস্কার বিতরণ আগে আমি দেখিনি। মনে হচ্ছে তিনি মন্ত্রী নন, জননী তাঁর সন্তানদের আদর দিয়ে পুরস্কৃত করছেন। এই দৃশ্য এপারে খুবই বিরল।
এই দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের বলিরেখা এখন অনেক মানুষের হৃদয়ে ফুটে আছে, ভাষার জন্য জীবন দান আজও বেদনার্ত অনুভূতি। এপারের স্বাধীনতার অনেক বয়স। যুদ্ধ ছাড়া যে স্বাধীনতা এসেছে, সেখানে এই অনুভূতির জীবন ক্ষণস্থায়ী হবে তাতে আর অবাক হবার কী আছে? ঠিক তাই হয়েছে। ড. নূর-উন নবী এই উপলক্ষে তাঁর ‘আমেরিকায় আমার যুদ্ধ’ নামের একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইটিতে তাঁর আমেরিকা থেকে বাংলার জন্য আন্দোলন, যুদ্ধ, সংগঠনের নানান ঘটনা লেখা আছে। ভবিষ্যতে যারা গবেষণা করবেন তাদের এই পুস্তকটি অনেক কাজে লাগবে। এই বইটার মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের শেষজীবনের আমেরিকা প্রবাসের বিশদ বর্ণনা আছে। আমি আগেও ড. নবীর মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছিলাম কোনও এক ইউটিউব চ্যানেলে। শিহরিত হয়েছিলাম, কেন না তিনি যেভাবে ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছেন বাংলাদেশে, সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আজ সামনাসামনি তাঁকে দেখে এবং তাঁর কণ্ঠে সেই ঘটনার বর্ণনা শুনে নতুন করে শিহরিত হলাম। সেই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। বার বার বাংলাদেশের মেয়েদের বললেন, ‘সবাই চাকরি করবে। নাহলে একদিন নবীর মতো শুনতে হবে, কাল চাকরি ছেড়ে দেব। তখন তোমাকে চালাতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।’ বুঝতে পারছিলাম তাঁকে কোনও একসময় এমনই এক সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই অবস্থার কথা তিনি অন্যভাবে বলে দিলেন।
অনুষ্ঠানটি শেষ হল, আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। তারপর রাজিয়ার ফোন। আগামীকাল সে আমাদের নিয়ে ‘মিলেনিয়াম টেলিভিশন’-এ একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছে। বিকালে নিতে আসবে। বনানীতে তাদের স্টুডিও। আমরা কিছুই চিনি না। তাই সে নিজে আমাদের হোটেল থেকে নিয়ে যাবে। অনেকটা হুকুমের মতো বলল, ‘কোনও প্রোগ্রাম রাখবেন না দাদা। কোথাও যাবেন না। কাল আমি আপনাদের বুক করে দিলাম।’ রাজিয়াকে না বলা মুশকিল। এমন আন্তরিকতা দিয়ে সে কথা বলে যে, মনে হয় সে বহু বছর চেনে। পরদিন সেই সরল মেয়েটি চলে এল আমাদের হোটেলে। ঠিক চারটেয়। আমরা তৈরি ছিলাম। স্টুডিওতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধে হয় হয়। আমাদের গাড়ি একটি তিনতলা বাড়ির নিচে থামল। রাজিয়ার পিছন পিছন বাড়ির উপরে গিয়ে দেখি বেশ বড় একটি স্টুডিও। সব কিছু সাজানো। রাজিয়া বলল, ‘এটা আমাদের প্রেসিডেন্টের বাড়ি। উনি থাকেন আমেরিকায়। এটা একযোগে আমেরিকাতেও প্রচার হবে। আমরা নানান অনুষ্ঠান করি, খবর করি।’ আমরা চা খেলাম। রাজিয়া একটু প্রসাধন করে নিল। এর মধ্যে একটি ছেলেকে দেখলাম ক্যামেরার কাছে দাঁড়িয়ে। বলল, ‘আমি রেডি। আপনারা শুরু করবার আগে আমাকে বলবেন। বাকি সব ঠিক আছে।’ মেঝের একদিকে একটি লম্বা সোফা, সেখানে আমি আর অনিন্দিতা বসলাম, তার পাশের একটি সোফায় রাজিয়া। প্রোগ্রাম শুরু হল। রাজিয়া পরিচয় করে দিল আমাকে ও অনিন্দিতাকে। রাজিয়া বলল, ‘আজকের অতিথি ওপার বাংলার একজন লেখক আর একজন আবৃত্তি শিল্পী। এটা ইন্টারভিউ নয়। আলাপচারিতা। তাই ঘরোয়া আলোচনা। সরল প্রশ্নের সরল উত্তর।’
আমি আমাদের সাহিত্য চর্চার কথা, লেখালেখির কথা বললাম। বাংলা ভাষায় সমস্যার কথা আলোচনা হল। অনিন্দিতা আবৃত্তি করল, কথা বলল, আমাদের জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা হল। প্রায় ত্রিশ মিনিট আমরা আলো আর শব্দতরঙ্গে থাকার পর একসময় আলো নিভল, ক্যামেরা বন্ধ হল। রাজিয়া বলল, ‘দিদি, খুব ভাল লেগেছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলে। এই অনুষ্ঠানটি অনেক দিন মনে থাকবে।’ আমি বললাম, ‘আমাদেরও অনেক দিন মনে থাকবে এত তাড়াতাড়ি তোমার এই বাবস্থাপনা ও যোগাযোগ। খুব তৎপর না হলে এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয়।’ হাসল রাজিয়া। ভঙ্গিটা এমন, এ আর কী দেখলেন দাদা। একটু অপেক্ষা করুন, আরও অবাক হয়ে যাবেন। আমাকে ছোট্টখাট্টো দেখতে হলে কী হবে, আমি কিন্তু একটি বারুদের সমাহার। বাড়ির পথে রাজিয়া বলল, ‘আপনাদের একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমেরিকায় থাকেন। ঢাকায় এসেছেন।’
রাতে আমাদের এক সাংবাদিক-বন্ধু এন আর বি নিউজের অমর ভাই খেতে আমন্ত্রণ করলেন। অমর ভাইয়ের দুই বাংলায় অবাধ বিচরণ। তিনি যেমন ওপার বাংলায় থাকেন আবার দুমাস অন্তর অন্তর কলকাতায় আসেন তার নিউজ চ্যানেলের কাজে। এখানে তিনি নানা প্রোগ্রাম সংগঠিত করেন। তিনি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সতত সতর্ক সৈনিক। দীর্ঘ দিন সাংবাদিকতা করেছেন, পৃথিবীর নানান প্রান্তে ঘুরেছেন, বিপুল তাঁর অভিজ্ঞতা। আমাদের রাজধানী দিল্লিতেও গেছেন অনেক বার। এসবই তাঁর মুখ থেকে শোনা। আমি তাঁকে চিনি খুবই সামান্য। কিন্তু এই অল্প চেনার মধ্যে আন্তরিকতার শেষ নেই। অমায়িক এই মানুষটির সঙ্গে সে দিন রাতে দুই দেশের অনেক গল্প হল। আমার লাভ এই যে, অনেক অজানা তথ্য জানা গেল অমর ভাইয়ের সৌজন্যে। এটিও একটি ফেসবুক মাধ্যমে পরিচালিত সংবাদমাধ্যম, যেমন মিলেনিয়াম টিভি। এই এক নতুন ট্রেন্ড এসেছে প্রযুক্তির কল্যাণে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে সারা বিশ্বকে শুনিয়ে দেওয়া যায় এই মুহূর্তের খবরাখবর।
||৯||

আসা ইস্তক এখনও বইমেলায় যাওয়া হয়নি। প্রাণ ছটফট করছে, যার জন্য এত কাণ্ড করে আসা। নাহিদার সৌজন্যে সিম কার্ড পেয়েছি। কথা বলতে কোনও অসুবিধা নেই। নাহিদাকে ফোন করলাম। নাহিদা বলল, ‘দাদাভাই, তোমরা পৌঁছে যাও, আমার একটু দেরি হবে। মেয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। তার জন্য সময় কাটছাঁট করতে হচ্ছে।’ এর চেয়ে আর আনন্দের কী হতে পারে। মেয়ে এসেছে মায়ের কাছে অনেক দিন পর। বললাম, ‘দেখা হবে। সময়মতো চলে এসো। আমরা তোমার স্টলেই থাকব।’ নাহিদা বলল, ‘জলধি স্টল। একটু এগিয়েই দেখতে পাবে, না হয় কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। নম্বর ধরে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।’
ঘটনা একেবারেই সত্য। এমন বিশাল বইমেলা, ছড়ানো বইয়ের পাহাড়, হাজার হাজার বই। প্রতিদিন একশো করে বই প্রকাশ হচ্ছে এই ত্রিশ দিনের বইমেলায়। পৃথিবীর কোনও মেলায় বই প্রকাশ উৎসব হয় শুনিনি। বইমেলায় ঢোকার কোনও বিশেষ নিয়মকানুন নেই। বই যারা ভালবাসে তাদের কাছে এটাই মহান তীর্থস্থান। এসেই জনবহুল বইমেলায় আমরা যেন হারিয়ে গেলাম সহজেই। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এক কোণে চোখে পড়ল ‘জলধি’। একটি মেয়ে আর একটি ছেলে, সামনে অনেক পুস্তকপ্রেমী। এমন দৃশ্য প্রায় সব ক’টি স্টলে। তার সামনে একটি বড় স্টল। সেখানে চারদিক খোলা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মানুষ। দূরে একটি জলাশয়ের উপরে ফোয়ারা। সেখান থেকে ঠান্ডা হাওয়া উড়ে আসছে।
আমি আর আনিন্দিতা বই উলটেপালটে দেখছি, এমন সময় নাহিদা এসে হাজির। বলল, ‘দাদাভাই, তুমি ভিতরে বসো, আমি দিদিভাইয়ের সঙ্গে গল্প করি।’ নাহিদা জানে আমার কিছু দিন আগের একটি দুর্ঘটনার কথা। তাই তার এই হুকুম। আমি স্টলের ভিতরে বসেছি। নাহিদা অনিন্দিতার সঙ্গে আলাপ করছে আর কোনও লেখক-লেখিকা বন্ধু এলেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে। এমনি করে প্রথম দিনেই পরিচিত হলাম তরুণ কথাসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী জয়দীপ দে, কবি ও গল্পকার মোস্তাফা মোহাম্মদ, গল্পকার ইসরাত জাহান ও জয়দীপ গুপ্তর সঙ্গে। আলাপের পর নিজেদের এক একটি করে বই উপহার দিলেন। এ এক তারুণ্যের সমাহার। আপন আত্মবিশ্বাসে সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ এই প্রবীণ ও নবীনদের দেখে ভাললাগায় মন ভরে যায়। আর তার সঙ্গে নাহিদার নানা গল্প আরও মজাদার করে তোলে। আমরা যে স্টলের পাশেই আড্ডা দিচ্ছি, পাঠকরাও মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। এখানেই আলাপ হয়েছে লন্ডন প্রবাসী ও নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে, যারা সারা বছর কোথাও না গেলেও ঢাকায় আসেন। তরুণদের বই কেনেন। অনেক প্রকাশনীর বইয়ের তালিকা নিয়ে যান। অনলাইন কিনে নেবেন। ডিজিটাল সভ্যতার সময় ওজন আর কে বইতে চায়? এখন আমরা তারহীন জীবনে অভ্যস্ত।
ঢাকায় আমার পরিচয় ছিল না নাহিদার বন্ধুমহলে। নাহিদাই প্রথম এই কাজটি করে আমাকে অনেক উপকার করেছে। তার এই সহজ আপ্যায়নে আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি। প্রথম বারেই। যেটা সচরাচর হয় না।
সাড়ে সাতটার সময় রাজিয়ার ফোন। ‘দাদা আপনি কোথায়?’
‘আমি জলধি-তে।’
শুনে বলল, ‘‘চলে আসুন ‘কারুলিপি’-র স্টলে। আমি আছি।’ আমি জলধি থেকে কারুলিপির স্টলে গিয়ে দেখি রাজিয়া স্টলের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে নিয়ে গেল কারুলিপির কর্তার কাছে। পরিচয় করিয়ে দিল। এর পর সে আমাকে আর এক প্রকাশক গফুর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তার বইয়ের স্টলে। গফুর ভাই রাজিয়ার বইয়ের প্রকাশক। সেখান থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার বই ‘অহনার মুক্ত পৃথিবী’ মোড়ক উন্মোচনের মঞ্চে। যাবার পথেই সে একদল বাংলাদেশের কবি ও আবৃত্তিকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, ছবি তুলল, হাসিমজা করে যখন মঞ্চে পৌঁছল, তখন সেখানে কেউ নেই। আমাকে বলল, ‘দিদিকে নিয়ে আসুন দাদা, ততক্ষণে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব।’
আমি অনিন্দিতাকে আনতে গেলাম। গিয়ে দেখি জলধিতে বিশাল ভিড়। আরও অনেক লেখক ও কবিরা এসেছেন। সেখানেই আলাপ হল পেনসিলভানিয়া থেকে আসা একটি পরিবারের সঙ্গে। দুই মেয়েকে নিয়ে এই সময় ঢাকায় এসেছেন। এক মাস থাকবেন। বইমেলায় আসবেন রোজ। এইটাই তাদের পুজো উৎসব, এটাই তাদের ঈদ। বললেন হামিদ ভাই, ‘প্রতি বছর তো আসতে পারি না, খরচসাপেক্ষ। দুবছর অন্তর অন্তর আসি। যাতায়াতের খরচ বেড়ে গেছে অনেক। তবে না এসে থাকতে পারি না। এ যে কী টান সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আপনারা ভারত থেকে দেখতে এসেছেন আর আমরা আসি টানে। পুরো দেশ তো দেখাতে পারি না। দেশের বই কিনে পড়াই। বইই তো দেশ, বলেন? বই পড়লেই তো দেশ চেনা যায়। আমার দুই মেয়েকে আমি তাই বলেছি। ওদের নিয়ে আসি। বই পড়তে পড়তে দেশকে কখন ভালবেসে ফেলেছে। প্রতি বছর আসতে চায়। আনতে পারি না। এই আমার বড় দুঃখ। কী যে করি?’ বলে করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে। তার পর সামনের স্টলের দিকে এগিয়ে যান। আমি অবাক হয়ে ভাবি, দেশকে জানতে বই পড়া পাঠক ও পাঠিকা এখনও আছে পৃথিবীতে? এই জানাও এক অপার আনন্দের।
জলধিতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রাজিয়ার কাছে পৌঁছে দেখি, যারা বই উন্মোচন করবেন তারা এসে হাজির। রাজিয়া নেই। সে গেছে কোনও এক কাজে। সেখান থেকে ফিরেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল গফুর ভাই আরও অনেক পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে। সব নাম মনে নেই। পুস্তক উন্মোচন হল। একটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি হল। সেখান থেকে আবার আমরা জলধির দিকে। হঠাৎ রাজিয়া বলল, ‘দাদা আমি নাহিদা আপাকে ফোন দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করেন।’ ফোন করে নাহিদাকে বলল, ‘আমাদের মিলেনিয়াম টিভির ভাইস প্রেসিডেন্ট এসেছে আমেরিকা থেকে। সে নেমতন্ন করেছে। তোমাকে যেতে হবে।’
নাহিদা বলল, ‘আমি কী করে যাব? স্টল চলছে না?’
‘তাহলে দাদা-দিদিকে নিয়ে যাব?’
নাহিদা বলল, ‘হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমি সময় করতে পারলে যাব। ওরা তো আবার এখানে আসবে। কোনও সমস্যা নাই।’ শুনে সে ফোনটা কেটে দিয়ে বলল, ‘চলেন আমার সঙ্গে। নাহিদা আপার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। উনিও আসবেন।’
‘কোথায়?’
আপনাদের হোটেলের কাছেই। বলে মেলা থেকে বেরিয়ে সিএনজি-তে উঠে পড়লাম। আমরা একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোতলায় উঠে দেখি একটি রেস্তোরাঁয় আমাদের জন্য একটি লম্বা টেবিল ব্লক রাখা হয়েছে। রাজিয়া বলল, ‘আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট আজম সাব এসেছেন। আজ আপনাদের আপ্যায়ন করবেন। তাই এখানে আসা।’ বলতে বলতেই দেখি সুপুরুষ, আমেরিকার ব্যবসায়ী সংগঠক কাজী আজম এসে আমাদের নমস্কার করলেন। তাঁর সহৃদয় উপস্থিতি এতই সুন্দর যে, মনেই হল না তিনি আমাদের অপরিচিত। খোলামেলা আলোচনা হল অনেকক্ষণ। তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে খেলেন না। কারণটি খুব সাধারণ। শাশুড়ি-মাকে কথা দিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে ডিনার করবেন। তাঁর অনেক বয়স হয়েছে। ঢাকায় থেকেন। সঙ্গীকে আমাদের কাছে রেখে যাবার আগে রাজিয়াকে বললেন, ‘কাল একটা অনুষ্ঠান করা যায় না? আমি কিছু শিল্পীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাই, তার একটা প্রথম মহড়া হলে ভাল হয়।’ রাজিয়া বলল, ‘সময় খুব কম। তবে দেখছি।’ আজম সাহেব চলে গেলে রাজিয়া বলল, ‘আপনারা কাল চলেন। জমে যাবে। দিদি আবৃত্তি করবেন। আমি ক’জন শিল্পীকে দেখি যোগাড় করতে পারি কি না।’
আমি বললাম, কাল আমাদের গুলশানে একটা নেমন্তন্ন আছে দুপুরে। পারব কি না জানি না।’ রাজিয়া বলল, ‘দরকারে আমি সিএনজি পাঠিয়ে দেব। নিয়ে আসবে। কাল থাকতেই হবে। আজম স্যার দিদির আবৃত্তি শুনতে পারবেন। কাকে নিয়ে যাবেন সে তো তাঁর মর্জির ওপর। কোনও কথা শুনব না। যেখানে যাবেন সেখানে বলে রাখুন, বিকেল অব্দি থাকবেন। রাতে নয়।’
||১০||

ফিরদৌস থাকে গুলশানে। ঢাকা শহরের অন্যতম আধুনিক ও উন্নত আধুনিক অঞ্চল এই গুলশান। জানা ছিল। আমাদের হোটেল থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল গুলশান পৌঁছতে। গাড়িটি যখন গুলশানে ঢুকছে সেই সময় বুঝতে পারছি একটি শহর থেকে আর একটি শহরে এসে গেছি। চওড়া রাস্তা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নগর সভ্যতার ঝকঝকে নিদর্শন এই গুলশান। প্রথমে চোখে পড়ল একটি বিশাল মল। এই মুহূর্তে আধুনিক সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। ফিরদৌস বলে দিয়েছিল, মলটি পেরলেই দেখবে পর পর বিদেশি অ্যামবাসি। বাম দিক ফলো কোরো। দেখবে কিছুটা এগলেই বাম দিকে আমার বাড়ির রাস্তা। একটু ঢুকলেই ডান দিকে আমার ফ্ল্যাট। সঙ্গে গুগল ম্যাপ আছে। না খুঁজেই পৌঁছে গেলাম। লিফট থেকে তিনতলায় উঠে বেল বাজাতেই দরজা খুলে গেল। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল ফিরদৌস। কত দিন পর সুতপনদা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার ডায়মন্ড রেসিডেন্সিতে ফিরে গেলাম।
বিশাল ফ্ল্যাট। ফিরদৌস বাংলাদেশের একটি বিশাল কোম্পানির মার্কেটিং হেড। তাকে কোম্পানি কেতাদুরস্ত রেখেছে। বাড়ি দিয়ে, মাইনে দিয়ে, গাড়ি দিয়ে, ড্রাইভার দিয়ে। যদিও ‘আমার অফিস পায়ে হাঁটা।’ হাসতে হাসতে বলল ফিরদৌস।
তিন কামরার ফ্ল্যাট, গিন্নি গেছেন ভারতে। না বেড়াতে নয়। এমিরেটাস বিমানের কাজের সূত্রে তাকে মাঝে মাঝে উড়ে যেতে হয় পৃথিবীর নানা প্রান্তে। সেখান থেকেই ফোন এল। জানতে চাইল আমরা এসেছি কিনা? কী কী ব্যবস্থা হয়েছে আপ্যায়নের, কখন এসেছি? যা যা বলে গেছিল গীতা বলে রান্নার মেয়েটি সব রান্না করেছি কি না? আর সর্বোপরি বলল, বগুড়া থেকে যে দই, তা আনানো হয়েছে? তা যেন ফিরদৌস আমাদের দিতে না ভোলে। আমরা তো হতবাক। শুনেছি বাংলাদেশের আন্তরিকতা বিশ্ববন্দিত। তবে এই রিমোট কন্ট্রোলের আতিথেয়তা আমার স্বপনের অগোচরে ছিল। আমি বললাম, ‘বড় ভাল মেয়ে তোর বউ।’ ফিরদৌস হেসে বলল, ‘তোমাদের শুভেচ্ছা। তবে রেগে গেলে রক্ষে নেই। পাগলের মতো করতে থাকে।’ অনিন্দিতা বলল, ‘কোথাকার মেয়ে?’
‘বরিশাল।’
‘বলিস কী রে! তবে তো হবেই।’
‘হবেই মানে? কী করে জানলে?’
‘আমি নিজে যে? জানব না?’ অনিন্দিতার দৃপ্ত উত্তর।
‘তুমি বরিশাল? জামতাম না তো?’
আমি মনে মনে ভাবছি, সেখানেই যাচ্ছি বরিশাল? হলটা কী? বসে আমি ভাবছি। ফিরদৌস বলল, ‘তবে তো কিছুই বলার নেই। বাট সি হ্যাজ গোল্ডেন হার্ট।’ অনিন্দিতার আবার সদর্পে উত্তর, ‘হতেই হবে।’ আমরা নানা গল্পে মেতে গেছি। কখনও কলকাতা, কখনও ঢাকা। গল্পের বল কিছুক্ষণ এক গর্ত থেকে লাফিয়ে অন্য গর্তে চলে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম, ঢাকার জীবন অনেক শান্ত, সুগঠিত, উচ্ছৃঙ্খলতা কম, আত্মিক যোগাযোগ অনেক বেশি। কলকাতার ঠিক বিপরীত। ফিরদৌস আমাদের তার নতুন জীবনের গল্প করল অনেক বেশি। যাদবপুর সন্তোষপুরের ছেলে ফিরদৌসের কলকাতায় তার প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের পর ঢাকায় চাকরি নিয়ে চলে যায় সে। সেখানেই তার বউয়ের সঙ্গে দেখা এক পার্টিতে। কোভিড তাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তারপর বিয়ে। কোভিড তাহলে কিছু ভাল কাজ করেছে! আমার ছেলে রুন ফিরদৌসের খুব প্রিয়। একবার আমেরিকা থেকে এসে ঢাকায় গবেষণার কাজে গিয়ে ফিরদৌসের বাড়িতে ছিল ক’দিন। দুজনে খুব মজা করেছে শুনেছি। অফিস থেকে ফিরে প্রায় রোজই কোথাও বাইরে খেয়েছে দুজনে। তখনও সে আমেরিকার ইলিনয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে। এখন সে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক শুনে খুব খুশি হল সে।
গল্প করতে করতে চারটে বেজে গেছে খেয়াল করিনি। খেতে বসলাম। তার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে ফিরদৌস নিয়ে গেল কাছেই একটি পার্কে। ভিতরে দেখি একদল কলেজের বা স্কুলের ছেলে ডফলি বাজিয়ে গান করছে। চেহারায় তারা পার্বত্য এলাকার, গান তাদের পাহাড়ের ও মাটির, আনন্দের ও উদাসীনতার। ফিরদৌস বলল, ‘আমি অনেক দিন দেখেছি ওদের। কী প্রাণবন্ত তরুণ, আপনমনে পল্লিগান করে, ভাটিয়ালি করে। বিকেলটা মাতিয়ে রাখে।’ দেখতে দেখতে একটা বিরাট পুকুরের ভিতর একটা ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের গোড়ায় পাশাপাশি বসে আছে দুই তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা। ব্রিজের ওপর অনেকগুলো পরিবার সেলফি তুলতে ব্যস্ত, এক নববিবাহিত যুগল ফিরদৌসকে ছবি তুলতে অনুরোধ করে সিনেমার ভঙ্গিতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলল। এ এক মানুষের মুক্তাঞ্চল। এখানে বোরকা নেই, মোল্লাদের বিধিনিষেধ নেই, মানুষের মুক্ত মন প্রকাশের কোনও বাধা নেই। কেবল খোলা বাতাস। আমি একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার বাড়ি কোথায়?’ সে উত্তর দিল, ‘নেপাল। ডাক্তারি পড়তে এসেছি।’
‘ঢাকা কেমন লাগে?’
‘দারুণ। বেটার দ্যান কাটমান্ডু।’
‘কেন?’
ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল, ‘পিউপল আর গুড।’ বলে চলে গেল পুকুরের দিকে। পুকুরের ধার দিয়ে আমারা ঘুরতে ঘুরতে এবার পৌঁছলাম প্রায় অন্য প্রান্তে। সামনে একটি বইয়ের দোকান। দোকানটি মনোরম। বাংলা বইয়ের সঙ্গে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি বইয়ের বিচিত্র সমাহার। আমার মনে পড়ল পার্ক স্ট্রিটের বা দিল্লির খান মার্কেটের বইয়ের দোকানের কথা। এই একটি বইয়ের দোকান দেখলে জায়গাটার অবস্থানগত ও বৈচিত্র্যগত পরিচয় পাওয়া যায়। আমি ভিতরে ঢুকে দেখি এখানে আরাম করে বসবার জায়গা আছে, বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের সঙ্গে অনেক বিদেশি আছেন যারা এই বইয়ের দোকানের খরিদ্দার।
এক সময় বিদায় জানালাম ফিরদৌসকে। আমরা বনানীর দিকে মুখ করে বেরোলাম। বনানীতে রাজিয়ার স্টুডিও। সেখানে অপেক্ষা করে আছে সে। আগের দিন রাজিয়া নিয়ে এসেছে। আজ ফিরদৌসের মহিদুল। একটি লেকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিশ্চিন্ত সফর আমাদের।
স্টুডিওতে ঢুকে দেখি অনেকেই এসে গেছে ততক্ষণে। এসেছেন কাজি আজম, আবু আতাহার (মার্কিন দেশের একজন উদ্যোক্তা, এখন ঢাকায় থাকেন), বিখ্যাত পল্লিগীতি শিল্পী লাভলি দেব, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত আচার্যি ও তাঁর স্ত্রী ঋধিতা ইন্দিরা, একজন বিখ্যাত আধুনিক গানের শিল্পী মাহাফুজ রুমি, একজন সঙ্গীত পরিচালক ও সঙ্গীতশিল্পী ইমারুল বাবু ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া একজন পল্লিগীতির শিল্পী। সঙ্গে আমি ও অনিন্দিতা।
জমজমাট সমাবেশ। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, রাজিয়ার কী ক্ষমতা! মাত্র একদিনের নোটিশে সে এতজন বিখ্যাত শিল্পীকে হাজির করে দিয়েছে! আজম সাহেব খুব খুশি। তাঁর যে কাজে এই জমায়েত, সেটা হয়ে যাবে মনে হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে আজম সাহেব বললেন, ‘আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমি কিছু গানের শিল্পীকে আমেরিকা নিয়ে যাবার জন্য বেছে নেব। তাই এক আয়োজন। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।’ ফলে অনুষ্ঠানের প্রথমে মান সম্বন্ধে একটি নির্ধারণ সূচক দিয়ে দিলেন আজম সাহেব। তারপর রাজিয়া শুরু করল তার অনুষ্ঠান পরিচালনা।
আধুনিক গান গাইলেন মাহাফুজ রুমি, লাভলি দেব গাইলেন লালনের গান, জয়ন্ত গাইলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। একধিক গান গাইলেন অন্য শিল্পীরা। মাঝে মাঝে আলাপচারিতা বাদ গেল না। আমরা পরিচালক ইমারুল বাবুর কাছে শুনতে পারলাম নানান সঙ্গীত জগতের মজার মজার গল্প। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত শিল্পী।
অনুষ্ঠান চলল প্রায় এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। আমরা রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। আতাউর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল। বললেন, ‘একবার আমেরিকায় আসুন। আমি যদিও ঢাকায় থাকি, আমি যোগাযোগ করে দেব।’ আজকের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অনেক শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হল। রাজিয়া না থাকলে এইসব হত না। রাজিয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরব বলে গাড়িতে উঠছি। রাজিয়া বলল, ‘দাদা, কাল মেলায় দেখা হবে। আমি আসব সাড়ে ছ’টায়।’
||১১||

সক্কাল সক্কাল লাগেজ নিয়ে এসে হাজির হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হলে। দেখলাম আমাদের সাদরে অভ্যর্থনার জন্য একজন অল্প বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে হলের গাড়িবারান্দায়। আমাদের দেখে একগাল হেসে আলাপ করল, ‘আমি ড. রুবায়েত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।’ আমি তো অবাক। বললাম, ‘আপনি আবার আমাদের জন্য এলেন কেন? আমরা নিজে নিজেই…’। কথাটা কেড়ে নিয়ে রুবায়েত বলল, ‘তাই কি হয়? নাঈমা আপা আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনারা আসছেন। নাঈমা আমার কোলিগ। আমি তো আপনাদের জন্য অ্যাকোমোডেশন দেখছিলাম। ভাগ্য ভাল পেয়ে গেছি।’ বলে তিনি ইন্টারন্যাশনাল হলের তিন তলার একনম্বর ঘরে পৌঁছে দিলেন। বললেন, ‘হাসান সাব এখানের প্রশাসনিক প্রধান। আসবেন দশটার পরে। রেজিস্ট্রেশনটা করে নেবেন। বাকি আমি রেকমেন্ড করে সই করে দেব। কোনও অসুবিধা হলে ফোন করবেন। রাতে দেখা হবে ‘ এরপর নিজের কার্ডটি এগিয়ে দিলেন রুবায়েত।
এখানে এসে যেন শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছি কেন যেন মনে হচ্ছিল, এই তো সেই স্থান, যার সন্ধানে এই দেশে আসা। এই দেশের বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি, সব এই পুণ্যমাটি থেকে উদ্ভূত। ছায়া সুনিবিড় শান্ত রাস্তার দুদিকে আগামী প্রজন্মের ভিড়। আমাদের থাকার হলটির নাম স্যার পি. জে. হাটগ ইন্টারন্যাশনাল হল। স্যার হাটগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নামেই এই হলে বিদেশি ছাত্র, অধ্যাপক, বিভিন্ন ইন্সটিটিউটে পাঠরত ছাত্র ও ভিজিটিং অধ্যাপকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা। কিচেন, ডাইনিং হল, টিভি রুম, ইন্টারনেট পরিষেবা ও গ্রন্থাগার আছে এখানে।
প্রথমেই খবর পাঠালাম নাহিদাকে। শুনে নাহিদা বলল, ‘দাদাভাই, এবার তোমরা ঠিক জায়গায় উঠেছ। মেলায় দেখা হবে।’ তারপরেই নাঈমার ফোন। ‘দাদা, ঠিক আছেন তো? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমি ক্লাস শেষ করে বিকেলে আসছি। একটু রেস্ট নিয়ে নিন।’ বলে ফোনটা ছেড়ে দিল।
গাড়িবারান্দায় প্রবেশদ্বার, প্রায় পনেরো ফুট উঁচু হলের ছাদ, সামনের দুপাশে বাগান, অনবরত মানুষের যাতায়াত। ঢুকেই বাম দিকে একটি দোকান; যেখানে বিস্কুট, রুটি, চকোলেট, স্ন্যাক্স পাওয়া যায়।
হাসান সাহেব আসার পর আমি রেজিস্ট্রেশন করে দিলাম। বললেন, ‘যত দিন ইচ্ছে থাকেন। আমি কলকাতা মাঝে মাঝে যাই। আপনাদের সঙ্গে দেখা করে ভাল লাগছে।’
আমি প্রাতরাশ করে ফোন করলাম কামাল ভাইকে। ‘আজ অফিসে আছেন?’ কামাল ভাই ওদিক থেকে বললেন, ‘চলে আসুন দাদা। আছি, দুজনে লাঞ্চ করব।’
কিছুক্ষণ পরেই আমি কারোয়ান বাজারের দিকে সিএনজি নিয়ে রওনা হলাম। ঢাকার রাস্তাঘাট চিনি না। কারোয়ান বাজারের মোড়ে নামিয়ে দিল। তারপর কামাল ভাইয়ের অফিস পৌঁছতে অনেকটা হাঁটাপথ। মেট্রোর কাজ চলছে। চারিদিকে ধুলো। এ দৃশ্য আমাদের কাছে নতুন নয়। কলকাতা মেট্রোর সময় আমরা মায়াকাননের ফুল দেখতাম। এখানে মাটির উপরে, তাই সবই সাক্ষাৎ চোখের সামনে। তার অফিসটি কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ের ওপর, ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে কোনওক্রমে তার অফিস বিল্ডিংয়ের ছয়তলায় পৌঁছলে দরজা থেকে সোজা কামাল ভাইয়ের চেম্বারে। দেখি মোস্তাফা কামাল ভাই বসে আছেন তাঁর সম্পাদকের চেয়ারে। সঙ্গে তার তিন সহকর্মী। আলাপ করিয়ে দিলেন। যেন কত দিনের চেনা। গল্প জমে উঠল। কামাল ভাইয়ের একটি বই কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরিয়েছে মুজিবুর রহমানের ওপর। দীর্ঘ ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘বঙ্গবন্ধু’। খুব বিখ্যাত হয়েছে, ভাল বিক্রি হয়েছে কলকাতায় বইমেলায়। আমরা বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থা, বিশ্ব পরিস্থিতি, মৌলানা ভাসানী, মুজিবুর রহমান, বাংলা সাহিত্য, ঢাকার জীবনযাত্রা নিয়ে গল্পে মেতে গেলাম। অনেক তা সময় পেরিয়ে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ কামাল ভাই বললেন, ‘চলুন, লাঞ্চ করে নি। বিরিয়ানি চলবে তো?’
না বলি কী করে? ততক্ষণে পেটে তুমুল খিদে। খেতে খেতে বললেন, ‘আমি দেখি সময় করে এক-দুদিন মেলায় যাব। আমার একটি বই বেরিয়েছে। তিনটি উপন্যাস নিয়ে একটি বই।’ এর চেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে? কামাল ভাই বাংলাদেশের প্রবীণ সাংবাদিক, সংবাদ, প্রথম আলো কাগজে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ২০১২ থেকে ২০২০ সাল ‘কালের কণ্ঠ’ নামক কাগজে নির্বাহী ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করে এখন নিজের সংবাদপত্র করেছেন। ঢাকাপ্রকাশ। অনলাইন সংবাদপত্র। অচিরেই প্রিন্ট-এ প্রকাশিত হবে। ভিতরে ভিতরে তাই তাঁর এক বিরাট উত্তেজনা।
মোস্তফা কামাল বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় একটি বিখ্যাত নাম। তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুনাম দিয়েছে তা নয়, পাশাপাশি সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি একজন সফল লেখক। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতায়। ঢাকায় এইভাবে দেখা হবে ভাবিনি কোনওদিন। বিরিয়ানি খেতে খেতে নানা গল্প চলল। বেশিরভাগটাই সাহিত্য বিষয়ে। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার সাম্প্রতিক অবস্থান। একসময় কামাল ভাই বললেন, ‘আমার কাগজে লেখা দিন।’ আমি বললাম, ‘দুবাই নিয়ে একটা বড় লেখা আছে।’
কামাল ভাই বললেন, ‘কত শব্দ?’
বললাম, ‘কুড়ি হাজার।’
বললেন, ‘ত্রিশ হাজার করুন।’
মনের মধ্যে আলো পড়ল যেন। এমনি করে তো কেউ আমাকে বলেনি আগে। বললাম, ‘আচ্ছা। লেখা হলেই আপনাকে জানাব।’
অনেক ধন্যবাদ দিলাম। এর পর তিনি উপহার দিলেন তাঁর ‘উপন্যাস ত্রয়ী’। পরিচ্ছন্ন ছাপা, সুন্দর প্রচ্ছদ। তিনটি উপন্যাস ‘মানব জীবন’, ‘অপরাজিত’, ‘আমি কবি’। একত্রে একটি বই। কামাল ভাইও বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের আন্ধারমানিক গ্রামের মানুষ। আবার বরিশাল! আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনে তার ‘জননী’ উপন্যাসের ইংরেজি ‘দি মাদার’ লন্ডনের অলিম্পিয়া পাবলিশার্স।
এবার ফেরার পালা। অফিস থেকে নিচে নেমে এলেন কামাল ভাই। সিএনজি থামছে না। প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করে এবার কামাল ভাই কিছুটা দূরে একটি দোকানের সামনে সিএনজি দেখে তাতেই আমাকে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কোথায় যাব। এই আন্তরিকতা একটি সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকের কাছে থেকে পাওয়া এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা। আমি পিছন ফিরে এই প্রতিভাবান মানুষটির অফিসে ফিরে যাওয়া দেখলাম। হয়তো ফিরেই তাঁকে কোনও জটিল বিশেষ খবরে মনঃসংযোগ করতে হবে। আজ শনিবার। ঢাকায় এখানের সোমবারের মতো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে দেখি, দল দল ছাত্রছাত্রী বাড়ি ফিরছে বা আড্ডা দিচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ পরেই বইমেলার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

অনেক আগেই ঠিক ছিল। অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেছিলেন, সোজা বইমেলা থেকে রিকশা নিয়ে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে চলে আসবেন। কোন গেটে নামতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবুও ভুল গেটে গিয়ে পরে ফিরে এলাম প্রকৃত প্রবেশদ্বারে। রিকশাটি যেখানে থামাল সেখান থেকে এক গাড়িবারান্দা পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আমরা অবাক। একটি মুক্তমঞ্চ। সেখানে গোল হয়ে বসে আছে অধ্যাপক নাঈমা, ড. গোলাম রহমান (প্রাক্তন অধ্যাপক), বর্তমানে ‘আজকের পত্রিকা’-র সম্পাদক, সুভাষচন্দ্র সিংহ রায় (রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সম্পাদক) এবং ড. আফরোজ সোমা। আছে কবি প্রকাশনীর সজল আহমেদ। সজলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতার কফি হাউসে। আমি ও অনিন্দিতা। আলাপ পর্ব শেষ হতে না হতেই রোবায়েত লাফিয়ে উঠল। তারিক এসে এক লাফে আমাদের মধ্যে বসে পড়ল। তারিক কাল রাতে লন্ডন থেকে এসেছে ঢাকায়। আজ এসে গেছে আড্ডায়। সুভাষবাবু আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের এপারের বইমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছেন। অনিন্দিতার আবৃত্তি দিয়ে সূচনা হল এই মিলন সভা। তার পর রহমান সাহেব কবিতা পড়লেন। তার পরে সোমা কবিতা পড়লেন। বাইরে রাতের অন্ধকার, ভিতরে গোল হয়ে বসে কবিতাপাঠ, নানা দেশের গল্প, দেশের নানান ঘটনা এইসব নিয়ে মশগুল আমরা। সুভাষবাবু খুব সুন্দর বক্তা, অসম্ভব উপযুক্ত যুক্তি ও বিশ্লেষণ তাঁর প্রায় সব বিষয়ে। আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই আলোচনায় আমরা আধুনিক বাংলাদেশের অনেক বড় বড় কৃতির খোঁজ পেলাম, জাতি সমন্বয়ের নানা ব্যবস্থার কথা জানলাম। গোলাম সাহেব মহীশূরে পড়াশনা করেছেন। তার অভিজ্ঞতা শুনলাম, জমাট লন্ডনের গল্প বলল তারিক। অনেক রাত হয়ে গেলে আমরা আবার রিকশা ধরে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এলাম। আজকের এই মজলিশের পর রোবায়েত বলেছে, ‘আর একদিন হবে অন্য পার্টি। সেটা আরও অনেক আন্তর্জাতিক।’ বলে মুচকি হেসেছিল রোবায়েত। তার অভিসন্ধি বুঝিনি সেদিন।
||১২||

বিশ তারিখে নাঈমা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রথমে সূর্য সেন ভবন ঘুরিয়ে দেখাল। সূর্য সেনের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। এবার নাঈমা বলল, ‘পিছনে একবার দেখে নিন।’ আমি পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি বিজ্ঞাপন। দশ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা। বিজ্ঞাপনটি এই রকম:
“বিজ্ঞাপন। ১০,০০০ টাকা পুরষ্কার। এত দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, যে কেহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মোকদ্দমার নিম্নলিখিত ফেরারী আসামীর সন্ধান করিয়া ধরাইয়া দিতে পারিবে তাহাকে দশহাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া যাইবে। এই পুরষ্কার অদ্য হইতে একবৎসর পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। নিম্নে যে ফটো দেওয়া হইল উহা ১৯২৪ সালে লওয়া হইয়াছিলঃ–’’।
তারপর মাস্টারদার ছবির নিচে লেখা:
‘‘নাম– সূর্য্যকুমার সেন ওরফে মাষ্টার দা। পিতার নাম– মৃত রাজমনী সেন। গ্রাম– নওয়াপাড়া। থানা– রউজান। জেলা– চট্টগ্রাম। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, খর্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি কামান, দেশী মিলের সরু-পেড়ে ধুতি, ফতুয়া এবং সার্ট পরিধান করিত। বঙ্গদেশীয় পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনেরাল মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে। তাং ২২শে জুন, ১৯৩২।’’
সারা শরীরের ভিতর দিয়ে শিহরণ বইছে। আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে এই মানুষটির মাথার দাম ধার্য করেছিল ব্রিটিশ? আমাদের ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় এই মানুষটির স্কেচ দেখেছি। তাঁর মাথার যে এত বিপুল অর্থের ছিল সে আন্দাজ এখানে না এলে জানতাম না। আর মনে হচ্ছিল, কোথায় চট্টগ্রাম আর কোথায় ভারতের অন্য প্রান্ত। স্বাধীন ভারতের মানুষ কি জানে এই মাস্টারদার মূল্য?
অধ্যাপক নাঈমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সংস্থার সহ-পরিচালিকা। তাদের সেই সংস্থার হলে নিয়ে এল আমায়। এ এক তীর্থক্ষেত্র। বিদ্বান, গুণী মানুষের ছবি দেওয়াল জুড়ে। এক একজন তাদের নিজের নিজের বিষয়ে বিশ্বনন্দিত অধ্যাপক। পাকসেনারা যে দশজন অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী একসঙ্গে হত্যা করেছিল, তাঁদের দিকে তাকিয়ে মাথা নত হয়। অনেকদিন পর মনে হল, এই বিশাল জাতির সদস্য আমি। এই জন্য গর্বিত। সেখান থেকে আমরা এলাম প্রো-ভিসির অফিস। তাঁর চেম্বারে নাঈমা ঢুকেই সহকারীকে বলল, কলকাতার লেখক ও মেহমান, একবার স্যারের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। প্রো-ভিসি ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল তাঁর সহকারীকে খুব আস্তে বললেন, ‘সামনের চেয়ারে বসতে বলুন, কফি দেন।’ আমি মানুষটিকে দেখেই মুগ্ধ। অত্যন্ত সুপুরুষ, আধুনিক কেতাদুরস্ত পোশাকে ঘর আলো করে কাজ করেছেন, যেন এক তপস্বী। একের পর এক ফাইল এসে হাজির হচ্ছে তাঁর টেবিলে। নিমগ্ন হয়ে ফাইল দেখছেন। দেখতে দেখতে একবার মুখ উঁচু করে বললেন, ‘আর পাঁচ মিনিট। খুব চাপ। কফি খান।’ আমি অভিভূত হয়ে তাকিয়ে মাথা নাড়ালাম। মাকসুদ কামাল টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট, অত্যন্ত গুণী অধ্যাপক, পরিবেশ সংক্রান্ত অনেক প্রোজেক্টের কর্ণধার। আমরা তাঁর ঘরে নানা কাজে আসা মানুষের ভিড় দেখছি। বাংলাদেশের নানা প্রান্তের কলেজ থেকে আসা মানুষ, কান পাতলেই বোঝা যায়। একসময় চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের পরিচয়পত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘একটু দেরি করিয়ে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। পরীক্ষা চলছে তো, তাই খুব চাপ।’ বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ‘আপনার আপয়েনমেন্ট না নিয়েই তো এসেছি। সময় লাগবে জানি।’ মাকসুদ সাহেব বললেন, ‘না না, যখন খুশি চলে আসবেন। আমার দরজা সব সময়ই খোলা। কোনও আপয়েনমেন্টের দরকার নাই।’ বলে আহ্বান করলেন, ‘আসুন আমরা একটি ছবি তুলি।’ তাঁর সহকারীকে আদেশ করলেন, ‘আমাদের তিনটি ছবি তুলুন। আমাকে একটা পাঠাবেন। ভুলবেন না যেন।’ নাঈমার মোবাইলে সেই ছবি ধরা রইল। তারপর নিজের চেয়ারে বসে নানা ব্যাপারে গল্প করলেন পাঁচ মিনিট। শেষে আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আর একবার কফি?’
নাঈমা বলল, ‘না স্যার, অনেক লোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা আসি।’ বলে বিদায় নিলাম। আমার মানসপটে এক গুণী মানুষের নিরহংকারী ব্যবহারের উদাহরণ হয়ে রইলেন মাকসুদ সাহেব। বাইরে বেরিয়ে নাঈমাকে বললাম, ‘কী সুন্দর মানুষ!’
নাঈমা বলল, ‘মানুষটি দেখতে যেমন, তেমনই স্বভাব। এত গুণী মানুষ যে কী বলব। উনিই হয়তো ভিসি হবেন।’ তাঁর চেম্বারের পাশ থেকে আমারা এবার প্রোক্টরের অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলাম। নাঈমা আমাকে শিখিয়ে দিল, ‘দাদা, প্রোক্টর একুশের অনুষ্ঠানের চিফ। আমি আলাপ করিয়ে দেব। আপনি দুটো পাসের কথা অনু্রোধ করবেন। দিলে তো খুব ভাল হয়। তবে সময় খুব কম।’ পাস মানে একুশের শহিদ মঞ্চে পুষ্প অর্পণের সময় আমন্ত্রিত অতিথি। সে এক বিরল সুযোগ। ঘরে ঢুকে দেখি নাঈমা আগেই বলে রেখেছে। ড. এ. কে. এম গোলাম রাব্বানি বসে আছেন। তাঁর চারপাশে বেশ বড় সহ-পরিচালকের দল। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁদের নিয়েই গঠিত একুশে ফেব্রুয়ারির বিধি, নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব। ঠিক রাত বারোটায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ফুল দেবেন ভাষা আন্দলনের স্মৃতিসৌধে। তার প্রস্তুতি প্রায় সব শেষ। রাব্বানি সাহেব ঘন ঘন ফোনে বলছেন তার প্রস্তুতির কথা। তাঁর হাতে এই বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। নাঈমাকে বললাম, ‘এখন না এলেই ভাল ছিল। উনি খুব ব্যস্ত তো?’
নাঈমা বলল, ‘দেখি না পাঁচ মিনিট। উনি জানেন আমি আপনাকে নিয়ে আসব।’ আমাদের দেখেই ইশারায় সোফায় বসতে বললেন। নাঈমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কথা বলল।
কাজের এক ফাঁকে আমাদের ডেকে নিলেন। বললেন, ‘আজ খুব চাপের দিন। বসিয়ে কফি খাওয়াতে, গল্প করতে পারছি না বলে খুব দুঃখিত। যদি কিছু দিন থাকেন, অন্য একদিন চলে আসুন বিকেলে দিকে। একটু হাল্কা থাকে। প্রফেসার নাঈমা আমাকে বলেছে আপনাদের কথা।’ আমি ধন্যবাদ দিলাম। বললেন, ‘প্রবলেম কি জানেন, আপনারা কলকাতার হলেও বিদেশি। বিদেশিদের পাস দেবার অনেক প্রসিডিওর আছে, পরীক্ষা আছে, সে সব করার মতো সময় আর নাই। তাই খুব দুঃখিত। পরের বার আগে আসবেন।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, সে তো বটেই। এই সময়ে ওসব করা সম্ভব নয় বুঝেছি।’ রাব্বানি সাহেব বললেন, ‘ঠিক তাই। তবে আপনারা সকালে দশটার সময় শহিদ স্থলে আসবেন। দেখতে পাবেন।’ ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় নাঈমাকে বললাম, ‘তুমি বলে রেখেছ, এই ব্যস্ততার মধ্যেও ঠিক মনে রেখেছেন?’
নাঈমা বলল, ‘ওঁর সব মনে থাকে। রাত অব্দি কাজ করেন। দেখেছেন কোনও ক্লান্তি নেই। সর্বদা হাসছেন?’
আমার মাথার মধ্যে ‘বিদেশি’ শব্দটা লাট্টুর মতো ঘুরে চলেছে। কাঁটাতার সেই তো পড়ে আছে সীমান্ত জুড়ে। ভাগ হয়ে গেছি আমরা। আট ঘণ্টার যেতে-আসতে, তাই বিদেশ। আর ভারতের অন্য প্রান্ত পৌঁছতে দুদিন দুরাত লাগে ট্রেনে। ক’জন মানুষ, রাজনীতি করেছে বলে মেনে নিয়েছিল দেশভাগ বা মত দিয়েছিল ইংরেজের চালাকিতে। তারা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। আর তার ফল ভুগছে পরের পর প্রজন্ম।
||১৩||

রাত বারোটায় টেলিভিশন দেখছি। একুশের মানুষ-প্রবাহ। প্রথমে রাষ্ট্রপতি, পরেই প্রধানমন্ত্রী ফুলের গোলাকার মালা শহিদস্তম্ভের পায়ের নিচে রেখে শ্রদ্ধা জানানোর পর মানুষের ঢল। একে একে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মালা দেবার পালা। কোনও বিশৃঙ্খলা নেই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের মতো এই দেশের মানুষ একে একে মালা নামিয়ে রাখছেন শহিদদের পায়ের কাছে। ধীরপায়ে ছেড়ে যাচ্ছেন মণ্ডপ। এই দলে যেমন দশ বছরের বালক আছে, তেমনই আছেন সত্তর বছর বয়সের মানুষ। ধৈর্য্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে একে একে এগিয়ে আসছেন। একটি জাতির ভিতর কতখানি শ্রদ্ধাবনত চিত্ত থাকলে এই দৃশ্য সম্ভব। এই নিয়মনিষ্ঠা দেশটিকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে অল্প সময়ে।
দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। পরদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ‘স্বনন’-এর অনুষ্ঠান। এখানেও মুক্তমঞ্চ। কর্ণধার অধ্যাপিকা রূপা চক্রবর্তী। সঙ্গে নাজমুল আহসান। সকালের গাছের পাতার আড়াল দেয়া নরম আলোয় একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। যে যেখানে পারছেন বসে পড়ছেন। একসময় জনসমাগম সন্তোষজনক হলে অনুষ্ঠান শুরু হল। এ যেন মুক্তমঞ্চ মিলনায়তন। অনিন্দিতার এখানে কবিতা করার কথা। এখানেই দেখা হল আবার ভাস্বরবাবুর সঙ্গে। অনিন্দিতাকে বললেন, ‘আপনার আবৃত্তি শুনে বাড়ি ফিরব।’ ভাস্বরবাবুর আবৃত্তির পরে পরেই সংবর্ধনা জানানো হবে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি বাংলদেশের একজন আবৃত্তিকার ও কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। তিনি একবার একুশে পদকে সম্মানিত হয়েছেন এবং পদক নিয়েছেন গতকাল মাতৃভাষা মিলনায়তনে।

জয়ন্তবাবু স্টেজে উঠে দাঁড়ালেন আর তারপর এক অভাবনীয় দৃশ্য। দেখি এক এক ঝুড়ি ফুল এনে তাঁর মাথার ওপর ঢেলে দেওযা হচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি ফুলের ঝর্নায় স্নান করছেন এই পুণ্য সকালে। এই দৃশ্য, এমন সম্মানজ্ঞাপন পদ্ধতি আমি কোনও দিন আগে দেখিনি। মুগ্ধ হয়ে গেছি। কোনও মালা পরানোর হিড়িক নেই। একে একে এসে মাথায় ঢেলে দিচ্ছেন ফুলের চুবড়ি। আর জয়ন্তবাবু হাতজোড় করে ভালবাসায়, আনন্দে প্রতিটি মিনিট উপভোগ করছেন। তার পর তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখি ভাস্বরবাবুর সঙ্গে। এর পর আবার কবিতা।
এক ফাঁকে আলাপ হল বাংলা একাডেমীর নিপু ভাইয়ের সঙ্গে। কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর পিছনে বন্ধুদের সঙ্গে বসলেন। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি চলছে এই মরমী সকালে। এর মাঝে একবার ভাস্বরবাবু উঠে গিয়ে বলেও এলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা ফল হল না। যারা উপস্থাপনায় ছিলেন তাদের হাতে লম্বা লিস্ট। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন, তাই ঠিক করতে পারছেন না। মহাফাঁপড়ে পড়েছেন তারাও। একসময় আনিন্দতার ডাক পড়ল। তার কবিতার পর অনেকে তাকে অভিনন্দন জানালেন। ভাস্বরবাবুও বাড়ি ফিরলেন। আমরাও অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি, অনিন্দিতা ও নাঈমা হাঁটতে হাঁটতে আবার হলের দিকে ফিরি। সকাল থেকে অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়েছি। এবার বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে শহিদবেদি।
তখন একুশের বিকেল ছ’টা। তখনও পা ফেলার জায়গা নেই শহিদস্তম্ভের চত্বরে। এখন মানুষ দলে দলে আসছেন, ফুল দিচ্ছেন, সেলফি তুলছেন, ছবি তুলছেন, জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে-সেখানে। আমরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেয়ে ফুল দিলাম। বেদির সামনে তখনও ফুল রাখবার জায়গা নেই পাদমূলে। এখন মানুষ আসছেন বেশি, জায়গা খালি হচ্ছে কম। ফলে মাঝে মাঝেই ভিড় হয়ে উঠছে। আমরা খুব বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না। বেরিয়ে এলাম জনাকীর্ণ চত্বর থেকে। শান্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চারিদিকে। বাইরে বেরিয়ে আবার আমরা রিকশা নিলাম। আর মনে পড়ল গতকাল রাত বারোটা থেকে মানুষের মিছিল চলছে। এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।
এর মধ্যে শিবরাত্রি এসে পড়েছে। অনিন্দিতা খোঁজ নিতে আরম্ভ করল, কোথায় শিবমন্দির আছে? হাসান সাহেব বললেন, জগন্নাথ হলে চলে যান। সামনেই। এক বিকেলে আমরা জগন্নাথ হলে ঢুকে পড়লাম। গা শিরশির করছিল এই মহান পুণ্যভূমিতে পা রেখে। ১৯৭১-এর ২৫-এ মার্চের পাকিস্থানি সেনাদের ধ্বংসলীলায় রক্তাক্ত হয়েছিল এই জগন্নাথ হল। এই হলটি হিন্দু, মাইনরিটি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ছাত্র ও অনেক অধ্যাপকের বাসস্থান ছিল। রাতের অন্ধকারে নিধন হয়েছিল নিষ্পাপ প্রাণ। আবার বাসভবনে হত্যা করা হয়েছিল অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও গোবিন্দচন্দ্র দেকে। ইতিহাসের পাতায় এই অধ্যায় নিন্দার ও লজ্জার। সেই জগন্নাথ হলের ভিতরে গিয়ে দেখি একটি মাঠের মধ্যে মন্দির, মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গ। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক মানুষের ভিড়। তরুণতরুণী, মধ্য বয়সের মানুষ, বয়স্কা মহিলাও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শিবলিঙ্গে দুধ ঢালবেন। মন্দিরের সিঁড়ি থেকে লাইনটি নিচে অনেকটা এগিয়ে এসেছে, প্রায় মাঠের শেষপ্রান্তে। অনিন্দিতা লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আস্তে আস্তে সময় এলে মন্দিরের ভিতরে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ কানে এল। মূর্তির সামনে দেখলাম একে একে শিবরাত্রির পুজো হচ্ছে। আমরা যে ঢাকায় আছি, মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আমাদের বেহালার কোনও মন্দিরে দুধ হাতে লাইনে। একটি মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?
উত্তর দিলাম, ‘কলকাতা থেকে এসেছি।’
মেয়েটি একটু হেসে বলল, ‘আমার পিসি থাকে কলকাতায়। আমরা প্রতি বছর যাই।’
‘কলকাতার কোথায়?’
‘চন্দননগর।’ বলেই বোধ হয় খেয়াল হয়েছে আমরা কলকাতার, তাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, ‘ঠিক কলকাতা নয়। কলকাতার কাছেই।’
সেই মেয়েটি অনিন্দিতার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। পুজো করতে সাহায্য করল। আমরা রাতে জগন্নাথ হল দেখলাম। বসবাসের জন্য চারটি বিল্ডিং আছে জগন্নাথ হলে। গোবিন্দ চন্দ্র দেব বিল্ডিং, সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন (নতুন), অক্টোবর মেমোরিয়াল বিল্ডিং ও জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা বিল্ডিং। জগন্নাথ হল থেকে আমরা বেরলাম তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা।
||১৪||

আমার প্রকাশিত তিনটি বই সঙ্গে আছে। তার একটি সেট বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর জেনারেল ও জাতীয় কবি নূরুল হুদাকে দেব। কিন্তু প্রথম যেদিন বাংলা একাডেমীতে যাই, সেদিন তিনি একুশের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কখন অফিসে আসবেন বলা মুশকিল। তাঁর সহকারী জানিয়েছিলেন, আজ একবার চেষ্টা করতে। ‘ওঁর সকালেই অফিসে আসার কথা। একবার চান্স নিয়ে দেখবেন। যদি দেখা করেন তো ভাল। মনে হয় করবেন। তবে তিন থেকে পাঁচ মিনিট। তার বেশি সময় দিতে পারব না। মনে রাখবেন।’
সেইমতো এসে গেছি বাংলা একাডেমীতে। সঙ্গে তিনখানি বই। অফিসে পৌঁছে শুনলাম, এখনও আসেননি। ‘তবে বসুন। এসে যাবেন।’
বসে আছি, আমার সঙ্গে এক মহিলা বসে আছেন। স্তব্ধ চারিদিক। নানান পত্রিকার কপি উলটেপালটে দেখছি। আমার সামনে হুদা সাহেবের আগের প্রধানদের ছবি দেওয়ালজুড়ে। হঠাৎ তাঁর সহকারী এসে বললেন, ‘একটু বসুন। আমি ভিতরে ডেকে নেব। উনি আসছেন।’ দেখতে পেলাম কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকে গেলেন হুদা সাহেব। মিনিট পাঁচেক পর তাঁর সহকারী আমার সামনের ভদ্রমহিলাকে ডেকে নিলেন। আমি বসে আছি বাইরে।
ভাবছি, এত বড় মাপের কবি ও পদাধিকারী বেশি সময় নেবেন না। আমার ডাক আসবেই। যেখানে বইয়ের প্রথমে তাঁর নাম লিখেছি, তার বানানের সঙ্গে চেম্বারের বাইরের নামের বানানের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। যাতে কোনও ভুল না হয়। মিনিট তিনেকও পার হয়নি, ডাক পড়ল আমার। আমার সময় ঠিক এমনই হবে। ভেবে ভিতরে ঢুকতেই হুদা সাহেব হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন তার ডান দিকে বসতে। আমি পরিচয় দিতে তিনি তখন আমার পাশেই বসা মহিলার পরিচয় করিয়ে বললেন, ‘ইনি কনকচাঁপা চাকমা, খুব উঁচু মাপের চিত্রশিল্পী। সময় পেলে ওঁর স্টুডিও একবার ঘুরে যাবেন। ভাল লাগবে।’ প্রতিনমস্কার করতেই তিনি তাঁর কার্ডটি আমাকে এগিয়ে দিতেই আমি আমারটি বিনিময় করি। তারপর আমার বই তিনটি দেখলেন। আমাকে বললেন, ‘আপনার মোবাইলটা আমার সহকারীকে দিন।’ আমি এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর চেয়ার ছেড়ে বইগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, ‘চারটে ছবি নাও।’ সেইমতো ছবি বন্দি হয় গেল আমার কামেরায়। নিজের চেয়ারে বসে প্রতিটি বইয়ের পাতা উল্টে দেখে বাম দিকে রাখা নিজের ব্যাগে গুছিয়ে রাখলেন। তার পর বললেন তাঁর জীবনের কথা, কোভিডকালে তিনি প্রায় সাত কোটি মানুষের চিকিৎসা করেছেন। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, তাই সেই চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বললেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ‘আমি অনেক বার কলকাতা গেছি। ভাল লাগে।’ এবার তিনি পাশে বসা চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমরা খুব কাছাকাছির মানুষ। আপনি চট্টগ্রামের ভাষা বোঝেন?’
আমি অসহায়ের মতো করে বললাম, ‘না। একদম বুঝি না।’ এবার প্রায় আমার ক্লাস নেওয়া শুরু হল। বললেন, ‘শুনেন, এই ভাষার মতো ভাষা পৃথিবীতে নাই।’ বলে তিনি এক একটি বাক্য বলেতে লাগলেন আর তার সরল বাংলা করলেন। আমরা তিনজনেই হো হো করে হাসি। খুব মজায় মেতে ওঠেন হুদা সাহেব। আমরা অনেকক্ষণ চট্টগ্রামে ছিলাম, এবার ঢাকায় ফিরে এলাম। তারপর বলেন, ‘এবার শেষ করা যাক। আমাকে মেলে যোগাযোগ রাখবেন।’ তখন ঘড়িতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। তাঁর সহকারী আমাদের দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘কী ব্যাপার বলুন তো! পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলে আমি বকা খাই, আর আজ? বলেছিলাম, বেশি সময় নেবেন না?’
বললাম, ‘আমরা নিইনি। ওঁর কথা শুনছিলাম। উনি বলছিলেন।’ আমার সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলা বললেন, ‘ঠিক বলছেন। আমরা চুপচাপ শুনছিলাম।’ আমি বাইরে দেখি নাঈমা এসেছে। আসবে বলেছিল কিন্তু আগে আসেনি। আবার ভিতরে গেলাম। নাঈমাকে রেখে বাইরে এলাম। নিচে নিপুর ঘরে গেলাম। ফোনেই কথা বলছিলেন। একসময় ফোন ছেড়ে বললেন, ‘বসের সঙ্গে দেখা হল?’ বললাম, ‘হল। প্রায় পঞ্চান্ন মিনিট ওঁর ঘরে ছিলাম।’ প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠার অবস্থা। ‘বলেন কী? আমরা পাঁচ মিনিট সময় পাই না। আপনি তো খুব ভাগ্যবান।’ বললাম, ‘কী জানি। তবে অনেক গল্প হল।’
এবার নিপু ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতার অনেক গল্প হল। নিপু ভাই কলকাতায় মাঝে মাঝেই আসেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে। খুব মিশুকে মানুষ, সদা চঞ্চল, গভীর চোখ, দেখলে বোঝা যায় দায়িত্বশীল মানুষ। তাঁর পরিচিতি আমরা জানি, তাঁর কাজের জন্য তাঁর খ্যাতি। সেকথা অনেকের মুখে শুনেছি। বাংলা একাডেমীতে মানুষের সঙ্গে মিশে কেন যেন প্রগাঢ় তৃপ্তির স্বাদ পেলাম। এখানে আড়ম্বরের চন্দ্রিমা নেই, আত্মম্ভরিতার ফোলানো সামিয়ানা নেই, নিয়মকানুনের অহেতুক চোখরাঙানি নেই। মানুষকে সাদরে আবাহন করে, মূল্য দেয় ও সম্মান করে। এই না হলে কি ভাষার প্রতি ভালবাসা হয় জাতির ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের?
||১৫||

বইমেলায় ঢুকে পড়লে আর কোনও কিছুই মনে থাকে না। চারিদিকে মানুষ আর বই। আমরা দুজনে অনেকগুলো বইয়ের দোকানে বিচিত্র বই ও স্টলের ডিজাইন দেখে মুগ্ধ। ‘পাঠক সমাবেশ’ নামের একটি স্টলে দেখি একজন ছেলে পরের পর রশিদ কেটে যাচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে নানা বিযয়ের বই। প্রতিটি প্রকাশকের ঘরে নানান ধরনের বই। কবিতার বই প্রায় সকলের আছে। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়; ভ্রমণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম সব বিষয়ের পাঠক আছে এই দেশে। শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার দেখলে চমকে যেতে হয়। কলকাতার প্রকাশকের বই এখানে নেই। কেননা পশ্চিম বাংলার বই বাংলাদেশের প্রকাশক যদি প্রকাশ করেন তবে মেলায় বিক্রি হতে পারে। না হলে আদেশ নেই। যদিও বাংলাদেশের প্যাভেলিয়ন হয় আমাদের কলকাতা বইমেলায়। সেখানে বাংলাদেশে অনেক বিখ্যাত প্রকাশক অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় বাংলাদেশের বইয়ের খুব চাহিদা, আমি নিজে চোখে দেখেছি। আসলে বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্যাভেলিয়ন নেয়। পশ্চিমবঙ্গ দেশ নয়। সে ভারতের হয়ে প্যাভেলিয়ন করতে পারে না। এখানেও সেই রাজ্য ও দেশের সম্পর্ক। ভিতরটা চিনচিন করে। কিন্তু উপায় নেই। চোরাগোপ্তা যে নেই তা নয়। কিন্তু প্রায়ই মেলা কর্তৃপক্ষ টহল দেয়, বই চেক করে। ধরা পড়লে শাস্তি অনিবার্য।
এখানেই আলাপ হল একদল তরুণ কবি, গল্পকার, উপন্যাসিকের সঙ্গে। একে একে এসে হাজির জলধি প্রকাশনার এক পাশে। নাহিদা আলাপ করিয়ে দিল কবি শাহিদা মিল্কি, গল্পকার ইসরাত জাহান, কবি ও গল্পকার মোস্তাফা মোহাম্মদ, কথাসাহিত্যিক জয়দীপ দে ও আরও অনেকে। একফাঁকে কবি লিলি হক ঘুরে গেলেন তার ছেলের প্রকাশনার স্টল ছেড়ে। আমরা একে অপরের বই বিনিময় করলাম। দেখলাম এখানে একজন অক্ষরকর্মীর লেখা বই অন্য অক্ষরকর্মী কেনেন, পড়েন এবং মতামত জানান। এটা কলকাতায় খুব একটা দেখা যায় না। এই সব আলোচনার মধ্যে তাদের বর্তমান জীবনের খোঁজখবর নেন অনেকে। ক্রমে আড্ডা জমে উঠল। নাহিদা এখানেই বলল, ‘দাদা, কাল কবিতা কাফেতে চলুন। সবাই যাবে। মেলার পর ওখানে সামান্য খাওয়া আছে। আপনার তো বাড়ি ফেরার তাড়া নাই।’
‘না। তা নেই।’
‘তয় চলুন।’
বইমেলায় সেদিন মাত্রাতিরিক্ত ভিড়। এই ভিড়ের দিন কলকাতা বইমেলায় মানুষের হাতে ব্যাগ থাকে কম। এখানে চলমান বইসন্ধানীদের প্রায় প্রতি হাতে বইয়ের ব্যাগ। জলধির স্টলেও বেশ বিক্রি হচ্ছে। আমি একফাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম নাহিদাকে। তোমার পত্রিকার নাম বা প্রকাশনার নাম ‘জলধি’ রাখলে কেন?
একমুখ হেসে নাহিদা বলল, ‘অনেকেই এই প্রশ্নটা করে দাদা। তোমার মনে এসেছে?’
‘হ্যাঁ।’
নাহিদা বলল, ‘‘ডি. এল. রায় প্রতিষ্ঠিত জলধর সেন সম্পাদিত ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার কথা মনে আছে? ১৯১৩-তে শুরু করে একটানা চব্বিশ বছর সম্পাদনা করেছিলেন জলধর সেন। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার প্রথম প্রচ্ছদ করেন শিল্পী দ্বিজেন্দ্রনাথ গোস্বামী। চিত্রটি ছিল এক নারীর, যার মাথায় মুকুট, হাতে শস্যগুচ্ছ, গলায় সাতনরী হার। বামদিকের একটু উপরে সূর্যাস্তের চিত্র। ফেনিল জলরাশি থেকে সিক্ত বসনে যেন উঠে আসছেন ভারতমাতা। ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ/ সেদিন বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।’
এ ছাড়াও তুমি জলধি শব্দের উল্লেখ পাবে, কাজি নজরুলের ‘সিন্ধু হিল্লোল’ কবিতায়, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে। প্রথম সর্গেই এতবার ‘জলধি’ শব্দটি আছে যে গুনে শেষ করা শ্রমসাধ্য। এছাড়া আছে জীবনানন্দ ও অনেক নমস্য কবিদের কবিতায়। একটা কথা এ অবধি এসে না বললেই নয়। জলধি সাহিত্য পত্রিকার শুরুতেই কয়েকটি সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে নিয়েছিলাম পাকাপোক্তভাবে। তা হল, আমার লেখকসত্তাকে যেন সম্পাদক-সত্তার সাথে গুলিয়ে না ফেলি। সেজন্যে জলধি পত্রিকায় সম্পাদকীয় ছাড়া আমার কোনও লেখাই কখনও ছাপা হবে না। জলধি অনিয়মিত প্রকাশ হোক, সমস্যা নেই। লেখকের লেখকসম্মানী যেন অনিয়মিত না হয়। জলধি সংখ্যার বিচারে নয়, মানের বিচারে যেন এগিয়ে যায়। এভাবেই জলধির সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে জলধির পথচলা।
আমি কথা শুরু করেছিলাম ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকাটি দিয়ে। সম্পাদক জলধর সেন সেদিন জানতেন না শতবর্ষ পরে কেউ তাঁর পত্রিকাটির কথা উল্লেখ করে তার পত্রিকার নামকরণ করবে? আমি স্বপ্ন দেখি, একশত বছর পরে কেউ একজন ঠিক এমন করেই জলধির কথা লিখবেন।’’
আমি মুগ্ধ হয়ে নাহিদাকে দেখি। একটি লিটল ম্যাগাজিনের নামকরণের পিছনে তার চিন্তার পরিসর শুনে অবাক। আমিও একসময় লিটল ম্যাগাজিন করেছি। নাহিদার কথা শুনতে শুনতে জেনে অবাক হয়েছি আজকের দিনেও, বাংলাদেশে সেই এই প্রতিবন্ধকতা সামলে করতে হয়। উদাসীনতা, আর্থিক অসহযোগিতা, গুরুত্বহীনতা এই লাস্ট পাঁচ দশকে না বদলেছে এখানে, না বাংলাদেশে। তবু নাহিদার মতো লেখক, সম্পাদক সব ছেড়ে লিটল মাগাজিনের পাশে দাঁড়ায়। নতুন লেখক তৈরি করে, উৎসাহ দেয়, বুকের ভিতর থেকে উৎসারিত সাহিত্যচেতনাকে বিনাশর্তে প্রকাশ করে তাদের পত্রিকার পাতায়। একদিকে জন্মযন্ত্রণা ও অন্যদিকে প্রকাশের আনন্দ আর কোনও শিল্পে আছে কিনা জানা নেই। নাহিদাদের এখানেই জিত।
||১৬||

দিনটি শুরু হল ভোর ছ’টায়। নাঈমা বলে রেখেছিল গাড়ি আসবে। বেড়াতে নিয়ে যাবে নাঈমা। পূর্বাচল। আন্তর্জাতিক হলের বাইরে এসে দেখি সামনের লেন ধরে একটি গাড়ি ঢুকছে। আমরা গাড়িতে ঢোকার আগেই নাঈমা আলাপ করিয়ে দিল তার ভাই ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে। তিনি স্টিয়ারিংয়ে বসে ভোরের ঢাকার টুকরো টুকরো বর্ণনা দিতে দিতে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকার জনবহুল এলাকা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম। নাঈমা বলল, নতুন ঢাকা দেখেন দাদা। একের পর এক নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে একদিন নতুন ঢাকা আধুনিকতায় সেজে উঠবে। রাস্তার দুপাশে জনবসতির জন্য প্লট বিক্রি হয়েছে অনেককাল আগে। কাজ হয়নি। আবার কাজ শুরু হয়েছে। অনেকটাই নতুন উপনগরী।
ঘণ্টাখানেক পরে আমরা এক নদীর কাছে পৌঁছলাম। নৌকার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে দুটো বড় স্টিমার। নাঈমা বলল, এই শীতলক্ষ্যা। আমাদের সঙ্গে আছে নাঈমার ছেলে। সেই আমাদের পথপদর্শক। আমরা একটি স্টিমার ডেকের ওপর উঠলাম। বিস্তৃত জলরাশি, দূরে, অনেক দূরে ছোট ছোট গ্রাম, মাঝিমল্লাদের চোখে পড়ছে। এই নদী ব্রহ্মপুত্র নদের থেকে বের হয়ে তারই সমান্তরালভাবে বয়ে গেছে বাংলাদেশে। নারায়ণগঞ্জে এর পাশ দিয়ে পূর্ব ঢাকার পাশ দিয়ে গিয়ে মিশেছে ধলেশ্বরী নদীটির সঙ্গে। আমার রবীন্দ্রনাথের ‘কিনু গোয়ালার গলি’ কবিতার কথা মনে পড়ল। এখান থেকে স্টিমার ভাড়া করে সারা দিন নদীবক্ষে ঘুরে আবার ফিরে আসা যায় ঢাকায়। এই ভ্রমণের কথা আমাদের আগে জানা ছিল না। আমরা অনেকক্ষণ এই ঘাটের আশেপাশে ঘুরে বেড়ালাম। সকালের নদীর ঘ্রাণই আলাদা। নদীর উপর তখন কুয়াশার হাল্কা পর্দা। এর পরের বার এলে ঢাকা থেকে বুক করে আসব। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াব শীতলক্ষ্যায়।
দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে আবার বইমেলায়। আজ আলাপ হল একুশে পদক-প্রাপ্ত জয়ন্ত চট্টোপাধ্যাযের সঙ্গে। একটি স্টলে বসেছিলেন তিনি। অনিন্দিতা ও আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প করলেন। বই কিনলাম তাঁর। আবৃতি করলেন তাঁর দুই কবিতার বই ‘আমি’ ও ‘স্বল্পকথা কল্পকথা’ থেকে। ক্রিয়েটিভ ঢাকা পাবলিকেশনের এই দুটি বই অনন্য পরিবেশনা ও নতুন আঙ্গিকের কবিতা। তার মাঝে মাঝে মজার মজার কথায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন এই স্মরণীয় সন্ধ্যা।

রাতে নাঈমার নেমন্তন্ন ছিল ধানমন্ডির স্টার রেস্তোরাঁয়। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন নাঈমার বিচারক স্বামী জেলা জজ শরীফ লুৎফর রহমান। তিনি খুব মজার মানুষ। তিনি বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে ভালবাসেন। সেইমতো অর্ডার দিতে লাগলেন। সঙ্গে বিচারকের মতো আদেশ করতে লাগলেন, কীভাবে পরিবেশন করতে হবে। ফলে খুব আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। খেতে খেতে তিনি দেশের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে নানান গল্প করছিলেন। আমরা বাংলাদেশের এই সব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক পরিবর্তনের কথা শুনিনি।
||১৭||

রুবায়েতের আমন্ত্রণ ছিল বিশেষ পার্টির অনেকদিন আগে থেকেই। আমি আর অনিন্দিতা সন্ধে হতেই রিকশা নিয়ে হাজির হলাম অধ্যাপক শান্তনু মজুমদারের বাসায়। ইউনিভার্সিটির উল্টো দিকেই একটি মনোরম আবাসনের মধ্যে তার ফ্ল্যাট। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না এত বড় এলাকা জুড়ে এই অধ্যাপকদের বসবাস। ভিতরে ঢুকে দেখি রুবায়েত এসে গেছে। আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ করল শান্তনু। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। লন্ডন ইউনিভার্সিটির পিএইচ. ডি। আমরা এসে বসলাম একটি বিরাট হলঘরে। শিখা, শান্তনুর স্ত্রী তখনও বাড়ির বাইরে। আস্তে আস্তে এসে পড়ল তারিক, আফরোজ শোমা, রহমান স্যার। কানাডাবাসী শিউলি ও তার ছেলে, কলম্বোয় অবস্থিত বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাট আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক।
এমন সময় প্রায় ঝড়ের মতো বাড়িতে ঢুকল শিখা। আমাদেরকে দেখেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, একটু কাজে আটকে গেছিলাম। কোনও অসুবিধা হয়নি তো? ততক্ষণে শিউলি ঘরের এক কোণে বসে আপনমনে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে চলেছে। শিউলি কানাডায় থাকে কিন্তু তার কথা ও গান শুনে মনে হচ্ছে, সে শান্তিনিকেতন থেকে এইমাত্র নেমেছে। আর তার ছেলের কেন জানি আমাকে খুব ভাল লেগে গেছে। বার বার বলছে, ‘সুতপনমামা, তুমি আমার কাছে এসো।’ পানীয় লন্ডন থেকে এনেছে তারিক। সেই উপলক্ষে আজকের পার্টি। প্রাথমিক গানের পর গল্প শুরু হল। কোনও বিশেষ গল্প নয়, সবই এলোমেলো। যে যেমন পারছে বলে চলেছে তাদের দেশের গল্প, সাম্প্রতিক ঘটনা, তাদের প্রভাব এইসব। একসময় কবিতায় পেয়ে বসল। কবিতা পড়লেন আফরোজ শোমা, রহমান সাহেব পড়লেন তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা, অনিন্দিতা আবৃতি করল। রাত ক্রমে জমে উঠেছে। তুমুল আড্ডা ও ঢাকার গল্প হচ্ছে। রুবায়েতও মজার মজার গল্পে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।
আমি একফাঁকে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠল। রাতের অন্ধকারেও বাইরে নানা গাছের সমারোহ বোঝা যায়। পাখিটির ডাক শুনে আরও দু-তিনটে পাখি ডেকে উঠল। আমার পাশে কখন একজন এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, আমাদের এই কমপ্লেক্সটা খুব সুন্দর, প্রচুর গাছ, প্রচুর পাখি, অনেক শাকসবজি হয়। বর্ষার সময় খুব সুন্দর দেখতে। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় শিখা আমাদের খাবার খেতে ডাক দিল। যেখানে খাবার জায়গা সেখানে পৌঁছে প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড়। বাইশটা পদ পর পর সাজানো। শিখা বলল, ‘সব নিজে হাতে রান্না করেছি। খেতে হবে কিন্তু।’
‘নিজে হাতে?’ অনিন্দিতা বলেই ফেলল।
‘হ্যাঁ দিদি। জিনিসপত্তর আমার নিজের হাতে কেনা। রান্না আমার নেশা। আমি এই রান্না অ্যান্ড দেশ এত ভালবাসি যে, লন্ডনে আইন পড়া শেষ করে দেশে ফিরে এসেছি।’
আমি অবাক হয়ে শিখার দিকে তাকাই। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দাদা এবার এলে আমার বাড়িতে যত দিন ইচ্ছে থাকবেন। আমার একটা ঘর খালি পড়ে আছে। আমি রোজ রান্না করে খাওয়াব। কোনও চিন্তা নেই। সারা দিন ঘুরে আসবেন। খাওয়ার চিন্তা থাকবে না। আমি খুব খুশি হব।’
আসলে রুবায়েত আমাদের সেই অফারটাই দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু হয়নি। এবার তো মনে হচ্ছে এমন সুন্দর, নিরিবিলি জায়গায় থাকা যাবে। ভাবতেই পারছি না। কিন্তু কে খাবে এত সব? সবাই মিলে যে যা পারল তুলে নিতে লাগল। আমি অল্প খাই রাতে। ফলে যে খাবারটা পনেরো মিনিটে খাই, সেটাই সকলের সঙ্গে একঘণ্টা লাগল। রাত সাড়ে বারোটায় আন্তর্জাতিক আড্ডা শেষ হল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম হলে।
||১৮||

পরের দিন আমরা মেলা-শেষে যে যার মতো এসে হাজির হলাম ‘কবিতা কাফে’-তে।
কবিতা কাফের ধারণাটা নিতান্ত কবি, সাহিত্যিক, আবৃতিকারদের মেলমেশার প্রয়োজন প্রয়াস। আইনজীবী, চিকিৎসকদের ক্লাব আছে, সমিতি আছে, পেশাগত মানুষের মিলনের স্থান আছে, তাহলে অক্ষরকর্মীদের থাকবে না কেন? এই ভাবনা থেকে মেন রাস্তার চৌমাথায় ঢাকা শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে দোতলায় নাহিদার ‘কবিতা কাফে’। ভিতরে ঢুকেই বলে উঠলাম, ‘আমি আর আজ কোথাও যাচ্ছি না।’ আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে প্রতিধ্বনি করল। ঢাকা যাবার আগেই আমি কবিতা কাফের কথা জানি। প্রথমেই মনে হল নিজের বৈঠকখানায় এসে গেছি। আর চিন্তা নেই। বসার কোনও নিয়ম নেই, বই পড়ার কোনও অভাব নেই, বিশ্রামের কোনও অভাব নেই। আর আড্ডা? সে তো সারাদিনই চলতে পারে। এমনই এক পরিবেশে কবিতা কাফে লেখক, কবিদের তীর্থক্ষেত্র। তার সঙ্গে আছে চা ও স্নাক্সের আয়োজন। খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নেওয়া যায়।
আমাদের সামনে একটা লম্বা টেবিল, সেখানেই সবাই একে একে বসে পড়েছে। বইমেলার এক জলধি থেকে আর এক জলধির মধ্যে আমরা সবাই। দূরে একটি বেশ বড় সোফা। তার সামনে দুই পাশে বসার জায়গা। তিন দিকে বইয়ের লাইব্রেরি। এক কোণে কাফের মুখ। সেখানে নানা নোন্তা, মিষ্টি, আধা মিষ্টি বস্তুর পাশাপাশি বসবাস। এখানে আলাপ হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সঙ্গে। আমরা প্রায় বারোজন, উত্তাল করে তুলেছি কবিতা কাফে। নাহিদা আমদের সব ঘুরিয়ে দেখাল। এমনই এক প্রতিষ্ঠান চালাতে নাহিদাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়। কোভিডের সময় নিজের গয়না বিক্রি করে কর্মীদের বেতন দিতে হয়েছে নাহিদাকে। সে কবিতা কাফে-কে ভালবেসে বাঁচিয়ে রেখেছে, নতুন প্রতিভাকে আবিষ্কারের জন্য। প্রবীণ ও নবীনের মেলবন্ধনের জন্য তার নিরলস প্রয়াস। দুই বাংলার প্রায় সব গুণী সাহিত্যকর্মী একবার এখানে ঘুরে গেছেন। নাহিদা আমাদের এই কাফের নানা কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে বলল, ‘এমনই একটা কাফে খুব দরকার ছিল আমাদের। কত মানু্ষ যে এর থেকে উপকার পায় বললে বিশ্বাস করবে না।’ আমি আবার বললাম, ‘আমি কি আজ রাতে থেকে যেতে পারি?’ নাহিদা বলল, ‘অবশ্যই। কাল সকালে টাঙ্গাইল যাব। তোমরা এখান থেকেই নিচে গাড়িতে উঠে পড়বে। এখান থেকেই তো গাড়ি ছাড়বে সাড়ে সাতটায়।’
বললাম, ‘সেটা মন্দ হয় না।’
এর পর কাফের ভিতর থেকে সে একে একে নান, বাটার চিকেন মসালা, শিক কাবাব এনে হাজির করল সকলের জন্য। আমি অবাক হয় জিজ্ঞেস করলাম, ‘এখানে নর্থ ইন্ডিয়া ফুড কোথায় পেলে?’
‘আছে আছে। ঢাকায় সব আছে। আমাদের কাছাকাছি একটা নতুন রেঁস্তোরা খুলেছে। দেখো তো কেমন করেছে?’
আমি নান আর বাটার চিকেন মুখে দিয়ে যেন দিল্লিতে আছি মনে হল। দীর্ঘদিন দিল্লির কালকাজীতে জীবন কাটিয়েছি। এ যেন সেই কালকাজী মার্কেটের রেস্তোরাঁর খাবার।
নাহিদা বলল, ‘দেখলে তো কেমন সারপ্রাইজ দিলাম। ঢাকায় দিল্লির খাবার খাইয়ে দিলাম। ভেবেছিলে?’
বললাম, ‘না। একেবারেই না। সত্যি দারুণ করেছে। পুরো নর্থ ইন্ডিয়ান রেসিপি।’
||১৯||

পরের দিন টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠান। সকালে কবিতা কাফে থেকে যাত্রা।
ইউনিভার্সিটি হল থেকে কবিতা কাফের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়ে দেখি একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কবিতা কাফের নিচে। সেখানে এক আধুনিক সাজসজ্জায় মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে এক ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তারাও টাঙ্গাইল যাবেন। ফোন দিলাম নাহিদাকে। সে রাস্তায়। একসময় গাড়িতে সবাই উঠে পড়লাম। গাড়ি ধানমন্ডি হয়ে টাঙ্গাইলের দিকে মুখ করল। ঢাকা শহরের এই দিকটা বেশ আধুনিক। চওড়া রাস্তা। তার দুপাশে বড় বড় অট্টালিকা। মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর ব্রিজ। জনপদ বিস্তৃত নতুন নগর তৈরি হয়েছে। নাহিদা বলল, ‘এদিকে প্রচুর ফ্যাক্টরি আছে। এইসব কারখানায় প্রচুর লোক কাজ করে।’ বললাম, ‘কই কারখানার শেড দেখছি না তো?’
‘এই কারখানার শেড দরকার নেই। বিল্ডিংয়ের মধ্যেই গারমেন্টস তৈরি হয়। ধনী মানুষের বসতি এই পথের দুপাশে।’ আমাদের সঙ্গে একজন বিদগ্ধ মানুষ মুজতবা আহমেদ মুরশেদ যাচ্ছেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা। তিনি আমার একটু দূরে বসে চুপচাপ। গোটা রাস্তায় মাঝে মাঝে হাসির শব্দ, নানান মজার গল্প চলছে।
শহর থেকে বেরিয়েই সেই অপার বিস্তৃত শ্যামলিমা। চোখ জুড়ানো পল্লিপ্রকৃতি। আধুনিক বাংলাদেশের চওড়া হাইওয়ের দুপাশে ফসলের সমারোহ। এই দেখতে দেখতে একসময় বাঘা সিদ্দিকির কথা উঠল। টাঙ্গাইলের বাঘা সিদ্দিকির গল্প বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কাগজে পড়তাম, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যুদ্ধের খবরে তাঁর নাম বারে বারে উঠে আসত। সেইসব দিনের কথা ইতিহাসের মণিমুক্তোর মতো ভেসে উঠল। বাংলাদেশের আর এক বিখ্যাত নেতা ছিলেন মাওলানা ভাসানী। তাঁর খ্যাতিও ভারতের আন্দোলনকারী জনজাতির কানে পৌঁছে গিয়েছিল সে সময়। সেই টাঙ্গাইল যাচ্ছি। বুকের ভিতর দুন্দুভি বাজছে। যিনি এই যাত্রার আয়োজন করেছেন তিনি কবি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মুস্তাফা উঠলেন সাভার নামের একটি এলাকা থেকে। সেখনেই তাঁর ফ্ল্যাট। রাস্তায় একবার থেমে গেল গাড়ি। জলপানের বিরতি। এখানেই আলাপ হল কবি মুন, আবৃতিকার সুমি, কবি ও উপন্যাসিক মুজতবা মুরশেদের সঙ্গে। মুরশেদ দিনাজপুরের এক বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্র বক্তা, ডিবেট করে ক্যাম্পাস কাঁপানো ছাত্র ছিলেন। আজ প্রায় কুড়ি বছর পরে কবি মুনের সঙ্গে দেখা। আচমকাই। সেও এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। মুন না বললে আমরা জানতেই পারতাম না। আজ তার জীবনের দুই প্রান্তের পথিক। আমরা ইংরেজদের শাসন, দেশভাগ ও বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে অনেকক্ষণ চা সহযোগে মতবিনিময় করলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ এসে গেল অবধারিতভাবে। এক একজনের এক এক মত, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের এই ভিন্ন মতামত এক নতুন গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। মুরশেদকে বললাম, ‘আপনি তো জাপানি হাইকমিশনে উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। নিজের দেশকে সেখান থেকে দেখতে কেমন লেগেছে? মানে নিরপেক্ষ চোখে?’ মুরশেদ সতর্ক হলেন। বোধ হয় আগেও তিনি এই প্রশ্নের সামনে পড়েছেন। তিনি বললেন, ‘একটা নতুন দেশ যেমন হয়। আবেগ ও ভালবাসা মেশানো একটি দেশ।’
নাহিদা যেতে যেতে নানা গল্প করতে লাগল টাঙ্গাইলের। দীর্ঘ পথ। একসময় প্রধান রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের সরু রাস্তা ধরলাম। এক মোড়ের মাথায় মুস্তাফা ভাই গাড়ি থামিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে বললেন। একটু ঢুকেই মুস্তাফা ভাই কাকে যেন চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ডাক্তার মোদকের বাড়ি কোথায়?’ দোকান থেকে উত্তর এল, ‘সোজা এগিয়ে যান। সামনে একটা ওষুধের দোকান, তার ডান দিকে।’ আবার গাড়ি চলতে শুরু করল।
এবারে এখানে আসার কারণটি বলি। টাঙ্গাইল বিভাগের এই গ্রাম নারান্দিয়া। এখানে মিনি বইমেলা আয়োজন করেছে নারান্দিয়া উন্নয়ন পরিষদ। একুশে বইমেলা ২০২৩। ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি। স্থান দৌলতপুর খেলার মাঠ। আমাদের জেলা বইমেলার মতো এখানেও ব্লকের বইমেলা। সেখানে আমরা ভারত থেকে অতিথি, আর ঢাকা থেকে এই বইমেলায় এসেছেন কবি, গল্পকার, সাহিত্যিক ও আবৃতিকার। মুস্তাফা ভাই নিয়ে এসেছেন। নাহিদা আমন্ত্রণ করেছে আমাদের। বলে ছিল, ‘আমরা টাঙ্গাইল যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে চলেন। ভাল লাগবে।’ সেই আসা। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন পঞ্চায়েতের এক কর্মকর্তা। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে আমরা ডাক্তার মোদকের বাড়িতে ঢুকলাম। লম্বা সোফা বসানো, ঘরের তিন দিকে বসার জায়গা, মাঝে একটা টেবিল। আমরা যে যার মতো বসে পড়লাম। পরিচ্ছন্ন বসার ঘর। ডাক্তার মোদকের স্ত্রী সকলকে বললেন, ‘প্রথমে চা দি?’ তারপর কাছে এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, ‘কী খুশি যে হয়েছি আপানারা এসেছেন। খুব ভাল লাগছে। নিজের হাতে খাবার বানিয়েছি। খেতে হবে কিন্তু। সেই কখন ঢাকা থেকে বেরিয়েছেন।’
ডাক্তারবাবু ক্লিনিক থেকে এসে পড়েছেন। তার মুখেই শুনলাম, ঢাকা থেকে মেডিক্যাল পাশ করে এই গ্রামে পোস্টিং হয়েছিল তাঁর। জীবনে প্রথম চাকরি। সেই যে এসেছেন আর কোনও দিন গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবেননি। জিজ্ঞেস করলাম, ‘দেশভাগের সময় যে এত লোক এপার থেকে ওপারে গেল, তবু ইচ্ছে হয়নি?’
‘না। আপনাদের ওখানে আমার সব আত্ময়ি। রানাঘাট, নৈহাটি, ব্যরাকপুর, গড়িয়া, হাওড়া, ধুলাগড়, বাগনান সব ছড়িয়েছিটিয়ে আছে আমার পরিজন। আমি যাইনি?’
‘ভয় করেনি?’
এবার ডাক্তার একজনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, ‘এই যে দেখছেন কাসেমকে। এরাই আমাদের যেতে দেয়নি। বুক দিয়ে আগলেছে। এই গ্রামের আমরা চার ঘর হিন্দু। বাকি সব মুসলমান। কিন্তু ওরাই আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, বিপদে রক্ষা করেছে, আনন্দে দুঃখে সঙ্গ দিয়েছে ও দেয়। আমাদের আর বাইরে যাওয়া হয়নি। আর যাব কেন? এটাই আমাদের দেশ। আপনারা বাইরে থেকে যা শোনেন, তা সব সত্য নয়। এই দেখুন, এখানে থেকেই আমার এক ছেলে চিন দেশে ডাক্তারি পড়ে আর এক ছেলে ইস্কুল ফাইনাল দেবে।’
বললাম, ‘ভারতে বেড়াতে যাননি?’
‘গেছি। বহু বার। আবার চলে এসেছি। কোথাও থাকিনি। আমাদের এই নদীনালার দেশ ওখানে কোথায়? আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন শুনে আমাদের ব্লক সভাপতি বললেন, তা হলে লাঞ্চটা ওনার ওখানেই হবে। আপনারা এখানে প্রাতরাশ করে ওনার ওখানে দুপুরে খাবেন। সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।’ মুরশেদ আমাকে ফিসফিস করে বললেন, ‘এখন বারোটা বাজে। এর পর আবার লাঞ্চ? খেয়েই তো লটকে যাব।’ কথাটা মিথ্যে নয়। রোগাপটকা চেহারা মুরশেদের। খুব যে খেতে পারেন তা নয়। একটাই উপায়, এখনে কম খেয়ে ওখানে লাঞ্চ করার। কিন্তু তা কি হয়? এখানের আয়োজন একে একে আসতে আরম্ভ করল। কাসেম ভাই বললেন, ‘এই যে দেখছেন আমরা ওনার বাড়িতে যে কোনও সময় আসতে পারি। বউদি আমাদের মায়ের মতো। আমরা সবাই একে অন্যের আত্মীয়। এই বন্ধন দেশভাগ ভাঙতে পারেনি। পারবেও না।’
আমার বুকের মধ্যে কোথায় যেন বসন্তের হাওয়া লাগল। দেশভাগের এতদিন পরেও এমন শান্তির দ্বীপ আছে, না এলে জানতে পারতাম না। কাসেম ভাই বললেন, ‘রাজাকাররা এখানে আসেনি ভাবছেন? এসেছে। আমাদের ভয়ে পালিয়েছে। তাই আমাদের গ্রামে কোনও হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, এখানে সবাই নিজেদের মানুষ ভাবে।’ মুস্তাফা বললেন, ‘এটাই বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছে ছিল।’ ততক্ষণে খাবার এসে গেছে। খাওয়ার পর অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। ডাক্তারবাবু আমাদের বিদায় জানালেন। সকলের উদ্দেশে বললেন, ‘আবার আসবেন।’
||২০||

এখান থেকে গাড়ি করে দুপাশে মাঠ মধ্যে রেখে পৌঁছলাম চেয়ারম্যান মাসুদ তালুকদারের বাড়ি। বাড়ির সামনে একটি প্রশাসনের বড় গাড়ি। বৈঠকখানায় তাঁর বিশাল বসার ঘরে সারিবদ্ধ হয়ে বসলাম সবাই। মাসুদ সাহেব এসে আলাপ করলেন, নিজের পরিচয় দিলেন, সকলের পরিচয় নিলেন, তারপর আন্তরিক গলায় বললেন, ‘সব রকমের খাবার আছে। যে যা ভালবাসেন খাবেন। আমি আমার ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছি। সেই এই আহার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবে। আপনারা একে একে ভিতরের ঘরে চলে আসুন।’ এক ব্যাচে সবার হবে না। প্রথম ব্যাচে মেয়েদের ডাক পড়ল। পরের ব্যাচে আমাদের ডাক। দুরকম মাছ, খাসি ও মুরগির মাংস, গোরুর মাংস, মিশ্র সবজি, বেগুন ভাজা, ডাল, ট্যাংরা মাছ, পারশে মাছ, চিংড়ি মাছ, চাটনি, পাঁপড়, দই ও টাঙ্গাইলের বিখ্যাত মিষ্টি। এলাহি ব্যাপার।
বিকাল সাড়ে চারটে, আমরা মাসুদ সাহেবের বাড়ি থেকে মেলার দিকে মুখ ঘোরালাম। মেলা খুব বড় নয়। এক দিকে পর পর অনেকগুলি বইয়ের দোকান। মাঝখানে মেলায় ঘুরে দেখার ফাঁকা জায়গা। আর অন্য দিকে বিশাল প্যান্ডেল। প্যান্ডেলের একপ্রান্তে বাঁধা মঞ্চ। সেখানে তিন সারি চেয়ার। ডান দিকে পোডিয়াম। অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমাদের অপেক্ষায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ডাক্তার দিলীপকুমার মোদক। মুস্তাফা সাহেব পোডিয়ামের সামনে গিয়ে বললেন, ভারত থেকে আমাদের দুই অতিথি এসেছেন। আমরা তাঁদের অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।’ দর্শক আসন থেকে জোরে হাততালির শব্দ। এই অনুষ্ঠানে বিডিও এক সুন্দরী মহিলা শামীম আরা রিনি (উপসচিব ও উপপরিচালক) স্থানীয়, সরকার টাঙ্গাইল, এসেছেন। প্রধান অতিথি। তিনি স্টেজের ওপর মুস্তাফা সাহেবকে প্রণাম জানালেন। মুস্তাফা সাহেব তাঁর বকৃতায় বললেন, ‘আজ আপনাদের সামনে যিনি সম্মানীয় অতিথি, তিনি আমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময় ছাত্রী ছিলেন। আমি খুব খুশি যে, আমার ছাত্রী আজ এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন।’ আর এক বার জোরে হাততালি পড়ল।
ডাক্তার মোদকের বক্তৃতা ছিল, কী করে নানান বাধার ভিতর দিয়ে এই বইমেলা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, তারই বিবরণ।
শামীম আরা রিনি পরিচ্ছন্ন ভাষায় বললেন, কীভাবে তিনি এই পরিমণ্ডলকে আরও বড় আকারে দেখতে চান। তার কিছু পরিকল্পনা ভাগ করে নিলেন সকলের সঙ্গে এবং সকলে সর্বতোভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াবেন সেই আশা তাঁর আছে। তিনি তাই সকলের কাছে আবেদন রাখলেন, যাতে এই দেশ সব দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়াই প্রধান কাজ, বার বার মনে করিয়ে দিলেন।
আমি অনেকের আলাপ করেছি, তাদের বক্তা হিসেবে দেখিনি। নাহিদা আশরাফী এসেছে বিশেষ অতিথি হয়ে কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে বিশ্রাম নিতে পাঠানো হয় ডাক্তার মোদকের বাড়ি। মুজতবা আহমেদ মুরশেদ প্রধান বক্তা। মুজতবা সাহেব বললেন, ‘যে বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিতে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সত্যকে ধরে রাখতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ আবার নানান বাঁক নিয়েছে, মৌলবাদীদের উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে, যা দেশের স্বাধীনতার মূল আদর্শ থেকে ভিন্ন। সকলকে সেই দিকে নজর দিতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশ যেমন সকলের, তেমনই সকলের জন্য বাংলাদেশ, এই কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার দিন এসেছে।’ বর্তমান সময়ের কথা বললেন। মুরশেদ আলোচনা করলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতোত্তর জনজীবন ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত। আমরা স্টেজ থেকে লক্ষ করছিলাম মেলায় লোক সমাগম বাড়ছে, বইয়ের দোকানের সামনে জটলা বাড়ছে। একসময় মাঠ ও প্যান্ডেল ভরে গেছে মানুষে মানুষে। শুধু কালো মাথা। অনুষ্ঠানে ছিল কবিতা পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা। অনুষ্ঠানের শেষ অব্দি একজন মানুষও চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। বইয়ের প্রতি এই ভালবাসা, সংস্কৃতির প্রতি এই ভালবাসা চোখে পড়ার মতো।
আমরা যখন ফিরতে শুরু করলাম তখন রাত প্রায় সাতটা। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে ঢাকায় ফিরতে। মাঝপথে রাস্তার ধারে ডিনারের ব্যবস্থা। হাইওয়ের ধারে এমন রিসর্ট কাম রেস্টুরেন্টে এক বিশাল আয়োজন। রিসর্টের মালিক আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, ‘আমি তো আপনাদের কলকাতায় প্রায় যাই। সদর স্ট্রিটে এক হোটেলে থাকি, ধর্মতলা ঘুরে বেড়াই। খুব ভাল লাগে।’ আমাদের খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপর বললেন, ‘দেশভাগটা না হলে দেখতেন আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হতাম। এত জমি, এত মানুষ আর এত প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দেশের আছে বলুন তো। মানুষের সেবা তো মানুষই করে। আমাদের মতো মানুষ কোথায় পাবেন। ভাগ হয়ে, যুদ্ধ হয়ে কী হল? অনেকে মারা গেল, অনেকে দেশের বাইরে চলে গেল খালাসি খাটতে, অনেকে বড়লোক হল আর যারা রইল তারা ঢাকায় রিকশা টানে। বুঝতে পারছেন কী বলতে চাইছি?’
আমি তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করব। যেন তিনি আমার প্রশ্নটি বুঝতে পেরে বললেন, ‘আপনাদের ওখানে স্বাধীনতার পরে যা হয়েছে, এখানেও তাই। গণতন্ত্রের গোড়ায় গলদ আছে জানেন। মানুষ বকবক করার স্বাধীনতা পায় বটে, তবে তলে তলে কালোবাজারি বেড়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছে। না হলে এর অর্ধেক দামে আপনাদের খাওয়াতে পারতাম।’ বলে একজনকে অর্ডার করলেন, ‘ফ্রিজ থেকে টাটকা ফল নিয়ে সার্ভ করো।’ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘নিজের খেতের ফল। তিন একর জমিতে রিসর্ট করেছি। বাকি চার একর জমি আছে পিছনে। চাষ হয়। ফলের বাগান আছে, পুকুর আছে, দিনের বেলায় এলে দেখাতে যেতাম। হাঁটতে হত না। গাড়ি করেই ঘুরিয়ে দিতাম।’ মনে মনে বললাম, এই তো আধুনিক জমিদার। হয়তো এমনি এক জমিদারি ওপারের উদ্বাস্তু পরিবারের ছিল। জীবনের ভয়ে সব ছেড়ে চলে গিয়েছিল ওপারে। তারই সম্পত্তিতে এই ভদ্রলোক জমিদারি সাজিয়ে বসেছেন। জিজ্ঞাসা করি, ‘আপনি রাজনীতি করেন না?’
একটু হেসে বললেন, ‘তা সে না করলে চলে নাকি? তবে খুব অ্যাকটিভ আর করি না। বয়স হয়েছে। ছোটাছুটি করতে পারি না। দলের ছেলেরা ছোটাছুটি করে, আমি মাঝে মাঝে সভায় গিয়ে বক্তৃতা করি। আর এই এস্টেট চালাই।’
‘আপনার ছেলেমেয়ে?’
‘তারা সবাই বিদেশে। ছেলে আমেরিকায়, দুই মেয়ে ইংল্যান্ডে। বছরে দুই বার আসে। বাপেরে দেখতে। এলে খুব ভাল লাগে বুঝলেন। সময়টা খুব হাসিঠাট্টা করে কেটে যায়। আমার আর কী? ওদের জীবন, সংসার ওরাই সামলায়।’
‘এত বড় সম্পত্তি, একা সামলান কী করে? লোকের উপর নির্ভর করতে হয় বলুন। আপনার তো বয়স হচ্ছে?’
‘দেখেন, সম্পত্তি মানে তো দেশের জমি? এ কখনও নষ্ট হয় না। হাতবদল হয়। এখন আল্লা আমার হাতে দিয়েছেন। পরে অন্যের হাতে দেবেন। কার কী বলার আছে? আসলে আমরা তো এই মাটির জন্য লড়াই করেছিলাম, মানুষের জন্য নয়। মানুষ আসবে যাবে। জমি থেকে যাবে বুঝলেন। তাই একদিন আমিও জমি ছেড়ে দেব। তবু যতদিন পারি।’ বলে কফিতে চুমুক দিলেন। আমাদের খাবার এসে গেছে। ঢাকায় ফিরতে রাত বারোটা বাজবে। আমি নাহিদাকে সিমটি ফেরত দিয়ে বললাম, ‘ভাগ্যিস দিয়েছিলে। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। এছাড়াও আরও অনেক ধন্যবাদ তোমার পাওনা।’ নাহিদা বলল, ‘আমি সিমটা যত্ন করে রেখে দেব। পরের বার এলে আবার ভরে নিয়ো। ভালভাবে ফিরে যাও সেই প্রার্থনা করি। আর যাবার সময় টাঙ্গাইলের ল্যাংচা সাবধানে নিয়ে যেয়ো। রস গড়ায় না যেন।’ রাতের অন্ধকারে আমরা নেমে পড়লাম আন্তর্জাতিক হলে।
||২১||
ঢাকা ক্যান্ট থেকে ভোরের মৈত্রী এক্সপ্রেস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটা সময় লাগে। ঢাকায় ট্যাক্সির চল কদাচিৎ। সিএনজি-র দেখা পাওয়া ভার এই ভোরবেলায়। অধ্যাপক রুবায়েত বললেন, ‘আমি আমার এক চেলাকে বলে দেখি। পাওয়া যায় নাকি।’ অনেক পরে খবর এল পাওয়া গেছে। কিন্তু ভোরে টাইমে এল না। কাকভোরে দাঁড়িয়ে আছি হলের গাড়িবারান্দায়। যতবার ফোন করি, ততবার সে বলে, ‘আসছি।’ কোথায় সে কে জানে? একসময় মনে হল আর আসবে না। আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি, ট্রেন মিস করব। ইউনিভার্সিটি চত্বরে কোনও সিএনজি নেই। হঠাৎ ভোরের স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে গর্জন করতে করতে এসে হাজির হল ট্যাক্সি। শান্ত শহরে তীব্র বেগে আমরা ছুটে চললাম স্টেশনের দিকে।
ট্রেন ছাড়তে খুব বেশি দেরি ছিল না। কোনওক্রমে সব কাজ সেরে একসময় ট্রেনে উঠে পড়লাম। মনকেমন করছিল। বেশ তো ছিলাম ক’দিন। আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভাল হত। দুজনে দুপাশের শ্যামলিমা দেখতে দেখতে ফিরে আসছি কলকাতার দিকে। ট্রেনের দুলুনিতে কখন ঘুম ঘুম এসেছিল। হঠাৎ কানের কাছে সেই সুরেলা পরিচিত কণ্ঠস্বর, ‘দুপুরে কী নেবেন? মোরগ বিরিয়ানি?’ আমি ঘুম ঘুম চোখে ঠিক বুঝতে পারি না, কোন দিকে যাচ্ছি? ঢাকার দিকে, না কলকাতার দিকে!