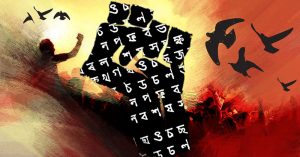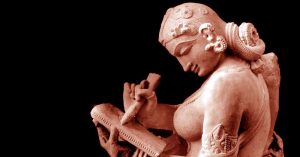‘‘যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলী
শৃণু তথা জয়দেবসরস্বতীম্।।’’
কুলুকুলু করে বয়ে চলেছে অজয়, নাতিদূরে মন্দিরের চবুতরায় বসে একমনে লিখে চলেছেন এক যুবক। সাদা ধুতি, সাদা চাদর আর সাদা উপবীত চাঁদের আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তিনি লিখছেন বসন্ত রাসের বর্ণনা—
‘‘উন্মদমদনমনোরথ পথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুলবকুলকলাপে।।
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদ নবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয় বিদারণমনসিজ নখরুচিকিংশুকজালে।।’’
মন্দিরের মহামণ্ডপে বসে স্বামীর প্রতীক্ষা করছেন পদ্মাবতী। স্বামীটি তাঁর বড়ই জেদী, এদিনের জন্য নির্দিষ্ট যেটুকু লেখা সেটুকু শেষ না হলে উঠবেন না। হ্যাঁ, এই জেদী ব্রাহ্মণযুবকই হলেন কোমলকান্ত পদাবলী গীতগোবিন্দম্-এর কবি শ্রীজয়দেব। কিন্তু মানসচক্ষে যাঁকে দেখলেন, তাঁর স্থান ও কাল নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। সবার কাছেই কবি জয়দেব তাদের ভূমিপুত্র। আমরা বাঙালিরা যেমন বলি, তিনি আমাদেরই লোক; তেমনই ওড়িয়া, মারাঠি এবং গুজরাতিরাও জয়দেবকে নিজেদের ভূমিপুত্র বলে দাবি করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় বলেও দাবি করেন। যদিও তথ্যগত দিক থেকে বাংলা আর ওড়িশার দাবিই অধিক। আসুন দেখি, এই তথ্যগত দাবিতে কে জেতে কে হারে।
কবি জয়দেবকে নিয়ে বাঙালির পরেই যাদের দাবি সবচেয়ে বেশি তারা হলেন ওড়িশা বা উড়িষ্যার মানুষ। তারা কোনওভাবেই মানতে পারেন না যে কবি জয়দেব ওড়িয়া নন। তাদের মতে, কবি জয়দেবের জন্ম কেন্দুবিল্ব গ্রামে। আরে না মশাই, এ বীরভূমের কেন্দুবিল্ব বা কেদুলি নয়, এ হল ওড়িশার কেদুলি শ্মশান।
লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিলালিপি, সিংহচাল মন্দিরের শিলালিপি ও মধুকেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি হতে জানা যায় যে কবি জয়দেব কূর্মপাটক বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছেন। জগন্নাথ মন্দিরে ওড়িশি নৃত্য সহযোগে গীতগোবিন্দম্-এর গান করার রীতি অনেক প্রাচীন। গুরুগ্রন্থসাহেবে জয়দেবের পদ সংকলিত হয়েছে। এটা গুরু নানকের জয়দেব প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। হতে পারে পুরীতে এসেই তিনি কবি জয়দেবের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হন।
ওড়িশি সঙ্গীতশিল্পী ও কবি গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক অতি প্রাচীন ওড়িয়া ভাষায় লেখা গীতগোবিন্দম্-এর পুঁথি উদ্ধার করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ওই পুঁথি কবি জয়দেবের হাতের লেখা পুঁথি যা কবি জয়দেবের ওড়িয়া হওয়াকেই প্রমাণ করে। পট্টনায়ক তার গ্রন্থে আরও বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সেই ওড়িশার কেদুলি শ্মশানে যেতেন ও গভীর ভাবানুরাগে গীতগোবিন্দম্ পাঠ করতেন।
এবার আসি বাংলার দাবির বিষয়ে। আর সে আলোচনার শুরুতেই যে প্রশ্নটা আসে সেটি হল, কবি জয়দেবের জন্ম হয়েছিল যে কেন্দুবিল্বে সেটি বীরভূমের কেদুলিতে, না ওড়িশার কেদুলি শ্মশানে?
কবি জয়দেব ছিলেন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের (১১৭৮ খ্রি.-১২০৬ খ্রি.) সভাকবি। সুতরাং তাঁর বাঙালি হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাঠকেরা বলবেন, প্রমাণ কোথায়? আসি প্রমাণের প্রসঙ্গে। ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ গ্রন্থে কবি জয়দেবের একত্রিশটি শ্লোক আছে। এরমধ্যে মাত্র পাঁচটি গীতগোবিন্দম্-এর শ্লোক আর বাকিগুলির মধ্যে কয়েকটি শ্লোকে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের স্তুতি আছে—
‘‘লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ! জঙ্গমহরে! সংকল্প কল্পদ্রুম!
শ্ৰেয়ঃ সাধকসঙ্গ সঙ্গর কলা-গাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়!
গৌড়েন্দ্ৰ! প্রতিরাজরাজক! সভালংকার! কারাপিত—
প্রত্যার্থিক্ষতিপাল! পালক সীতাং! দূক্টোহসি, তুষ্টা বয়ম!’’
যে স্তুতি প্রমাণ করে যে কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। এছাড়াও তিনি লক্ষ্মণসেনের আরও সভাসদদের নাম করেছেন। যেমন কবি শরণ। কবি শরণ সম্মন্ধে বলছেন— ‘শরণঃ শ্লাঘ্যে দুরূহ-দ্রুতে’, অর্থাৎ কবি শরণ দুরূহ ও দ্রুত শ্লোকবন্ধনে এতটাই পটু ছিলেন যেটা প্রশংসাযোগ্য।
বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপ রাজদরবারে একটা শিলালেখ দেখেছিলেন, তাতে লেখা ছিল— ‘গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।/ কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।’ অর্থাৎ গোবর্ধন, শরণ, কবি জয়দেব, উমাপতি ধর এবং কবিরাজ ধোয়ী— এই পাঁচজন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন ছিলেন।
পরোক্ষ আরেকটি প্রমাণ হল এই যে, ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’-এ যেসব কবির শ্লোক রয়েছে তাঁরা সবাই বাঙালি ও লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। এঁদের মধ্যে শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাঞ্চাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবাট, পপীপ, (জনৈক) বঙ্গাল, চন্দ্ৰচন্দ্ৰ, গাঙ্গোক, বিম্বোক, শুঙ্গোক ইত্যাদি সবাই বাঙালি। তাই কবি জয়দেবও যে বাঙালি, তা প্রমাণিত।

অনেকেই বলেছেন যে, বীরভূমের কেদুলি হতে গৌড় অনেক দূর। কবির বাসস্থান হতে কর্মস্থল এতটা দূরে কীভাবে সম্ভব! সম্ভব। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণনগর বা লক্ষ্মৌর ছিল বীরভূমের রাজনগরে, যা মহারাজ লক্ষ্মণসেন পালরাজাদের কাছ থেকে দখল করে নেন। মিনহাজউদ্দীনের ‘তবকৎ-ই-নাসিরি’-তে এই লক্ষ্মৌরের উল্লেখ মেলে।
এছাড়াও জনশ্রুতি আছে এই যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতা বল্লালসেনের কোনও এক ধর্মগর্হিত (মহারাজ বল্লালসেন নীচজাতীয়া পদ্মিনী রমণীকে সাধনসঙ্গিনী করেছিলেন।) কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে অজয় নদের দক্ষিণে সেনপাহাড়ীতে বসবাস শুরু করেন।
১২০২ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির নদীয়া বিজয়ের পর মহারাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যেতেই লক্ষ্মৌর চলে যায় ওড়িশার গঙ্গ রাজাদের দখলে। সম্ভবত এসময়ই গঙ্গ রাজাদের আনুকূল্যেই কবি জয়দেব উড়িষ্যায় যান।
হলায়ুধ রচিত ‘শেখ শুভোদয়া’ গ্রন্থে কবি জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে একটা গল্প আছে। গল্পটি একটি পুরস্কার গ্রহণ সমারোহকে কেন্দ্র করে। পদ্মাবতী তখন স্নানে চলেছেন। পাশেই রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ হতে দুন্দুভি-করতালের ধ্বনি ভেসে আসছে। তিনি পথচারীদের শুধালেন, ‘রাজপ্রাসাদে কীসের উৎসব হচ্ছে?’
পথচারী বললেন, ‘আপনি জানেন না মা, আজ যে দেশের সেরা গাইয়ে বুঢ়ন মিশ্র মহারাজের কাছ হতে সম্মান গ্রহণ করবেন।’
—‘কীসের জন্য সম্মান?’
—‘এ মা, এও আপনি জানেন না! বুঢ়ন মিশ্র যে গানের সুরে অশ্বত্থ গাছের সব পাতা ঝরিয়ে দিয়েছেন। কী এলেম তার, যেন গন্ধর্ব স্বয়ং!’
পদ্মাবতী সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। রাজাকে গিয়ে বললেন যে, ‘অশ্বত্থ গাছের পাতা তো বাতাসেও ঝরে, এরজন্য পঠমঞ্জরী রাগের কী দরকার। ওই অশ্বত্থ গাছে নতুন পাতা গজাতে পারবেন কি মিশ্রমশাই?’
বুঢ়ন মিশ্র পারলেন না। তখন সভায় ছিলেন জয়দেব, তিনি গান ধরলেন বসন্ত রাগে। ‘ততো জয়দেবমিশ্র বসন্ত রাগ মুদ্গীরিতবান্।’ আর দেখতে দেখতে সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের ডালে নবকিশলয়ও দেখা গেল। কোকিল গেয়ে উঠল পঞ্চমে। রাজা লক্ষ্মণসেন জয়পত্রটি তুলে দিলেন কবীন্দ্র সরস্বতী জয়দেবের হাতে।
এই গল্প যে হলায়ুধ লিখেছেন, তিনি জয়দেবের সমসাময়িক, সুতরাং তথ্যবিকৃতিতে তাঁর স্বার্থ দেখতে পাই না। অর্থাৎ কবি জয়দেব যে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজসভাতেই ছিলেন, এই গল্প হতেও এটা স্পষ্ট। অপরদিকে পদ্মাবতীর দক্ষিণ ভারতীয় হওয়া বা দেবদাসী হওয়ার গল্পেরও এখানেই ইতি পড়ে যায়।
কবি জয়দেব যে জীবনের শেষের দিকে বৃন্দাবন সহ ভারতভ্রমণ করেছিলেন তার ইঙ্গিতও একটা লোককথায় মেলে। গল্পটা এইরকম— কবি জয়দেব একবার তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাধামাধবের বিগ্রহকে ফেলে যাবেন কোথায়? এই বিগ্রহ না থাকলে শালগ্রামগুলো ঝোলায় ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতেন। কিন্তু হায়! সে কপালে নেই। এই ভেবে রাধামাধবের নাম নিয়ে শুয়ে পড়লেন। সকালে উঠেই দেখলেন রাধামাধবের বিগ্রহ নেই। মহানন্দে শালগ্রামগুলো ঝোলায় ভরে বেরিয়ে পড়লেন।
এবার আসি গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়কের পুঁথির বিষয়ে, তার উদ্ধারকৃত পুঁথিটি যে আটশো বছর আগের কবি জয়দেবের হাতের লেখা অরিজিনাল পুঁথি তার কোনও প্রমাণ নেই। শুধু দাবিমাত্র। আর কবি জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দম্ মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রিয় হতেই পারে। অমৃতের সমান সুললিত পদ তো ‘দেবভোগ্যমিদং’। এছাড়াও জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে রাঢ়ের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। উদাহরণস্বরূপ মুরারই মিশ্র নামের একজন কবি জগন্নাথদেবের উৎসব উপলক্ষে ‘অনর্ঘ রাঘব’ নামে একটি নাটক রচনা করেন। যা জগন্নাথ মন্দিরে গাওয়াও হয়।
সুতরাং কবি জয়দেব যে বাঙালি ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পরবর্তী সময়ে ওড়িশায় যেতে পারেন। তবে সেও শেষের দিকে। সুতরাং যে যাই বলুন, কবীন্দ্র জয়দেব সরস্বতী আমাদের আপনারই জন।
কবি জয়দেব বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ধূসরিত অধ্যায়। সেই ধূসর পট হতে উঠে আসবে আরও অজানা বহু তথ্য। তথ্য আর তত্ত্বে ভরে উঠবে উৎসুক পাঠকের পাঠাগার। কিন্তু সেই সমান তালে ও লয়ে আমাদের মনের জগতীতে ধ্বনিত হবে গীতগোবিন্দম্-এর সুললিত কোমলকান্ত পদ, ধ্বনিত হবে কবি জয়দেবের জয়ধ্বনি।