ইউরোপে আমস্টারডামকে বলা হয় উত্তরের ভেনিস। তবে আমি ভেনিস দেখার আগেই আমস্টারডাম দেখেছিলাম। তাহলে কি আমি ভেনিসকে বলব দক্ষিণের আমস্টারডাম? কিন্তু ভেনিস প্রাচীনতর, তাই দাবি তারই। অবশ্য খাল ও খাল-পোলের সংখ্যা আমস্টারডামে একটু বেশি। আমি ভেনিস গিয়েছিলাম ২০০৫-এর সেপ্টেম্বরে। এ.আই.এল.সি./ আই.সি.এল.এ., মানে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার জন্ম ১৯৫৪-তে অক্সফোর্ডে হলেও তার প্রথম কংগ্রেস হয়েছিল ভেনিসে, ১৯৫৫-র ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর। ২০০৫-এর ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ভেনিসে এক আন্তর্জাতিক সম্মিলন করে তার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপিত হল। সম্মিলনের নামই ছিল : ‘ভেনিসেই যা শুরু হয়েছিল : উত্তরাধিকার, উদ্বর্তন, দিগন্ত : এ.আই.এল.সি.-র পঞ্চাশ বছর’। সম্মিলন আহ্বান করেছিল ‘উনিভের্সিতা “কা’ফসকারি” ভেনেৎসিয়া’। ভারত থেকে আর গিয়েছিলেন দিল্লির ড. চন্দ্রমোহন। উঠেছিলাম এক মধ্যবিত্ত পেন্সিওনোতে। মার্কো পোলো এয়ারপোর্ট থেকে ওয়াটার ট্যাক্সিতে মিনিট কুড়ি মতো আদ্রিয়াতিকের খাড়ি (ভেনিস উপসাগর) পেরিয়ে সেন্ট মার্কস স্কোয়ার ঘাটে। সেখান থেকে গ্র্যান্ড কানাল-বাহী ভাপোরেত্তোতে করে দর্সোদুরো এলাকার কোনও ঘাটায় নেমে একটু হেঁটে, একটা ছোটো পোল পেরিয়ে, আরো কয়েক পা এগোলেই ওই পেন্সিওনেটি। খুঁজে নিতে অসুবিধে হয়নি। রাত্রিবাস ও প্রাতরাশই কেবল সেই সরাইখানায় লভ্য।
পিয়াৎসা সান মার্কো যে ভেনিসের প্রধান দ্রষ্টব্য তা ভাপোরেত্তো ধরবার তাড়ায় তক্ষুনি বুঝে উঠতে পারিনি। তার জন্য পরে ওখানে আসতে হয়েছিল। এত পর্যটক তখন দেখেছিলাম সেখানে, নিশেন উড়িয়ে এদেশ ওদেশের নানান দল, মনে হয়েছিল বুঝি ভেনিস লোকে আসে শুধু ঘুরে দেখতে। আমরা যে সম্মিলন করতে এসেছি তা কি ওই নিশেনধারীরা বিশ্বাস করবে? বলবে, ছুতো। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-শেষের অনুষ্ণতায়। আমার কোরিয়ো বন্ধু কিম উচাং দু-তিনটে চীনে পর্যটকদল দেখে বলে ফেলেছিলেন, কবে ভারতীয়দেরও অমন দল বেঁধে আসতে দেখা যাবে?
যাই হোক, আমি কিন্তু ভেনিস দেখব বলে সম্মিলনের কোনও অধিবেশন থেকে পালাইনি। তবে অধিবেশন যেদিন একসঙ্গে একাধিক জায়গায় (কা’ দলফিন ছাড়াও, আতেনেও ভেনেতো-তে, বা সান মার্গেরিতা প্রেক্ষাগৃহে, বা পালাৎসো জ়র্জ়ো-তে), সেদিন ছুটে ছুটে না বেড়িয়ে এক জায়গায়ই বসে থেকেছি সারাদিন। দিনশেষে কোনও দিন সম্মিলনপ্রদত্ত সাদর অভ্যর্থনায় গেছি, কোনও দিন কোথাও এক পিয়াৎসায় বসে সম্মিলনে আগত কারো কারো সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। আবার, এক সন্ধেয় সম্মিলনের আমন্ত্রণে এক ইতালীয় কনসার্ট শুনলাম— তাতে সুবর্ণজয়ন্তী সমিতির সভানেত্রী পাওলা মিলদোনিয়ানের বোনই বোধকরি, সুসান্না মিলদোনিয়ান, চমৎকার হার্প বাজালেন। আর যথারীতি সমুদয় অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে পর, এ.আই.এল.সি./ আই.সি.এল.এ.-র প্রথানুসারে এক মহতী সান্ধ্যভোজের আয়োজন হয়েছিল লিদোর এক প্রশস্ত উন্মুক্ত রেস্তোরাঁয়— সেই লিদো যেখানে টমাস মান্-এর ‘ভেনিসে মৃত্যু’-র প্রৌঢ় আশেনবাখ সমুদ্র থেকে উঠে আসা রূপবান কিশোর তাদ্ৎসিয়ো-তে জীবনের পরিপূর্ণতা দেখতে পেলেন। তবে বাস্তব লিদোকে ওই কল্প-লিদোর মতো রহস্যময় লাগল না। তাছাড়া কি ইতিমধ্যে এক শতকের সব দ্রুতিচিহ্ন ধারণ করে নিয়ে লিদোও খানিক পাল্টে যায়নি?
খালের শহরের যে-নিত্যকার চারিত্র একদা গন্দোলায় অভিব্যক্ত ছিল তা কি এখনো অটুট? অন্তত ২০০৫-এ তো আমি ভেনিস গিয়ে গন্দোলানাম্নী ওই গাঢ় গলুইয়ের ছত্রহীন নৌকো দেখে মুগ্ধ হয়েছি কিন্তু চড়িনি, বা চড়বার অবকাশ আমার হয়নি— ভাপোরেত্তোতেই প্রয়োজন মিটেছে। আদৌ নয়নহরণ নয় বটে ভাপোরেত্তো, কিন্তু কাজের, তাছাড়া শস্তা। পিয়াৎসা সান মার্কোর তটে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে যে-গন্দোলাবাহিনী, তা কারা চড়ে? নিশ্চয়ই পর্যটকেরা। এক ঘণ্টা গন্দোলা-ভ্রমণ—খালে-খালে ঘুরে বেড়ানো— নব দম্পতি হলে তো সুখের শেষ নেই। ভাড়া বিস্তর। হলই বা, এটা তো আর রোজ ঘটছে না। ভুলে গেছ তুমি ভেনিস এসেছ? দেখো দেখো, কী সুন্দর লগি ঠেলছে ওই সুঠাম গন্দোলিয়র। টমাস মানের আশেনবাখ কি তাকে আকেরনের কারণ ভাবতে চান? ভাবুন; তুমি কি দূর আদ্রিয়াতিকের পাঠানো এক হালকা ঢেউয়ে দুলে উঠছ না? ভেনিসে সম্মিলন করতে আসা কেজো লোকটি একবার তার পোল পেরোতে পেরোতে ঈর্ষাভরে তাকিয়ে দেখুক।
২
সম্মিলনশেষে প্রায় দেড়দিন হাতে পেলাম। অনেক চিত্র-প্রদর্শশালা ভেনিসে। ভেনিসীয় ধারায় বিখ্যাত তিশিয়ান (তিৎসিয়ানো) ও তিনতরেত্তো। বেশ ক’টা তিশিয়ান কি দেখতে পেলাম না পিয়াৎসা সান মার্কো-স্থিত দজ-এর প্রাসাদে? এই পরিক্রমায় আমি সঙ্গী হয়েছিলাম কিম উচাঙের—তিনি পাশ্চাত্য চিত্রকলায় আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ। দজের প্রাসাদ তো এক খনি, কী নেই সেখানে? তিশিয়ানের গুরু বেল্লিনি, আবার তিশিয়ান-উত্তর তিনতরেত্তো। তিনতরেত্তোরই অতীব বৃহৎ ‘ইল পারাদিজ়ো’ সেই প্রাসাদের প্রধান হল্ যেন-বা দখল করে আছে। ভেনিসে কোথায় নেই তিনতরেত্তো? তবে স্কুলা গ্রান্দে দি সান রক্ক-তে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, যেমন দেয়ালজোড়া তেমনি ছাতজোড়া। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে আমরা দেখেছিলাম মনে আছে। আর ছাতে আঁকা ছবি দেখতে আয়না বসিয়ে তার বিম্বদর্শন করতে হয়েছিল। শোনা যায় প্রায় ক্ষিপ্তের মতো ছবি আঁকতেন বলে তিনতরেত্তোকে ‘ইল ফুরিয়োসো’ বলা হত। তিনি নাকি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন তিশিয়ানের কাছে, কিন্তু তিশিয়ান তাঁকে সহ্য করতে পারেননি। তিনতরেত্তো নিজেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর স্টুডিওর শিরোদেশে তিনি উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন : ‘মিকেলাঞ্জেলোর অঙ্কন আর তিশিয়ানের রং’। তিশিয়ানের রঙের একটা বিশেষ ভেনিসীয় উদাহরণ বুঝি-বা ফ্রারি গির্জের ‘ভার্জিনের আবির্ভাব’। তাঁর শেষ ছবিও আছে ভেনিসেই, ‘পিয়েতা’, আকাদেমিয়া গ্যালারিতে। দেখেছি। শুনেছি [১৫৭৬-এর প্লেগে] তাঁর নিজের মৃত্যুর আভাসও এই প্রায়-সমাপ্ত ছবিতে আছে। ভেনিসের আরেক গর্ব, তিনতরেত্তোর শেষ আত্মপ্রতিকৃতি, আমার দেখা হয়ে ওঠেনি।
‘বিয়েনাল’ তথা দ্বিবার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী ভেনিসেই শুরু হয়। ২০০৫-এ তা ১১০ বছরে পা দিয়েছে। এখন যা ‘পেগি গুগেনহাইম সংগ্রহ’ নামে ভেনিসে স্থায়ীভাবে আছে তা ১৯৪৮-এ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, নাট্য, চলচ্চিত্র (ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল) ইত্যাদির প্রদর্শন সবই বিয়েনালের আকারপ্রকার হয়ে এসেছে। বিবিধ শিল্পকর্ম প্রদর্শনে এই এক জগজ্জয়ী ভূমিকা ভেনিসের। এখন তো এদেশেও বিয়েনাল হচ্ছে—কোচির বিয়েনাল শুনছি রীতিমত আকর্ষণীয়। ২০০৫-এ যে-বিয়েনাল হচ্ছিল ভেনিসে তা তার একান্নতম বিয়েনাল। ১২ জুন থেকে ৬ নভেম্বর। এতে কিম উচাঙের আত্মীয়া এক তরুণ কোরিয়ো শিল্পীর কাজ ছিল। উচাঙের সঙ্গে সেই প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। আশ্চর্য ‘অভিজ্ঞতা’। ‘শিল্প’ (অভিজ্ঞতা ও শিল্প দুটো শব্দেই উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারের কারণ ‘শিল্প অভিজ্ঞতা’ ছিল ওই বিয়েনালের ঘোষিত ‘থীম’) কথাটার অর্থ যে কী ব্যাপক হতে পারে তার প্রতীতি হল। আরো বিশেষ করে যেহেতু শুনলাম ভেনিসীয় ‘আর্সেনাল’-এও—যা একদা জাহাজশালা ছিল—এবার, ‘একটু এগিয়ে গিয়ে্’ (‘থীম’ তথাকার), সম্পন্ন বা সক্রিয় এমন কিছু কাজ দেখা গেল যাকে শিল্প বলতে বাধবে না।
৩
অন্য খালের শহর, আমস্টারডাম কি শিল্পসম্পদে পিছিয়ে? আদৌ না। ১৯৯৭-তে একবার লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গেছি এ.আই.এল.সি./ আই.সি.এল.এ. কংগ্রেসে। আমস্টারডাম লাইডেন থেকে মিনিট চল্লিশেক। একটু সময় করে চলে গেলেই হল। তা-ই করেছি বারদুয়েক। গন্তব্য ‘রাইক্স্ম্যুজ়িয়ম’ ও ‘ভান গখ ম্যুজ়িয়ম’। রাইক্স্ বিশাল, ভান গখ আয়ত্তাধীন। রাইক্সে যতটা পারি রেমব্রান্ট আর কিছুটা ফ্রান্স হাল্জ় ও ভারমীর। রেমব্রান্টের ‘নৈশপ্রহরা’ দেখছি : কে যেন বলেছিলেন রেমব্রান্টে আলো বাইরে থেকে আসে না, ক্যানভাস থেকেই বিচ্ছুরিত হয়। বোধকরি এক্ষেত্রে তাই-ই। তিনি ভেনিসীয় রেনেসাঁস থেকে দূরে। আবার রুবেন্সের চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতাও তাঁর নেই। বারোক? তাও বুঝি পুরোপুরি নয়? কেউ কেউ বলবেন তিনি ওলন্দাজ স্বর্ণযুগেরই মুখ্য প্রতিভূ। যে-প্রতিকৃতি চিত্রণ ছিল তাঁর প্রধান উপার্জনের উপায় তারও দুটো নমুনা দেখতে পেলাম। তাছাড়া তাঁর দুই বয়সের দুটো আত্মপ্রতিকৃতিও দেখলাম— দ্বিতীয়টি তো আলোআঁধারিতে বিশুদ্ধ রেমব্রান্ট। তবে তাঁর যে-কয়েকটি অবিস্মরণীয় আত্মপ্রতিকৃতির কথা জানি তা আছে অন্যত্র। রাইক্স্ আলো করে আছে তাঁর ‘নৈশপ্রহরা’।
রেমব্রান্টের তুলনায় কি ফ্রান্স হালজ় একটু সুখকামী? তাঁর দুই বিখ্যাত ছবি কি সেই সাক্ষ্যই দেয় না : ‘লুট-বাদক’ ও ‘খুশি সীধুপায়ী’? ঢের প্রতিকৃতি তিনিও এঁকেছেন, কিন্তু যে-দম্পতির ছবি প্রথমেই চোখে পড়ে তা তাঁরই স্বাক্ষর বহন করে। এমনকী যে-সম্ভ্রান্ত মহিলাকে দেখলাম তিনিও রীতিমতো দীপ্তিময়ী। ওই একই যুগের একটু অন্য ধরনের আঁকিয়ে, ভারমীরের তিনটি ছবি দেখলাম রাইক্স্মুজ়িয়মে। রেমব্রান্ট বা ফ্রান্স হাল্জ়ের মতো অজস্র ছবি তিনি আঁকেননি। আর যাও বা এঁকেছিলেন তা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রাইক্সের এই তিনটি ছবির নাম যথাক্রমে ‘দুধওয়ালি’, ‘সরু রাস্তা’, ‘প্রেমপত্র’। তাঁর জগৎটা যেন অপেক্ষাকৃত কাছের।
আগে একবার অন্য কোথাও যাবার পথে আমস্টারডামে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। তখন শুধু ভান গখ ম্যুজ়িয়মে যেতে পেরেছি। খুব বেশি ছবি দেখা হয়নি। আর্ভিং স্টোন-এর ‘লাস্ট ফর লাইফ’-এ যে-ভিনসেন্টকে পেয়েছি তাঁকেই মুখ্যত খুঁজতে গিয়েছিলাম সেখানে। (আন্না ফ্রাংকের বাড়িটাও কি সেবারই দেখেছিলাম— কোন এক খাল বেয়ে এসে একটা চিহ্নিত ঘাটে নেমে গিয়ে?) এবার, অর্থাৎ ১৯৯৭-তে, ভান গখ ম্যুজ়িয়মে অনেকটা বেশি সময় কাটিয়েছি। অনেক ছবি দেখেছি যা আগে দেখিনি। যথা ‘আমন্ড পুষ্প’ বা ‘কুটির’ বা ‘পাইপ-মুখে আত্মপ্রতিকৃতি’। আগে-দেখা ছবিও খুঁটিয়ে দেখেছি, যেমন ‘যারা আলু খাচ্ছে’ বা ‘শোবার ঘর’। তবে তাঁর বিখ্যাত ‘সাইপ্রেস সারি’ ও ‘নক্ষত্রখচিত রাত’ আছে ন্যু ইয়র্কে। তা আগেই দেখেছি। এখানে তাঁর অন্য ছবিগুলোর সঙ্গে দেখলে ভালো হত। বিশেষ করে দ্বিতীয়টি।

চিত্র: গুগল
আরও পড়ুন…





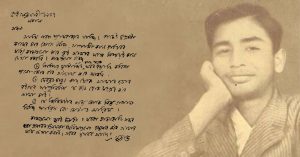









অনেক কিছু জানতে পারলাম।