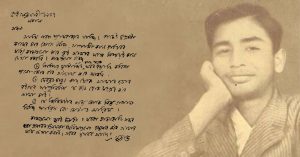পুরাণ, শাস্ত্র থেকে বয়ে আসা ঐতিহ্যধারার এক বিপুল স্রোত সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে বাংলা ক্যালেন্ডারের চতুর্থ মাস, শ্রাবণ মাসের সঙ্গে। অগণিত ভক্ত এই মাসের প্রতিটি সোমবার পুণ্য অর্জনের জন্য বহু শৈবতীর্থে ছুটে যান, এরাজ্যের হুগলি জেলার তারকেশ্বর তার মধ্যে অন্যতম। শ্রাবণ মাস বাবা ভোলানাথের মাস হিসেবে খ্যাত। কিন্তু এই লেখা যাঁকে নিয়ে তিনি নামে ভোলা হলেও, হুগলি জেলার একটি সুপ্রাচীন জনপদে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের সম্পর্কে তিনি পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:
আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই।
চিন্তামণির চরণ চিন্তি
ভাজনা খোলায় ভাজি খৈ।
আসলে ভোলা ময়রা ছিলেন একজন স্বভাবকবি। খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত কবিয়াল। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ভোলানাথ মোদক। কুলগত পেশা মোদক বা ময়রাবৃত্তি। পিতা কৃপারামের মিষ্টান্নের দোকান ছিল কলকাতার বাগবাজারে। শৈশবে তিনি স্বল্প সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। ভোলানাথ একটু বড় হয়ে প্রথমে পিতার দোকানে কাজ করতেন। পরে কবিয়ালরূপে খ্যাতি লাভ করেন।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ব্রিটিশ শাসকরা যখন কায়েমি শাসকে পরিণত হয়ে ওঠে, তখন প্রচলিত সমাজের ভিত নড়ে যায়। আগে যারা ছিল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদের অনেকেই অর্থ, পদ, সম্মান হারিয়ে পিছিয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু বেনিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বল্পশিক্ষিত, ব্রিটিশদের আনুগত্যপ্রাপ্ত, লোভী, মানমর্যাদাহীন কেরানি ও বণিক শ্রেণি সমাজের কেষ্টবিষ্টু হয়ে ওঠে।
কিন্তু রাতারাতি আর্থিক ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও স্বাভাবিকভাবেই এদের রুচির পরিবর্তন হয়নি। আর এই নব্য ধনী গোষ্ঠী উন্মত্ত আনন্দে, চটুল রঙ্গরসিকতায় গা ভাসানোকেই সংস্কৃতিচর্চা বলে মনে করত। সেই চাহিদা পূরণেরই এক উপায় ছিল কবিগান ও কবিয়ালরা।
রবীন্দ্রনাথ ‘কবিসঙ্গীত’ প্রবন্ধে কবিগান সম্পর্কে জানিয়েছেন, ‘‘প্রথমে নিয়ম ছিল দুই প্রতিপক্ষ দল পূর্ব থেকে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর-প্রত্যুত্তর লিখে আনতেন। পরবর্তীকালে আসর করে দুজন কবিয়াল পরস্পর বাগযুদ্ধে কবির লড়াই জমিয়ে দিতেন।’’ তিনি লিখেছেন, ‘‘কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা, এবং উপস্থিত মতো জবাব ছিল কবিগানের মুখ্য আকর্ষণ।’’ হারজিত যতক্ষণ না নিষ্পন্ন হত ততক্ষণ চলত গানের লড়াই। এমনকি তিনরাত্রি পর্যন্ত গড়িয়ে যেত কবিয়ালদের এই লড়াই।
ঢোল ও কাঁসর কবিগানে ব্যবহৃত দুই প্রধান বাদ্য। পূর্বে কবিগানের সাথে টিকারা, কাড়া ও জোড়খাইয়ের ব্যবহার হত। সজনীকান্ত দাশ তাঁর ‘বাংলার কবিগান’ গ্রন্থে লেখেন, ‘‘বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সময় প্রচলিত বিভিন্ন সঙ্গীতধারার মিলনে কবিগানের জন্ম। এই ধারাগুলোর নাম বহু বিচিত্র— তরজা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপকীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কাগীতি ইত্যাদি।
কবিয়ালরা ছিলেন সাধারণত কবিদের থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। তাঁরা বিশেষ কোনও কবিতা রচনা করতেন না। ক্ষণিকের আনন্দদানের জন্যেই হত তাঁদের কাব্য সৃজনের প্রয়াস। তাঁরা গুরুতর বিষয়ে কোনও কবিতা লিখতেন না, বিপক্ষের ছোড়া কটাক্ষ বা প্রশ্নের জবাব হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে উচ্চারণ করতেন কয়েকটি পঙ্ক্তি।
কবিগানের পালায় থাকত দুটি করে দল। প্রতি দলে থাকতেন একজন করে কবি। এছাড়া দুই দল মিলিয়ে পাঁচ থেকে সাতজনের মত দোহার ও তিন-চারজন বাদক থাকতেন। দুই দলের দুই কবি মুখোমুখি মঞ্চে দাঁড়িয়ে অবতীর্ণ হতেন কবির লড়াইয়ে। এক কবি প্রথমে অপর দলের কবিকে উদ্দেশ করে প্রশ্নাকারে কোনও পঙ্ক্তি ছুড়ে দিতেন। অপর কবি সেই অনুযায়ী তাৎক্ষণিক একটি ছন্দ বানিয়ে পাল্টা জবাব দিতেন। প্রথম দলের কথাকে বলা হত ‘চাপান’, আর দ্বিতীয় দলের কথাকে বলা হত ‘উতোর’। এসব পঙ্ক্তিতে রুচির খুব একটা চিহ্ন থাকত না। একে অপরকে কথার আক্রমণে পর্যুদস্ত করে ক্ষণিকের আনন্দ লাভই ছিল মূল লক্ষ্য।
তবে কবিগানের শিল্পগুণ একেবারে অবহেলা করার মত না। কবিগান একাধারে গান, ছড়া, বিতর্ক, সমালোচনা ও পর্যালোচনাও বটে। সাধারণ মানুষের মনের নানা দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতেন কবিয়ালরা। শাস্ত্রীয় বহু প্রসঙ্গের পরস্পরবিরোধী, অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি ও বক্তব্যগুলো দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে কবিয়ালরা বিষয়বস্তুর সত্যতার কাছে শ্রোতাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। এছাড়া বিভিন্ন কবিয়ালদের যুক্তি-তর্কের মধ্যে ভাববাদ ও আধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
কবিগান আমাদের লোকসাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনই লোকশিক্ষায় রেখেছে মূল্যবান অবদান। বাঙালির প্রাণের সামগ্রী, মানসসম্পদ, বাস্তব জীবানুভূতিসম্পন্ন লোকায়ত কবিগান গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সামগ্রিক পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করে গণমানসে অবস্থান করে নিয়েছে। দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম নিয়েও প্রচুর কবিগান রচিত হয়েছে। ভাল আর মন্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মানুষের চিন্তাজগৎকে আলোড়িত করেছে বহু কবিগান। প্রকৃতি, পরিবেশ, নৈসর্গিকতার উল্লেখও কবিগানে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। তবে সবার উপরে অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি কবিগানে বহুলচর্চিত ও গীত হয়েছে।
একবার ভোলা ময়রাকে তাঁর বিপক্ষের কবিয়াল তাঁর ছোট জাত নিয়ে ব্যঙ্গ করলে ভোলা ময়রা উত্তর দেন এভাবে:
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা ময়রাই বারোমাস
জাতি পাতি নাহি মানি, ওগো মোর কৃষ্ণপদে আশ।
ভোলানাথের গুরু ছিলেন কবিয়াল হরু ঠাকুর। তাঁর দলে দোহাররূপে ভোলানাথের হাতেখড়ি হয়; পরে দল গঠন করে তিনি স্বাধীনভাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কবিগান পরিবেশন করেন। কবিগান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে ভোলা ময়রার গুরু হরু ঠাকুর ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ, প্রখ্যাত কবিয়াল। তিনি ভবানী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে মানবীয় আবেদন সঞ্চার করে শ্রোতাদের অভিভূত করতেন।
হরু ঠাকুর সৌখিন গায়ক হিসেবে প্রথমদিকে পারিতোষিক নিতেন না; কিন্তু পরে পেশাদার শিল্পী হিসেবে গান গেয়ে প্রচুর অর্থের মালিক হন। তিনি কলকাতা, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে ধনাঢ্যদের গৃহে গান পরিবেশন করতেন। বিশেষত কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা ও সভাসদের আসন লাভ করে তিনি মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর প্রমুখ কবিয়াল তাঁর শিষ্য ছিলেন। পরে তাঁরা স্বাধীনভাবে দল গঠন করলে হরু ঠাকুর গান লিখে ও তাতে সুর দিয়ে তাঁদের সাহায্য করতেন। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে তিনি কবির লড়াইয়েও অবতীর্ণ হতেন। গুরু-শিষ্যের এই লড়াই বেশিরভাগ নবকৃষ্ণের গৃহপ্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হত।
হরু ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম হরেকৃষ্ণ দিঘাড়ী; কিন্তু কবিখ্যাতি লাভের পর তিনি ‘হরু ঠাকুর’ নামে পরিচিত হন। দারিদ্রের কারণে হরু ঠাকুরের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্বভাবকবির প্রতিভাগুণে বাল্যকাল থেকেই তিনি গান রচনা ও সুরারোপ করে গাইতেন। হরু ঠাকুর বিজয়া, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড় ও লহর রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সখীসংবাদ ও বিরহের গান গেয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন।
উতোর-চিতেন পর্বে অতি দ্রুত ছড়া বাঁধতে পারা ও চটকদার ছড়া গেয়ে আসর মাত করা, কবিগানের এই দুই বিশেষ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভোলা ময়রা হরু ঠাকুরের সুপরামর্শে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। হরু ঠাকুরের মত ভোলা ময়রারও খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তাঁর কবিগানে ব্যবহৃত সুপ্রযুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত শব্দযোজনা শুনে মুগ্ধ হতে হয়।
কবিগান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা কৃপানাথের ছোট্ট একটি ঝুপড়ি দোকানকে তিনি সেসময়ের কলকাতার সবচেয়ে বড় মিষ্টির দোকানে পরিণত করেন। নবাবি এবং ইংরেজ আমলের ময়রাদের মধ্যেও ভোলানাথই ছিলেন প্রথম, যিনি নিজেকে একটি ব্র্যান্ডে পরিণত করেন। তাঁর মিষ্টান্ন তৈরির হাত যেমন পাকা ছিল, তেমনি দক্ষতার সঙ্গে তিনি কবিগান পরিবেশন করতেন। কিন্তু স্বভাব কবিত্ব প্রতিভার তাগিদে তিনি কবিগান গাওয়াকেই প্রাধান্য দিতেন। কবিগানের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনু্রাগের পরিচয় মেলে এই কবিতাটিতে।
ফুরাইল বরোমাস, . ষড়্ ঋতুর নয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটি জানি।।
শীত এলে লেপ লই . গর্ম্মী এল ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে ‘কবির নেশায়’ দিই ঢালি।।
শরতে হেমন্তে . বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি।।
কালো মেঘে বর্ষাকালে . বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের পেকমের বাহার।
ষড় ঋতুর বারো মাসে, . মাঘের মেঘের শেষে,
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার।।
নহি কবে কালিদাস . বাগবাজারে করি বাস
পুজো এলে পুরির মিঠাই ভাজি।
বসন্তের ‘কুহু’ শুনে . ভক্তির চন্দন— সনে
মনঃফুল রামচরণে করি রাজি।।
তবে যদি কবি পাই . হটে কভু নাহি যাই,
হোক্ বেটা যতই মন্দ
জাহাজ ডোঙা শোলা নাও, . যাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।
ভোলা ময়রার একটি ছড়াগানে বাংলার কোন জেলার কী উত্তম তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়:
ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই। ঢাকার ভালো পাতাক্ষীর, বাঁকুড়ার ভালো দই। কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহের ভালো আম। উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম। রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহীর জামাই। নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই। দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো শুঁড়ি। পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি। বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ পরগনার গোপ। গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীঘ্র বংশলোপ। হুগলির ভালো কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো ঘোল। ঢাকের বাদ্য থামলেই ভালো, হরিহরি বোল।
যদিও ভোলা ময়রা তাঁর জন্মস্থানের প্রসিদ্ধ বস্তুটির উল্লেখ করেননি কিন্তু মিষ্টি তৈরি তাঁর পৈতৃক পেশা ছিল আর রসগোল্লার উদ্ভাবক নবীনচন্দ্র দাস তাঁর জামাতা ছিলেন বলে এই উল্লেখ বা অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আসলে খাদ্যরসিকদের কাছে গুপো সন্দেশই গুপ্তিপাড়ার প্রধান আকর্ষণ। আর গুপো সন্দেশকে বাংলার প্রথম ব্র্যান্ডেড মিষ্টি বলে মনে করা হয়।
বৈষ্ণব ধর্মচর্চার পীঠস্থান হওয়ার জন্য গুপ্তিপাড়াকে ‘গুপ্ত বৃন্দাবন’ বলা হত। ক্রমে ‘গুপ্ত বৃন্দাবন পল্লী’, তার থেকে ‘গুপ্ত পল্লী’ এবং পরিশেষে গুপ্তিপাড়া নাম হয়। কথিত আছে যে, গুপ্তিপাড়াতেই সন্দেশের জন্ম। এখানেই প্রথম তৈরি হয় সন্দেশের মিশ্রণ, যা মাখা সন্দেশ নামে পরিচিত। পরে সেই মাখা সন্দেশকেই আকার দিয়ে তৈরি হয় গুপো সন্দেশ। কলকাতায় এই সন্দেশ জনপ্রিয় হলে তা ‘গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ’ বা সংক্ষেপে ‘গুপো সন্দেশ’ বলে পরিচিতি লাভ করে। আবার একটি মত অনুসারে, লোকমুখে উচ্চারণে বিকৃতির ফলে গুপো সন্দেশ কালক্রমে ‘গুঁফো সন্দেশ’ নামে পরিচিত হয়েছে। অপর ভিন্ন মতে, সন্দেশটি খাওয়ার সময় গোঁফে লেগে যায় বলে তার নাম হয়েছে গুঁফো সন্দেশ।
আবার আসা যাক ভোলা ময়রার কথায়। মানবচরিত্রের আচরণের সঙ্গে বাংলা প্রবাদ প্রবচনের চটকপূর্ণ ব্যবহার ভোলা ময়রার এই ‘উতোরে’ খুঁজে পাওয়া যায়:
দারোগারই চেয়ে দেখছি চৌকিদারের হাঁক বেশী,
সূর্য থেকে বালিরই তাপ অধিক সে ভাই কোন দেশী?
সানাইটা না গর্জে যত তর্জেরে তার পো-এর দল
বালুচরেও দাঁড়িয়ে বলে হ্যাঁ এখানে হাঁটুজল।
কবিয়ালদের মধ্যে ভোলা ময়রার মত স্বাধীনচেতা আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রত্যেকেরই এক-একজন পেট্রন ছিলেন এবং মোসাহেবি করেই তাঁদের চলতে হত। ভোলানাথের কিছুরই বালাই ছিল না। একবার মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জাড়া গ্রামে ‘রায়’ পদবিধারী এক ধনিক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ি কবিগান হয়। জাড়ার কাছে মানিককুণ্ডু গ্রাম মুলোর জন্য বিখ্যাত। ভোলা ময়রা ও যজ্ঞেশ্বর ধোপা জাড়ায় জমিদারবাড়ি কবি গাইতে যান। খোশামুদে যজ্ঞেশ্বর জাড়ার জমিদারবাবুদের প্রশস্তি গেয়ে বলেন, ‘জাড়া গ্রামটা ঠিক যেন গোলোকবৃন্দাবন’। শুনে ভোলানাথ ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দেন:
কেমন করে বললি জগা,
জাড়া গোলোকবৃন্দাবন,
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে তার বাঁশের বন।।
জগা! কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
ওই সামনে আছে মানিককুণ্ড,
কর গে মুলো দরশন।
কেমন করে বললি জগা,
জাড়া গোলোকবৃন্দাবন।।
ওরে বেটা, ‘কবি’ গাবি, পয়সা পাবি,
খোশামোদি কী কারণ?
কেমন করে বললি জগা,
জাড়া গোলোকবৃন্দাবন।।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়,
মুফতের মধু অলি।
মাপ করো গো রায়বাবু,
দু’টি সত্যি কথা বলি।।
জগা ধোপা খোশামুদে,
অধিক বলব কী।।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া,
পান্তা ভাতে ঘি।।
ভোলার সৎসাহসের পরিচয় এই গান থেকেই পাওয়া যায়। যজ্ঞেশ্বরকে তোষামুদে বলেই ক্ষান্ত হননি, জমিদার রায়বাবুদের চরিত্রের ওপর টিপ্পনীও কেটেছিলেন।
বাস্তবিকই ভোলানাথ কবির লড়াইয়ে হটবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, রসবোধ, তাঁর শ্লেষ ও ব্যঙ্গবাণ, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে ভাবতেন, যে লোকটা পুরি-মিঠাই ভাজে, কোনওদিন ইংরেজি শেখেনি, চাকরি করেনি, মোসাহেবি করেনি, তাঁর এমন কাব্যপ্রতিভা কোথা থেকে এল? তাঁর নিজের ভাষায়, ‘‘জাহাজ ডোঙা শোলা নাও, যাহাতে মিলাইয়া দাও,/ ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।’’
যেসব কবিয়াল গ্রামবাংলার সঙ্গে সঙ্গে শহরের মানুষেরও মনোরঞ্জন করতে সফল হয়েছিলেন, ভোলা ময়রা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী মফস্বল থেকে শুরু করে বহু গ্রামেও তিনি কবিগানের পসরা নিয়ে ছুটে গেছেন। কবিগানের লোকমনোরঞ্জনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে লোকসঙ্গীতের এই গণ জনপ্রিয় ধারার নিবেদিত কবিয়াল, ভোলা ময়রাকে সমকালের প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মূল্যায়ন করে বলেছেন: ‘‘বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।’’
যেহেতু কবিগান পুরো বিষয়টাই মৌখিক ও তাৎক্ষণিক মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবনী উত্তর-প্রত্যুত্তরের আঙ্গিকে, তাই অনেক কবিয়ালের মতই ভোলা ময়রার অনেক কবিগানও মনে হয় কালের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে। কবিগান সম্পর্কে শিক্ষিতজনের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দশজন কবিয়ালদের জীবনী ও ২৭০টি গান সংগ্রহ করেন। এই কবিয়ালদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাসু, নিত্যানন্দ দাস, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, রাম বসু এবং অবশ্যই ভোলা ময়রা। ঈশ্বরগুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ ধারাবাহিকভাবে এঁদের সৃষ্ট বা গীত কবিগানগুলি (যেগুলো পাওয়া গেছে) প্রকাশিত হয়েছিল।
কবিয়ালদের সম্পর্কে অনেক সাহিত্য সমালোচক নেতিবাচক ধারণা পোষণ করলেও বাংলা লোকায়তসাহিত্যের এক বিপুল সম্পদ কবিগানের খনিতে জমা আছে, একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আর বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষা, জনসচেতনতার কাজেও কবিগান অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের লোকগান সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, যদি ভোলা ময়রাদের মত কবিয়ালদের নাম না নেওয়া হয়।
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল কবিগান এবং পাঁচালি গান কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, সাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতায় কবিগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও গ্রাম-বাংলায় এর জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমেনি।
ভোলা ময়রার জীবন অবলম্বনে পীযুষ গাঙ্গুলির পরিচালনায় ‘ভোলা ময়রা’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৭৭ সালে। এই ছবিটিতে অভিনয় করেন উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায় প্রমুখ। এছাড়াও ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ সিনেমায় অভিনেতা অসিতবরণ এবং ‘জাতিস্মর’ সিনেমায় খরাজ মুখোপাধ্যায় ভোলা ময়রার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
ভোলা ময়রার প্রবল প্রতিপক্ষ আ্যন্টনি ফিরিঙ্গিও ভোলা ময়রাকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। তিনি একজায়গায় বলেছেন:
জয় হোলো তোমার ভোলা কারসাধ্য তোমায় হারাতে
এবার তুমি থাকো গিয়ে ফুলবাবুদের পাড়াতে।
স্বয়ং বিদ্যেসাগর মশাই তোমায় ঠাঁই দিয়েছেন মাথাতে
তোমার মতো কবি কে আর আছে এ কোলকাতাতে
আমার জন্য থাকুক না হয় শুধুই কাঁটার জ্বালা
সবার মাঝে তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম মালা।
একজন কবিয়ালের সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার নিজের গলার মালা খুলে আ্যন্টনি ভোলা ময়রাকে পরিয়ে দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। সাহিত্যের আঙিনায় ভোলা ময়রা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য খুঁজে, জুড়ে, বুননের মাধ্যমে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটিয়ে তোলা এই লেখার উদ্দেশ্য একটাই, যুগ যুগ ধরে বাঙালি ভোলা ময়রাকে তাঁর ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দক্ষ কারিগরির সঙ্গে যুগের প্রতিনিধিত্ব করা স্বতঃস্ফূর্ত কবিগানের জন্যও মনে রাখুক, আর সেইসঙ্গে বাংলার লোকায়ত সাহিত্য ও লোকগানকে যথাসাধ্য সংগ্রহ ও সম্প্রচার করুক।