তখনও সাঁঝ নামেনি। তবে আলোও নিজের গা-মাখা হলুদের গরিমা হারিয়েছে। নরম শরীর ধোওয়া আলোয় নেচে নেচে সুধীর বাউল গাইছেন, ‘জীবন যখন বাউল বেশে,/ বেলার ধারে মুচকি হেসে…’। তখনও বিস্তর বালিয়াড়ির অনেকটা দেখা যায়। ওপারে শান্ত সমাহিত অজয়পাড়ের সোনালি গ্রামগুলি। বড় মায়া ছড়িয়ে রেখেছে। সবুজকলি বনমায়া ভেঙে ওপার থেকে অনেকেই ফিরছেন, দিনান্তের শেষ খমক বাজিয়ে। যে যার মাধুকরীর ছোট ছোট ঝোলা কাঁধে নিয়ে। রাধামাধবের নবরত্ন মন্দিরে তখন একাকী ‘গীতগোবিন্দম’ গীতের শেষ সম্রাট ফণিভূষণ দাস গাইছেন। মোহিত হয়ে বসে বসে মন্দিরের অদূরে শুনছেন, কেন্দুলির গৃহবধূর দল। তখনই পটু বাগদি এসে শ্রীখোলে হাত দেন। একটু পরে মধুমঙ্গল বাগদিও এসে কৃষ্ণমঞ্জরীতে তাল ঠোকেন। মোহন্তস্থলের ডাকে নেওয়া শেষ দ্বার টেনে অজয়ঘাট থেকে ফিরে এসে সন্ন্যাসী হাজরাও ততক্ষণে ধরেছেন সুর গীতগোবিন্দম-এর আসরে। একটু পর গানের আসর জমে উঠলে সেখানে এসে বসেন রাধাময় দাস। কেন্দুলির জয় ঠাকুর। তিনি ধরেন নিজের গান। সেই আসরের রেশটা বয়ে নিয়েই ফিরতেন, নিজের আশ্রমে। তখন আশ্রমে একদল মানুষ, হরিদাসের মন্দিরে বসে। শুনছেন মায়ের কথা। আশালতা গোস্বামী।
‘কে জানতো জয়দেবের মিলাতে গো মিলাতে/ তোমার সঙ্গে দেখা হবে, পোষের সাঁজ বিলাতে।।/ দিখা হলো ভালোই হলো/ কুন আখড়ায় উঠেছো/ উখান থেকে সঙ্গে করে/ কাউকে কি এনেছো।/ কেউ যদি না থাকে চল/ কাঙালের বটতলাতে।।’
(বানান অপরিবর্তিত)
শুনশান কদমখণ্ডীর ঘাট! মরা অজয়ের বিস্তীর্ণ চর! রাত বাড়ছে। গড় জঙ্গলের শৃগালের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, এপারের আশ্রম থেকেও। শুনশান নীরবতার অন্ধকার রাতে, তিনি গাবগুবি বাজিয়ে আশ্রমে বসেই গাইছেন নিজের পদ। পাশে বসে শুনছেন, এক সুবর্ণকঙ্কণ পরা অপূর্বসুন্দর নারী! ভাঙা এক কুচি চাঁদের লুকোচুরি চলছিল কৃষ্ণকালো আকাশের ঝুঁটিতে! দূরের নদীগহ্বর থেকে, শ্মশানভূমির দিক থেকে ভেসে আসছে মাতাল রাতপাখির চিৎকার। জ্বলন্ত উনুনের চোখের কিনারে চলকে ভেসে আসছে আলো! টিমটিম করে আশ্রমের আঙিনায় জ্বলছে কেরোসিন কুপি! শিখার সমবেত কালো গিয়ে মিশছে রাতের অন্ধকারে। আশ্রম চাতালে সাদা পোশাকের মাঝবয়সী সাধক বসে বসে তন্ময় হয়ে গাইছেন! তিনি দাস রাধাময়। কেন্দুলির আত্মজন জয় ঠাকুর। কেন্দুলির উন্নয়নের প্রথম কাণ্ডারী রাধাময় গোস্বামী।
শুনুন, দাস রাধাময় রচিত জনপ্রিয় লোকগান…
তাঁর জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে। বর্ধমানের খাসপুরের রশীদ ডাক্তারের ছেলে কাজী নুরুল ইসলামকে ছাত্রাবস্থায় অনেকেই দেখেছেন বীরভূমের খুজুটিপাড়া, বর্ধমানের মঙ্গলকোট এলাকাতে ঘুরে বেড়াতে। বাউণ্ডুলে জীবন। বর্ধমানের মঙ্গলকোটে পড়াশোনার সময় অজয়ের কোলে কোগ্রামের লোচন দাসের সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। তার বেশ কিছু কাল পরে তিনি বর্ধমান শহরে গিয়ে শুরু করেন বসবাস। সেখানেই তিনি সুভাষপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শুরু হয় অন্য জীবন। নুরুল ইসলামের ভাই হেমন্ত ইসলাম, খুজুটিপাড়া কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তবে পুঁথিগত শিক্ষায় নুরুল ইসলামের পড়াশোনা তেমন ছিল না।
স্থানীয় রাজনীতির ঘোলাজলে বেশিদিন টেকাতে পারেননি নিজেকে। পুনরায় নিজের জানাচেনার গ্রাম খুজুটিপাড়াতে ফিরে আসেন। ঠিক সে সময়েই খুজুটিপাড়া সরকারি হাসপাতালের সেবিকা আশালতাদেবীর সঙ্গে আলাপ। প্রথম আলাপেই তাঁর প্রেমে পড়েন নুরুল ইসলাম। আশালতাদেবী বীরভূমের কুণ্ডলা গ্রামের তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। আর তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল সিউড়ির ধ্বজাধারী চট্টরাজের সঙ্গে। ১৮ বছর বয়সে বৈধব্য আর তার ঠিক কিছু দিনের মধ্যেই পিতৃবিয়োগ ঘটে তাঁর। জীবনের সেই সংকটকালে, আশালতা কাজী নুরুল ইসলামের সঙ্গলাভ করেন। নিজেকেও বদলে নেন নুরুল ইসলাম। পূর্বাশ্রমের জীবন ছেড়ে তিনিও বৈষ্ণব আচারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের একটি কন্যা, নাম বন্যা।
‘মন্দ ভালো দুটিই সমান সংসারে।/ কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়/ একটু দেখ খোঁজ নিয়ে।’
ঠিক সেই সময়েই কাজী নুরুল ইসলাম সংসারের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে মুর্শিদাবাদের রাধারঘাট আশ্রমের নিতাই খেপার কাছে গিয়ে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা ও তাঁর থেকেই সন্ন্যাস নেন। সেই নবীন সন্ন্যাসীর জন্মনাম ছেড়ে সাধনার পথে নতুন নাম হয় রাধাময় গোস্বামী। রাধাময় গোস্বামীও কখন একসময় দাস রাধাময় হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণব ধর্ম নেবার মূলে তাঁর আশ্রয় ছিলেন বাউল সম্রাট পূর্ণদাসের মা ব্রজবালাদেবীই। এরপর থেকেই নিয়মিত মুর্শিদাবাদের বাউল তীর্থক্ষেত্র রাধারহাটে যেতেন দাস রাধাময়।
‘ও পরাণের কালো পাখি/ ভিজে ছোলায় ভোলে না/ সোনার খাঁচা গড়ে তুমি/ ধরা পেলে না!’

আশালতাদেবী তখন বীরভূমের পাঁচড়াতে চাকরি করতেন। সেখানেই কোয়ার্টারে থাকতেন। তার সঙ্গে থাকতেন রাধাময় দাসও। দুবরাজপুরের থেকে ৫-৬ কিমি দূরে পাঁচড়া। সেখানে থাকতেই দাস রাধাময়, পাকাপাকিভাবে কেন্দুলিতে থাকার পরিকল্পনা করেন। সে সময়ই ১৯৭০ সালে তিনি ‘চণ্ডীদাস প্রেস’ তৈরি করেন। তখন ‘পাহাড়েশ্বর’ পত্রিকার সম্পাদক নবী কাদেরী, পত্রিকাটি ওই প্রেস থেকে ছাপা হত। পরে দাস রাধাময় ‘চণ্ডীদাস’ কাগজ প্রকাশ করতে শুরু করেন, সালটা ১৯৭১।
এরপরই তিনি ধর্মসঙ্গিনী আশালতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন বীরভূমের অজয় নদের তীরবর্তী জয়দেব কেন্দুলির সেদিনের নির্জন গ্রামে। সেখানে শ্রীশ্রী হরিদাস আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে, গৃহী বৈষ্ণব সাধকের জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করেন। মনের আনন্দে বাঁধেন গান। ঠাকুর হরিদাসের মূর্তির সামনে বসে সে গান গাইতেন, লম্বা দীর্ঘদেহী ফর্সা কপালের মানুষটি। কাঁচা চুলের বৈরী ঝুঁটি মাথার উপরে আর মুখে কাঁচা-পাকা মানানসই দাড়ি। গালভরা হাসি। অন্যরকম ব্যক্তিত্বের চেহারার এই মানুষটি জয়দেবের মাটিতেই প্রথম শুরু করেন ‘চণ্ডীদাস’ পত্রিকা। তা ছাপা হত, তাঁরই নিজেরই দুবরাজপুরের ‘চণ্ডীদাস প্রেস’ থেকে।
‘বেনারসি ছিড়ে গেল হাঁসা পাথরে/ পিরীতির বেদনা আমার গায়ে গতরে।।/ লাগবে জোড়া ছেঁড়া কাপড়/ উঠবে সেরে ভাঙা গতর/ তাই পিরীতের হাঁসা পাথর/ লুকিয়ে রাখি পাঁজরে।।’

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে তিনি কেন্দুলির উন্নয়নের জন্য স্থানীয় মানুষদের নিয়ে শুরু করেন ‘জয়দেব অনুসন্ধান সমিতি’। এ-কাজে তাঁকে কেন্দুলির শ্রীশ্রী নিম্বার্ক আখড়ার মহান্ত মহারাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এদিকে ওড়িশার পণ্ডিতেরা সে সময় কবি জয়দেবকে তাঁদের ওড়িশার মানুষ বলে নানা দাবি তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, ওড়িশার কেন্দুলা নামের একটি গ্রামে তাঁর জন্মভূমি। সেখানেই নাকি ‘গীতগোবিন্দম্’-এর রচনা! এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ দাস রাধাময় জয়দেব কেন্দুলিতে ও বীরভূমের সিউড়িতে রাজ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতদের ডেকে এনে প্রতিবাদসভা করেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলনের মুখ। তাঁরই লড়াইয়ের ফলে মহান্ত আখড়ার শ্রী হরিকান্ত শরণদেব ব্রজবাসীর দেওয়া ‘জয়দেব অনুসন্ধান সমিতি’-র রেজিস্ট্রারকৃত জায়গায় বর্তমানে সংগ্রহশালা, বাউলমঞ্চ ও গ্রন্থাগার নির্মিত হয়েছে।
‘যারে যা বোষ্টমী যা ঘর থেকে/ আমি ভাত রেঁধে খাব কাল থেকে।/ আমি মাধুকরী করব নিজে/ চোখের জলে ভিজে ভিজে/ আবার পান্তা ভাতে ঘি খাব রে/ গায়ে গরম ত্যাল মেখে।।/ যা রে যা বোষ্টমী যা ঘর থেকে।’
দাস রাধাময় মনে করতেন ‘গৌরাঙ্গ দর্শনই মানুষকে মানুষ করার ও মুক্তির একমাত্র পথ।’ এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে তিনি ‘আন্তর্জাতিক শ্রী চৈতন্য দর্শন প্রচার সমিতি’ তৈরি করেন। জেলা থেকে জেলান্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ‘অখিল ভারতীয় ভাষা সাহিত্য সম্মেলনে’ জাতীয় সংহতির ওপর বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন।
‘পিরীতি হয় না জানি/ জাতে বেজাতে/ খিচুড়ি হয় মিশে গেলে/ ডালে আর ভাতে।।’
তিনি তাঁর আশ্রমে বসেই তিন শতাধিক জনপ্রিয় গান লিখেছেন। তাঁর বহু বাউলগান জনপ্রিয়। বহু শিল্পী তাঁর লেখা গান গেয়ে নাম করেছেন। অনেকে নিজের নামেও চালাচ্ছেন এখন তাঁর গান। ১৯৮৯-এর ১০ আগস্ট তিনি সিউড়ি হাসপাতালে লোকান্তরিত হন। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে। লিভার ক্যানসারে তিনি মারা যান। দীর্ঘ জীবনের লড়াইয়ে তিনি না খেয়ে খেয়ে এই রোগে পড়েন বলতেন আশ্রমমাতা। তাঁরই নির্দেশে তাঁর মৃতদেহ আশ্রমে এনে বকুলতলায় সমাধিস্থ করা হয়। আশ্রমে রয়েছেন আশালতার পূর্বাশ্রমের একমাত্র পুত্র সত্যকাম।
‘ঝিঙেফুলি সাঁঝেতে/ পেয়ে পথের মাঝেতে/ কাদা দিলি তু কেনে কাদা দিলি সাদা কাপড়ে।’
তাঁর একটি বিখ্যাত গান আজ অনেকেই নিজের নামে চালাচ্ছেন। যদিও গানটি প্রথম বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হেনা মুখার্জি ‘কিরণ কোং’ ক্যাসেট কোম্পানি থেকে রেকর্ড করেন, সেই সত্তরের দশকে। পরবর্তীকালে গানটি বেতারে গেয়েছেন জয়দেবের শিল্পী শান্তি রজক, সেটাও সত্তরের দশকের শেষ দিকে হবে।

লালমাটি আর বাউলদের দেশ বীরভূম। সেখানেও আপ্তবাক্যের সাধনা ছেড়ে ‘বাবু বাউল’-দের নিয়ে মাতামাতি। কেউ সাধন পথের পথিক নন, কেবল গান গেয়ে থাকেন। এঁরা যেন বাউল গানের গায়ক। সেই পরিবর্তন ধরতে গিয়েই দাস রাধাময় লিখেছেন— ‘দ্যাশ ভরেছে বাবু বাউলে/ তারা জামা জোড়া পরছে এখন/ ভোর কোপীন খুলে ফেলে।’ কিংবা অসম্ভব জনপ্রিয় একটি লোকগানে, এই বৈষ্ণব কবি তুলে আনছেন সাংসারিক কুটকচালি। স্বামী-স্ত্রীর নানান সাংসারিক ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই লোকগানটি। সেদিনের বিভিন্ন শিল্পীরা তাঁর এই গানটি গেয়েছেন। চালিয়েছেন নিজের নামেও! ‘ঠাটের কথায় হেসে বাঁচি না/ পাটের শাক লাটের বিটির মুখে উঠে না।।’
জীবন নদীর চরে ঘুরে তিনি দেখেছেন যে মরার আগে মরে সে কেবল মরে। জয়দেবের যে আশ্রম ঘিরে সাংস্কৃতিক উন্মাদনার ঝড় উঠেছিল ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে, সেই শ্রীশ্রী ঠাকুর হরিদাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও দাস রাধাময়। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সহধর্মিণী আশালতাকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে জয়দেবেই থাকতেন। তাঁর গানের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমীদের। পরবর্তীকালে বর্ধমানের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুমুদকিঙ্কর নামও নিয়েছিলেন। তিনি দুবরাজপুরে ‘চণ্ডীদাস প্রেস’ ও জয়দেব থেকে ‘চণ্ডীদাস’ পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি কেন্দুলিতে প্রতিষ্ঠা করেন ‘জয়দেব অনুসন্ধান সমিতি’।
‘তু দাঁড়া নদীর মাঝখানে/ এক খিলি পান খাব দু’জনে।/ (হায়) তলিয়ে গেলে মিলিয়ে যাবি/ কুযশ হবি ভুবনে।।’
তাঁর সাধনসঙ্গিনী আশালতা দেবী মারা যান ১৯৯৫ সালের, ৩০ জুলাই। পরবর্তীতে শ্রীশ্রী ঠাকুর হরিদাস আশ্রম ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে। যার মোট সদস্যসংখ্যা ১০ জন। কার্যকরী সভাপতি আল আফতাব, সম্পাদক শান্তি রজক। তাঁরই চালান আশ্রম। তবে আশ্রমের অধীনে থাকা জয় ঠাকুরের চণ্ডীদাস প্রেসটি বিক্রি হয়ে গেছে। আশ্রম সংলগ্ন ৯টি দোকান, বিস্তীর্ণ জায়গা রয়েছে। কেন্দুলিতে এখনও তাঁর গান গেয়ে মাধুকরী করেন বাঁকাশ্যাম, লক্ষ্মণ, তন্ময়, সাধু দাসেরা।





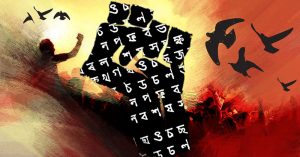



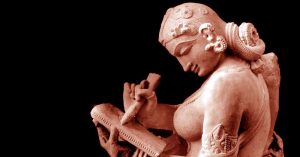





One Response
দারুণ। গান টা শুনে খুব ভালো লাগলো?