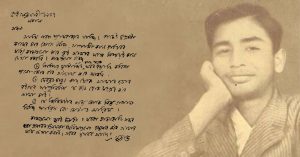কাল ভাল ঘুম হয়নি সনাতনের। সারারাত এপাশ ওপাশ করেছে, বাইরেও গেছে দু-তিনবার, আর আকাশের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। সন্ধ্যায় বিষ্ণুর দোকানে গেছিল নস্য কিনবে বলে। বিষ্ণু খাতির করে প্রায়ই বসায় সনাতনকে, চা সাধে। এমনিতে ব্যস্ত বিষ্ণু তার মুদিদোকান নিয়ে। যতক্ষণ খোলা থাকে, খদ্দের পড়তে পায় না। ন্যায্য দাম আর খাঁটি জিনিস, এর জোরেই আজ তিরিশ বছর ধরে অঞ্চলে আর কোন দোকানকে টিকে থাকতে হয়নি। কিন্তু এ হল গিয়ে বিষ্ণুর বেচার মূলমন্ত্র। কেনার মন্ত্রও আছে তার। সাচ্চা মানুষ কেনার। মাসখানেক হয় এসেছে সনাতন। প্রায় রোজই আসে বিষ্ণুর দোকানে। ক’দিনেই বুঝেছে, এই সনাতনও একজন সাচ্চা মানুষ। দু’দিনের জন্য এসে মহাদেববাবুর বাড়িতে একমাস রয়ে গেল। বউ ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু কোনও পিছুটান নেই। চিঠিপত্তর? পায়ও না, দেয়ও না। জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘ও আছে। ভালই আছে মনে হয়।’
সনাতনকে প্রথম আলাপের দিন বিষ্ণু যথারীতি বসিয়েছিল দোকানের ভেতরে রাখা কাঠের টুলটিতে। এমনিতে নিপাট কাঠের টুল, তাতেই ক’দিন বসছিল সনাতন। কিছুদিন। কিন্তু যেদিন থেকে বিষ্ণু সাচ্চা মানুষ হিসেবে চিনেছে সনাতনকে, বাড়ি থেকে একটা পুরনো চাদর ভাঁজ করে পেতে দিয়েছে টুলের ওপর। আজও যথারীতি একই অভ্যর্থনা। কিন্তু আজ বিশেষ কথার ইচ্ছে নেই সনাতনের। অমাবস্যা আজ। মহাদেবাবুকে আজ একটু বেশিক্ষণ দলাইমলাই করতে হবে। তাছাড়া কাল রাতে ঘুম না হয়ে শান্তিতে নেই সনাতন। ঘুম না হবার সূচনাটা তো এই টুলে বসেই আবার। টুলে বসেই, প্রায় যেমন করে সনাতন, বিষ্ণুর দাড়িপাল্লার পাশে রাখা ছেঁড়া কাগজগুলোর দিকে তাকায়। তুলে নেয় দু-একটা। ওগুলো বিষ্ণুর কাজে লাগে খদ্দের যখন দু’টাকার চা অথবা এক টাকার জিরে চাইতে আসে। তখন ঠোঙা পোষায় না, খুচরা কাগজ। অনেক সময় পাড়ার কীর্তিমান ছেলেরা স্কুলের বই বিক্রি করে সেই পয়সায় বিড়ি ফোঁকে ক’দিন। তা সনাতন এই করে বিষ্ণু ছেঁড়ার আগেই প্রায় আস্ত একখানা ‘চিত্রে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ’ পেয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ সচিত্র ও বাংলা অনুবাদ সমেত। দাম দিয়েই কিনেছিল, পাঁচ টাকা কিলো দরে। ৪৬০ গ্রাম, কিনা দু’টাকা তিরিশ। কিন্তু খাতির করে তিরিশ নেয়নি বিষ্ণু। পড়াশুনার সঙ্গে সনাতনের সম্পর্ক খুব নিবিড় নয় কখনওই। খবরের কাগজটা পেলে অবিশ্যি পড়া আছে আদ্যন্ত। তা মহাদেববাবুর বাড়ি আসা ইস্তক রোজই হচ্ছে। তাকে তো পড়েও শোনাতে হয়। তাছাড়া কাল ওই ছেঁড়া কাগজ পড়াটাই কাল হল সনাতনের। প্রায়ই ছেঁড়া কাগজ টেনে নিয়ে তার দু’পৃষ্ঠাই পড়ে ফেলে দোকানে বসে, যে কাগজের আদি নেই, অন্তও না। কিন্তু কাল একটা ছেঁড়া কাগজ পড়তে গিয়ে মাথাটাই ঘুরে গেল সনাতনের। শনিগ্রহ নিয়ে লেখা। শনির নাকি সতেরোটা চাঁদ, আর সারাদিন ধরে কোনও না কোনও চাঁদ শনিকে পাহারা দিচ্ছে বলে শনিতে নাকি রাত বলে পদার্থ নেই। বলে কী! সতেরোটা চাঁদ একসঙ্গে ওঠে যদি, সূর্য হার মেনে যাবে যে! আর মানুষই বা সেখানে করে কী এত চাঁদ নিয়ে? পৃথিবী থেকে শনির দূরত্বের কথা, শনির অসীম শৈত্য সম্পর্কেও বার্তা ছিল ছেঁড়া পৃষ্ঠাটিতে, কিন্তু সে-সবের তাৎপর্য সনাতনের মালুম হয়নি।
বিষ্ণু চা আনায়। আসন্ন ইলেকশনের খবর জানতে চায় সনাতনের কাছে। সামনে ভোট। যথারীতি সারা দেশের মত এ-অঞ্চলও সরগরম। পোস্টার পড়ছে। মিটিং মিছিল চলছে, ছেলে-ছোকরারা তাই চনমনে। বিষ্ণুর দোকানে বিড়ি সিগারেট বিস্কুট মুড়ি চানাচুরের বিক্রি বেড়েছে। চাহিদা দেখে কেকও রাখতে হচ্ছে। তুলি রং আর্ট পেপার। চলবে আরও দিন পঁচিশ-তিরিশ। উত্তেজনাটা এ পাড়ায় একটু তুঙ্গে, কেন-না বনমালীপুর থেকেই এবার দাঁড়িয়েছে এক ক্যান্ডিডেট, একেবারে লোকসভায়। কিন্তু সনাতনের আজ আর কোনও হুঁশ ছিল না বিষ্ণুর করা নির্বাচনের প্রশ্নে। তার মাথায় এখন শনি। আর তার সতেরোটা চাঁদ। আরও নাকি আবিষ্কৃত হতে পারে। তখন তো চাঁদের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আলোও বেড়ে যাবে, নাকি চাঁদ বাড়বে শুধু? মালিশেও মন ছিল না আজ তাই। অমাবস্যা পূর্ণিমায় একটু কাহিল থাকে মহাদেবের শরীর। চোখ তো অন্ধ। বয়স? কেউ বলে পঁচাশি, আবার কেউ বলে নব্বই ছাড়িয়েছে। খাওয়াদাওয়া, ঘুম, তামাক টানা, জেগে থাকা এসবই ঠিক আছে। তবে পায়ে বল নেই, সেজন্যই মালিশ। বনমালীপুরে এবার সনাতন এসেছিল আসলে বিভূতির জামাইয়ের সঙ্গে। তা প্রায় বছর-ষোলো পর। রতিকান্তই বলেছিল বিভূতিকে, ‘মেয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ, সনাতনকে সঙ্গে পাঠাও, বড় পয়া। তিনশটি টাকা গুঁজে দিয়ো পকেটে। কিন্তু এমনিতে নেবে না। সংসার আছে, আয় নেই। সবাই দেয়। ওর কোনও ডিম্যান্ড নেই।’ বনমালীপুর শুনেই সনাতন খুশি হয়ে উঠেছিল। মহাদেববাবুর সঙ্গে দেখা হবে আবার। বেঁচে আছে তো? অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধারে মহাদেবের পায়ে মালিশ চালাতে চালাতে সনাতন ভাবে, এত চাঁদ নিয়ে শনি করে কী?
‘আস্তে সনাতন, আস্তে। তুমি যে মহীরাবণ হইয়ে উইঠলে। খালি হাড় আর চামড়া, মাংস নেই। বুঝে করো।’
দাওয়ায় কোনও আলো নেই। মাটির দোতলা ঘর। কুয়ো আছে, গোয়াল, পুকুর। উঠোনের তিনদিক ঘিরে ঘর, মধ্যখানে ফুলের বাগান। আকাশের অন্ধকার মহাদেবের দাওয়ায় একচ্ছত্র ছড়িয়ে। এতই, যে মহাদেবকে দেখা যাচ্ছে না। আর মহাদেবের কাছে তো আলো আর অন্ধকার, দুই-ই সমান। চিরকালই মহাদেবের এই দাওয়ায় শোওয়ার অভ্যাস। দেয়ালে তার হাঁসফাঁস। পরিবারে ছেলে, ছেলেবউ, নাতি-নাতনি, তা জনা-বারো। ছোটটা পলাশি যাতায়াত করে। মেজর ব্যবসা। বড়ছেলের নাতিও আছে। এই ঘরেই চার পুরুষ।
‘চৌকি দিতি পারবা সনাতন?’ প্রশ্ন সঠিক কানে যায় না সনাতনের। সে তখন দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে ঠায় তাকিয়ে— অগুনতি তারার মধ্যে শনিকে আর তার চাঁদগুলিকে শনাক্তকরণের চেষ্টায়।
‘ও সনাতন! কী ভাবতিছ, কও দিনি? চৌকি দিতি পারবা?’
এবার শুনতে পায়। হ্যাঁ পারবে, কেন নয়? রাত জাগা, তাও অভ্যাস আছে। মহাদেবই ভেবে ঠিক করেছে, কিছু একটা করা দরকার সনাতনের। বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে আছে। দু’দফায় পাঁচশো পাঁচশো হাজার দিয়েছে মহাদেব, লজ্জার মাথা খেয়ে নিয়েছে সনাতন। কিন্তু এবার টাকা দিতে চাইলে বাড়ি হাঁটা দেবে বলেছে। অবুঝ! এই বয়সেও অবুঝ সনাতন। আসবার দিন আবার এক কেজি মাগুর! সেই চোদ্দো বছর আগে বলেছিল মহাদেব, মাছ খাবে তো মাগুর, মহাদেব নিজে যা ভাল খায়। সে-ই কথা মনে রেখেছে। বারবারই মনে হয়েছে মহাদেবের, সনাতনের একটা কাজ দরকার। সনাতন থাকুক তার কাছে, জীবনভর থাকুক। মাঝে মাঝে যাবে বউ ছেলেমেয়েকে দেখতে।
‘রিদয়ডা তোর বড়ই রেইখে দিয়েছিল সনাতন। শুইনলাম আমার টাকাথথে মহিমরে দুইশত দান করা হইছে?’
উত্তর নেই এবারও। হৃদয় না কী একটা শুনেছিল বটে, কিন্তু সনাতনের চোখ এখন আকাশে, মনও। উঠে বসে মহাদেব। সন্ধেবেলার চা-জলখাবার অমনি একটু পেটে নাড়া দিয়ে যায়। নাড়া খায়, চাউর হয়, শব্দ করে, মহাদেব শোনে, সনাতন শোনে।
‘ও সনাতন! বাড়ির জন্য চিন্তা হচ্ছে?’
সনাতন চেতনায় ফেরে। লজ্জা পায়। বলে, একটা কিছু তো বলতে হয়ই, নইলে আরও লজ্জা। কথাটা শুনতে না পাওয়া মহাদেবের অপমান।
‘ওই তো, মনটন আর কী।’ বাইরে চৈত্রের অন্ধকার রাত, জোনাকির ওড়াউড়ি, ওরাও শুনতে পায়।
ধীরে হাত বুলায় মহাদেব, সনাতনের পিঠে।
‘তা কইনি। মন কইনি, বলিছি রিদয়। মন আর রিদয় কি এক হইল? দেবী মহামায়ার মন পইড়েছিল বক্রেশ্বরে, আর রিদয় পড়ে বদ্যিনাথে। দুড়ো এক?’
‘আচ্ছা মহাদেবদা! আকাশে ওইটে শনি, লয়?’
সনাতনের তাড়িত প্রশ্ন। এতই তাড়িত যে সে ভুলে গেছে মহাদেব এখন অন্ধ। মহাদেব আবারও হাসে। হাসে, আর হাত বুলায় সনাতনের পিঠে। কম্পিত আদর।
‘সেই এলি, চোখ থাকতি এলি নে সনাতন? তা ছাড়া শনি তো কথায় কথায় খালিচোখে দ্যাহা যায় না। আমি পেনশন পাই কত জানো?’
খালিচোখে দেখা যায় না শনিকে, এই বাক্যে গভীর প্রত্যয় আনতে গিয়ে হতাশ হয় সনাতন, মহাদেবের প্রতি সেইসঙ্গে তার মনোযোগও ফিরে আসে। মহাদেবের কপালে একটা জোনাকি বসেছে, তার আলোকে তাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। তা বাদে জানে মহাদেবদা, অনেক জানে। প্রায়ই তো রেডিও শোনে। মহাদেবের রেডিও সনাতনকেও শিখিয়েছে অনেক। কিন্তু ও রেডিও শুনতে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না সনাতনের। মহাদেবের রেডিও কেবল একটা সেন্টারই ধরে, তাতে ভারতবর্ষের খবর কদাচিৎ থাকে। ইলেকশনের মরসুম এখন, খবরের কাগজে কেবল হয়? দু-একবার মহাদেবকে কলকাতা ধরতে বলেছিল। মহাদেব হাসতে হাসতে বলেছে, ‘কিন্তু ওটি হতিছে না। এহানে আর সব পাবি সনাতন। না, এটি হচ্ছে না তোমার। তারপর কি করবা তা তোমার সিদ্ধান্ত।’ তাই আর ঘাঁটায়নি সনাতন। কেবল রেডিওর কারণেই তো আর বাড়িমুখো হওয়া যায় না। এই বৃদ্ধ বয়সে মহাদেবকে দেখবে কে? ভাগ্যিস ঘটনাচক্রে বনমালীপুরে এসে পড়া, আর এসে মহাদেবকে জীবিত দেখা।
বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মালতী ফুল ফুটছে আর বসন্তের বাতাস তার গন্ধ এনে দিচ্ছে। এখন একটু বসে থাকতেই ভাল লাগছে মহাদেবের। বড় সৎ আর অবুঝ এই সনাতনটা। ওর পিঠে হাত দিতে দিতে মনে হয়, রাত কত হবে? আটটা সাড়ে আটটা। বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে। কিন্তু মহাদেব এই দিকটায় নিরিবিলি থাকে, আলো জ্বলতে দেয় না। চোখ ছিল যখন, তখনও রাতে হ্যারিকেন জ্বালাত। বিজলি বড় প্রয়োজনাতিরিক্ত আলো দেয়। রিটায়ার করেছে তাও প্রায় বছর-তিরিশ। পেনশন আট হাজার, সনাতন জানে। নিজের জন্য মহাদেবের খরচ সামান্যই। বাকিটা জমায়। ছেলেমেয়ের জন্য দরকার হবে না, সকলেই প্রতিষ্ঠিত। জামাই হেডমাস্টার, তা সেও তো এখন পেনশনার। জমুক। এখন থেকে নিয়মিত দিতে হবে কিছু সনাতনকে। রাজি করাতে হবে নিতে।
“সনাতন! মনে পড়ে? কুমারধুবি, মনে আছে কুমারধুবি, মনে আছেনি তোমার? প্রথম আলাপ হল তোমার সনে? আমারডি অতগুলান টাকা? চল্লিশ হাজার! মনে পড়ে?’ পড়বে না কেন? সনাতন কদাপি স্মৃতিভ্রংশপরায়ণ নয়। জীবনের কত জায়গাতেই তো ডেরা বাঁধতে হয়েছিল তাকে, শিখতে হয়েছে কত পেশা। রান্নার বামুনগিরি থেকে কয়লা বিক্রি, কত রকম! আবার পৌরোজিহ্য। বাড়িঘর রং করা। তো সেবার সনাতন রাঁধুনি, কুমারধুবি ফায়ারব্রিক কোম্পানির এক সাহেবের বাড়ির বামুন। সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল দোকান ল্যাকটোজেন কিনতে, পথে আলাপ মহাদেবের সঙ্গে। মহাদেব যাবে ধানবাদে। ট্যাক্সি অটো কোত্থেকে পাওয়া জিজ্ঞেস করতে সনাতন একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করে নেয় মহাদেবের। তারপর জানায় তাকে, সব আছে, অটো, ট্যাক্সি সবই। কিন্তু সন্ধ্যার পর টাকার জন্যও এ দিগরে মানুষ খুন হয় তা বোধকরি জানা নেই ধুতিকোট পরা মানুষটির। অতএব মহাদেবকে সে তার আশংকার কথাটি ব্যক্ত করে। সর্বনাশ! মহাদেব যাচ্ছে ধানবাদে তার মেয়ের কাছে, নাতনির হার্টের ধরা পড়েছে, টাকা নিয়ে। আসানসোল পর্যন্ত ট্রেন, তারপর একটা বাস পেয়ে উঠে পড়ল, যদ্দুর এগোনো ধানবাদের বাসের দেরি আছে। মারাত্মক বেকুবি কাজ হয়েছে। কাল ধানবাদের ট্রেনে এলেই পারত। সাহেবের বিবির নবজাতকের জন্য ল্যাকটোজেন কিনতে আসা সনাতনের এদিকে দেরি যাচ্ছে অনেক। তবু সনাতন বিবেচনা করে, এই সহসা আগন্তুকের চকচকে জুতোজোড়ার জন্যই তো সে খুন হয়ে যেতে পারে!
‘আমার বাড়ি লন।’ বলেছে বটে, তবে একই বা বিশ্বাস কী? তবে নিশ্চিত করল শেষে ওই ল্যাকটোজেনের কৌটা। না, এই সন্ধ্যায় এই কৌটা নিয়ে কেউ ঠ্যাঙাড়ে সাজে না! যেতে যেতে সনাতনও বুঝতে পারে, এ লোককে তার কুচ্ছো রান্নাঘরের পাশের শ্যাওলা ধরা মেঝেয় রাত্রিবাস করানো যাবে না। সে তাকে নিয়ে গেল নিতাইয়ের ঘরে। ব্যাচেলর মানুষ, ওর খাটে এক রাতের মত এঁটে যাবে। নিতাই বরং আজ সনাতনের সঙ্গে থাকবে। হ্যাঁ রাতে আহারও করিয়েছিল সনাতন। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মহাদেব, না মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে। তার হয়তো কিছুই হত না সে রাতে বা রাহাজানি, মৃত্যু দুটোই হত। কিন্তু একজন মানুষ সময়মত ছিল বলে সেসব কিছুই হয়নি। সে-ই আলাপ। কত মহাদেবের কাছে ছিল সে রাতে, তা অবিশ্যি জানত না সনাতন বা মহাদেবের আশ্রয়দাতা সেই সনাতনবান্ধব, তবে তারা দু’জন মিলে মহাদেবকে সর্বস্বান্ত করলে তার কিছু করারও ছিল না।
পাখি ডেকে ওঠে। এ সময় তো ঠিক কূজনের লগ্ন নয়। শনির চিন্তায় ছিল বলেই কি…
‘আচ্ছা মহাদেবদা!’
‘কিছু করা, সনাতন?’ মহাদেব কখনও তুই, কখনও তুমি কয় সনাতনকে। মুড বুঝে।
‘আচ্ছা, সেই ভরণ্যপক্ষীর বিত্তান্ত?’ কথা বেশি বলে না সনাতন। না, লাজুক বা কথায় দড়ো নয় বলে নয়। পুরো একটা বাক্য নিতান্ত দরকার না হলে বলে না। দেখেছে কাজ বরং এতেই চলে বেশি। অল্পে হলে বেশিতে কী বা কাজ?
মহাদেব উত্তর করে না। সনাতন আবার ভরণ্যপক্ষীর কথাটা তোলে। বেদ পুরাণ খুব পড়েছে মহাদেবদা; বসে শুয়ে মালিশ নিতে নিতে সনাতনের কাছে গল্প করে। মহাভারত কিঞ্চিৎ তো সনাতনও জানত। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সারথির নাম ইন্দ্রসেন; উত্তরকুক যে সাইবেরিয়া, দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির যে সুযোধন ডাকতেন, এত জানত না সে। এইভাবেই ভরণ্যপক্ষীর কথা এসে পড়ে, শেষ হয়নি। এটি নিয়ে তাই কৌতূহল জেগে আছে। পাখির ডাক এখন সনাতনকে উসকে দিচ্ছে।
‘ভরণ্যপক্ষী? বলিছিলাম? আছে? আছে সে এক গল্প। আইজ না। পিরতিমের তো বিয়ে দিতে লাগে, কিনা? সেসব কী ভাবিছ কও। বয়স কত যেন?’
ভাবেনি সনাতন। বত্রিশ বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে একবারের জন্যও না। ভাবতে গেলেই মেলা ঝামেলা, টাকাপয়সার খেল, লোক খাওয়াও, হেন দ্যাও, তেন দ্যাও। তা না ভাবাই ভাল। তাতে হলে হবে বিয়ে। হয়ে যায়, সকলেরই তো হয়। ভাবলেও হয়, না ভাবলেও হয়।
মহাদেব বোঝে, সনাতনকে বৃথাই প্রশ্ন করা।
নব্বই প্রায় বয়স হয়েছে মহাদেবের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জন্ম, কম তো দেখেনি জীবনে। সেই কুমারধুবির ঘটনার পরদিন তাকে বাসে তুলে দিতে এসেছিল সনাতন। তার আগে নিজের পয়সা খরচ করে ধাবা থেকে চা জলখাবারও খাইয়েছে, কিছুতেই পয়সা দিতে হয়নি মহাদেবকে। কৃতজ্ঞ মহাদেব একশোটি টাকা হাতে দিতে গেলে স্মিত হাস্যে বলেছে, ‘আমি তো চাকরি করি।’ নাম ঠিকানা নিয়ে এসেছিল। ধানবাদের কাজ মিটে গেলে বাড়ি এসে দুশো টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে মহাদেব, আসতেও বলেছে একবার তার বাড়িতে। ‘সনাতন, ছোটভাইও আজকাল এত করে না, তুমি সেদিন যা করেছ। সময় করে একবার এসো আমার কাছে। টাকাটা পাঠালাম তোমার বউ ছেলেমেয়েকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য। আমার অধিকার।’ ঠিক এসেছিল সনাতন। তখন কুমারধুবি থেকে সে ঝাড়া হাত-পা। যাত্রাদলে যোগ দিয়েছে সে। সাতমাস কাজ করো, বারোমাস মাইনে পাও, তোফা চাকরি।
একটু মৃদু শব্দ হতে থাকে। যা ক্রমশ এগিয়ে আসে বলে মনে হয়, আর যত এগিয়ে আসে, বাতাসে ততই সেই জনতার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আলো ফেলছে ওরা টর্চের। দূর থেকে গাছপালা, বাড়িঘর ভেদ করে সেই আলো ঝিলিক দেয়, সনাতন দেখে। মহাদেব বলে, ‘কারা বোধ করি, এদিকিই আসতিছে সনাতন। ভোটের দল, পেত্যয়। রগড় শুরু হইছে আবার। চোখ নেই, হাঁটতে পারিনে, তবু ভোটওয়ালাগের আসার বিরাম নেই। রগড় রগড়, রগড় যুগলি খেলার রগড়। এবার আবার এ গ্রামেই ক্যান্ডিডেট। জয়রাম।’
হ্যাঁ, মহাদেবের অনুমানই অভ্রান্ত। প্রায় জনা পঁচিশ-তিরিশজন দ্রুতবেগে, হাতে অনেকেরই টর্চ, মহাদেবের উঠোনে এসে হাঁক পাড়ে, ‘দাদু আছেন নাকি?’ সনাতন ভাবে, ভরণাপক্ষী আজও হল না!
বলতে বলতে দাওয়ার কাছে এসে যায় তারা। অন্ধকারে ভাল মুখ দেখা যায় না কারও, নানান বিচিত্র গন্ধ পায় কেবল সনাতন। ‘দাদু’ শব্দে অন্ধকার থেকে মহাদেব শুধোয়, ‘আছি আছি। এইসো, উপরে উইঠে এইসো।’ বললেন বটে, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে অভিযান হবে কী করে বুঝতে পারে না জয়রাম আর তার দলবল। হ্যারিকেন রাখা ছিল একটা, বিশ্রামেই ছিল, সনাতন জ্বালে। দলের সবার মুখ প্রতিভাত হয় তাতে, সকলের উঠে আসার সুসারও।
জয়রাম এসে মহাদেবের ডান হাতখানা ধরে চুপ করে থাকে। সে জানে, হাতে হাত রেখে এখন মহাদেব লোকের নাম বলে দিতে পারে। একটু সময় ব্যয় হয়, তারপর হেসে বলে মহাদেব, ‘হারামজাদা! আমারে ঠগাবা জয়রাম! কেমন আছ কও ভাই।’
‘আশীর্বাদ নিতে এলাম। আজ রাত থেকে ইলেকশন ক্যামপেন শুরু করছি দাদু, একদম দিনক্ষণ দেখে, জ্যোতিষীর হিসেবমত। আপনার আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু। তার আগে একটু ম্যাজিক দেখান’, বলে জয়রাম ঘোষণা দেয়, ‘দাদু একজন জব্বর ম্যাজিশিয়ান। দেখবেন, আপনাদের তো সবাইকেই চেনেন দাদু, এখন না হয় চোখে দেখেন না। দাদুর সঙ্গে হাত মেলান, দাদু সবার নাম বলে দেবেন।’
এই ম্যাজিকের কথাটা সমাগত প্রায় সকলেই জানে। মহাদেবের অনন্ধকালে এরা, সতীনাথ, রামজীবন, সুবল, খালেক, জনার্দন, সবাইকেই দেখেছে, চিনেছে মহাদেব। আর মহাদেব চোখ হারালেও এরা বহুবার এসেছে। সহানুভূতি জানাতে কেউ, খোশ-গল্পের জন্য, উৎসবে নিমন্ত্রণ জানাতে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তখন করমর্দনের মাধ্যমেই পরিচয়প্রদান চলত। অন্ধ হবার পর স্বভাবতই মহাদেব আয়ত্ত করে এই হাত ধরে মানুষ চেনা। এতে সে নিজের কোনও বাহাদুরি দেখে না। প্রত্যেক হাতের মুঠি আলাদা, বার্তা আলাদা, এ বোধ আনতে তার অন্ধত্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এটাই আশ্চর্য করে বরং মহাদেবকে।
প্রথমেই যে হাত নিয়ে এগিয়ে আসে, মহাদেবের ক্ষীণ হাতটি ধরে নিজেই সে আঁতকে ওঠে, এ হাত, না শীতল আর নিরুত্তেজিত শিঙ্গি মাছ! মহাদেব বলে ওঠে, ‘আরে হাসান! তুমিও দলে নাম লেহালে? রাম! চিন্ময়ীর থানে যাওয়া হয় নেই? আমার আশীর্বাদের আর জোর নেই। গেছ চিন্ময়ীর থানে?’
প্রশ্নটা বিব্রতই করে জয়রামকে। পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষী জানে, এ তল্লাটের সবাই জানে, কোনও শুভ কাজে হাত দিতে গেলে প্রথমেই সবাই গ্রামের শেষ প্রান্তে জঙ্গল আর আগাছায় ভরা চিন্ময়ীর থান দর্শন করে, তারপর যাত্রা শুরু করে। বড় প্রাচীন থান, আর সেখানকার পুরোহিতকে দেখলে মনে হয়, তিনি দেব-দেবতাদেরই সমবয়স, অনেক দেবতাকে জন্মাতেও দেখে থাকবেন। বনমালীপুর থেকে এক ক্রোশ। ভিন্ন মৌজা, তবু এখানকার সবাই যায়। গ্রামের বর নববধূ আনতে যাবার আগে যায়, নববধূকে নিয়ে এসে বাড়িতে ওঠার আগে যায়। জয়রামও গিয়েছিল আজ। এই তো সেখান থেকেই তো এখেনে আসা। একই দল। সেখানে কোনও হিন্দু-মুসলমান বিচার নেই, ধনী-নির্ধনেরও। তা জয়রাম একটু অতিরিক্ত উৎসাহই প্রকাশ করে ফেলেছিল পুরোহিতের সামনে।
‘ঠাকুরমশাই! তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে চিন্ময়ী মা-র তো নাম পাইনি। যদি একটু বুঝিয়ে…’
‘বাঞ্চোৎ, চিন্ময়ী মার নাম শোনোনি? বাঞ্চোৎ চিন্ময়ী মার…’ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটা পায়ে না ঠেকলে সত্যাম্বর পুরোহিত মামলা কদ্দুর নিয়ে যেতেন, ঠাহর হচ্ছিল না জয়রামের।
সামনে ইলেকশন, জিতলে দিল্লি, মন্ত্রিত্বও হয়তো লেখা আছে কপালে, আর আজ এই ভরসন্ধ্যায় এই গেঁয়ো পুরোহিতের মুখে তাকে এহেন সম্বোধন শুনতে হল? আঠারো-বিশ বছরের ছোকরারাও তো আছে তার সঙ্গে, হজম করা যায়? যায়, কেন না এ এমন এক সময়, প্রলয়পয়োধিজলে বিষ্ণুর যোগনিদ্রার মত, নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য, যখন ঈশ্বরের মত, ধরিত্রী আর ইবলিসের মত তাকেও সহনশীল হতে হয়। তারপর কর লো দুনিয়া মুঠঠি মে। নইলে, রইলে! দিল্লি দূর অস্ত। অতএব…।
সে মন্দিরে আরও ফ্যাচাং। এত প্রকার ফ্যাচাং নিয়ে মন্দির গড়ল কে, পরে এ নিয়ে তদন্ত করাবে জয়রাম। কিন্তু সম্প্রতি সমস্যাটা হচ্ছে, নিজের জন্য এখানে কিছু প্রার্থনা করা যাবে না, নিষেধ একেবারে। শুদ্ধ ভক্তি নিয়ে মা চিন্ময়ীকে প্রণাম করো, চলে যাও। জয়রামও জানত, তবে কিনা জানা জিনিসেও সময়বিশেষে মরচে পড়ে, জং ধরে। তা আজ এই ভোটের আগে বলাইচণ্ডীর হাট থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে নগদ সাতশো এক টাকার বৃহদাকার যে জবার মালাটি খরিদ করা হল মাকে পরাব বলে, তাতে কি মাকে বলব আমার বিরোধী প্রার্থীকে জিতিয়ে দাও মা চিন্ময়ী, এজন্যই আমি এই মালা পরালাম তোমায়? তাই কিছু প্রার্থনা না করেই ফিরে আসতে হয়েছে। এখন মা চিন্ময়ী মালা বুঝে যা হয় করবে। তারপর এই মহাদেব। চিন্ময়ী মহাদেবরা তো জানে না, ইলেকশন কী যন্তর। আর পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষীও তেমনি, বিধান দিয়েই খালাস।
‘ভোটের দিন আমি আপনারে নিজে নিয়ে যাব এসে। সকাল সকাল সারা করবেন, লাইন না আপনার। মুখে খালি বলবেন আমার নাম, ব্যস। বাকি কাজ আমার লোকের। কি, ঠিক আছে?’
‘ও জয়রাম! আমারে তুমি ঘোড়া দেচ্ছ, তয় চাবুক হাতে দিতি ডরাচ্ছ ক্যান? অ্যাঁ? তালি দিল্লি যাতিছ? একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থ! তা বেশ! এরপর তার মানি শাহ্-ই-বেখবর একছের তুমি, না? জানো তো সে-সবের বিত্তান্ত, ইতিহাস? মোগল রাজত্বির খবরাখবর জানা আছে?’
এ আর এক ফ্যাচাং। সত্যি জয়রামের আজ নিতান্ত ফ্যাচাং দিবস। দাদুর কাছে পড়া মুখস্থ বলতে হবে? আশীর্বাদ নিল, চলে গেল। রাতে আজ কত কাজ! না, বেখবরটবর জানা নেই তার। সত্যেশদা বলে দিয়েছে, জয়রামের কনস্টিটিউয়েন্সিতে মাইনরিটি ভোট প্রায় কুড়ি পার্সেন্ট। অতএব নামাজ, রোজা, মহরম, মিলাদ, ঈদ এগুলো নিয়ে যেন একটু নাড়াচাড়া করে। আর মিথ্যে হলেও সত্যি মনে করে যেন বলে, জয়রাম জমজমের পানিও খেয়েছে। মুসলমান বাড়িতে গিয়ে জলটল চায় যেন। ক’দিন ধরে সেই পাঠ চলছে তার। পাঠদাতা হাসান। গত এক মাসে আরবি মাসের বারোটা নামই কণ্ঠস্থ হয়েছে তার। ঈদুজ্জোহা, ঈদুল ফিতরের সুলুক জেনে গেছে। আর সালামালেকুমটাও বলতে পারে। আরও হবে। কিন্তু মোগল ইতিহাস! না, এতবড় সিলেবাসে এখন আর পোষাবে না! সংক্ষেপ চাই, সংক্ষেপ। ওসব জিতবার পরে হবে। পাঁচটা বছর তো হাতে পাচ্ছে সে।
জয়রামকে নীরব দেখে মহাদেবই তার বাক্য শুরু করে। এখন তার হাত জয়রামের পিঠে। জয়রাম উৎফুল্ল। এই হাত আর একটু ওপরে উঠলেই কেল্লা ফতে! জেতা তখন আর আটকায় কে? একটু, একটু ওপরে!
‘তুমি বলবা, তুমি নিয়ে যাবা, তারপর ভোট দেব? ক্যান, আমি কি ভোদাই? সাঁইতিরিশ সনের থে ভোট দিচ্ছি রাম, ভোট দিতি আমি জানিনে?’
‘সে কথা না দাদু। বেদ্দো মানুষ, না নিয়ে গেলে যাবেন ক্যামনে? আর চোখ নাই বলে কি ভোটটা নষ্ট হবে?’ জয়রামের হয়ে এগিয়ে আসে হাসান।
‘হাসান, তুমি তো বদরের যুদ্ধির কথা শুনিছ, তাই না? হ, কি না?’
‘শুনেছি। তা হঠাৎ বদরের কথা কেন দাদু?’
‘কারণ আছে। আর তুমি, জয়রাম, ভরণ্যপক্ষীর গল্পডা জানো বোধ করি?’
হাওয়া দিচ্ছে! সেই হাওয়ায় জোনাকি উড়ছে। একবার জয়রামের ঠোঁট ছুঁল, ভাল লাগল না। তাই দূরে কামিনী গাছটায় গিয়ে বসল। জয়রামের প্রস্টেটের গোলমাল আছে। বাষট্টি। একবার চিন্নয়ী, না চিন্ময়ী নয়, বাঞ্চোৎ শব্দের আফসোসে পেচ্ছাপ করে নিয়েছিল জঙ্গলে। এবার এই বদরের যুদ্ধ, ভরণ্য না কী পক্ষী, বেগ এল আবার। উঠবে?
‘একদিন সময় করে এসে শুনব সব আপনার কাছ থেকে। আজ খুব তাড়া, রাত্তিরে মিটিং। জলদি মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন। আপনার আশীর্বাদেই জয় হবে আমার। দ্যান।’
‘মুড়ি খাবা, জয়রাম? কয়জন আসিছ মোট? সনাতন! মুড়ি আর নৈলেন গুড় নে আয় তো ঘরেত্থে। বসো, খাও। অতিথি নারায়ণ।’
তা ঠিক, তবে কিনা এখন মুড়ি চিবোনোর সময় আছে নারায়ণদের? হাসান ইঙ্গিত করে, সেই ভাল। হ্যারিকেনের আলোয় ঠাহর করে নিতে অসুবিধে হয় না জয়রামের। সনাতন এদিকে আদেশ পেয়ে উঠে গেছে। সুখেন তার হাতের ক্যামেরাটা সামনে রেখে বসেছিল, ঘুরে বসতে গিয়ে ওটার ওপরই পাছা রাখতে যাচ্ছিল, মুহূর্তে সামলে নেয়। আশীর্বাদের ছবি তোলা হবে, তাই সুখেন ক্যামেরাসহ। জয়রাম ভাবে, আসন্ন পেচ্ছাপের ভবিষ্যৎ আমার! এই সময় জয়রামের ঘাড় পর্যন্ত উঠে গেল হঠাৎ করে মহাদেবের হাত। হ্যারিকেনের আলোয় জয়রাম। মহাদেবকে দাওয়ায় অতিকায় দেখাচ্ছে। হাতটা আর একটু ওপরে উঠলেই— কিন্তু এত মহাদেবের পোষা হাত, এ হাতে জয়রামের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।
না, মুড়িই চলুক, আশীর্বাদ পাওয়াটাই যখন জরুরি। এজন্য মুড়ি কেন, রাতটা কাটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কবুল। কেন না কথাটা বলেছে পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষী। সোমবার রাত্রি ন’টা গতে অন্তর্দশা শুরু, ইস্তক মধ্য রাত্রি দুটো একত্রিশ। তারপর প্রত্যন্তদশা। অতএব ওই রাতটুকুর মধ্যেই মহাদেবের আশীর্বাদ… নইলে বিকল্প দিন আছে অবিশ্যি শুককুরবার দিবা আটটা তেরো গতে, না, আর শুককুরে দরকার নেই। পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষীর হেলে পড়া কাঁচা বেড়ার ঘর, মুলিবাঁশ দিয়ে ঠেকনো দেওয়া, নেই দৃষ্টে ভাবে জয়রাম, দেরিতে সব হেলে পড়ে। এখন তাই ভাবছে, যা সেরেখখো, আজই শেষ হোক। আসুক মুড়ি। আর সেই ফাঁকে, ওই যে কী বললেন পক্ষীবিষয়ক সমাচার, শুনে নেওয়া যাক বরং। এক ঢিলে যতগুলো পাখি মারা যায়, সময় অল্প। আগে পেচ্ছাপটা…
ছোট হাজারি সারা করে এসে জয়রাম দেখে, দলটা ততক্ষণে মুড়িমগ্ন। তৎসহ পাটালি গুড়। আর কথা বলছে রূপরাম। ‘এসময় হাসান ভাই, বোঝলেননি, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কোনও ফুসলানিতেই দেবেন না।’ মুড়ি খেতে খেতে মাথা নাড়ে হাসান, দেখে খুব তৃপ্তি পায় জয়রাম, তার তৃপ্ত হাতে মুড়ি উঠে আসে। স্তব্ধতা এখন। হাসানের মনে হচ্ছিল রূপরামকে, ক্ষণিকের জন্য, নামুস যেন এই রূপরাম, জিব্রাইল আর কী। যদিও নিজের মস্তিষ্ক সঞ্চালনের সময় হাসানের এ-ও মনে ছিল, বক্তা রূপরাম বাড়ি করেছে। বাহারি নাম সে বাড়ির ‘মায়ের কোল’। আর মা থাকে ভাই ঘনরামের বাড়ি। জলপাইগুড়ি, বেগুনটারিতে। তবু মানে হাসান, অন্তর দিয়েই মানে, এখন, হ্যাঁ, ঐক্যবদ্ধ থাকাই জরুরি।
‘দাদু, সেই কী পাখিটির কথা বলবেন বলেছিলেন, বলুন, শোনা যাক।’ জয়রাম তার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ফেলেছে। সনাতনের মনে হয়, শনি, ভরণ্যপক্ষী, অন্তত একটার কৌতূহলনিবৃত্তি জরুরি।
হ্যারিকেনটাও নিথর হয়ে গল্পটা শোনার প্রতীক্ষায়। একটু দপদপ করে আবার স্থির হল তাই। মহাদেব নিবিড় স্থিরতায় বসে, অতএব কাহিনি শুরু হতে চলেছে, মনে হয় সনাতনের।
‘ঐক্যের কথাখান কলো কে? রূপরাম! মায় আছে কেমন?’
প্রশ্নটায় কোনও ব্যঞ্জন ছিল না, ব্যঞ্জনাও নয়, তবু উত্তর দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত তো হতে হয়ই। মা কেমন আছে তা জানা নেই ভালমত। তবু মা-র ভাল থাকারই বার্তা দেয় রূপরাম।
‘শোনো তয় বেবাকে। মহাভারতের কাহিনি। তয় মহাভারতের মদ্যি পাতিও পারো, না-ও পাতি পারো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধুর প্রারম্ভ। যুদ্ধু শুরু হয় নেই তহনো, করতিছে। তা অঘ্রাণ মাস, মাডে মাডে ফল ফুল শস্য। দুর্যোধনেড্ডে ফেইল মারি কৃষ্ণ রাস্তায় বারোয়ে আইসে দেখতিছে, ধরা এক্কেরে শস্যে পূর্ণ। আর গাছের ডালে ডালে আশঙ্কার আলোড়ন, যুদ্ধিতে তো কিছুই থাকপে নানে। গাছের শাখাবেশাখায় কত শত পক্ষী। তাগের মুখি মড়াকান্না। দুর্গা বিসর্জনের পর নীলকণ্ঠ পক্ষী দেশ ছেইড়ে উইড়ে গেছে বছরকারের মতন, আর তারই ফেইলে যাওয়া বাসায় বরাবরের মতন আশ্রয় করিছে অরণ্যপক্ষীরা, ভরণ্যপক্ষীরা। কুরুক্ষেত্তরের মাঠও তো লম্বায় বহরে খুব খাডো না! তাতে আছে সব পেরকাণ্ড পেরকাণ্ড বিরিক্ষ— আম জাম সিদ্ধান্ত তেঁতুল বকুল কদম শিরীষ শ্যামল বয়রা জারুল আমলকী। তারই এক পারুলগাছে আশ্রয় ছিল এক ভরণ্যপক্ষীর সংসার। ভরণ্য, ভরণ্যা আর তার ছাওয়ালরা। তা যুদ্ধু হবে। যুদ্ধু কারে কয় জানো? কও তো জয়রাম, বকুল বকুল ফোডে কি রকম কইরে? আর অশোক ফুল ফোডার রহস্যই বা কী?’ বলে থামেন মহাদেব।
ফুল ফোটারও বৃত্তান্ত, রহস্য আছে নাকি আবার? ইলেকশনে নেমে রোজই তাকে এখন জলধি পার হতে হচ্ছে, সেই নমিনেশন জমা দেওয়া থেকে। এখন তো জাতির উৎসর্গ করার ধুম। তার এরিয়ায় এরকম কিছু কিনা যাকে সে জাতির নামে উৎসর্গ করতে পারে, এই কথাটাই ঘুরছিল তার মাথায়, এমন সময় সহসা বকুল ফুলের ফুটনরহস্য নিয়ে প্রশ্ন! বকুল ফুল আছে যার বাড়িতে, সেই কওসরও এহেন প্রশ্নে নির্বাক।
‘জানি না দাদু, আপনিই কন।’ ফুলটুলে এমনিই জয়রামের মতি কম। তার কেবল ফলে আগ্রহ। আর মদ।
‘মদিরা। মদিরা আর পদাঘাত। বুইছ? রমণীর পদাঘাতে অশোকফুল ফোডে, আর তার মুখির মদ পান করার আগে যদি কুলকুচো করি বকুল গাছের তলায় ফেলে, তালি পর বকুলফুলের জন্ম হয়।’
‘তা যুদ্ধের কথা কী বলছিলেন চাচা?’ বিষয়ে যাবার ইচ্ছা ইদ্রিসের। তার ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরেই যেন মহাদেবের খেই ফেরে। হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।
‘যুদ্ধু কারে কয় জানো? যবের পাঁচটি শীষ আর ধানের বেরোয় শত, তখন জানিস যুদ্ধে সবাই হয় ক্ষতবিক্ষত’ বলে একটু থামে। জল খায়। পাশে বসা লোকটির গায়ে হাত দেয়, পিঠে, কাঁধে, তারপর নিজের হাতের মুঠিতে তার হাত ধরে বিবেচনা করে বলে, ‘কেডা? অম্রেত? আমারে এট্টা ধাঁধার উত্তর দিতে পারো, অম্রেত? ভাল কইরে ভাইবে বলবা। দুইদিন সময় নেও, দরকার হলি।’
জয়রামের উৎকণ্ঠা উত্তুঙ্গে এখন। সনাতনেরও। যদিও এই উত্তুঙ্গতার পেছনে রাসায়নিক কারণ ভিন্ন ভিন্ন। একজনের মিটিং-এর উৎকণ্ঠা, অন্যজনের শনির, তার সতেরোটা চাঁদের।
‘তারপর শোনো। আগে কাহিনিডাই কই যুদ্ধির কথাডা। যুদ্ধির আগে জল আর কবচের মধ্যেত্থে আগুন বেরোতি থাহে। ধ্বজ পুইড়ে ভস্ম হইয়ে যায় বেবাক। তেরো দিনি পক্ষ হয়। রাক্ষসেরা রক্ত খায়ে খায়েও তৃপ্ত হতি পারে না। ঘোটকীর প্যাডে গোবৎসা হয়, হাতির মূত্রত্যাগ থামতি চায় না। শিয়াল আর কুকুর পাখির খাবারে ভাগ বসাতি চায়। আরও আছে। শকুনি রুধিরবমন করে। এরই নাম যুদ্ধু বাবাজীবন! আর কেতু চিত্রা নক্ষত্রে স্থায়ী হয়ে বসতি করে, যুদ্ধু শেষ না হওয়া পর্যন্ত নড়তি চায় না। এরই নাম যুদ্ধ বাবাজীবন!’
সমবেত শ্রোতার রোমাঞ্চ ও গাত্রদাহ হয়। হাসান ভাবে, যুদ্ধ কি তবে কেয়ামত? জেলহজ্বের সেই সূর্য না ওঠার দিনে, সূর্য সেদিন উঠবে, তবে পশ্চিমে, স-অ-ব হরফ অদৃশ্য হয়ে যাবে! আর ঘোড়ার গর্দান নিয়ে সাফা পর্বত থেকে বেরোবে তাব্বাতুল আরদ! উটের মত পা নিয়ে। লেজ গোরুর মত। আর হাতদুটি বানরের। ইস্রাফিলের শিঙা বাজবে আল্লাহর আদেশে, কানে তালা ধরে যাবে তাতে। পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠবে। কোনও মানুষেরই মৃত্যু ছাড়া গতি নেই সেদিন। এক থাকবেন আল্লাহ, আর তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁর বান্দা ফেরেশতাদের। হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সাথে মিল আছে বটে। তবে অ-মিলও আছে। কেয়ামত ভবিষ্যতের ব্যাপার। কুরুক্ষেত্র অতীত। আর কেয়ামতশেষে ইস্রাফিলের দ্বিতীয়বার শিঙা বাজার মধ্যে আশ্বাস আছে মৃত মানুষ, মায় জ্বিন পরীরও জীবিত হয়ে ওঠার, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর পর কেউ উঠে আসেনি। হাজার হাজার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও না। তেরো দিনে পক্ষ, শকুনি রুধিরবমন করে, বাপরে বাপ!
প্রমীলা এসময় চা দিতে আসে। চাকর দু’দফায় চা, সঙ্গে মুড়ি ও আরও গুড় দিয়ে যায়।
‘নাও বাবা, খেইয়ে ন্যাও, নয় চাডা জুড়োয়ে গেলি মজা পাবা নানে।’
সতীনাথের হয়েছে মুশকিল। জনার্দন রাতে বাসায় আসবে, আর এখন এই অবস্থায় গল্পকে বাদ দিয়ে উঠে যাওয়াও যায় না!
হঠাৎ পাশের বাড়িতে মহিলাকণ্ঠে তীব্র কান্না। সুবল গোপ এএসআই বউ পেটাচ্ছে। আর এই দলের মধ্যেও বসে আছে এক সুবল, সুবল খাঁড়া। না, পুলিশটুলিশ নয়, রেজিস্ট্রি আপিসের দালাল। এই সুবলেরও খুব ভাল লাগে পিটুনি খাওয়া বউয়ের কান্না শুনতে। সে খুব আরামের বস্তু পায় এতে। ‘চালা, চালা’, মনে মনে সে আখর কাটে। সে নিজেও নিয়মিত পেটায় তার বউকে। ভাল লাগে, মনটা ভাল হয়ে যায় নিমেষে। ভাল ও গ্লানিমুক্ত। খুশিতে চোখ মুদে আসছে সুবলের। দুটি চোখই, যে চোখদুটোয় খুব ছোটবেলায় তার মা কাজল পরিয়ে দিতেন। পেটাচ্ছে তো অন্য একজন তার বউকে, আহা, তাইতেই সুবলের কী ফুর্তি! আজ সে-ও বাড়ি গিয়ে… মনে মনে সে আওড়ায়, ‘আম জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।’ না, বাড়ি গিয়েই… বউ পেটানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, তবে পিটুনি খেয়ে বউয়ের আওয়াজ খুব। গতিজাড্য, মনে মনে ভাবে সুবল। আর তার কিনা ইংরেজিও জানা ছিল মাধ্যমিকে ইংরেজিতে চুয়াল্লিশ অর্জন বাবদ, তাই ইমপেটাস শব্দটিও মনে আসে সুবলের।
অস্বস্তিকর কান্না! ‘কাঁদে কে খুড়ো?’ বয়সে প্রবীণ রামজীবনের প্রশ্ন এটি।
‘কান্দে কেডা জানো না? সুবল, তোমাগো বিপক্ষ দল করে। নেশা খেইয়ে বাড়ি এইসে পিডোচ্ছে তার বউরি। আজই মাইনের দিন সুবলের, ষাঁড়াষাঁড়ির বান!’
‘নেশা খেলেই সুবল মনে করে তার বউ অসতী, তাজ্জব কাণ্ড, লয়?’ এতক্ষণে একটা কথা বলার জোশ পায় সনাতন। জয়রাম সনাতনের দিকে তাকায়। একে চেষ্টাচরিত্তির করেও করা গেল না এবার ভোটার, জয়রামের এই ভাবনার দীর্ঘশ্বাস পাশে বসা খালেকের জামায় লেগে হ্যারিকেনে মৃদু পড়ে, হ্যারিকেন টের পেয়ে কাঁপে তাই একটু।
‘বউডারে আমসত্ত্ব বানায়ে শ্যাষ করি ফেলতিছে। আহাম্মক অপোগণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড, খোদার খামোখা শালা সুবল! এ দ্যাশে এহন সর্বদা রজনী বোজলানি? কেডা কইবে মৈত্রেয়ীর দ্যাশ, দ্রৌপদীর দ্যাশ? মেইয়েছেলে মাইর খায়, বেগুনপোড়া হয়? আর তোমরা মনুষ্যি? পণপ্রথা চালু গার্গীর দ্যাশে। পারবা? ভোটে জিতলি সুরাহা জানা আছে জয়রাম? ধাঁধাডা তালি কই, অম্রেত?’
‘খুড়ো! কিন্তু সেই ভরণ্যপক্ষীর গল্পটা?’ রামজীবন সমবেত জনতার উৎকণ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করে। মহাদেব রামজীবনের প্রশ্নটা শুনে তাকায় জয়রামের দিকে। চোখ না থাকলেও ধ্বনিসন্ধানে অভ্যস্ত তাকানো। একটু আগেই তার তরফ থেকে জয়রামের কাছে প্রশ্নটা ছিল পারবে কিনা। উত্তরটাও জানা মহাদেবের। পারবে না। এরা তো ভোটে দাঁড়াবার অনেক আগেত্থেই চামড়া গণ্ডারের কইরে থোয়, মেহেনত, যত্ন নিয়ে। ইলেকশন! নেতা। মন্ত্রী! এসবের আগে গাছে বসা ডালের পাখি রেইখেই বিককিরি করার কায়দা জানতি হয়। মাছেরেও সাঁতার শিখোনের পর নমিনেশন। তয় কিনা বাজিকর এরা। হাজার নাচুক দড়ির ওপর, বকশিস নিতি নিচি নামতি হয়, হচ্ছে না? বাঘের প্যাডে জন্ম এগের, থাবা ছাড়া দ্যাহা যায়? তা এহন তো শাসক আর বিরোধী দল, পেত্যয়, উকিল-মুহুরি। টাকায় এক আনা হিস্যা। পেরমান জানিনে, তয় মনে হয়।
ঝিঁঝি পোকার মত এসময় ভরণ্যপক্ষী, ভরণ্যপক্ষী শুনতে বিরক্ত হয় ও মনে মনে ‘অভাগা বর্ষাকাল, হরিণ চাটে বাঘের ছাল। শোনরে হরিণ তোরে কই, সময়কালে সবি সই।’ সামান্য হাসি, তারপরেই গাম্ভীর্য।
‘আর ভরণ্যপক্ষী! সে ঘুমচ্ছে এখন, অসময়ে তারে ডাইকে না। কত ভোট দেখলাম সাঁইতিরিশেত্থে। কত রঙ্গ কত তামাশা। বেশুমার সব কাণ্ড। কথাহান কি জানো জয়রাম? আমার পেত্যয়, আমি কোনও পেরমান জানি নে, ভুলে ভরা দ্যাশ হইয়ে ভাইরে ভাই। মুড়ি মিছরি একদর। পড়িছি কালের কবলে। জাতকের হেই গল্প তো জানো বাপ? এক ছেলেন কুমির। দুপুরে সে নদীর পারে রৈদ পোয়াইতেন। তার গা ভর্তি জলৌকা, কিনা জোঁক। শরীরির রক্ত খায়ে শরীরির মধ্যি সিধোয়ে গেছে। জোঁকও আর কুমির ছাড়ে না, কুমিরিও আর জোঁক তাড়ায় না। এক শিয়াল তাই দেইখে কলো, ‘ও কুমির ভায়া! ল্যাজখানা খালি একবার ঝাড়ন দিলি তো পারো, বেবাক জোঁক পালায়ে যাতি পারে। তুমি তো রক্তশূন্য হইয়ে মইরে যাবানে আহাম্মক!’ কুমির হাসে আর কয়, ‘এই না তুমি পণ্ডিত শিয়াল ভাই। তয় বোজলা না ল্যাজ নাড়াই না ক্যান? কাজ নেই, জোঁক তাড়ানোয় কাজ নেই। তাতিই বরং সর্বনাশ। জোঁক যা রক্ত খাবার, খেইয়ে থুইছে। খেইয়ে আমার গতরে লেইগে রইছে, এডা তাগো মনের সুখ। লড়েও না চড়েও না, রক্তের স্বাদ অকম্মা এহন। এগুলিরে তাড়ায় কোন্ বলদে? তাড়ালিই তো আবার নতুন উৎপাত, আবার রক্তশোষা। বুয়িছ জয়রাম, কী কবার চাইলাম?’
কোটরগত চোখ মহাদেবের, দেখে বোঝার যো নেই, দুটোরই দৃষ্টিশক্তি গেছে। এখন চেয়ে থেকে মনেও তো হচ্ছে, না, যায়নি। মহাদেব দেখতে পায়। চোখ থাকা না থাকা বাহুল্য, তবে দেখতে পায়। কিন্তু নিয়ত ফলপ্রত্যাশী জয়রাম এখন করে কী? মহাদেবের জটা থেকে সবে জাতক বেরোল, এরপর আর কোন ভূশণ্ডীর খেয়ায় চড়বে সে, কে জানে? লোকটা প্রসঙ্গে থাকে না। তাহলে কি আজকের উদ্যমটা বৃথা? কত কী পাওয়া যায় ভোটে জিতলে, কত কী! রঙিন মশারির মত ভেবে চলে জয়রাম, বারোমান প্লেনে ঘোরো ফেরো ওঠো নামো, স্রেফ বিনে পয়সায়। প্লেনে চড়া হয়নি এ পর্যন্ত। টেলিফোন বিল, তাও মকুব। এমনকি মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া যায়। না, একেবারে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত একলপ্তে হতে চায় না সে, ধীরে, আহিস্তা। জিতলে কমসে কম মন্ত্রিত্বটন্ত্রিত্ব, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী সো ভি আচ্ছা…
গব্বজন্তন্না আর কারে কয়, ভাবছে সনাতন। মহাদেব তো এক প্রসঙ্গে নেই! অস্থির হয়ে ওঠে সে। ভরণ্যপক্ষী গেল? শনির তো প্রশ্নই নেই আজ আর। তবু প্রয়াসের প্রয়াস সনাতনের, ‘দাদা ভরণ্যপক্ষীটো…’
‘রও রও সনাতন। তুমি তো ধৈর্য হারায়ে ফেলতিছ। মাছি ধরবা ঝটপট, তাছাড়া আর সব কামে ধৈর্য লাগে, বুঝিছ?’
‘আপনার ধাঁধাখান?’ অমৃত নামধারী যুবক মওকা পেয়ে শুধোয়।
‘আজই আর ভরণ্যপক্ষী, ধাঁধা, কিছু না কিছু না। রাম, রাম, ও রাম!’
উৎসাহী রাম সহসা এগিয়ে আসে। মহাদেবের প্রায় কোল ঘেঁষে বসে। হ্যারিকেন আর মহাদেবের মাঝে এখন জয়রাম, ফলে মহাদেবের গ্রহণ লাগে। হাতটা মাথায় আসবে কি এইবার? ক্যামেরা অন করতে বলবে? একবার! মাত্র একবার মাথায় হাত!
‘শোন কী কই। আত্মাডারে নিষ্পাপ রাখবা। দ্যাখবা সেড়াই তোমার এট্টা খাসা বালিশ। তাতে ঠেস দিতি পারো, রাত্তিরি তোফা ঘুমোতিও পারো।’
এই! বালিশ শুনে আবারও পেচ্ছাপ পায়, আর জয়রাম ভাবে, ইলেকশনে জিতলে বম্বে গিয়ে, না এখন তো মুম্বই, অপারেশন করিয়ে নেবে। না, বিলেতে। হিথরোতে নেমে স্ত্রী বীণাপাণিকে বলবে, নাও, এই তোমার বিলেত। এজন্য তো মন্ত্রী হওয়াও লাগে না। খালি জেতো, আর বিলেত যাও।
‘খুড়োর বয়স কত?’ রামজীবন বুঝতে পারে না দেশ স্বাধীন হল সাতচল্লিশে, তবে বুড়ো সাঁইত্রিশে ভোট দেয় কী করে? নাকি ভীমরতি খুড়োর?
‘বয়স? তা হইছে। আমার জন্মসনে ব্রিটিশের গোলায় কাবাশরীফের গেলাফে আগুন লাগে। গোলা ছুড়েছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। উনিশ’শ ষোলো। আর এখন দুই হাজার চাইর। হিসাব করো। অষ্টাশি পাইলা, তাই না?’
জয়রাম ভাবে, আজ এসবই হোক, মিটিং একটু বেশি রাতেই হবে। বিয়াল্লিশের জাতক সে। জন্মাতে দেখেনি নিজেকে, শুনেছে সে সময়ের অনেক কথাই। ইংরেজ ভারত ছাড়ো, আজাদ হিন্দ, মন্বন্তর। আর সে সময়ও তো মহাসমর, দ্বিতীয়। প্রথমে দ্বিতীয়ে আজ একটু বিশ্রম্ভালাপ হোক তবে।
‘দাদু, আপনার কোন কলেজ?’
মহাদেবও পেলব হন প্রশ্ন শুনে। ‘বিএ পরীক্ষা দেলাম দৌলতপুর কলেজেরথে। মাইল্লাম ফেল। পড়া ওই পজ্জন্তি। তারপর এহানে জাইগীর থাইকে মাস্টোর, ওথায় ব্যবসা। শ্যাষে রেলোয়েতে ঢুকি চুয়াল্লিশে। কোথায় কও দিন?’
‘কোথায়?’ জয়রাম এখন প্রকৃতই কৌতূহলী।
‘প্যালিবোথরা। পেরথম পোস্টিং। অশোকের দ্যাশে।’
প্যালিবোথরা! অশোকের দেশ? সবটাই গ্রিক লাগছে জয়রামের কাছে। আর সেখানেও রেল ছিল? তায় আবার ভারতীয় রেল?
‘প্যালিবোথরা? সেটা কোথায়?’
‘চুপ! আর কথা কইয়ে না, চুপ! দ্যাশ স্বাধীন হইয়ে ষাইট বছরের হতি চলল, এহনো বার্ডোয়ান চলতিছে, কনটাই চিনপুরা ডামডাম করতিছ, আবার কথা! সাহেবরা কইতে পারত না, কইত চিটাগং, চান্দেরনগর, আমরাও? এ দ্যাশ স্বাধীন?’
আশ্বিন মাসে বাজ পড়লে এরকম আওয়াজ হয়। মহাদেবের কণ্ঠস্বরের মত ঠিক। জয়রাম কাঁপেও একটু। আজ শালা গাল খাবার দিন। পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষীটা…
রামজীবনের গলায় ঝুলে আছে প্রশ্নটা সেই থেকে। তাই বলে, ‘আচ্ছা সাঁইতিরিশে ইলেকশন হয় কী করে? দ্যাশ তো পরাধীন…’
‘তোমারে সব কমু ক্যান? ভোটের ক্যানভাসার হইছ, পড়াশুনাডা তো কইরে বাইরোয় মানুষ? জানবা, এই মহাদেব গাঁজা খেইয়ে কথা কয় না। জয়রাম! আসো। অন্যদিন সময়গময় হাতে নিয়ে আইসো পারলি। তয় এট্টা কথা কয়ে থুই। শুঁড়ির নাই কান, মুচির নাই নাক, আর তোমাগের ভোটওয়ালাগের নাই লজ্জা। রাইত হতিছে, বাড়ি যাও।’
আশীর্বাদের আশা তবে ঘুচল আজ? চা মুড়ি পাটালি গুড়েই অভিযান শেষ! একটা নেতিবাচক উদ্যোগ নেবে জয়রাম? প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এলে তাকে যেন আশীর্বাদ না করে, বলবে? না, সাহসে কুলোচ্ছে না। বেতমিজিও তো সেটা। আর তাকে যে সমূলে পছন্দ নয় মহাদেবের, বুঝতে বাকি থাকে এরপরও? অথচ পূর্ণাঙ্গ জ্যোতিষী তো ধন্বন্তরী। তার সাফ কথা, একবার মহাদেবের আশীর্বাদ পেলে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরেরও সাধ্য নেই তাকে হারাবার। তো দেখা যাচ্ছে কথাটা কড়ায় গণ্ডায় খাঁটি, কেন না ভোটে জেতা যত কঠিন, প্রায় ততই তো কঠিন মহাদেবের আশীর্বাদ পাওয়া। অতএব শুক্রবার আটটা তেরো-ই শেষ ভরসা।
রওনা দেয় তারা। অমৃত তবু দোনামনা করে, ধাঁধাটার জন্য। যাওয়ার আগে সে মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে, ‘আমাকে ধাঁধাটা বলুন না!’
‘ধাঁধা? আসলে নিজিই তো দিনরাত ধাঁধায় রইছি, অন্যের আর ধাঁধায় ফেইলে লাভ কী? আচ্ছা, কইলা যখন মণি, শোনো ধাঁধাখান। আর হ, তোমরাও শোনো বেবাকে। স্বাধীনতা কারে কয়? দ্যাশ স্বাধীন কিনা বোজবা কীসি? একখান দ্যাশ কয়বার স্বাধীন হয়? এই তিন ধাঁধা নিয়ে একখান ধাঁধা। জবাব দিয়ো তিনদিনির মদ্যি। বাঁইচে থাকলে শোনবানে।’
সতীনাথের হয়েছে মুশকিল। জনার্দন তার ঘরে এসে বসে আছে, অথচ সে এখনও… তা ছাড়া এখনও জয়রামকে বলাই হয়নি কথাটা! কী যে বলবে শুনলে!
ভোটপ্রার্থী সদলবলে চলে গেলে সনাতন দেখে, কার একজোড়া জুতো পড়ে আছে। উঠোনে, দাওয়ায় ওঠবার আগে। আশ্চর্য! কেউ জুতো পরতে ভুল করে? হ্যারিকেনের আলোয় ঠাহর করে দেখে ভাল করে। না, ভুল নেই, জুতোই। তাহলে? সন্তর্পণে দাওয়ার একপাশে এনে রেখে দেয় সে জুতোজোড়া।
‘সনাতন! কোথায় তুমি? কাছে আও।’
সনাতন কাছে এসে বসে। অমাবস্যার আকাশটি পূর্ণ হয়ে আছে তারায় তারায়। ওগুলোর নাকি নাম আছে আলাদা আলাদা। ওর মধ্যে অনেক তারা আছে, যারা মানুষের ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে আবার। আচ্ছা, সব তারারা কেন করে না? সনাতনের এইসব তারা, তারপর হাত দেখা, কোষ্ঠীবিচার, এইসবে আধাআধি বিশ্বাস। তবে বিষ্ণুর দোকানে লব্ধ ছেঁড়া পাতা থেকে অনেক বিষয়েই সে বিচ্ছিন্নভাবে জেনেছে। আর জানতে পারছে এই মহাদেবের কাছে থাকতে পেরে। এইমাত্র কত কী জানল।
‘সনাতন! না, তোমার পইরি দিতি কষ্ট হবে। নিত্য রাত জাগা, এ-বয়সে পোষাবে না। গুড় খাইলা?’
‘এজ্ঞে মুড়ি আর গুড়, অল্প এট্টু খান।’
‘জিরেনের গুড় হলি আরও ভাল খাইতা। এডা তুমি খাইলা দোকাটের গুড়।’ মহাদেবের সায়মাশ সন্ধ্যাসন্ধিই শেষ হয়। তারপর গভীর রাতে একটু দুধ, হরলিকস কখনও। ইচ্ছে হলে।
সনাতন বুঝল না গুড়ের ব্যাপারটা। আবার আশ্চর্য হচ্ছে, গুড় না খেয়েই গুড়ের সদসৎ বিচারটা মহাদেব সমাধা করল কী করে?
‘গন্ধেই মালুম, দোকাটের গুড়।’ শোয় একটু মহাদেব। ‘সনাতন! জোয়ান বয়সে কত গুড়ের হাট চইষেছি জানো? রূপদিয়া, ছাতিয়ানতলার হাট। পেত্যেক বিষ্যুবি ছাতিয়ারের হাট। হাজারে হাজারে গোরুর গাড়ি, তোরে কী কবো, শতে শতে ব্যাপারী। ভৈরব নদীর শৈবালে নৌকো ভাসতিছে, চোহি ভাসে এহনো। গুড় যায় ঢাকা, বরিশাল, ঝালকাঠি, কইলকেতা। রসের দ্যাশ ছিল রে আমাদের পুরা দ্যাশটা। আর এনে? নীরস, নীরস।’ বলে নিজেই নিজের বুকে হাত বুলোয়।
‘রেডিওতে খুলনে শুনি ক্যান সর্বদা বোজো আশা করি। খুলনেয় গ্রাম যে আমার, আঁধারমানিক। সে গ্রামে বড় হইছি, আমার আর কিছু ভাল লাগে না। বুকটা কেমন খালি খালি, কলজেড়া নেই।’
‘এ দ্যাশ তোমার নিজের মনে হয় না ক্যান?’ জীবনে এই প্রথম অসনাতন হল সনাতন।
‘অম্বর! সেও তো দ্যাশ আমার। মানসিংহ নিয়ে রেইখেছে যশোরেশ্বরের কালীরি। খুলনে তো সেদিন। আর এহন খুলনে নয়, যশোরেশ্বরী সাতক্ষীরের ভাগে পড়িছে, হ! সতীর দেহখণ্ডের মত দেশ ভাইঙ্গে, জেলা ভাইঙ্গে, মাইনষের মন ভাইঙ্গে, আর শুয়োরের শুয়োর আমি এহন শুয়ে…? হ, এডাও আমার দ্যাশ।’ প্রৌঢ়া রাত্রি যেন এই বৃদ্ধকে, জন্মাবধি যার নাম মহাদেব, প্রতাপাদিত্যের বাস্তুচ্যুত কালীর জন্য বিধুর, শয্যাশায়ী, রোমন্থক ও বিরহী করে দিচ্ছে। সনাতন ভাবে, চাঁদ আজ একটুও উদয় হয় না? শায়িত মহাদেবকে মুহূর্তের জন্য দেখতে চায় সে চাঁদের আলোয়। ভাবতে ভাবতে মহাদেবের কপালে হাত রাখে সনাতন। না, সেখানে কোনও চাঁদের মাধুর্যপ্রত্যাশায় নয়, শরীরের উষ্ণতা বাড়েনি তো? না, বাড়েনি।
‘হাত বুলোও। খুশি লাগতিছে। যশোর খুলনেয় খেজুরের রসের চিনি, শুনিছ কোনওদিন?’
ওপরের, ওই আকাশেরই নয় কেবল, নিচে এই পৃথিবীরই তো অনেক কিছু এ পর্যন্ত জানা হয়ে উঠল না, ভাবে সনাতন। খেজুরের রসে চিনি হয়? চিনির মত শাদা হয় সে চিনি? শনির চাঁদের চেয়েও তো আশ্চৰ্যকর সংবাদ।
‘চিনি! শাদা চিনি!’ বিস্ময়কবলিত প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে না এসে পারে না সনাতনের। কবে কোন ছেঁড়া পাতায় এ তথ্য তার নজরে পড়বে, এখন আর সে অপেক্ষা করা যায় না। কিছু মালতী ফুল ফুটল আবার, এইমাত্র। বাইরে, অন্ধকারে জন্মকালীন গন্ধ বিলোচ্ছে।
‘হ শাদা চিনি। তার জন্যি অনেক কাঠখড় পোড়ানোর ব্যাপার আছে। লাগে শ্যাওলা। কপোতাক্ষর শ্যাওলার দাম কত তুলতি দেহিছি শিউলিগো! চিনির কত কারখানা। হাজারে হাজারে কারিগররে সনাতন, হাজারে হাজারে। রসের, শাদা চিনির সুসময় সেডা।’
‘আর এখন? কারখানা নেই আর? কর্মচারীরা, ইয়ে, মইরে গেছে বেবাক?’ যেন সনাতন কারখানায় কাজ করতে ছুটবে এক্ষুনি, বা এখনও মরেনি এরকম গুড়ের ব্যাপারী আর মঞ্জুরকে কাঁধ দেবে তাদের আসন্ন মৃত্যুতে, তার উদ্বেগ এভাবেই নির্মিত ছিল।
‘মরে নেই। আমরা কেউ সহসা মরি নে রে! সিজারেরা সহসা মরে, সিজারেরা মরে সহসা। মরলি তো ভরণ্যপক্ষী মিথ্যে হইয়ে যায়! মহাভারত, সে কি মিথ্যে হতি পারে?’
আচ্ছা, এই ভরণ্যপক্ষীও মহাদেবদার আস্ত একটা ধাঁধা, লয়? ওই যে মহাদেবের স্বাধীনতার ধাঁধা, তার মত? শনিও কি তাই, নিপাট ধাঁধা? সেও তো মহাভারতের মত ছাপানো বই। তবে? ছাপানো জিনিস ধাঁধা হতে যাবে কোন দুঃখে? নাঃ, আজ একটা অন্ত চাই। শনিব, স্বাধীনতার, ভরণ্যপক্ষীর।
‘মহাদেবদা! শনিতি মানুষ ক’জন? বিয়েথওয়া কি সব এ-দ্যাশের মতন, সাত পাক? না আরও বেশি? আর সেথায় মানুষ বাঁচে কতদিন?’
মহাদেবের হাসিটি এ-বয়সেও উদাত্ত, ঋষভ আর ষড়জে মেশানো। প্রশ্ন শুনে বহুক্ষণই হাসতে হয় মহাদেবকে। এরকম পবিত্র হাসি তিনিও অনেককাল সুযোগ পাননি হাসবার।
‘কী কলি তুই? শনিতি মানুষ? সউত্তর বছর বয়স হইছে তোর, না? তালি নতুন কইরে সব শুরু করতি হয়! একছের অঙ্ক আষ্কেত্থে। তা শুরুর কি বয়স আছে কোনও? পারবি?’
মহাদেব ভাবেন, বদরের যুদ্ধিও কথাডা ওডলো, সারা হল না। রসুলুল্লাহর নির্দেশ ছিল, বদরযুদ্ধির বন্দিরা পেত্যেকে যদি দশজন করি মদিনার ছাওয়ালগো ল্যাহাপড়া শিখোয়, তয় তারা মুক্তি পাতি পারে। কী চমৎকার নিদানডা! ওই এহন যা রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কয়, নবীজি ভাবিছিলেন! অবাক কাণ্ড!
‘তোর মেইরের বিয়ের টাকার চিন্তে নেই, ভাবিসনে। পিরতিমের জন্য ছাওয়াল দ্যাখ। বিয়ের টাকা দিয়ে দেবানে। তুই পারবি শুরু করতি? জাইনে রাখ, এই বিশ্বব্রেহ্মাণ্ডে আমাগের এই পিরথিবিতি ছাড়া কোনোহানে মানুষ নাই। অমানুষও না। হ।’
মানুষ নেই, অথচ সতেরোটা চাঁদ? এত চাঁদ নিয়ে মানুষ সেখানে তবে করেটা কী? আচ্ছা, শনিতে তারা আছে? চন্দ্র তো উঠেই আছে, সূর্য ওঠে শনিতে? সেথায় স্বাধীনতা দিবস টিবস…
‘কী ভাবতিছ, সনাতন? শোনবা সেই ভরণ্যের গল্পডা? আইজ তোমারেই কই। শোনো তয়।
‘ভরণ্যার তো কেবল ভয়, যুদ্ধির মধ্যি পড়লি বাঁচপে নানে। আগুন আর অস্তরের ভয়ে সারা। ভরণ্য তারে আশ্বাস দেয়। আমাগের বিনাশ নাইরে ভরণ্যা। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমরা সব সাধারণ, খাই দাই সংসার যাপাই, সন্তান বড় কইরে থুয়ে তারপর মইরে যাই। শক্তিশেলে মরি নেই কোনওদিন, আর অন্যের মারতি বানাইও না শক্তিশেল। দুনিয়ায় রাজা যায় রাজা আসে, আমাগের তাতে কোন কচুপোড়া ভরণ্যা? যুদ্ধু হয় শান্তি নামে আবার যুদ্ধু, শান্তি, যুদ্ধু। রগড়ের খেলা সব মানুষির। এই পারুল গাছে বইসে বইসে ক’দিন রগড় দ্যাখ। ছলচাতুরি, মিথ্যা কথা, জবরদখল, ছাওয়ালের সাথি মা-র জীবনভর ছলনা…’
‘কুন্তী তো ছলনা করে নেই মহাদেবদা, তিনি তো নিতে আইছিলেন কর্ণরে? ছলনা থাকলে তো আগে…’
‘বাঃ বাঃ, বুজতি পারতিছে তাহলি সনাতনও, আশার কথা! তাইলে বুজাই। ওড়া একপ্রেকার ছলনাই। ক্যান জানো? কর্ণ তো ইতিমধ্যেই কবচকুণ্ডল খোয়ায়ে থুইছে কৃষ্ণেড্ডে, এহন বাকি খালি মনোবল। হেডা ভাইঙ্গে দিতি পারলিই… এট্টা কথা জানবা, কুন্তী ছেলেন কৃষ্ণের পিসি, তা স্বভাবে, চরিত্তিরে, সর্বত্র। কর্ণের ধারে যাইয়ে পরিচয় দিলি তুই, ছাওয়ালগো লইয়ে আইতে পারলিনে সাথে করি? যুধিষ্ঠির যদি মাথায় করি লইয়ে যাইতে কর্ণেরে, কইতে, দাদা চলেন, কর্ণের বাপের নি সাধ্যি ছেলে না করার? অরা তো জানতেই না কর্ণ বেবাকের বড় ভাই, কুন্তী অগোরে কোনওদিন বলিছে? হ, বলিছে, মৃত্যুর পর। কর্ণের মরণের পরে, মনে রাখবা। যুদ্ধির শ্যাষ। কুরুক্ষেত্তর তহন এক মহাশ্মশান। ধৌম্য, বিদুর, সঞ্জয়রা চন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, ঘের্ত লইয়ে চলিছেন সব, কিনা মৌত হওয়া বীরেগো সৎকার করতি হবে। দলে দলে। কুন্তীও ছেলেন ছাওয়ালগো লইয়ে। তহন, তহন ইস্ত্রীরা তাগের মড়া সোয়ামিগো পরিচর্যা করতিছে, ভাবো একবার! মাথা নাই কারো, ধড়হান পইড়ে রইছে, আবার কারো ধড় পাওয়া যাচ্ছে নে, খারি মাথা! অভিমন্যু, তারে মাইরে সপ্তরথীর কী কিল্বিষ, ওঃ! তার শবদেহে হাত বুলোয়ে দেচ্ছে উত্তরা। বিয়ের ছয়মাসের মদ্যি উত্তরা বিধবা। কী করা? কারগিল মনে পড়ে না? আর কর্ণ? সৎকার হবে কী, শিয়াল কুকুরিই তো সাবাড় করি থুইছে তার আশিভাগ! সেই শরীর দেহাতে কুন্তী কলেন, ছাওয়ালরা, অর্জুন এরে মারিছে, এ তোমাগের বড় ভাই। এ্যার সৎকার তোমরাই করবা! এই পেরথমবার। সন্তানগো কুন্তী কইলেন, কর্ণের মৌত হবার পর। ছলনা করা না? যুধিষ্ঠির তো কইয়েই বইলেন মায়েরে, তুমি আগে কও নেই! আমরা কর্ণের সাথে মিললি কুরুকুলের এই নাশ হতি পারে? যুদ্ধু হতি পারে, মা?’
সনাতনের পিঠে হাত বোলাতে থাকে মহাদেব। যেন কর্ণের মৃত্যুতে এ-মুহূর্তে সনাতনই কাতর। হাত বুলোচ্ছেন, আর দেখতে পাচ্ছেন, যেন জটাধারী ব্রাহ্মণেরা…
‘কাইলই যাও সনাতন, পিরতিমের বিয়ের যা ব্যবস্তা, কইরে আসো। ভরণ্যপক্ষীডা শুইনে নাও। কী জানো, কলেরা বসন্তে মরলি পর শকুনিতি ছুঁয়েও দ্যাহে না। আর যুদ্ধি যারা মরে, তাগের ছিঁড়ে খায় শিয়াল, কুকুর, শকুনি। কী ভয়াবহ দৃশ্য, পারুলের ডালে বইসে ভরণ্যা দেখতিছে, ভরণ্য দেহায়ে দেচ্ছে। ‘ওই দ্যাখ ভরণ্যা, ওই দেখ দুর্যোধন, গদা জড়ায়ে ধরি মইরে আছে। ওই দ্যাখ শকুনি, মাতুল শকুনি, তারে শকুনে খাচ্ছে। জয়দ্রথের দেহ লইয়ে ভাগ বসাচ্ছে কেডা, না গৃধ্ন আর শিয়াল। আমরা যে গাছে বসা, তার তলে দাঁড়ায়ে মাথা ঠুকতিছে কেডা, না দুঃশলা, একশো ভায়ের আদরের এক বোন। এত বড় যুদ্ধির মাডে দুঃশলা তার সোয়ামির লাশটাই খুঁইজে পাইতেছে না রে! আঃ, একবার চোখির শ্যাষ দ্যাহাডা… আর দ্যাখ, জটাধারী ব্রাহ্মণ, তারা সব ব্যস্ত দ্রোণাচার্যর চিতা তৈরিতে। দ্রোণাচার্য, কিনা অস্ত্রগুরু! অস্ত্রের পরিণাম দ্যাখরে ভরণ্যা, গুরু আর তানার শিষ্যেরা অস্ত্রের তলায় ক্যামনে তলায়, দ্যাখ! মোরা কিন্তু বেঁইচে রইছি, না? এট্টু চোখ জ্বালা, খাদ্যের অনটন গেল কয়দিন, তাছাড়া বেঁইচে তো আছি, ক বউ? আমাগের রাজ্যলোভ নাই, হরেক ভাষা জানা নাই, ষড়যন্তর নাই, লোভ ছলনা ফন্দি ফিকির নাই, শয়তানের লগে ওঠবস নাই, অকালমরণও নাই সেজন্যি। পাহাড় বন সমুদ্দুর নদী, গাছ পাখি, বেঁইচে থাকপে বরাবইর। বাঁচতি চাইলি সহজ হতি হয়। ভরণ্যা কইলে, মানুষের মদ্যি সহজ নেই? ভরণ্য কয়, আছে না? কুরুক্ষেত্তরের বাইরেও অনেক ক্ষেত্তর আছে, যেহানে বহু বহু মানুষ। আসলে অন্যত্রে যা নেই, মানুষে আছে, মানুষ, অমানুষ। দেখবি বউ, অভরণ্য হয় না, অপারুলও না, কিন্তু অমানুষ হয়। মানুষ বাঁইচে থাহে, ঘর গড়ে, ছাওয়াল মানুষ করে, অ-মানুষ তারে নিকেশ করতি চায়, পারে না। মানুষও মরে, তয় মরে আর বাঁচে, বিনাশ হয় না। যুদ্ধু শুরুর আগেই তো তোরে কইছিলাম, আমরা বেঁইচে থাকপার জাত। কই নেই? এই হইল তোমার বিত্তান্তখান।’
মহাদেব থামে। মধ্য আকাশে সব তারা এসে জড়ো এতক্ষণে, সনাতন দেখে। হ্যারিকেনটা কমানো হয়নি, তার আলো মহাদেবের মুখে। মুখটা এত কথা বলেও প্রসন্ন, রাত্রির মত কোমল আর মায়াময়। কথা শেষ, তবু মুখ দেখে মনে হয় সনাতনের, আঁধারের জ্যোত্স্না ফুটে উঠেছে যেন মহাদেবের মুখে। যেন আরও কিছু বলবে। ‘শোন সনাতন। আমি অবতার না। জয়রাম আমারে অবতার বানাতি চাইছিল। আমার আশীর্বাদে ফল হয়, মাইনষের ধারণা। গেরামে অনেকেরি মাথায় হাত রেইখে যা কইছি, হইছে। কেউ প্রোফেসর, কেউ আফিসের বাবু, হইছে। আসলে তারা হবার, হইছে তাই, গতিপথে বোজন যায় না? তোমারেও কই, ওসব শনিটনি ছাড়ান দ্যাও। এই পিরথিবি লইয়ে থাহো। গেরামে পাকা রাস্তা নাই। বড় ছাওয়ালের লগে পরামর্শ করিছি, সেও দেবে, চাঁদা উডোবে, আর আমার যা আছে, আগে রাস্তা করন লাগে। এহন কেও শনির চিন্তা করে? এই গ্রেহের বেবাকের খাওনপরন আগে, পড়ালেহা আগে, তারপর তুমি মঙ্গলে যাবা না শনিতি, তা ঠিক করবা। কপাল থুইয়ে অন্যত্র চন্দন মাহা।’
কে আসছে না? আঁধার কেটে কেটে উঠোনটা পেরিয়ে, মালতীফুলের গন্ধকে মৃদু নাড়া দিয়ে, হ্যাঁ, এখন স্পষ্ট দেখছে সনাতন তাকে। সতীনাথ।
‘ঘুমান নাই এখনও?’ প্রশ্নটা সতীনাথ সনাতনকেই করে। যদিও এখানে উপবিষ্ট দু’জন। উত্তর জানাও বাহুল্য মনে হয়।
‘সতীনাথ। এই রাত্তিরি?’
‘আমার জুতোজোড়া ভুলে… কোথায় যেন… এখানে পাওয়া গেছে?’
‘জুতা? কী কয়, ও সনাতন?’
‘পাওয়া গেছে।’ বলে দাওয়ার কোণ নির্দেশ করে সতীনাথকে সনাতন। সতীনাথ দক্ষিণে যায় জুতো আনতে।
‘জুতা ছাড়াই বাড়ি গেছিলা, সতীনাথ? তোমার হইছে কী কও দিনি। খুব বড় বিপদ ছাড়া তো.. ‘
হ্যাঁ, খুব বড় মুশকিল সতীনাথের। সেজন্যই সে জুতো ফেলে গিয়েছিল, একা আসবার অজুহাত তৈরির জন্য। যদিও জুতো নিয়ে গেলেও… বিপদে কত অদ্ভূতই তো হয়। তার শ্যালক জনার্দন, ইটভাটা, সিনেমাহল, আলুর হিমঘর নিয়ে দেদার বড়লোক। এবার ভোটে দশ লাখ টাকা দেবে জয়রামকে, ঠিক ছিল। জিতলে তার বহুগুণ উসুল করে দেবে রাম। কিন্তু ভোটে কে জিতবে, তার আগাম আভাস পাচ্ছে রোজই সতীনাথ তার চেম্বারে বসে। অপরিচিত-পরিচিত পেশেন্টকে একটা প্রশ্ন করে সে, ভোটে কে কে দাঁড়িয়েছে। সে জানে, ভোটারের সাধারণ মনস্তত্ত্ব। যাকে ভোট দেবে তার নাম সে আগে বলে। অন্যান্য নামের ক্ষেত্রে হয় সে ভুলে যায়, নয়তো পরে উচ্চারণ করে। অনেকে তো জিগ্যেস করলেই বলে, আমাদের অমুক দাঁড়িয়েছে। সতীনাথ দেখেছে, শতকরা কুড়িজনও জয়রামের নাম করছে না। এতগুলো টাকা… আজই জনার্দনের দেবার তারিখ গেছে, জনার্দনকে বলতে এখন তো সে এক বিন্দু রাজি নয়, সে এখন জয়রামকে না দিয়ে অপনেন্ট রামজয়কে টাকাটা দিতে চায়… এখন বাঞ্ছনীয় কী?
‘এই জন্যি জুতো থুয়ে রেইখে আবার আসতি হয়? তা তুমি ছাপোষা হোমিও, ন্যাবা রুগির পথ্য লইয়ে থাকো। জাহাজ সামলানো তোমার কাম না। জনার্দন যহন হিমঘর পজ্জন্তি গেছে, আবার সিনেমাহল, নানা পাট্টির লগে যন্তরমন্তর সারা। হে তো এহন মারকশা। হে তোমার মত কাঁচকলা দে কান ফোঁড়াতি চায় ক্যান? সংকেত বুইলাম না। চতুরের থে চাতুরী নিতি বলো। আর তোমারে শিখোলাম, টাকা দিয়ে কিছু করতি হয়, নিজি করো। ফলাশা কইরে না। তালিই ভাল। টাকা দেবা একজনরি, সে আবার সেডা বাড়ায়ে তোমারে ফেরত দেবে, মাঝখানেত্থে মাইনসের জেরবার। ও জয়রাম বলো আর রামজয়, কাগজের দুই পিড এক, শাদা, মানি ফক্কা। রামেরে না কইরে দেও। যা করবা, মজবুত মন নিয়ে করবা। আর যা করবা না, হেড়াও মজবুত মনে।’
‘আসি তবে?’
‘যাওন নাই। দুর্গা দুর্গা।’
এই দুর্গা নাম উচ্চারণই শেষ স্মৃতি ছিল না সম্ভবত মহাদেবের, সনাতনের কাছে। সে এরপর মহাদেবের মশারি টাঙিয়ে দেয়। এরপর মহাদেবের দু-তিনহাত দূরে রোজকার মত বিছানা করে শুয়ে পড়ে। পরদিন মহাদেব সকালে উঠে সনাতনের মেয়ের জন্য, আর সনাতনেরও ভবিষ্যৎ ভেবে একলাখ টাকা দেবে বলে। দেবে মানে ব্যাঙ্কে তার নামে জমা করে। বিয়েতে খরচ। আপাতত সুদের টাকাটা বাড়িতে পাঠাবে। সনাতনকে এ-ছাড়া মাসে থোক পাঁচশো। সনাতনকে বাড়ি পাঠায় উদ্যোগ নিয়ে, পরিবার দেখে আসতে, পারলে প্রতিমার সম্বন্ধ ঠিক করতে। নিজ গ্রামে বা তার আশেপাশে হওয়াই ভাল।
ভোটে হারে জয়রাম। আর রামজয়ের বিজয় মিছিল বেরোয় যেদিন, মহাদেবের সেদিনই মৃত্যু। তার অন্ধত্বের যেমন বিরাট হেতু ছিল না কোনও, কেবল বার্ধক্যের হেতু ছাড়া, মৃত্যুও সেই একই কারণে। শ্মশানে গিয়েছিল রাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয় মিছিলের দিনটায় এছাড়া সে করতই বা কী? সনাতন বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে এখনই। মৃত্যুর সময় সে ছিল না। পাত্র পাওয়া গেছে ধূর্জটিকে, জানানো গেল না। এসেই শোনে, মহাদেবদা শ্মশানে। দৌড়েই সে প্রায় শ্মশানে পৌঁছয়। জয়রামের দল তখন চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দিয়ে বাইরে এসে চা-সিঙারা খাচ্ছে। সনাতনকে দেখে তাকেও চা সাধে জয়রাম। তখনও মুখদর্শনের আশা আছে ভেবে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে এগোয় সনাতন। মুখও দেখে মহাদেবের। যাবার আগের রাতেও তো সুস্থ ছিল! ভোরে সনাতন যখন বাড়ি যায়, মহাদেব বলেছিল, ‘সনাতন! শনি ভুলতি পারিছ?’ এখনও কথা, গায়ে আগুন, তবু? সনাতন শোনে, ‘সুখী মানুষ কারে কয় জানো সনাতন? এ বিষয়ে যুধিষ্ঠির ধর্মেরে কইছিলেন, যে লোক ঋণী বা প্রেবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টমভাগে কিনা বেহানে শাক রন্ধন করি খায়, সে-ই সুখী। ঋণে সুখ নাই।’
‘আমি তো সুখী হব না তয়! আপনার ধারে ঋণী…’
‘ঋণ না, কুমারধুবির ঋণশোধ সনাতন। ঋণী তো ছেলাম আমি। বর্তমানে ঋণমুক্ত।’ চিতা থেকে উঠে আসে স্বর। সনাতন অনেকক্ষণ ধরেই শোনে ধোঁয়াশাময় শব্দ। আর শুনতে পারে না সনাতন। তার এসময় কান্না পায় বলে শ্মশানের পাশে নদীতীরে কাঁদতে যায় সে। কাঁদে। কিছুক্ষণ। তারপর দেখে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিষ্ণু। সনাতনকে একা একা কাঁদতে দেখে চুপ করে থাকে, কিছু বলে না। না, বলে। সনাতনের গায়ে হাত রেখে জানায়, মহাদেবের ডেথ সার্টিফিকেটটা সতীনাথ লিখেছে।
হঠাৎ হাসান এসে পড়ে ওদের মধ্যে। দু’জনকেই সে ব্যগ্র হয়ে চিতার কাছে আসতে বলে। চিতা নাকি জ্বলছে না, বারবার নিভে নিভে যাচ্ছে।
সে কী! জ্বলছে না মহাদেব! সনাতনের বারবার মনে হয়, ডেথ সার্টিফিকেটটা হোমিওপ্যাথ নেওয়া ঠিক হয়নি। এখন হাসান কয়, চিতা জ্বলে না। তবে তো মহাদেব মরেছে কিনা সন্দেহ!
চিত্রণ: চিন্ময় মুখোপাধ্যায়