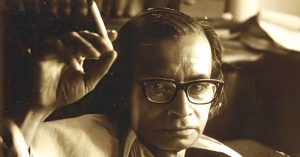পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মাছচাষের পুকুরে এবং আধুনিক প্রতিপালনপদ্ধতিতে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ রুই-কাতলা সহ অন্যান্য মেজর ও মাইনর কার্প মাছ, দেশি মাগুর এবং আধা-নোনাজলের মাছগুলি (ভেটকি, পারসে, ভাঙ্গন) সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদন করা হচ্ছে, মৎস্যবিজ্ঞানীরা তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মৎস্যচাষিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ২০১৮-১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৭৭ লক্ষ টন মাছ উৎপাদন করা হয়েছিল, এরমধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ টন অন্তর্দেশীয় মাছ, অর্থাৎ মিঠাজলের মূলত ছয়টি প্রজাতির মেজর কার্প মাছ ও কয়েকটি আধা-নোনাজলের মাছ, অধিকাংশ পরিমাণই উৎপাদন করা হয়েছে চাষপদ্ধতিতে, বাকি মুক্ত জলাশয়ে আহরণপদ্ধতিতে। বাণিজ্যিক কারণে বড় আকারের সুস্থসবল চারাপোনা পুকুরে মজুত রেখে ১৩৫-১৮০ দিনের মধ্যে পরিণত বড় আকারের মাছ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মাছচাষিরা উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন, গ্রামে গ্রামে অধিকতর মাত্রায় মৎস্যচাষ প্রসারিত হচ্ছে ও সমৃদ্ধিলাভ করছে।
বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তর্দেশীয় মুক্ত মিঠা/ স্বাদু ও আধা-নোনা জলাশয়গুলিতে (নদী, উপনদী, বিল, দিঘি, বৃহৎ বন্যাপ্লাবিত জলাভূমি, সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত নদী, মোহনা) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পরিণত রুই-কাতলা প্রায় পাওয়াই যায় না। তাই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সম্ভাবনাময় ও স্থিতিশীল ব্যবস্থা মৎস্যপ্রতিপালনপদ্ধতির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কার্প মাছ, দেশি মাগুর, দেশি কই, শিঙি, পাবদা, সরপুঁটি, বাটা, ট্যাংরা, চিতল, পাঙ্গাস, নাইলোটিকা তিলাপিয়া এখন পশ্চিমবঙ্গে চাষপদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে।
মাছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতি
আবদ্ধ জলাশয়ে ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিপালনযোগ্য মিঠাজলের মাছের মধ্যে দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড EPA, DHA-র প্রগাঢ়তা খাদ্যোপযোগী সামুদ্রিক মাছের তুলনায় অনেকটা কম থাকে, যা আমাদের শরীরে নিয়মিতভাবে যোগান দেওয়া অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্নপ্রকার সামুদ্রিক মাছ (তোপসে, ফ্যাসা, কড্, হেরিং, ম্যাকরেল, সারডিন, নেহেরে, কয়েক প্রজাতির টুনা, ইত্যাদি) হল EPA, DHA-র উৎস। স্বাভাবিকভাবে তৈলাক্ত ও সুস্বাদু পরিণত সামুদ্রিক মাছগুলি নিকটবর্তী ও গভীর সমুদ্র থেকে আহরণ করে বাজারজাত করা হয়; এই উপকারী পলিআনস্যাচুরেটেড লং-চেন ফ্যাটি অ্যাসিড দুইটি পর্যাপ্ত পরিমাণে এদের দেহমাংসে উপস্থিত থাকে। এরা সামুদ্রিক শৈবাল, স্থানীয় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও সমুদ্রের ছোট মাছ খেয়ে বড় হয়, যার মধ্যে EPA, DHA বেশি পরিমাণে থাকে।
প্রতিপালনযোগ্য অন্তর্দেশীয় মাছের স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিগুণ নির্ভর করে মাছগুলিকে কেমন পরিস্থিতিতে প্রতিপালিত ও কী খাওয়ানো হচ্ছে, তার ওপর। মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, মৎস্যচাষিরা খামারে চালের কুঁড়ো, সরষের খোল, বাদামের খোল, আটা, সোয়াবিনের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে মেজর কার্প মাছগুলির খাবার তৈরির সময়ে প্রতি কেজিতে যদি ১০০ গ্রাম শুঁটকি মাছের গুঁড়ো, ৫০ গ্রাম উদ্ভিদজাত ভোজ্য তেল (বাদাম, সূর্যমুখী বা সোয়াবিনের তেল) এবং ২০ গ্রাম ভাল মানের সামুদ্রিক মাছের তেল মিশিয়ে নেন, তাহলে মাছগুলির দেহমাংসে/ দেহপেশিতে EPA, DHA-র প্রগাঢ়তাকে বাড়ানো সম্ভব হবে। মাছের খাবারে সরষের খোল ফ্যাট বা স্নেহজাত পদার্থের উৎস, প্রতি কেজিতে ২৫ গ্রাম ঘিয়ের গাদ মেশানো যায়। মজুত পুকুরের জন্য খামারে তৈরি রুই-কাতলার খাবারে প্রোটিন থাকবে ২৫-৩২%, একই সঙ্গে স্নেহজাত পদার্থ থাকতে হবে ৬-৭%। সঠিক উপাদান সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে হালকা রান্না করে সুষম পরিপূরক মাছের খাবার তৈরি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড-সমৃদ্ধ দেহসার প্রোটিন, ভিটামিন এবং অণুপুষ্টিবিধায়ক পদার্থর কথা ধরলে পুকুরের মেজর কার্প মাছের দেহমাংসের পুষ্টিগুণ দক্ষিণবঙ্গের খুচরো বাজারে প্রাপ্ত সামুদ্রিক মাছের পুষ্টিগুণেরই সমতুল্য।
অন্তর্দেশীয় মাছের স্বাদ-এর নিয়ন্ত্রক
পশ্চিমবঙ্গের খুচরো বাজারগুলিতে বড় আকারের রুই, কাতলা ও অন্যান্য চাহিদাসম্পন্ন মাছের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, জীবিত অবস্থায়ও পাওয়া যায় কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় অনেক ক্রেতার মতে, মাছের স্বাদ আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ বলেন, প্রকৃতি থেকে মৎস্যজীবীদের ধরা রুই, কাতলা ও অন্যান্য মেজর কার্প মাছের (যা ১৯৭০-এর দশক, ১৯৮০-এর দশক পর্যন্তও ভাল পরিমাণেই ধরা পড়ত) স্বাদ পুকুরে চাষপদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছের তুলনায় বেশি, প্রথমটি বেশি ভাল খেতে। বড় পারশে, ভেটকি মাছও সুন্দরবন লাগোয়া কয়েকটি ব্লকে চাষপদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে; মোহনা ও নিকটবর্তী সমুদ্র থেকে ধরা ভেটকি অনেকে মনে করেন খেতে বেশি ভাল।
বর্ষাকালে বড় ইলিশ মাছ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বঙ্গোপসাগর থেকে হুগলি-মাতলা মোহনা পেরিয়ে ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ নদীর উপরিভিমুখে যাত্রা করে, তখন মাছগুলির দেহমাংসে গঠিত ফ্যাট/ স্নেহজাত পদার্থ এবং উপস্থিত স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে মোনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড হয়ে লং চেন পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তর– বিষয়গুলি মাছটির ভাল স্বাদ হওয়াকে প্রভাবিত করে। পুকুরে উৎপাদন করা বাজারজাত রুই-কাতলার দেহমাংসে যদি সঠিক মাত্রায় ফ্যাট এবং EPA, DHA বেশি পরিমাণে উপস্থিত করানো যায়, তাহলে মাছগুলির ভাল স্বাদ বজায় থাকবে। যদি মাছচাষের পুকুরের যত্ন ঠিকমত না নেওয়া হয়, তলদেশে জমে থাকা পাঁক বহুদিন সংস্কার করা হয়নি, কালচে জল, নিয়মানুযায়ী চুনদ্রবণ দেওয়া হয় না, পাঁক-গন্ধযুক্ত মাটি– এমন পুকুরে বেড়ে ওঠা মৌরোলা, বাটা-সহ অন্যান্য কার্প মাছের স্বাদগন্ধ ভাল হয় না, বাজারে ক্রেতারা তা অপছন্দ করেন।
প্রাকৃতিক অথবা হ্যাচারিতে উৎপন্ন অন্তর্দেশীয় মাছের চারাপোনা স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন পুকুরে মজুত রাখলে প্ল্যাঙ্কটন ও খোল-কুঁড়ো-বাসিভাত মেশানো খাবার খেয়ে মেজর কার্প মাছগুলির বেড়ে উঠতে বেশি সময় লাগে (১৪-২০ মাসে ১.২-২ কেজি)। গ্রামাঞ্চলে অনেক পুরনো পুকুরে বয়স্ক রুই, কাতলা, গ্রাসকার্প থাকে (২-৫ কেজি), স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, দেহমাংসে শক্তভাব (stiffness) বজায় থাকে এবং সুস্বাদু। গ্রামীণ মৎস্যচাষে ৫০০-৮০০ গ্রাম মাছের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অন্যদিকে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে পুকুরে কম সময়ে মাছের দ্রুত বাড়বৃদ্ধি ঘটানোর লক্ষ্যে বাহ্যিক সামগ্রীর ওপর নির্ভর করেন মাছচাষিরা। মাছগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, পুষ্টিগুণসম্পন্ন কিন্তু স্বাদ খুব ভাল নয়, দেহমাংস নরম বা ‘ভ্যাদভেদে’।
বাণিজ্যিক-কারণে মাছচাষের পুকুরে মেজর কার্প উৎপাদন করতে মুরগি ও ছাগলের নাড়িভুঁড়ি, মৃত পশুর দেহ-চামড়ার অংশ মাছকে খাইয়ে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ অজৈব রাসায়নিক সার ও মুরগির কাঁচা বিষ্ঠা পুকুরে প্রয়োগ করে চটজলদি অল্প সময়ে মাছকে বাড়িয়ে বাজারজাত করে যদি লাভবান হতে চান এ রাজ্যের কোনও মৎস্যচাষি, তাহলে অনুচিত হবে। উৎপাদিত মাছের স্বাদ ও গন্ধ ভাল তো হয়ই না, মৃত মাছ বাজারে বিক্রি না হলে তাড়াতাড়ি পচে যেতে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমদানি করা বরফে সংরক্ষিত ১-৪ কেজি সাইজের রুই-কাতলা অনেকেই কিনতে ও খেতে অপছন্দ করছেন, অসাধু পদ্ধতিতে রুই-কাতলা সংরক্ষণের কথা শোনা গিয়েছে। এ রাজ্যেই উৎপাদিত ৫০০ গ্রাম থেকে ১.২ কেজি ওজনের জীবন্ত বা সদ্যমৃত টাটকা মাছের ভাল চাহিদা রয়েছে খুচরো বাজারগুলিতে। কেন্দ্রীয় মিঠাজল মৎস্যপ্রতিপালন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের মতে, পুকুরে অণুখাদ্যের পরিমাণ বজায় রাখতে প্রতি হেক্টর পুকুরে (২৫০ শতক) মাছচাষ চলাকালীন ১৫ দিন অন্তর একবার করে ১০ কেজি ইউরিয়া ও ১৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট (এস এস পি) প্রয়োগ করতে হবে। নিমপীঠ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের মৎস্যবিশেষজ্ঞদের মতে, মাছের সঠিক বাড়বৃদ্ধির জন্য প্রতি বিঘায় (৩৩ শতক) মাসে একবার করে ৩.৩ কেজি এস এস সি এবং ২.৭ কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন।
পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক বনস্পতি বিশ্বাসের মতে, প্রতি মাসে বিঘাপ্রতি ৩-৪ কেজি ইউরিয়া এবং ৫-৬ কেজি এস এস পি মাছচাষের পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। মজুত পুকুরে মাছচাষে এইরকম সুপারিশ করা মাত্রার চাইতে বেশী রাসায়নিক সার কখনই প্রয়োগ করা উচিত নয়। বেশী পরিমান ইউরিয়া প্রয়োগ করলে সেই পুকুরের মাছের স্বাদ মোটেই ভাল হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মাছ হোক বা অন্ধ্রপ্রদেশের, সাধারণ মানুষের কাছে চাষপদ্ধতিতে উৎপাদিত বড় আকারের মেজর কাপ-এর গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে হলে মৎস্যচাষীদের ন্যায্য পদ্ধতি অবশ্যই মানতে হবে।
মাছের খাবার তৈরিতে চিটোগুড়
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে চিটেগুড় মেলে। একে ইংরাজিতে বলা হয় ‘molasses’। আখের গুড়কে পরিশুদ্ধ করবার সময়ে অথবা আগের রসকে ফুটিয়ে পরিশুদ্ধ গাঢ় সিরাপ থেকে চিনির দানা তৈরির সময়ে শেষপর্যন্ত যে অবশিষ্ট ঘন বাদামি বর্জ্য থাকে, সেইটি চিটেগুড়। ১০০০ কেজি আখ পিষে যে পরিমাণ খাঁটি রস উৎপন্ন হয়, এর থেকে ৪.৫-৫% চিটেগুড় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর মোট উৎপাদন পরিমাণের মধ্যে ১১.৬ লক্ষ টন আখ শুধুমাত্র গুড় তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, যার পরিমাণ ১.৪ লক্ষ টন৷ মিঠাজলের প্রতিপালনযোগ্য মাছ ও গবাদিপশুর পরিপূরক খাবারের উপাদান হিসেবে চিটেগুড় সহজপাচ্য প্রাণীগুলিকে শক্তি যোগায়, এদের পৌষ্টিকতন্ত্রে হিতকারী ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকলাপকে ত্বরান্বিত করে। দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক অন্যান্য খাবারের সঙ্গে দুপুরে খেতে দেওয়া হয় সরবত, প্রতি ১০ লিটার জলে থাকে ২০০ গ্রাম গুড়, ৫০ গ্রাম লবণ ও ৫০০ গ্রাম ছোলার ছাতু।
গমের আটা, ভুট্টা এবং চিটেগুড হল ভাল মানের জৈবজাত কার্বহাইড্রেটের উৎস, মাছের খাবারে ব্যবহার করা যায়। মিঠাজলের পুকুরে বাড়ন্ত মাছের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একজন মৎস্যচাষী প্রতি কেজি দানাখাবারে ব্যবহার করছেন সুবাবুল এবং অর্জুন গাছের পাতার গুঁড়ো ১০০ গ্রাম, ধানের গুঁড়ো ১৫০ গ্রাম, গমের আটা/ চালের গুঁড়ো ১৫০ গ্রাম, সূর্যমুখী/ মসিনার খোল ৩০০-৩৫০ গ্রাম, শুঁটকি মাছের গুঁড়ো ১৫০-২০০ গ্রাম, খেসারি ডালের খোসার গুঁড়ো ৫০-১০০ গ্রাম, কাঁচা হলুদগুঁড়ো ২০ গ্রাম, নিমপাতার গুঁড়ো ২০ গ্রাম এবং সাধারণ লবণ ১০ গ্রাম; এর সঙ্গে তিনি সরষের খোল, চালের কুঁড়ো, চিটেগুড় এবং বেকারি ইস্ট বা ব্রিয়ারস্ ইস্ট পাউডার) মিশিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে মিশ্রণটি খানিকটা পচিয়ে মাছকে খেতে দিচ্ছেন। পুকুরে জুভেনাইল দশাভুক্ত বাড়ন্ত বাগদা চিংড়ির দানাকার পরিপূরক খাবার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন, এতে থাকছে ঝিনুকের মাংস ও কুচো চিংড়ির গুঁড়ো (৩২৬ গ্রাম করে); গ্লুটেন প্রোটিন-সমৃদ্ধ গমের মাড় ও ভুটার গুঁড়োর অবশিষ্টাংশ (১৩৩৫ গ্রাম করে); চিটেগুড়, তালের তেল, কড্ মাছের যকৃত তেল ও ভিটামিন-খনিজ পদার্থ (২০ গ্রাম করে)।
পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী এক হেক্টর পুকুরে রুই-কাতলার চারাপোনার জন্য প্রতিবার খাবারে মিশিয়ে নিচ্ছেন সরষের খোল এবং চালের কুঁড়ো একত্রে ২০ কেজি, চিটেগুড় ১০ কেজি এবং বেকারি ইস্ট ৫০০ গ্রাম। মিশ্রণটিকে তিন দিন আংশিক পচিয়ে পুকুরে ১৫ দিন অন্তর ব্যবহৃত হচ্ছে, দশটি ১৬ কেজি সরষের তেলের টিনে প্রতিটিতে ৩ কেজি মিশ্রণ রাখা হয়। ইস্ট পুকুরে হিতকারী প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া উৎপাদনে সহায়তা করে। চালের কুঁড়ো, কালো কলাইয়ের কুঁড়ো, গমের কুঁড়ো, সরষের খোল গুঁড়ো, তিসির তেলের খোল, শুঁটকি মাছের গুঁড়ো, ০.৫% ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিশ্রণ এবং চিটেগুড় বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করে মেজর কার্প মাছের কম মূল্যের উপযোগী পরিপূরক খাবার তৈরি হয়েছে। পাঙ্গাস মাছের জীবনচক্রের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে তৈলনিষ্কাষিত চালের কুঁড়ো, ভাঙা চাল, ভুট্টা, ডাল, আখের গুড়, ফ্যাট-নিষ্কাষিত রেশমমথের পিউপা খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়৷ পুকুরে প্রতিপালনরত মেজর কার্প মাছের জন্য ২৫% গমের কুঁড়ো, ৩০% চালের কুঁড়ো, ২৫% সরষের খোল গুঁড়ো, ১০% শুঁটকি মাছের গুঁড়ো এবং ১০% গমের আটা/ চিটেগুড়– এইভাবেও খাবার তৈরি করেন মৎস্যচাষীরা।
পুকুরে প্রাণীজাত অনুখাদ্য বাড়াতে চিটেগুড়
কোচবিহার জেলায় মৎস্যচাষীরা ১ বিঘা মাছচাষের পুরুষের জন্য নিচ্ছেন ৪ কেজি চিটেগুড়, ৭ কেজি সরষের খোল এবং ১৫০ গ্রাম হিতকারী ছত্রাক ইস্ট। পাড়ে একটি (৬ x 8 x ১) ঘনফুট গর্ভে জল মিশ্রিত মিশ্রণটি স্থিরভাবে রাখা হচ্ছে, ছয় ঘণ্টা পর উপরিভাগের তরল অংশটি পুকুরে প্রয়োগ করবার পর পরবর্তী সময়ে প্রচুর পরিমাণ প্রাণীজাত অনুখাদ্য জ্যুপ্ল্যাঙ্কটন উৎপন্ন হতে দেখা গেছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কুন্ডুর মতে, পুকুরে প্ল্যাঙ্কটনের স্থায়িত্ব এবং জল ও মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধিকরণে প্রিবায়োটিকের মিশ্রণ প্রয়োগ করতে পারেন গ্রামাঞ্চলের মৎস্যচাষিরা। এতে থাকবে ২৫ কেজি চালের কুঁড়ো, ১০ কেজি চিটেগুড় ও ২৫০ গ্রাম ইস্ট, প্রতি হেক্টর পুকুরের জন্য। মিশ্রণটিকে চৌবাচ্চাতে ২-৩ দিন ঢাকা দিয়ে রাখলে গেঁজে উঠবে, পর্যায়ক্রমে তিনদিন প্রয়োগ করতে হবে।
অনেক চিংড়িচাষি পুকুরে জলের পিএইচ-কে কমিয়ে অতিরিক্ত নীলাভ-সবুজ শৈবালের প্রগাঢ়তাকে কমিয়ে ফেলতে জৈবসার অথবা চিটেগুড় ব্যবহার করেন। কিছু মাগুর মাছচাষি প্রজনন-উপযোগী মাগুর পরিচর্যার পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার জ্যুপ্ল্যাঙ্কটনের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োগ করেন অরগেনিক জুস; প্রতি ৩৩ শতক পুকুরে প্রতিবার ব্যবহৃত হচ্ছে পেষাই করা ধান ৭ কেজি, ইস্ট ৫০০ গ্রাম এবং চিটেগুড় ৪ কেজি। গামলায় মিশ্রণটিতে ৪-৫ লিটার জল মিশিয়ে তিন দিন ঢেকে রেখে দেওয়ার পর গাঢ় জলীয় পদার্থটি ১৫-২০ দিন অন্তর একবার ব্যবহৃত হয়। পুকুরে পিএইচ যদি খুব বেড়ে যায়, তাহলে কিছুদিন হেক্টরপ্রতি জলে দুইদিন অন্তর ৩০ লিটার চিটেগুড় প্রয়োগ করতে হয়। আধা-নোনাজলের ভেনামি চিংড়ির পুকুরে প্রয়োজনীয় অণুখাদ্যকণা উৎপন্ন করতে প্রতি ১০০০ বর্গ মিটারে ১৫ দিন অন্তর প্রয়োজন হবে ২৫০ গ্রাম ইস্ট, ৩ কেজি চালের গুঁড়ো, ১.৫ কেজি চিটেগুড় ও ২ কেজি শুঁটকি মাছের গুঁড়ো। অন্ধকার ঘরে চালের গুঁড়োতে ১ লিটার জল ও ইস্ট মিশিয়ে তিন দিন অক্সিজেন-বিহীন অবস্থায় রাখবার পর উপরিভাগের জুস অংশটি প্রথমদিন ৩৩% ও পরের দিন ৬৬% প্রয়োগ করতে হবে। এই চিংড়ির পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পোস্ট-লার্ভা মজুত রাখবার পূর্বে চালের কুঁড়ো, চিটেগুড় ও খোল মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়, যা হল ‘ফারমেনটেড্ অরগ্যানিক স্লারি’। গলদা চিংড়ি চাষে জুভেনাইল দশা মজুত রাখবার পূর্বে এই অরগ্যানিক স্লারি প্রস্তুত করতে লাগবে আখের গুড় অথবা চিটেগুড় ৫ কেজি, চালের কুঁড়ো ১০ কেজি, ইস্ট ২৫০ গ্রাম ও প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া ১৫০ গ্রাম; প্রতি ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে জলকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ করিয়ে ১২-১৮ ঘণ্টা পচিয়ে মিশ্রণটি পুকুরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।
বায়োফ্লক্ মাছচাষে চিটেগুড়ের প্রাসঙ্গিকতা
মৎস্যবিজ্ঞানী ড. বিজয়কালি মহাপাত্র আলোচনা করেছেন বায়োফ্লক্ পদ্ধতিতে মিঠাজলের মাছচাষের ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন তিলাপিয়া, দেশি মাগুর, দেশি কই, গুলশে ট্যাংরা, দেশি ট্যাংরা, শিঙি, পাবদা, পাঙ্গাস, সরপুঁটি ১০০০০-১৮০০০ লিটার গোলাকার আধারের জলে মাছগুলির নাইট্রোজেন-জাত বর্জ্যপদার্থ ও না-খাওয়া খাবার অণু-প্লোটিনে রূপান্তরিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে সঠিকভাবে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতকে (১০-২০ : ১) বজায় রাখতে কার্বহাইড্রেট-যুক্ত উপাদান চিটেগুড় ব্যবহৃত হয় কার্বন-এর উৎস হিসেবে, এতে থাকে ৫০% কার্বন। প্রতি ১০০০০ লিটার জলের জন্য দরকার ১ কেজি কমদামি চিটেগুড়, থাকবে র-সল্ট, ডলোমাইট, প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া। এই পদ্ধতিতে প্রতি ২ পিপিএম টোটাল অ্যামোনিয়াক্যাল নাইট্রোজেন (TAN)-এর জন্য প্রতি ১০০০ লিটার জলে ৪০ গ্রাম চিটেগুড় দিতে হবে। ‘বায়োফ্লক্ তৈরি করে মাছ ছাড়া’ পদ্ধতিতে শুরুতে অপরিশোধিত সামুদ্রিক লবণ ও ডলোমাইটের পর প্রতি ১০ লিটারে ১ কেজি চিটেগুড় দিতে হবে। এতে প্রোবায়োটিক মিশিয়ে, জলকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ করিয়ে আধারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে, যা তৈরি করবে অগণিত ফ্লক্ পদার্থ, ৫০-২০০ মাইক্রন আয়তন। ‘মাছ ছাড়ার পর বায়োফ্লক্ তৈরি করে নেওয়া পদ্ধতিতেও এইভাবে প্রোবায়োটিক ও চিটেগুড়ের মিশ্রণ তৈরি করে আধারের জলে প্রয়োগ করতে হবে।
ন্যাশনাল ফিশারিস্ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতি ১৫০০০ লিটার জলে ফ্লক্ উৎপাদন করতে ১৫০ লিটার জলে ইনোকিউলাম তৈরি করতে হবে; থাকবে পুকুরের মাটি, ইউরিয়া, ৩০ গ্রাম কার্বনের উৎস– যা হতে পারে চিটেগুড়, আটা অথবা টেপিওকা ময়দা। অক্সিজেনসমৃদ্ধ করিয়ে মিশ্রণটি ২৪-৪৮ ঘণ্টা পর আধারে প্রয়োগ করতে হবে। মাছ ছাড়বার পর প্রতিদিন প্রতি কেজি মাছের দানাখাবারের জন্য ৬০০ গ্রাম চিটোগুড় দিলে আধারের জলে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত বজায় থাকবে ১০ : ১। উৎপন্ন হওয়া ফ্লকের ঘনত্ব যদি হয় লিটারপ্রতি ১৫-২০ মিলিলিটার, এমন অবস্থায় চিটেগুড় যোগ করবার প্রয়োজন হবে না।
কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত, TAN ও চিটেগুড়
নিয়মিতভাবে মাছচাষ চলাকালীন সুকরোস্ এবং চিটেগুড় বায়োফ্লক আধারের জলে যোগ করলে হেটেরোট্রফিক ব্যাকটেরিয়ার বাড়বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে, ফ্লক্ তাড়াতড়ি তৈরি হয়। মাছের খাবারে প্রোটিনের উপস্থিতি কম থাকলে অল্প পরিমাণ চিটেগুড় প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় আধা-নোনাজল মৎস্যপ্রতিপালন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের মতে, বায়োফ্লক্ পদ্ধতিতে চাপড়া এবং ভেনামি চিংড়ি চাষে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত সঠিক রাখতে প্রতি ঘনমিটার জলে ৮.০৬ গ্রাম কার্বন যোগ করা হয়। যেহেতু চিটেগুড় এবং অন্যান্য কার্বহাইড্রেটের উৎসের মধ্যে ৫০% হল জৈব কার্বন, তাই প্রতি ঘনমিটারে ৪.০৩ গ্রাম কার্বন প্রয়োজন হয় (কার্বন : নাইট্রোজেন = ১৫ : ১)।
বায়োফ্লক্ পদ্ধতিতে নাইলোটিকা তিলাপিয়া চাষে আধারের জলে প্রাথমিক পর্যায়ে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত থাকতে হবে ২০ : ১। চাষপর্ব চলাকালীন জলে যদি TAN-এর মাত্রা নির্ধারণ করা হয় লিটারপ্রতি ১-২ মিলিগ্রাম, তাহলে চিটেগুড় এমন পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে যাতে ওই দুইটির অনুপাতের মাত্রা থাকে ৬ : ১। স্নেহজাত পদার্থবিহীন চিটেগুড়ের মধ্যে থাকে ৪.৪৫% প্রোটিন এবং ৮৩.৬৩% কার্বহাইড্রেট। গরমের সময়ে আধা-নোনাজলের চিংড়িচাষ বা মিঠাজলে মাছচাষের পুকুরে (যদি নিগমন নালা দিয়ে জল বের করা না হয় অর্থাৎ শূন্য জল-পরিবর্তন) বেশিমাত্রায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হওয়ার সময়ে চিটেগুড় ব্যবহার করলে হিতকারী হেটেরোট্রফিক অর্থাৎ পরভোজী ব্যাকটেরিয়া (ব্যাসিলাস গণ ও অন্যান্য প্রজাতি) তৈরি হয়, যা অ্যামোনিয়াকে ব্যবহার করে ফেলে এবং মাছের জন্য ক্ষতিকারক নাইট্রাইট স্থূলাণুর উৎপত্তি হওয়াকে রোধ করে। চিটেগুড়ের ঘনত্ব অনেকটা মধুর মত, কখনও দানা বাঁধে না, ভালমানের জৈব সার এবং আধা-নিবিড় ও নিবিড় মাছচাষের পুকুরে অ্যামোনিয়ার নিয়ন্ত্রক।
চিত্র: গুগল
নরেশচন্দ্র দত্ত: যাঁর সম্মানে এক মাছের নাম রাখা হয় Hara nareshi