তৎকালীন কলকাতার চিৎপুরে ‘ঘড়িওয়ালা বাড়ি’ নামে বিখ্যাত মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোন মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় ‘ন্যাশনাল থিয়েটর’ নাম নিয়ে একশ পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে টিকিট কেটে যে থিয়েটরের প্রচলন, সেটাই সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনাক্ষণ বলে চিহ্নিত নাট্যশালার ইতিহাসে৷ যার প্রভাব প্রবলভাবে পড়বে পরবর্তী প্রায় একশ বছর বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে৷ আমোদপ্রমোদ বা বিনোদনের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান, হাফ আখড়াই ইত্যাদিতে অভ্যস্ত বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বিনোদনের অভাব অনুভব করতে শুরু করে, এতদিনের গতানুগতিক দেশীয় আমোদ প্রথা তাদের কাছে মনে হতে থাকল রুচিহীন৷ এই নব্য ইংরেজি শিক্ষিতদের জন্য প্রয়োজন হল ইংরেজি ধাঁচের বিনোদন, যাতে ইন্ধন যোগালেন ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্ররা৷ এর আগে প্রায় আশি বছর, ১৭৯৫ সালের রুশদেশবাসী লেবেদেফের বাংলা নাট্যশালা তৈরির প্রয়াসের সময় থেকে, ধনী বা অভিজাত বাঙালিরা বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যশালা প্রবর্তনের কম চেষ্টা করেননি৷ কিন্তু সেইসব উদ্যোগই ছিল ধনী বা অভিজাত কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত আগ্রহের সুফল৷ তাঁদের মৃত্যু বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যার অবলুপ্তি ঘটে৷ ফলে এইসব নাট্যশালা কখনওই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি৷ সাধারণের জন্যও এইসব নাট্যশালার অভিনয় উন্মুক্ত ছিল না, কেবলমাত্র আমন্ত্রিতরাই আসতে পারতেন, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ইংরেজ সম্প্রদায় অথবা অভিজাত বাঙালি৷ যাঁরা এইসব নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করতেন তাঁদের নাট্যভিনয় বিনোদনের প্রতি প্রীতি ছাড়াও শাসক ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা সম্প্রীতি গড়ে তোলার আগ্রহও কম ছিল না৷ নাট্যশালার প্রবর্তন বাবু সম্প্রদায়ের কাছে একটা স্ট্যাটাস সিম্বলও ছিল৷ শোনা যায়, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ আর তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রবর্তন করে সেই আমলে (১৮৫৮) ‘রত্নাবলী’ নাটক প্রযোজনায় দশ হাজার টাকা খরচা করেছিলেন৷ ইংরেজদের বোঝার জন্য এই নাটক তাঁরা ইংরেজিতে অনুবাদও করিয়েছিলেন যার দায়িত্ব বর্তেছিল মধুসূদন দত্তের ওপর৷ এই নাটকের প্রযোজনা দেখে মাইকেল নাটক লিখতে আগ্রহী হন, আমরা ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকটি পাই৷
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকে এই যে একের পর এক নাট্যশালার উদ্ভব আবার কিছুদিনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার যে সংস্কৃতির সূত্রপাত, রাজারাজড়া জমিদার থেকে ক্রমশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থকেও যে সংস্কৃতিতে আগ্রহী করেছিল, সেই রকম সময়ে উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের জনা কয়েক যুবকের মনেও নাট্যভিনয়ের ইচ্ছে জাগে, যার ফলশ্রুতি ‘বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটর’৷ পরে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘শ্যামবাজার নাট্যসমাজ’ রাখা হয়৷ এই যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর আর অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী৷ এঁদের হাত দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা৷
নিজেদের সেরকম আর্থিক বাহুল্য নেই তাই প্রযোজনায় খরচ কম এমন যে নাটক তাঁরা প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন তা হল দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’৷ এর চতুর্থ অভিনয়ে দীনবন্ধু মিত্র নিজে দর্শক ছিলেন৷ এরপর যে নাটকটি তাঁরা বাছেন সেটা হল দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’৷ চাঁদা তুলে এই নাটক প্রযোজিত হয়৷ এর সুখ্যাতি এত বিস্তৃত হয়েছিল যে অনেককে জায়গা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল৷
‘লীলাবতী’-র সাফল্যেই নগেন্দ্রনাথের মনে টিকিট বিক্রি করে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা মাথায় আসে যেখানে সাধারণ মানুষেরা নাটক দেখতে আসতে পারেন৷ অবশ্য এর আগে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটর’ নামে সর্বসাধারণের জন্য একটা নাট্যশালা খোলার প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা ফলপ্রসু হয়নি৷
শ্যামবাজার নাট্যসমাজের যুবকদের কেউই কিন্তু থিয়েটরের টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কথা ভাবেননি৷ টিকিট বিক্রির পিছনে তাঁদের অন্য ভাবনা ছিল৷ থিয়েটর প্রযোজনার জন্য তখন আয়না থেকে চিরুণী সবই কিনতে হত৷ সামগ্রী ভাড়ায় পাবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না৷ প্রযোজনার এই ব্যয়ভারের যোগান হত চাঁদার মারফত৷ বারবার চাঁদা চাইতে গেলে পাড়া-প্রতিবেশীরা বিরক্ত হতেন৷ যেহেতু নাটকে অভিনেতাদের মাইনে দেবার ব্যাপার নেই, টিকিট বিক্রির টাকায় অন্তত প্রযোজনার খরচটা মেটানো যাবে আর টিকিট মূল্যের পরিবর্তে আগ্রহী যে কেউ এসে থিয়েটর দেখতে পারবেন৷ চাঁদা চাইতে গিয়ে কারও বিরক্তির মুখে পড়তে হবে না৷
অথচ শুরুটা খুব একটা মসৃণ হয়নি৷ টিকিট বিক্রি করে থিয়েটর করার জন্য নির্বাচিত হল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ৷ দলের নামকরণ প্রস্তাবিত হল ‘ন্যাশনাল থিয়েটর’৷ আর এখানেই আপত্তি জানালেন চার বন্ধুর একজন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ৷ পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র নিজেই এই আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে… ‘ন্যাশনাল থিয়েটর নাম দিয়া, ন্যাশনাল থিয়েটর উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল৷ কারণ একেই তো তখন বাঙালির নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশনাল থিয়েটর দেখিলে কি না বলিবে— এই আমার আপত্তি৷’ কিন্তু সেই আপত্তি বাকিরা শোনেননি৷ তাঁদের মত ছিল যেমন সামর্থ্য, তেমনই আয়োজন হবে৷ ফলে গিরিশচন্দ্রের দলত্যাগ আর তাঁকে বাদ দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা৷ টিকিটের মূল্য অনুযায়ী দর্শক আসন ভাগ করা হয়েছিল তিনটে শ্রেণিতে৷ প্রথম শ্রেণির জন্য ভাড়া করা চেয়ার, দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বাঁশের কাঠামোর ওপর পাটাতন বসিয়ে বেঞ্চি আর তৃতীয় শ্রেণির জন্য দালানের সিঁড়ি ও রোয়াক৷ প্রথম রজনীতে টিকিট বিক্রি বাবদ আয় হয়েছিল দু’শ টাকা৷

নীলদর্পণ-এর প্রযোজনা আর অভিনয়ের প্রশংসা সেইসময় সব সংবাদপত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল, যা নিশ্চয়ই গিরিশচন্দ্রের নজর এড়ায়নি৷ ‘ইন্ডিয়ান মিরার’ পত্রিকায় ১৮৭২-এরই ১৯ ও ২৭ শে ডিসেম্বর নীলদর্পণ প্রযোজনা সম্পর্কীয় দুটো চিঠি বেনামে প্রকাশিত হয় যা আগাগোড়াই ছিল বিদ্রুপ আর নিন্দায় ভরা৷ বেনাম অর্থে একটির প্রেরকের জায়গায় স্বাক্ষর ছিল ‘A Father’ অন্যটির ‘A spectator’, কারও নাম ছিল না৷ এই দুটো চিঠিরই প্রেরক গিরিশচন্দ্র, এমনটাই মনে করা হয়৷
নীলদর্পণ নাটকের দুটো অভিনয় হয়েছিল, যদিও প্রথম ও দ্বিতীয়বার অভিনয়ের মধ্যে ‘জামাই বারিক’ নাটকের অভিনয় হয়৷ এছাড়া ‘সধবার একাদশী’, ‘নবীন তপস্বিনী’, ‘লীলাবতী’, ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নাটকের অভিনয় হয়৷
ন্যাশনাল থিয়েটরের সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় দলে ফিরে আসতে বাধ্য করে, মাইকেলের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে৷ যদিও নাটকের বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম গোপন রাখা হয়েছিল৷
এই যে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা এর প্রথম পর্বের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ছয় মাস৷ ১৮৭৩-এর ৮ই মার্চ ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’ আর ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ এই দুটো নাটকের অভিনয় দিয়ে প্রথম পর্বের শেষ হয়৷ এর কারণ বর্ষা এসে পড়ায় স্যানাল বাড়ির প্রাঙ্গণে জল ঢোকার জন্য অভিনয় করা বন্ধ করে দিতে হয়৷
এর পরে পরেই কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়িতে ওরিয়েন্টাল থিয়েটর নাম দিয়ে কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়৷ এই সময় কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ, অনেক বিশিষ্টজনকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করে ‘বেঙ্গল থিয়েটর’ নাম দিয়ে একটা নাট্যালয় স্থাপন করেন৷ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, মাইকেলও ছিলেন৷ এই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় নিজস্ব নাট্যগৃহ পেল৷ ১৮৭৩ সালের অগস্টে মাইকেলের ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক অভিনয় দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটরের সূচনা৷ নানান কারণে সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বেঙ্গল থিয়েটর গুরুত্বপূর্ণ৷ এখানেই প্রথম মহিলা চরিত্র মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়৷ ‘দুর্গেশ নন্দিনী’ নাটকে জগৎ সিংহ-এর ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোষ ঘোড়ায় চেপে মঞ্চে উপস্থিত হতেন৷ ১৯০১ সাল অবধি বেঙ্গল থিয়েটর টিকে ছিল৷
অন্যের বাড়ি বা প্রাঙ্গণ ভাড়া নিয়ে থিয়েটর করার যে অনিশ্চয়তা, পরিবর্তে নিজেরা নাট্যশালা বানাতে পারলে তার স্থায়িত্ব হয়তো বেশি, এমন ধারণা থেকে আর বেঙ্গল থিয়েটরকে দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে ধর্মদাস সুর, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটর সেখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর নাম দিয়ে নাট্যশালা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন৷ প্রথম অভিনয় রাত্রে থিয়েটরে আগুন লাগলেও আরও প্রায় বছর চারেক এই থিয়েটর চলে৷ এই থিয়েটরেই ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে নাটক প্রযোজনা হয় যার ফলস্বরূপ তৈরি হয় Dramatic Performance Control bill, যা পরে Act of 1876 নামে আইন হয়ে নাট্যশালার স্বাধীনতার খর্ব করে দেয়৷
১৮৭৭ সাল নাগাদ গিরিশ ঘোষ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের ইজারা নিলেন৷ আর তারপর থেকে তিন দশক বাংলা নাট্যশালার অধীশ্বর হয়ে তিনিই থাকেন৷ এই পর্বে তিনি বাংলা নাট্যশালাকে লালন করেছেন বলা যায়৷ তাঁর অভিনয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশও এই সময়৷ তিনি অভিনয়ের জন্য স্বনামে বেনামে নাটক লিখেছেন, নিজে অভিনয় করেছেন, অন্যদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন, নাট্যশালা নির্মাণের জন্য নিজের অর্জিত অর্থ অনায়াসে দান করেছেন৷ কলকাতার বিখ্যাত ধনী গোপাল লাল শীল ‘স্টার’-এর জমি কিনে নিয়ে ‘এমারেল্ড’ থিয়েটর স্থাপন করেন৷ গিরিশ ঘোষকে ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন কুড়ি হাজার টাকা বোনাস আর মাসিক তিনশ টাকা মাইনেতে৷ এই টাকার ষোলো হাজার টাকা গিরিশচন্দ্র স্টারের সত্ত্বাধিকারীদের দিয়ে দেন নতুন নাট্যশালা নির্মাণের জন্য৷ গিরিশ ঘোষের সঙ্গে গোপাল শীলদের শর্ত ছিল আর কোথাও নাটক দিতে পারবেন না৷ সেই শর্তকে এড়ানোর জন্য বেনামে নাটক লিখতে শুরু করেন গিরিশ, যা স্টার-এ অভিনীত হতে থাকে৷ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রসার আর উন্নতির প্রকল্পে গিরিশ ঘোষের অবদানের মত কোনও দ্বিতীয় উদাহরণ আর হয়নি৷ এই সময়টা নাট্যশালার ইতিহাসে তাই গিরিশ যুগ বলে চিহ্নিত৷ অনেক অবস্থাপন্ন বড়লোক বাড়ির ছেলে সেইসময় থিয়েটরে আসেন যেখানে অভিনয়ের চেয়েও প্রাধান্য পেতে থাকে নানান স্থূল গিমিক৷ একাধিক নাট্যশালা গজিয়ে উঠতে থাকে যাদের আয়ু হত নেহাতই সংক্ষিপ্ত৷ থিয়েটর লাভজনক ব্যবসা ভেবে অনেক অবাঙালিও এতে লগ্নি করতে আগ্রহী হন, গিরিশ ঘোষের প্রশ্রয়ও পান৷ যদিও ব্যবসার বাইরে অন্য এক স্পৃহাও এই লগ্নিকারীদের ছিল, তা হল অভিনেত্রীদের আকর্ষণ ও কিছুটা তাঁদের সহজলভ্যতা৷ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে গিয়ে থিয়েটরের অন্যান্য সূক্ষ্ম দিকগুলোর দিকে নজর দেবার সুযোগ গিরিশ পাননি৷ নিজের অনবধানেই তৈরি করেছিলেন একটা ধাঁচ, লোকজনদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে থিয়েটরও লাভজনক ব্যবসা হতে পারে৷ সেই সময় নাটক হত দীর্ঘ, কাহিনির সঙ্গে থাকত উপকাহিনি৷ সারারাত্রি ব্যাপী অভিনয় হত৷ নাটকে নাচ আর গানের ছিল আধিক্য, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সবসময়ই জমকালো পোশাক ব্যবহৃত হত সামঞ্জস্য ছাড়াই৷ দর্শক আকর্ষণ করতে, ব্যবসায়িক চাহিদা মেটাতে এই ধাঁচ মেনে নিতে হয়েছিল গিরিশ ঘোষকে৷ এই ধাঁচই ছিল বাংলা থিয়েটরের অভিমুখ যতদিন না শিশিরকুমার ভাদুড়ি এসে তাকে অন্যপথে নিয়ে গেলেন৷ থিয়েটরে এল একটা শিক্ষার আবহাওয়া, সার্বিক সমন্বয়৷ এল রুচি৷ শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু শিক্ষিত মেধাবী মনীষা যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যুক্ত হলেন থিয়েটরের সঙ্গে, সরাসরিভাবে না হলেও৷ যে থিয়েটর ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে বিপথে যাবার রাস্তা, শিশিরকুমার তাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করলেন৷ শিশিরকুমারের আকর্ষণে মঞ্চে এলেন কঙ্কাবতী সাহু, মঞ্চে প্রথম শিক্ষিত গ্রাজুয়েট মহিলা৷ যা ভবিষ্যতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের থিয়েটরে যোগদানের পথ প্রশস্ত করবে৷ থিয়েটরের প্রতি দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল, দর্শকের চরিত্র বদলে গেল, একটা শিক্ষিত বাতাবরণ তৈরি হল থিয়েটরকে ঘিরে৷ আজকের যে থিয়েটার মডেলটা আমরা দেখি তা অনেকটাই শিশিরকুমারের অবদান৷ সাধারণ রঙ্গালয়ের জনক ও কৈশোর উত্তীর্ণ সময় অবধি অভিভাবক যদি গিরিশ ঘোষ হন তাহলে তার যৌবনের সারথি অবশ্যই শিশিরকুমার, যিনি রঙ্গালয়কে দিয়েছিলেন সামাজিক কৌলিন্য৷ তাঁর সময়টা শিশির যুগ বলেই অভিহিত৷
কিন্তু এঁরা একা নন, সাধারণ রঙ্গালয়ে গিরিশ ঘোষ বা শিশিরকুমারের সঙ্গে আরও অন্যান্যরা প্রয়াসী না হলে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটত না৷ ১৮৮৪ সালে ‘স্টার’ থিয়েটারে বিনোদিনী অভিনীত ‘চৈতন্যলীলা’ অভিনয় দেখতে রামকৃষ্ণদেবের প্রথম নাট্যশালায় আসাও সাধারণ রঙ্গালয়ের সামাজিক স্বীকৃতি জায়গায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা৷

সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা কেউই থিয়েটর করে জীবন নির্বাহ বা থিয়েটরকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবেননি৷ থিয়েটর চালানোর খরচ তুলতে আর সর্বসাধারণ যাতে সামান্য অর্থের বিনিময় থিয়েটর দেখতে আসতে পারেন সেই ভাবনা থেকে টিকিট বিক্রি করে সাধারণ রঙ্গালয়ের শুরু৷ আর এর ভিতরে সুপ্ত ছিল বাবু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদজনিত এক আদর্শ৷ কিন্তু এভাবে যে থিয়েটর বেশিদিন চলতে পারে না এই বিষয়টা বুঝেছিলেন গিরিশ ঘোষ৷ থিয়েটর চালাতে গেলে চাই ব্যবসায়িক বুদ্ধি, যা পূর্বে বুককিপারের চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে গিরিশ ঘোষের ছিল৷ এই প্রয়োজনীয় বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে গৌণ হয়ে গেল বাকি সব কিছু৷ থিয়েটরে যে ধাঁচটা তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সেটা হল ম্যানেজর অ্যাক্টরের ধাঁচ৷ ওঁর ক্ষেত্রে নাট্যকার ম্যানেজর অ্যাক্টর৷ কেননা এক বছরের মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র আর মধুসূদন দত্ত৷ লোকজনের থিয়েটর দেখার আগ্রহ বাড়ছে, গজিয়ে উঠছে নাট্যশালা৷ এমত অবস্থায় নাটকের অভাবে কলম ধরা ছাড়া গিরিশ ঘোষের আর কোনও গত্যন্তর ছিল না৷ কারণ থিয়েটরকে টিকিয়ে রাখতে হলে চাই নাটক৷ এইসব করতে গিয়ে থিয়েটরের উৎকর্ষের দিকে নজর দিতে পারেননি গিরিশ৷ থিয়েটরে উৎকর্ষ এল শিশিরকুমারের হাত ধরে৷ কিন্তু শিশিরকুমারও সেই একই ধাঁচে আটকা পড়লেন৷ থিয়েটরের উন্নতি করতে হলে চাই স্বাধীনতা, যা নিজের থিয়েটর ব্যতীত সম্ভব নয়৷ আর যেই নিজের থিয়েটর হল, অভিনেতা, নির্দেশক হয়ে উঠলেন ব্যবসায়ী৷ তখনই ব্যবসা এবং শিল্পের মধ্যে এল সূক্ষ্ম সংঘাত৷ যা একে অপরের পরিপূরক হতে পারত, হয়ে উঠল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী৷ আর এইখানেই পরাজয় ঘটল দুপক্ষেরই৷ থিয়েটর আর ব্যবসার৷ সাধারণ রঙ্গালয় অবলুপ্তির পিছনে এটাই অন্যতম প্রধান কারণ৷
শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয় ছেড়ে দেন, বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ১৯৫৬ সালে৷ বাড়ি ভাড়া দিতে পারছিলেন না৷ ততদিনে গণনাট্য সংঘ এসে গিয়েছে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ এসে গিয়েছেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিমুখ এঁদের হাত ধরে গড়াল অন্যপথে৷ শিশিরকুমারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের গৌরবের দিন শেষ হলেও আরও প্রায় দু’দশক তা টিকে ছিল৷ মহেন্দ্র গুপ্ত শেষ অবধি স্টার থিয়েটারে অভিনয় করে গেছেন, উত্তমকুমার অভিনীত ‘শ্যামলী’ নাটকও হৈ হৈ করে বহুদিন চলেছে৷ সারকারিনা বা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ অথবা রঙমহল বা অসীম চক্রবর্তীরা চেষ্টা করেছেন সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখতে, নিয়ে এসেছেন নানান আকর্ষক উপকরণ কিন্তু মূলত আর্থিক সমস্যার জন্য তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি৷ লগ্নিকারীরাও ভরসা পাননি৷ উৎপল দত্ত বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়রাও কিছুদিনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে তা চলেনি৷
দেড়শ বছর পার করে সাধারণ রঙ্গালয় তাই এখন স্মৃতি মাত্র৷









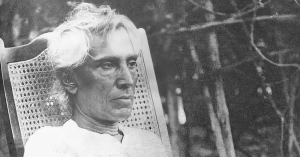





সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্ত সুখপাঠ্য। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ।