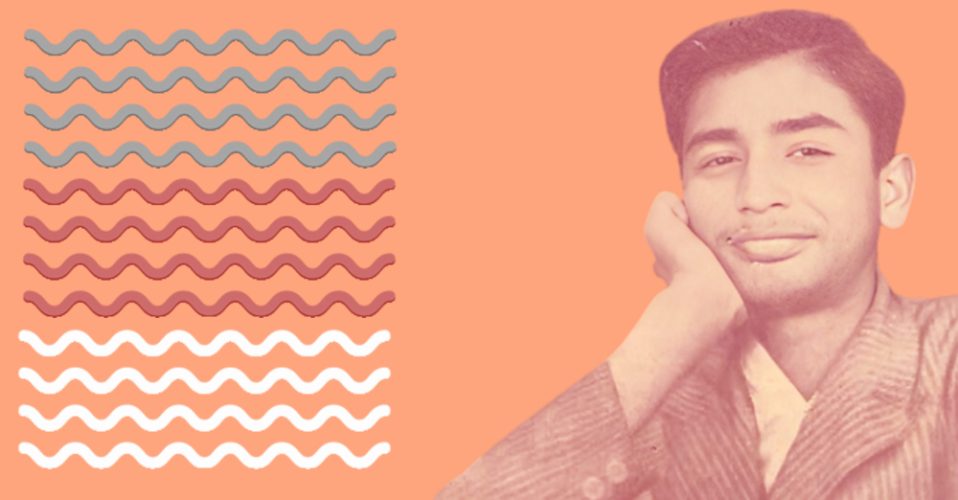প্রাগ্ ভাষ
আবহমান বাংলা কবিতা বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত গর্ব। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী-ময়মনসিংহগীতিকা, মুসলমান কবিদের লেখা ধর্মনিরপেক্ষ রচনা ‘ইউসুফ জুলায়খা’-‘শিরি ফরহাদ’-‘লাইলা মজনু’-‘জঙ্গনামা’, ও পরবর্তী কবিদের লেখায় যে শাশ্বত উচ্চারণ, তা অদ্যাপি আমাদের নন্দনকে পোষকতা দেয়। আমরা ভুলি না লুইপা আর ভুসুকুকে, বা শাহ মুহাম্মদ সগীর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গরীবুল্লাহ, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, আবদুল হাকিম, কাজী নজরুলের পূর্বসূরি সৈনিক-কবি আলাওল, চন্দ্রাবতী-রহিমুন্নিসা, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত পর্যন্ত প্রসারিত কবিকুলকে। এঁদের হাত দিয়েই আমরা পেয়েছি বহু অমর পঙক্তি, ‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরী’, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’, ‘যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সেসবে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি’, ‘সুজনক পীরিতি নউতন নিতি নিতি’, ‘তুমি হইয়ো গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি’, ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’, ‘এমন মানবজমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা’!
আধুনিক কালে এসে বাংলা কবিতার জগতে যে বিপুল বিস্তৃতি ও কবিসমাগম ঘটল, তা এককথায় বিস্ময়কর। তবে প্রতিভা ও স্থায়িত্বের বিচারে নিঃসন্দেহে সামান্য কয়েকজনের নাম-ই উঠে আসবে। আমরা নির্দ্বিধায় এক্ষেত্রে যে পঞ্চকবির নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি, তাঁরা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য। কী কাব্যসিদ্ধির বিচারে, আর কী জনপ্রিয়তার, এই পাঁচজন কবির নাম বাংলা কবিদের চিরায়ত ও স্থায়ী নাম রূপে উঠে আসবেই। এঁদের মধ্যে সুকান্ত, অতীব দুর্ভাগ্যের, মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রয়াত হন। কিন্তু পাশাপাশি এ-ও আশ্চর্যের, ওই আগ্নেয় প্রতিভা একুশ বছর বয়সের কবিতাকায়ায় যে ফসল ফলিয়েছেন, বাংলা কাব্যের জগতে তা সোনালি রোদ্দুর হয়ে আছে, থাকবে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তাঁর কবিতা ‘গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী’। আহ্বান জানিয়েছেন সেই ভবিষ্যৎ কবিকে, কর্মে ও কথায় যে আত্মীয়তা অর্জন করেছে, শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভুলিয়ে। সেই কবি, যেন কবিগুরুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেই তাঁর জীবিতকালেই ‘ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে’ আবির্ভূত হয়েছিলেন। আজ সুকান্তর জন্মশতবর্ষ পূর্তির দিনটিতে (তাঁর জন্ম ১৫.০৮.১৯২৬) তাঁকে, তাঁর কৃতিকে স্মরণ করবার দিন।
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
সুকান্তের জন্ম দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে সাতবছর আগে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে তাঁর তেরবছর বয়সে। সত্যি-ই সময়টা ছিল এক ক্রান্তিকাল, যে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারত তথা বাংলায় ঘটে গেছে দাঙ্গা, রাজনৈতিক ডামাডোল, তিরিশের মন্দা, গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্ব, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন মোতাবেক ‘৩৭-এর সাধারণ নির্বাচন। তৎপরবর্তীকালের ঘটনায় উত্তাল সমগ্র দেশ। বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে আরও ঘটনার ঘনঘটা,– ভারত ছাড়ো আন্দোলন, স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা। স্বাধীনতা ও দেশভাগ সুকান্তকে দেখে যেতে হয়নি, ১৯৪৭-এর ১৩ই মে প্রয়াত হন বলে। কিন্তু আসন্ন স্বাধীনতা লাভ ও তার বিধুরতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে।
সুকান্তর কবিতা তাঁর সময়ের ধারাবিবরণী। সমকালীন এমন ঘটনা নেই, যার প্রতিফলন তাঁর কবিতায় রেখাপাত করেনি। আর তাঁর স্বল্পকালীন কবিজীবনে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সময়ের উপযোগী ভাষা। টি এস এলিয়েট তাঁর ‘Four Quartets’-এ যা লিখেছেন, ‘For last year’s words belong to last year’s language,/ And next year’s words await another voice’, সুকান্তের বাগ্-ধারা যেন তার-ই অনুসারী। ওই স্বল্প বয়সের মধ্যে তিনি কী করে নিপুণ ছন্দ ব্যবহার শিখলেন, তৈরি করলেন নিজস্ব বাগ্-ধারা, প্রায় প্রত্যেক সমসাময়িক ঘটনাকে কবিতায় আনলেন, ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যে এত কিছু! এ বয়স তো প্রস্তুতি নিতেই অতিক্রান্ত হওয়ার কথা, বদলে সম্-এ এসে পৌঁছাতে হল তাঁকে! তবু সুকান্ত অক্ষয় এক প্রতিভার নাম, বালক বীরের বেশে বিশ্ব না হোক, জয় করেছিলেন বাঙালির হৃদয়, যাঁর কবিতা, কবিতায় সুর প্রয়োগ করে গান লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে আজ-ও আবেদনসঞ্চারী। কেন? বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।
সময়, দেশ, বিশ্ব এবং সুকান্ত
দশকের হিশেবে যদি ধরি, তাহলে সুকান্ত চারের দশকের কবি, অর্থাৎ যে যুগে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, মণীন্দ্র রায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন প্রমুখ বাংলা কবিতার যুগপুরুষরূপে চিহ্নিত। কিন্তু তিনি কোনও দশকে সীমায়িত থাকেননি। তাঁর খ্যাতি একেবারে গোড়া থেকেই সময়ের গণ্ডি-অতিক্রমী।
আদি দেশ পুব-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কোটালিপাড়া, কয়েক শত বছর ধরেই যেখানকার সারস্বত চর্চা কেবল বাংলা নয়, ভারত-ব্যাপ্ত। নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া ইত্যাদির মতো কোটালিপাড়াও বঙ্গের মেধাবিকাশের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার ভূমিপুত্র শতবর্ষজীবী মধুসূদন সরস্বতী ষোড়শ শতাব্দীতে সারা উপমহাদেশের এক বরেণ্য নাম, যাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁকে এমনকি সম্রাট আকবরের সমীপবর্তী পর্যন্ত করেছিল।
সেই পুণ্যভূমির প্রবহমানতা রক্তে নিয়ে তাঁর জন্ম ১৯২৬-এর ১৫ই আগস্ট (বাংলা সন ১৩৩৩-এর ৩০-এ শ্রাবণ), দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে, এক সারস্বত পারিবারিক পরিমণ্ডলে। তাঁর মায়ের নাম সুনীতি দেবী, বাবা নিবারণচন্দ্র। জেঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত, আর বাবা পুস্তক প্রকাশক, গান-জানা লোক। যৌথ পরিবারটিতে সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে শৈশব-কৈশোর কাটে সুকান্তের। তাঁর নামকরণেরও ইতিহাস আছে। সেকালের এক বিখ্যাত উপন্যাস মণীন্দ্রলাল বসুর ‘রমলা’। সেই উপন্যাসের নায়কের নামে সুকান্তের নামকরণ করেন তাঁর বাড়িতে জেঠতুতো দিদি, রাণীদি।
শৈশব-কৈশোরে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতায় থাকতে হয়েছে তাঁকে। কালীঘাট থেকে বাগবাজারে আসেন জেঠামশাইয়ের বাড়িতে, পরে বেলেঘাটায়। ভর্তি হলেন সেখানকার কমলা বিদ্যামন্দির-এ। পরে দেশবন্ধু হাইস্কুলে। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক দেন, কিন্তু পাশ করতে পারেননি।
সাহিত্যে হাতেখড়ি কিন্তু এর মধ্যে হয়ে গেছে। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তেই স্কুল থেকে বের করে ফেললেন হাতে লেখা পত্রিকা ‘সঞ্চয়’, আর পরবর্তীতে, যখন তিনি সেভেনের ছাত্র, বন্ধুত্ব হয়েছে দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে পড়তে আসা অরুণাচল বসুর সঙ্গে, যা পরে ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হবে, দুই বন্ধু মিলে ক্লাস সেভেনে থাকতেই বের করলেন ‘সপ্তমিতা’। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র হাসির গল্প লিখেছেন যেমন, স্কুলে দল বেঁধে ‘ধ্রুব’ নাটক করেছেন। কালীঘাটের বন্ধুদের নিয়ে নিজের লেখা নাটক ‘বিজয় সিংহের লঙ্কাজয়’ লিখেছেন, পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। এসব তাঁর গড়ে ওঠার পাথেয়। ম্যাট্রিক দিতে না দিতেই, যেন তাঁর কবিতার মতোই স্বপ্নপূরণ হল তাঁর, ‘আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে’! কবিতা লেখা ও প্রকাশিত হওয়া তো শুরু হয়ে গিয়েছেই, যোগ দিয়ে ফেললেন ছাত্র ফেডারেশনে। শুরু হল তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম।
এই সময় থেকেই দেশ ও বিশ্বের ঘটনাসমূহে আবর্তিত হতে লাগল তাঁর জীবন ও সাহিত্য। তাই তাঁর কবিতায় দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, রাজনৈতিক ডামাডোল যেমন বিষয়বস্তু হিশেবে এসেছে, তেমনি এসেছে বিশ্বযুদ্ধের অরুন্তুদ ভয়াবহতার কথা, নতুন পৃথিবীর প্রতি আশাবাদিতা, প্রার্থনা করেছেন, ‘শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক/ সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে’ (১লা মে-র কবিতা ‘৪৬)। তিনি রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-জিন্নাহকে নিয়ে কবিতা লেখেন, আবার লেনিনকে নিয়ে, লেখেন যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে, ‘মার্শাল তিতোর প্রতি’। চট্টগ্রাম নিয়ে কবিতা আছে তাঁর, আছে ‘ইয়োরোপের প্রতি’। এই আন্তর্জাতিক বোধ সুকান্তকে অনন্যতা দিয়েছে।
সুকান্ত: তাঁর সমগ্রতা ও সম্ভাবনা
‘–ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে’, সুকান্ত লিখেছেন নিজের সম্পর্কে। বলেছেন, ‘আমি এক অঙ্কুরিত বীজ’। এই বীজ মহীরুহে পরিণত হতে পারল না, বাংলা সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এটা। কিন্তু তাঁর একুশ বছরের জীবনে তিনি আভাস দিয়ে গেছেন, তাঁর সম্ভাবনা কতদূর প্রসারিত হতে পারত। সুকান্ত মানে একজন কবিমাত্র নন, তার চেয়েও আরও অধিক কিছু। রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁকেই আমরা নৃত্যনাট্যকাররূপে পাই। ‘অভিযান’, আর ‘সূর্য-প্রণাম’ নামে দুটি নৃত্যনাট্য তার উদাহরণ। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি একাধিক কবিতাও লিখেছেন। আর তাঁর হাতের লেখাকেও অতি যত্নে করে তুলেছিলেন রাবীন্দ্রিক।
সুকান্ত কিছু গল্প-ও লিখে গেছেন। বন্ধু অরুণাচল বসুর সঙ্গে মিলে একটি উপন্যাস রচনাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু বন্ধুর অসহযোগিতায় তা শেষ করা হয়নি। তার পাণ্ডুলিপিও কালের গর্ভে। আর লিখেছেন কিছু শিশুতোষ কবিতা। সেক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা ধরা পড়ে, যখন তিনি লেখেন, ‘বড়োলোকের ঢাক তৈরি গরীবলোকের চামড়ায়’। ‘মিঠেকঠা’-তে বিধৃত তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতাগুলো বস্তুত অন্য এক সুকান্তকে চিনিয়ে দেয়, যিনি হাস্যরসের কারবারি।
সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ-ও রয়েছে তাঁর। আর আছে গান। এগুলি লেখা হয় তাঁর গায়ক মামা বিমল ভট্টাচার্যের উৎসাহে। ১৯৪২, অর্থাৎ ষোলোবছরের কিশোর গান লিখছেন, খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়? আরও কৌতূহলকর খবর, পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে ‘আকাল’ নামে একটি কবিতা-সঙ্কলনের সম্পাদনা করে সময়ের দাবিকে মর্যাদা দিয়ে গেছেন তিনি।
আর আছে তাঁর পত্রসাহিত্য। এত নিবিড় বোধ আর অন্তরঙ্গতা, ভাষার কারুকাজ ও সেইসঙ্গে রসবোধ, রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে স্পর্ধিতভাবেই তা দাঁড়াতে পারে। সাহিত্যগুণে চিঠিগুলি যেমন, তেমনই কবিকে অন্তরঙ্গভাবে চেনার জন্যও চিঠিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এইসব, এবং আরও কিছু। পার্টির কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখা, ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার ছোটদের পাতা সম্পাদনা করা, ‘কিশোর বাহিনী’ নামে সংগঠনের কাজ করা, আর অবিরাম পাঠ, পাঠ আর পাঠ। এর মধ্যে কখনও রাঁচি, আবার কখনও বা বেনারস, কাশ্মীর ঘুরে আসা। একুশ বছরের জীবনে আর কী-ই বা আঁটে! এই নিয়ে সমগ্র সুকান্ত, বা সুকান্ত সমগ্র। বাংলার আরও বেশ কয়েকজন তাঁর মতো ক্ষণজীবী ছিলেন, যেমন তরু দত্ত, ডিরোজিও (তাঁকে বাঙালি-ই বলব, মনেপ্রাণে বাঙালি), সোমেন চন্দ, হুমায়ুন কবীর (‘কুসুমিত ইস্পাত’!) কিন্তু ডিরোজিও ছাড়া এত বর্ণময় ছিলেন না বাকিরা।
সুকান্ত-সুভাষিত
বেশ কিছু অমর পঙক্তি আমরা সুকান্তের কবিতায় পাই, যা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত। এরকম-ই কয়েকটি উদ্ধৃতি, যা থেকে যাবে আবহমান কাল ধরে।
১. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,/ পূর্ণিমা রাত যেন ঝলসানো রুটি।
২. রাত্রির ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
৩. সকালের একটুকরে রোদ্দুর–/ একটুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।
৪. আমার হদিস জীবনের পথে মন্বন্তর থেকে/ ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূরে গিয়ে মুক্তির পথে বেঁকে।
৫. বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।
৬. তুমি তো প্রহর গোনো, তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি।
৭. বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
৮. কলম তুমি চেষ্টা করো, দাঁড়াতে পারো কিনা।
৯. –আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,/ নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/ অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,/ আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।
১০. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/ স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।
উদাহরণ আরও আছে। আপাতত এটুকুই।
সুকান্ত: একুশেও অনন্ত অর্জন
সুকান্তর সীমিত আয়ুতেও তাঁর কবিতাকে সুর দিয়ে তাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ভারতের এক যুগন্ধর সঙ্গীতপ্রতিভা সলিল চৌধুরী। আর সে গানকে অমর করে গিয়েছেন সুকণ্ঠী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এমন কোনও বাঙালি নেই, সলিল-সুরারোপিত এবং হেমন্ত-পরিবেশিত ‘রানার চলেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে’, আর ‘ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু’ শোনেননি। সুকান্তের আরও একটি কবিতার সুর দেন সলিল, যা হেমন্ত ও দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় আলাদাভাবে পরিবেশিত,– ‘অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি’। ঋত্বিক, বাঁধনছেঁড়া দামাল এক প্রতিভা, সুকান্তের এই অমোঘ ও হৃদয়দ্রাবী আর্তিটি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর ‘কোমলগান্ধার’ ছায়াচিত্রে, দেবব্রতর গলায়।
আরও একটি গান, সুকান্তের কবিতা থেকে সুরাবদ্ধ, গেয়েছেন অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়,– ‘একটি মোরগের কাহিনী’। ‘রানার’ অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য একক নৃত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এটিকে। বোধ করি বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তার দুই প্রতিস্পর্ধী নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ আর সুকান্তর ‘রানার’। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু বিখ্যাত শিল্পী আবৃত্তি করেছেন কবিতাটি, হাসান ফিরদৌস, উৎপল কুণ্ডু, কাজী আরিফ, শিমুল মুস্তাফা, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, বেলায়েত হোসেন, মৌমিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।
সুকান্তকে নিয়ে কবিতা লেখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘বসন্তে কোকিল কেঁদে কেঁদে রক্ত তুলবে, সে কীসের বসন্ত?’ কেবল তাই নয়, মানিক তাঁর সুকান্তপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন নিজের ছেলের নাম সুকান্ত রেখে। ছন্দের প্রশ্নে একবার সুকান্ত-সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিমত হলে বুদ্ধদেব বসু সুকান্তের সপক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। সুকান্তকে নিয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে প্রতিবছর, প্রবন্ধের তো সীমাসংখ্যা নেই, গবেষণাও হচ্ছে। তৈরি হয়েছে সুকান্ত চর্চাকেন্দ্র। ফরিদপুরের কোটালিপাড়াতে তাঁর পৈতৃক ভিটে অধিগ্রহণ করে সেখানে তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। জীবিতকালেই তাঁর কবিতা ইংরেজি, রুশ ও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। হয়েছে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়। তাঁর কবিতা স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকায়। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের সঙ্গে সুকান্তের জন্মদিনটিকে বহু জায়গায় যে এক-ই সঙ্গে পালিত হয়, তাতেই প্রমাণিত, তিনি জনমানসে কতখানি সমীহা আদায় করতে পেরেছেন।