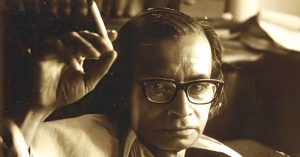বর্ষার ধূমল-গম্ভীর আকাশ, বসন্তের মাধুরী এমনকি গ্রীষ্মের আগ্রাসী খরতাপ নিয়ে বাংলা কবিতা-গানের ভুবন যতটা আলোকিত ও মুখর, তার এক-দশমাংশও নয় হেমন্তকাল নিয়ে। তারপরও শিল্প-সাহিত্যে-চিত্রকলায় নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে হেমন্তকাল। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা দুহাত উজাড় করে এঁকেছেন হেমন্তের অপরূপ রূপময়তা, তবে কারও কারও ছবিতে পড়েছে বিষণ্নতার ছোপ ও ছায়া। ভ্যান গঘের ছবি থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে সর্বকালীন বিষাদের অপার্থিব সুর। বাঙালি কবিরা অধিকাংশই হেমন্তকে দেখেছেন ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিন হিসেবে, অবশ্য কারও কারও কবিতায় হেমন্তকাল মানে জরা-মৃত্যুর গন্ধ ছড়ানো বিষণ্ন দিনরাত্রি। তবে হেমন্তে ফসলের প্রাচুর্য ও পাকাধানের গুচ্ছের উজ্জ্বল সোনালি বিভা আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের গানে-কবিতায় হেমন্তকাল সেইভাবে ঠাঁই পায়নি। কেতকী কুশারী ডাইসনের ‘রবীন্দ্রনাথের বর্ণভাবনা’ থেকে জানা যায়, তিনি নাকি হেমন্তের লাল-গেরুয়া রংটি দেখতে পেতেন না। এ কারণে তাঁর সৃজনবিশ্বে বর্ষা, বসন্ত, শরৎ এমনকি গ্রীষ্ম ঘুরেফিরে এলেও হেমন্তের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েছেন নিদারুণভাবে। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্ত বারবার ফিরে এসেছে বিচিত্র রূপে বিচিত্র বর্ণে। বাংলার গাছপালা, লতাগুল্ম, মেঠোচাঁদ, নদী-নিসর্গের অপরূপে মুগ্ধ কবির কাছে হেমন্ত মানে অঘ্রাণ— তাঁর কাছে কার্তিকের চেয়ে অগ্রহায়ণ ঢেরবেশি উজ্জ্বলতর। তিনি লিখেছেন: ‘অশ্বত্থ পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে/ শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া,— অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;/ সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে/ হেমন্ত এসেছে তবু;’ (অঘ্রান প্রান্তর, বনলতা সেন)।
অগ্রহায়ণ মানেই ‘আমন’ ধান কাটার মাস। ‘বাংলার শস্যহীন প্রান্তরে’ যখন ‘গভীর অঘ্রান’ এসে দাঁড়ায়, তখন উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ে বাংলার আকাশ-অন্তরীক্ষে। অগ্রহায়ণ বয়ে আনে ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিন, বয়ে আনে সমৃদ্ধি। ফসলের সম্ভার কিষাণ-কিষাণীর প্রাণমন ভরিয়ে দেয় অলৌকিক আনন্দে। বর্ষায় রোয়া ‘আমন’ ধান অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়। ধান কাটার পরপরই গ্রামের ঘরে আয়োজন করা হয় ‘নবান্ন উৎসব’। আমাদের দেশে হেমন্তকাল নবান্নের কাল হিসেবে বিবেচিত হয়।
কলকাতা থেকে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের ‘বাংলার কৃষক’ (১৮৭৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমন ধান ভরা বর্ষায় রোপণ হয় নিচু জমিতে। ধানকাটা হয় বাংলা সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে। অগ্রহায়ণের নবান্ন উৎসবকে ‘আমন পার্বণ’ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমন কাটা শেষে আনন্দ-উল্লাসের সাথে বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান হলো ডিসেম্বরের শীতের মতো উষ্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভোজন এবং বিভিন্ন উপায়ে তৈরি উষ্ণ ও সুস্বাদু পিঠা বিতরণ।’
নবান্ন মূলত ভূমি-নির্ভর বাংলার একটি লোকায়ত উৎসব, ধর্মের সঙ্গে এর কোনও বিরোধও নেই, সম্পর্কও নেই। এর সবটাই বাঙালির চিরায়ত জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ উপলক্ষে ঘরে ঘরে উপাদেয় খানাপিনার আয়োজন করা হয়। লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর ‘পল্লী বৈচিত্র্য’ (১৯০৫) গ্রন্থে লিখেছেন, ‘বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতেই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসের একটি আনন্দপূর্ণ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উৎসব। পল্লীবাসীগণের মধ্যে হিন্দু মাত্রেই পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উদ্দেশ্যে নূতন চাউল উৎসর্গ না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন না।’
লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল শিক্ষক গৌরী সাহার কণ্ঠে। তিনি জানালেন, বরিশালে আমন ধানের চিকন চাল হয় প্রচুর পরিমাণে। আগের রাতে জলে ভিজিয়ে রাখা চিকন-আতপ চাল পরদিন ভোরে স্নান সেরে গৃহবধূরা পাটানোড়া দিয়ে বেটে গুঁড়ো প্রস্তুত করে। সেই গুঁড়োর সঙ্গে নতুন গুড়, আদা, মশলা, দুধ মিশিয়ে নবান্ন বানানো হয়। ন’রকমের ফলও এতে মেশাতে হয়। নতুন চালের পায়েস ছাড়াও থাকে চিঁড়া ও মুড়ি-মুড়কি। এসব খাবার সর্বপ্রথমে গৃহদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয় এবং পরে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
এক সময় নবান্ন উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে যাত্রাপালা, জারি গান, কীর্তন গান, বাউল গানের আয়োজন করা হত। ধানকাটা শেষ হলে মেহেরপুরের চরগোয়ালগ্রাম, দীঘিরপাড়া, আমঝুপিতে লাঠিখেলা হত। গ্রামের পথে পথে মানিকপীরের নামে গান গেয়ে বেড়াত গ্রামের গায়েন-বয়াতিরা। এক সময় মেহেরপুরের পিরোজপুর, সাহারবাটী, দারিয়াপুর, আমদহ, চুয়াডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া, আসমানখালি গ্রামে আমন কাটার পরপরই যাত্রাগানের আসর বসত। মেহেরপুর শহরে হত ঢপ গান ও কবিগানের আসর। সাহারবাটী, পিরোজপুর, আসমানখালি, হাটবোয়ালিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত এসব আসরের স্থিতিকাল ছিল পাঁচ থেকে সাত রাত পর্যন্ত। মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলায় যাত্রার আসর আর তেমন হয় না। তবে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলার অজপাড়াগাঁয়ের বাউল আখড়াগুলিতে বাউলগানের আসর বসে। সারারাত জেগে আসরের গান উপভোগ করেন গ্রামের মানুষ।

সরেজমিনে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, দিগন্তজোড়া মাঠ ভরে উঠেছে এখন পাকা ধানের সুঘ্রাণে। ইতিমধ্যেই কারও কারও ধান গোলায় উঠে গেছে। কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় জানতে চান, ‘এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে, তাই না?’ জানাই, ‘হ্যাঁ, খুব ভাল ফলন হয়েছে।’ —‘নবান্ন হয়?’ তাঁকে জানাই, ‘দেশভাগের পর হিন্দুরা ওপারে চলে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে আর নবান্ন হয় না, তবে প্রতিদিনই গ্রামে গ্রামে চলছে নবান্ন উৎসব। অধিকাংশ বাড়িতে চলছে ক্ষীর-পিঠা-পুলি আর হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে পায়েসের ধুম। প্রতি বাড়িতে প্রতিদিনই চলছে নবান্নের প্রচুর আয়োজন। যেসব বাড়িতে নবান্নের আয়োজন হয়নি, তারাও হয়তো অন্য বাড়ি থেকে আসা নবান্নের উপাদেয় খাবার সপরিবারে উপভোগ করছে।’
দীনেন্দ্রকুমার রায় ‘নবান্ন’ সম্পর্কে ‘পল্লী বৈচিত্র্য’ গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, ‘নবান্নের দিন অপরাহ্নে পল্লীপ্রান্ত এক সময় হর্ষকলরবে মুখরিত হত। নদী তীরবর্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠী গাছের ছায়ায় গ্রামের রাখাল-কৃষাণ-মজুরেরা সমবেত হয়ে বিশ্রাম নিত। আজ তাহাদের বর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের দিন, আজ তাহারা কেউ কাজে যাইবে না।’ ‘পল্লী রমনীগণ নদী জলে গা ধুইয়ে কলসি ভরিয়া জল লইয়া গৃহে ফিরতো।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘ছেলেরা সমস্ত দুপুর বাড়ির বারান্দায়, চিলেকোঠার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়াল ঘরের অন্তরালে’ লুকোচুরি খেলত। প্রত্যেক বাড়িতেই আয়োজন করা হত ডাল, ভাল মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস প্রভৃতি সুস্বাদু আহার। শিব মন্দিরের বারান্দায় বসে নেশাখোর বাউলের দল ডুগডুগি বাজিয়ে গাইত,
বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চলে।”
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৬৯-১৯৪৩) সময়ের সেই রঙিন দিনগুলি আর নেই। যুগের হাওয়ার পরশে সবকিছুই বদলে গেছে। বদলে গেছে বাংলাদেশ, বদলে গেছে দুই বাংলার গ্রামগুলি। গ্রামকে ফালি ফালি করে ফসলের মাঠ চিরে নির্মিত হয়েছে পিচঢালা পাকা রাস্তা, নেই রাস্তার দু’কিনার বেয়ে গ্রামে ঢুকেছে বিজলি বাতি আর কেবল চ্যানেলের তার। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কি গ্রামের শ্যামলিমা, ফসলের মাঠ, লোকায়ত জীবন ও কৃত্যাচারগুলি গিলে ফেলবে! যন্ত্রদানবের উদ্ধত পদাঘাতে পৃথিবীর বনে আর কী অস্ত্রাণ আসবে না? কিংবা পৌষের নরম রোদের ঘ্রাণে চারদিকটা কি আর ভরে উঠবে না! নবান্ন কি দূর অতীতের ইতিহাস হয়ে যাবে? না, তা বোধহয় হবে না। অগ্রহায়ণ-পৌষে তাই তো বাজার ভরে গেছে শিম, শাক, আলু, ‘সাকারকুণ্ড’ আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংসহ নানারকম শাক-সবজিতে। এসব দিয়েই বাংলার গ্রামে গ্রামে চলছে নবান্নের আয়োজন।