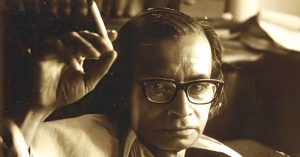“বহু দিন ধ’রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭ই পৌষ ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন
বছর দশেক বয়সে সত্যজিৎ রায় প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের দর্শন পেয়েছিলেন। তার বহু আগেই সত্যজিতের বাবা সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়েছে। সত্যজিতের বাবা সুকুমার রায় বা ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির সঙ্গে লেখালেখির কারণে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। সত্যজিৎকে প্রথম শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা সুপ্রভাদেবী। বালক সত্যজিতের সেসময় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করার নেশা পেয়ে বসেছিল। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় সত্যজিৎকে মা সুপ্রভাদেবী যখন প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য উত্তরায়ণে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সত্যজিতের ভীষণ শখ ছিল, তাঁর নিজস্ব অটোগ্রাফ সংগ্রহের খাতায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ছোট্ট একটি কবিতা লিখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ায়। রায় পরিবারের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। এমনকি উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ছোটদের জন্য দু-একটি ছড়া-কবিতাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যজিতের যখন আড়াই বছর বয়স, সেসময় সত্যজিতের বাবা সুকুমার রায় মারা যান। সত্যজিতের জন্ম হয়েছিল উত্তর কলকাতার একশো নম্বর গড়পার রোডে। সে বাড়ি থেকেই ‘সন্দেশ’ পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ছাপানো হত। সুকুমার রায় তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে ‘সন্দেশ’ পত্রিকা প্রকাশনার দারিত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু সুকুমারের অকালমৃত্যুর পরে তখনকার মত সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।
যাইহোক, দশ বছর বয়সে দেখা রবীন্দ্রনাথ সত্যজিতের সারা জীবন জুড়েই নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে সত্যজিৎ রায়ের অর্জন করা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের নানা কাজে ঘুরেফিরে এসেছে। সেই ছোটবেলার প্রথম দিনে উত্তরায়ণে সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর বেগুনি রঙের অটোগ্রাফ সংগ্রহের খাতাটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতার আবদার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎকে কিছু লিখে দেননি। খাতাটি রবীন্দ্রনাথ নিজের কাছে রেখে দিয়ে সত্যজিৎকে বলেছিলেন, পরের দিন এসে তাঁর কাছ থেকে খাতাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে।
রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত পরের দিন মায়ের সঙ্গেই ফের রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন বালক সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখামাত্রই তাঁর লেখার টেবিলের উপরে রাখা খাতাপত্র চিঠি বইয়ের স্তূপের ভিড়ে খুঁজে বের করেন সেই বেগুনি রঙের সত্যজিতের অটোগ্রাফ সংগ্রহের খাতাটি। সেই খাতার একটি পাতায় লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এই কবিতাটি— “বহু দিন ধরে… বহু ক্রোশ দূরে…।” আট লাইনের এই কবিতাটি এখন প্রায় সকলেরই জানা। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আরও এক বিখ্যাত প্রতিভাধর বাঙালি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেদিন থেকেই। পরে অবশ্য সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ছাত্র হয়েছিলেন। একদিকে পূর্বসূরিদের থেকে অর্জন করা শিল্পপ্রতিভা সত্যজিতের রক্ততেই ছিল। শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ‘শিক্ষা’ শেষ না করে কলকাতায় ফিরে এলেও পরের জীবনে নিজেকে বিজ্ঞাপনের দপ্তরের ‘শিল্পী’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যজিৎকে বেগ পেতে হয়নি। কলকাতার সেসময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডে জি কিমারের অফিস থেকে সত্যজিৎকে যখন লন্ডনে চাকরি সূত্রে বদলি করে দেওয়া হয়, তখন লন্ডন যাওয়ার সময় জাহাজে বসেই সত্যজিৎ তৈরি করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস থেকে ‘পথের পাঁচালী’ ছবির চিত্রনাট্য। শুধু তাই নয়, চিত্রনাট্যের সঙ্গে ‘সিনেমাটোগ্রাফি’ কেমন হবে, তার একটা খসড়ার ছবিও এঁকে রেখেছিলেন।
যাইহোক, ছবি আঁকা শেখার জন্য সত্যজিৎ তো খুব বেশিদিন শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসাবে ছিলেন না। তবে যে ক’বছর ছিলেন, জীবনের বিভিন্ন সময়ে সত্যজিৎ নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন, তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে থাকার ‘মূল্য’ অনেক বেশি। ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হয়েছিলেন। পাঁচ বছরের সেই কোর্স ছিল। সেই ছবি আঁকার কোর্স শেষ করলে একটা ডিপ্লোমা পাওয়া যেত। এমনকি, শিল্পকলার প্রশিক্ষক হতে গেলেও ওই ডিপ্লোমার দাম ছিল অনেকটাই। কিন্তু সত্যজিৎ সেই গতানুগতিক পথে চলতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পরে সত্যজিৎ কলা ভবন ছেড়েছিলেন। তখন তাঁর কোর্সের মেয়াদ আরও দেড় বছরের বেশি বাকি।
তবে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থেকে শান্তিনিকেতনের প্রভাব সত্যজিতের জীবনের নানা কাজে জুড়ে ছিল, তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার অনেক পরে সত্যজিৎ রায় যখন নিজে লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার, তখনও তাঁর লেখা গোয়েন্দা ফেলুদার গল্প ‘রবার্টসনের রুবি’ বা ‘কৈলাশে কেলেঙ্কারী’-তে শান্তিনিকেতনের কথা এসেছে ঘুরেফিরে। শান্তিনিকেতনে ছাত্র থাকার সময় সত্যজিৎ অজন্তা ইলোরা গুহার শিল্প পর্যবেক্ষণ করতে ছাত্র হিসাবে গিয়েছিলেন। যার ভিত্তিতে ওই ফেলুদার গল্প ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারী’। আর সিনেমাতে, যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, নিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে। রবীন্দ্রনাথের গল্প- উপন্যাস ‘পোষ্টমাষ্টার’ থেকে ‘চারুলতা’ বা ‘ঘরে বাইরে’ থেকে আরও অনেক ছবি তৈরি করে গিয়েছেন নিরলসভাবে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শান্তিনিকেতন— এমনভাবে সত্যজিতের জীবনে জড়িয়ে ছিল যে এই উদাহরণ দিতেই হচ্ছে।
শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে জাপানি জুদো শেখানোর ব্যবস্থা চালু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যজিৎ তখন সেখানকার ছাত্র। জুদো এক্সপার্ট তাকাগাকি-কে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে চালু করেছিলেন জুদো শিক্ষা। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এই শিক্ষাটি খুব বেশিদিন না চললেও সত্যজিৎকে বিষয়টি এতটাই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল যে কলকাতা ফিরে ১৯৩৪ সালে বালিগঞ্জে এক আত্মীয়র বাড়িতে জুদোর প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেছিলেন।
আসলে সত্যজিৎ রায় নিজেই নানা জায়গায় পরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর জীবনে পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং সিনেমা এতটাই জায়গা দখল করে নিয়েছিল, যা তাঁকে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে শান্তিতে ছবি আঁকা শেখার কাজটি শেষ করতে দেয়নি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং সিনেমার টানেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর একবছরের মধ্যে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতন ছাড়েন। ততদিনে অবশ্য যা শেখার, ততটা আঁকার পদ্ধতি রপ্ত করে নিয়েছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত সত্যজিৎ রায় একমাত্র লেখক, যিনি তাঁর গল্পের ‘ইলাসট্রেশন’-এর কাজ নিজে করতেন। দু-একটি গল্প-উপন্যাস ছাড়া। এছাড়া অন্য লেখকের বইয়ের প্রচ্ছদ, ইলাসট্রেশন করেছেন অসংখ্য। এইসব ছবি আঁকার কাজ কখনও সূর্যের আলো ছাড়া সত্যজিৎ করতেন না। বিশেষ করে ইলাসট্রেশনের জন্য রঙিন ছবি আঁকার কাজ তো বটেই। যা তিনি শিখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমলে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে। সত্যজিতের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর একবছর বাদে, যেসময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছাড়লেন, সেসময় তাঁর মাথায় ভর করে রয়েছে ফিল্মের নেশা। পৃথিবীর কোথায় কী ধরনের ছবি তৈরি হচ্ছে, সেসময়ের শান্তিনিকেতনে বসে সত্যজিৎয়ের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছিল না। সেসময় কলকাতায় নানা সিনেমা হলে পাশ্চাত্যের নামী পরিচালকদের সিনেমা দেখানো হত। এই পাশ্চাত্য সিনেমার টানেই কলা ভবনের ‘মাস্টারমশাই’ নন্দলাল বসুকে গিয়ে শান্তিনিকেতনের ঘরানায় ছবি না এঁকে কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট হওয়ার চেষ্টার কথা জানিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন সত্যজিৎ। কিন্তু আমৃত্যু তিনি ভুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি এবং শিক্ষাকে। যা তাঁর সারা জীবনের নানা কাজে বারবার ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর সেরা পুরস্কার হিসাবে ভারতে সাহিত্যে প্রথম ‘নোবেল’ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সিনেমায় পৃথিবীর সেরা পুরস্কার ‘অস্কার’ প্রথম যে ভারতীয় জীবিত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়। ছাত্র এবং গুরু— দুজনেই প্রথম ভারতীয়, যারা দুটো ক্ষেত্রে দেশকে এনে দিয়েছেন বিশ্বের সেরা সন্মান।