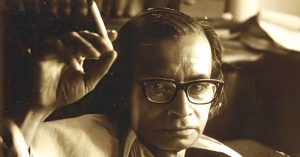আজ থেকে ২৫৬৬ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের জনক মহামানব গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের জন্মের আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থান ছিল চার দেয়ালে বন্দি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের জীবন ছিল স্বামী কিংবা পুত্রদের অধীন। নানা সামাজিক কুসংস্কার, বৈষম্য ও অবহেলায় নারীরা ছিলেন জরাগ্রস্ত। ঠিক তখনই শাক্যরাজা শুদ্ধোধন ও মায়া দেবীর ঘরে বুদ্ধের আগমন। তাঁর জন্মের পর জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, তিনি গৃহত্যাগ করবেন এবং বুদ্ধ হবেন। পরে রাজা শুদ্ধোধন পুত্রকে সংসারী বানানোর জন্য খুব অল্প বয়সে বিয়ে দেন যশোধরার সঙ্গে এবং তাঁদের ঘরে পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। এত কিছুর পরও তিনি সংসারের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেননি, জগতের সব প্রাণীর দুঃখমুক্তির জন্য ৬ বছর কঠোর ধ্যান-সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর অর্জিত জ্ঞান শিষ্য-প্রশিষ্যরা দেশ ও বিদেশে প্রচার করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বছর মানবের কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচার করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বলেছিলেন, বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে মাতার মত, তরুণীকে ভগ্নির মত আর বালিকাকে নিজ সন্তানের মত জ্ঞান দান করবে। কেননা নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষ অচল। নারীরা এ বিশ্বে যত মহামানব, মুনি-ঋষি আছেন, সবার ধাত্রী।
যশোধরা
যশোধরা শুদ্ধোদনের ভগিনী অমিতার কন্যা ছিলেন। যশোধরা ও সিদ্ধার্থ গৌতম একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষোল বছর বয়সে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ গৌতমের বিবাহ সম্পন্ন হয়। উনত্রিশ বছর বয়সে যেদিন তাঁদের রাহুল নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, সেইদিন সিদ্ধার্থ গৌতম পরমসত্যের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। এহেন উদার বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু তাঁর স্ত্রী বহুদিন অভিমান করেছিলেন পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করে প্রবজ্যা গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন বলে।
পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের কঠিন কঠোর সন্ন্যাসজীবনের বিস্তারিত জানতে পেয়ে যশোধরাও স্বামীর ন্যায় রাজবস্ত্র ও অলঙ্কার ত্যাগ করে সাধারণ হলুদ কাপড় পরতে ও সারাদিনে একবেলা আহার করতে শুরু করেন। কথিত আছে, সে সময় অনেক রাজকুমার তাঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে এলেও তিনি তাঁদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।
বুদ্ধত্ব লাভের পর শুদ্ধোধনের অনুরোধে গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু যান। দ্বিতীয় দিনে অন্যান্য ভিক্ষুদের সঙ্গে বুদ্ধ শহরে ভিক্ষা করতে বেরোলে যশোধরা সেই সংবাদের সত্যতা বিচারের উদ্দেশ্যে প্রাসাদের জানালা দিয়ে তাঁকে দেখতে পান। বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের গরিমায় মুগ্ধ যশোধরা প্রশংসাসূচক আটটি শ্লোক রচনা করেন, যা নরসীহগাথা নামে পরিচিত। কিন্তু সেই দিন প্রাসাদের সকল নারী বুদ্ধের দর্শনের জন্য গেলেও যশোধরা তাঁর নিকটে যেতে অস্বীকৃত হন। এমনি আত্মদৃঢ় চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন তিনি, বরং বুদ্ধদেবকে সংবাদ পাঠান যে, যশোধরার মধ্যে কোনও গুণ অবশিষ্ট থাকলে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যেন তার নিকটে আসেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন ও তাঁর নিকট যান এবং তাঁর ধৈর্য ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। কপিলাবস্তু শহরে বুদ্ধের সপ্তম দিন, যশোধরা তাঁর পুত্র রাহুলকে পিতা গৌতম বুদ্ধের নিকট পাঠান এবং পিতার নিকট উত্তরাধিকার চেয়ে নিতে বলেন। রাহুল ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের অনুরোধে সারিপুত্ত তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করেন।
পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধ নারীদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিলে যশোধরা ভিক্ষুণী হিসেবে সংঘে যোগদান করেন ও পরে অর্হৎ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ এমন কেউ যিনি মানব অস্তিত্বের সত্যিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছেন।
মায়াদেবী
মায়া দেবী বা রানি মায়া ছিলেন বুদ্ধদেবের গর্ভধারিণী। মায়া দেবী কোলীয় গণের একজন সুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল অঞ্জন। তিনি ও তাঁর ভগিনী মহাপ্রজাপতি গৌতমী উভয়েই তাদের খুড়তুতো ভ্রাতা ও শাক্য প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত প্রধান শুদ্ধোধনকে বিবাহ করেন।
বৌদ্ধ প্রবাদ অনুসারে, এক পূর্ণিমা রাত্রে প্রাসাদে ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন যে, চারজন দেবতা তাকে হিমালয়ের কোলে এক পবিত্র সরোবরে স্নান করিয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়ে সুগন্ধী ও ফুল দিয়ে তাঁকে সজ্জিত করে তোলেন। এরপর এক শ্বেতহস্তী শুঁড়ে একটি শ্বেতপদ্ম ধারণ করে তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে ডানদিক থেকে তার গর্ভে প্রবেশ করে। এই স্বপ্নদর্শনের পরে মায়াদেবীর গর্ভাবস্থা উপস্থিত হয় বলে প্রবাদ। শাক্যদের প্রথা অনুসারে, গর্ভাবস্থায় মায়াদেবী শ্বশুরালয় কপিলাবস্তু থেকে পিতৃরাজ্যে যাবার পথে অধুনা নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে এক শালগাছের তলায় সিদ্ধার্থের জন্ম দেন। তার জন্মের সপ্তম দিনে মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়।
জন্মের পরেই মাতৃহারা সন্তান বলেই কি সাধারণ মানুষের শোক, তাপ, দুঃখ তাঁকে রাজকুমার হয়েও থিতু হতে দিল না, মানুষকে পরিত্রাণ মার্গ খুঁজে দেওয়ার এই আন্তরিক আকুলতা কি সেই জন্মমূহূর্তে মাতৃস্নেহ বুভুক্ষার তাড়নাজনিত খুঁজে ফেরার আকুতি, মনস্তত্বের গভীরে হয়তো এর উত্তর প্রোথিত আছে।
মহাপ্রজাপতি গৌতমী
এবার যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে প্রথম নারী, যাকে বৌদ্ধসংঘে ভিক্ষুণী হিসেবে জীবনযাপন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধের বিমাতা ও মাসি ছিলেন।
সিদ্ধার্থের জন্ম দিয়ে মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীই তাঁকে লালনপালন করেন।
সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করার কয়েক বছর পরে তাঁর পিতা শুদ্ধোধন মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসারধর্ম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং গৌতম বুদ্ধের নিকট বৌদ্ধসংঘে যোগদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তখনও কোনও নারীকে সংঘে যোগ করার ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। হতাশ না হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী মুণ্ডিতমস্তক হয়ে পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে শাক্য ও কোলীয় প্রজাতন্ত্রের বহুসংখ্যক নারীকে একত্র করে বুদ্ধের অনুসরণ করে পদব্রজে বৈশালী যাত্রা করেন। বৈশালীতে পুনরায় তিনি বুদ্ধের নিকট তাঁর আবেদন জানান। এই সময় বুদ্ধের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও সহায়ক আনন্দ মহাপ্রজাপতির হয়ে বুদ্ধকে সংঘে নারীদের ভিক্ষুণী হিসেবে যোগদানের অনুরোধ করেন ও অবশেষে গৌতম বুদ্ধ এই প্রস্তাবে রাজি হন কিন্তু ভিক্ষুণীদের জন্য তিনি আটটি কঠিন নিয়মাবলির প্রচলন করেন।
এই আটটি গুরুধর্ম ছিল—
১. ভিক্ষুণী যত বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রজ্ঞাবতীই হোন না কেন, একদিন-দীক্ষিত ভিক্ষুর সামনেও তাঁকে উঠে দাঁড়াতে হবে ও অভিবাদন জানাতে হবে।
২. অর্ধমাসিকভাবে যে ধর্মীয় উপাচারগুলি পালিত হয়, তার জন্য ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের অনুমতি ও উপস্থিতি প্রার্থনা করবেন। তাঁদের অনুমোদন ব্যতীত উপসোথ আচার পালন করা যাবে না।
৩. ভিক্ষুদের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষুণী একা কোনও স্থানে বর্ষাবাস অতিবাহিত করতে পারবেন না।
৪. বর্ষাকাল কেটে যাওয়ার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের সামনে জানাতে হবে, ওই সময়কালে তিনি কী দেখেছেন, কী শুনেছেন, কী অনুভব করেছেন (পভরন আচার)।
৫. কোনও অপরাধ করলে ভিক্ষুণীকে অর্ধমাস যাবৎ শাস্তিমূলক ‘মানত্তা’ আচার পালন করতে হবে।
৬. দুই বৎসর যাবৎ এই নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করলে, তবে তিনি উপসম্পদা লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারবেন। একে বলা হয়, ‘ছ ধম্ম’।
৭. ভিক্ষুণী কখনওই ভিক্ষুকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না।
৮. ভিক্ষুসংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুণীদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হলেও, বিপরীতটা অনুমোদিত হবে।
গৌতমী এই নিয়মাবলি মেনেই সংঘে যোগদান করেন। তবে ধম্মপদত্থকথা অনুসারে, গৌতমীর উপসম্পদা আনুষ্ঠানিকভাবে না হওয়ায় পরবর্তীকালে ভিক্ষুণীরা তাঁর সঙ্গে উপোসথ (বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান) করতে অরাজি হন, কিন্তু গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং তাঁকে নিয়মনিষ্ঠ উপসম্পদাপ্রদান করেছিলেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের দ্বারা ধর্মশিক্ষা লাভ করেই তিনি অর্হত হন। জীবনের বাকি সময় ভিক্ষুণী হিসেবে কাটানোর পর ১২০ বছর বয়সে মহাপ্রজাপতি গৌতমী মৃত্যুবরণ করেন।
আম্রপালি
আম্রপালি, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে প্রাচীন ভারতের বৈশালী প্রজাতন্ত্রের (বর্তমান বিহারে অবস্থিত) প্রসিদ্ধ নগরবধূ তথা নর্তকী ছিলেন। বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে তিনি আরহান্ত হয়েছিলেন। পুরাতন পালি গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ রীতিনীতিতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।
আরহান্ত অর্থাৎ যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে মানবজীবনের অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লব্ধ হয়েছিলেন।
আম্রপালি খ্রিস্ট-পূর্ব ৬০০-৫০০ অব্দে মহানামের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে, বৈশালীর এক রাজকীয় বাগানে আম গাছের পাদদেশে জন্মগ্রহণের জন্যই তার এমন নামকরণ হয়েছিল। আম্রপালি অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন এবং বিবিধ শিল্পজ্ঞানে প্রতিভাময়ী ছিলেন। বহু তরুণ অভিজাত তাঁর সঙ্গ পেতে আকুল ছিলেন। বৈশালীর রাজা মনুদেব যখন আম্রপালিকে নগরীতে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখলেন, তখনই তিনি তাঁকে ‘নিজের’ অধিকারে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। তিনি আম্রপালির বিয়ের দিন আম্রপালির শৈশব প্রেমিক এবং হবু বর পুষ্পকুমারকে হত্যা করেন এবং একটি সরকারি ঘোষণায় আম্রপালিকে বৈশালীর ‘কনে’ অর্থাৎ, নগরবধূ হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁকে সাত বছরের জন্য রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী ও মেধাবী মেয়েদের জন্য নির্ধারিত বৈশালী জনপদ কল্যায়ণী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। আম্রপালী তাঁর প্রেমিকদের নির্বাচন করতে পারতেন কিন্তু পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে তিনি কোনও একজনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারতেন না।
নগরবধূ ঘোষণার পর আম্রপালি রাজনর্তকী বা রাজ দরবারের নৃত্যশিল্পীও হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা এবং সৌন্দর্য এত মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল যে এই সময়ের মধ্যে বৈশালীর গৌরবের কৃতিত্ব, আম্রপালীর খ্যাতির জন্য ভাবা হয়। আম্রপালির শিল্পপ্রতিভা দেখতে প্রতি রাতে পঞ্চাশটি কর্ষপান মুদ্রা ব্যয় করতে হত। ফলে তাঁর রাজকোষ, কিছু কিছু রাজার কোষাগার থেকেও অনেক সমৃদ্ধ আকার নিয়েছিল।
আম্রপালির সৌন্দর্যের গল্প মগধের শত্রুপক্ষীয় প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা বিম্বিসারের কান অবধি পৌঁছেছিল। তিনি বৈশালী আক্রমণ করেছিলেন এবং আম্রপালির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিম্বিসার খুব ভাল সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আম্রপালী ও বিম্বিসার পরস্পরের প্রেমে পড়ে যান। বিম্বিসারের আসল পরিচয় জানার পর, আম্রপালী অবিলম্বে তাঁকে চলে যেতে বলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। প্রেমে মুগ্ধ বিম্বিসার আম্রপালি যা বলেছিলেন তাই করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা বৈশালীর লোকদের দৃষ্টিতে তাঁকে কাপুরুষে পরিণত করে। যা হোক পরে, আম্রপালী বিমলা কোন্দন্না নামে বিম্বিসারের একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।
পরবর্তীতে রানি কোসালা দেবীর গর্ভে জন্ম নেওয়া বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু তার ভাইদের সঙ্গে বিরোধের সূত্রে বৈশালী আক্রমণ করেছিলেন। তিনিও আম্রপালির সৌন্দর্যে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে আম্রপালিকে যখন বন্দি করা হয়েছিল, তখন তিনি পুরো বৈশালীকেই পুড়িয়ে ফেলেন। এই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞে তাঁর প্রিয়তমা আম্রপালী ছাড়া প্রায় সবাই মারা গিয়েছিল। কিন্তু প্রিয় মাতৃভূমির এ সকরুণ অবস্থা দেখে আম্রপালি অজাতশত্রুর প্রতি স্বীয় ভালবাসা পরিত্যাগ করেছিলেন।
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু আগে বৈশালীতে তাঁর শেষ সফরকালে আম্রপালি তাঁকে খাবার পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। আম্রপালী নিকটবর্তী এক উদ্যানে বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশ শুনে গভীরভাবে আলোড়িত হন এবং তাঁকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধদেব তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময়, আম্রপালির রথ বৈশালীর যুবরাজদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে যারা নিজেরাও বুদ্ধদেবকে তাঁদের সঙ্গে ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা আম্রপালিকে ‘আম-মহিলা’ ও দুর্নামধারী বলে অপমান করতে থাকেন এবং রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে অভিজাতদের যাবার জায়গা করে দিতে বলেন। আর তখনই আম্রপালি বলেন যে, বুদ্ধদেব তাঁর বাড়িতে আসছেন। একথা শুনে হতাশ যুবরাজগণ বুদ্ধকে আপ্যায়নের বিনিময়ে আম্রপালিকে স্বর্ণ প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আম্রপালির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার কারণে বুদ্ধদেবও তাঁদের ফিরিয়ে দেন।
বুদ্ধদেব আম্রপালির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্যই নিজের শিষ্যদের আম্রপালির উপস্থিতিতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে তারা তাঁর প্রতি মোহিত না হয়ে যান। বুদ্ধদেবের আগমন উপলক্ষ্যে আম্রপালী তাঁর বিশাল বাড়িকে বিশেষভাবে সজ্জিত করেছিলেন এবং নিজের সকল অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধদেবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়ার শেষে, তিনি বুদ্ধদেবের নির্দেশে নিজের সমস্ত সম্পদ ও উদ্যানসমূহ বৌদ্ধসংঘে সমর্পণ করে দেন, যা পরবর্তীতে বুদ্ধদেবের একাধিক ধর্মোপদেশ ঘোষণার মূলকেন্দ্র ছিল।
এর পরপরই, আম্রপালি রাজনর্তকী হিসেবে নিজের পদ পরিত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মমত অবলম্বন করে বৌদ্ধ অনুশাসনের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হন। তিনি দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবায় নিজের বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আম্রপালির পুত্রও বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন।
আম্রপালির গল্প সমকালীন বারাঙ্গনাদের প্রতি বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও আম্রপালি একজন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তবুও বৈশালীর যুবরাজগণ তাকে গণিকা ও পতিতা বলেই সম্বোধন করতেন, যা অবমাননাকর অভিব্যক্তি বহন করে। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর প্রতি এই ধরনের নিম্ন মনোভাব পোষণ করেননি। তিনি তাঁর গৃহে অন্নও গ্রহণ করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মোপদেশের জন্য তাঁর বাগানও গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টি প্রায়শই নারীদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতহীন মনোভাবের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়।
বুদ্ধদেব তখন বুদ্ধদেব হননি; তিনি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে চাইছেন। তখন তিনি সত্যজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কঠোর তপস্যায়, অনিদ্রায়, অনাহারে তাঁর শরীর শীর্ণ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। এই সময় একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে ফিরে আসার সময় তিনি শারীরিক দুর্বলতার জন্য মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। এমন অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন এক দেবপুরুষ সেতার বাজাচ্ছেন। তাঁর সেতারের তিনটি তার, প্রথম তারটি খুব শক্ত আর খুব টান করে বাঁধা। তৃতীয় তারটি খুব আলতো করে কোনও মতে দুপ্রান্ত বাঁধা আছে, এতে কোনও রকম টান নেই, ঝুলে পড়ে আছে। আর মাঝের তারটি না খুব টান করে বাঁধা, না খুব আলতো করে সুন্দরভাবে সুর দিয়ে বাঁধা। যে দেবপুরুষ সেই সেতার বাজাচ্ছেন তিনি শুধু মাঝের তারটিতেই মধুর সুর তুলছেন।
সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়ালেন, বুঝলেন এটাই জীবনের সত্য, মনুষ্য জীবন সেতারের তারের মত। কঠোর তপস্যা করেও নয়, আবার চরম ভোগবিলাসে জীবন এলিয়ে দিয়েও নয়, মাঝের পথ বা মধ্যপথ (মঝঝিম পন্থা) হল আসল পথ, সত্য লাভের উপায়। তখনি তিনি স্থির করলেন আর চরম কৃচ্ছ্রসাধন নয়, পরিমিত আহার করে তপস্যা করতে হবে। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে কিছু কাজ হবে না।
সুজাতা
কিংবদন্তি রয়েছে, ওই সময় সেনানী নামক নিকটবর্তী এক গ্রামের এক ধনিক কৃষক পরিবারে সুজাতা নামের এক অপরূপা কুমারী কন্যা বসবাত করতেন। এই নারী তাঁর উপযুক্ত একজন স্বামী এবং সন্তানের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হচ্ছিল না। প্রাজ্ঞ লোকেরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন নিরঞ্জনা নদীর তীরস্থ এক নির্দিষ্ট বটবৃক্ষের তলে গিয়ে বৃক্ষদেবতার নিকট কাঙ্খিত স্বামী ও সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করেন। তিনি তাই করলেন আর খুব শীঘ্রই তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তার কোলে এক সন্তান এল, তখন তিনি ভীষণ খুশি হলেন এবং বৃক্ষদেবতাকে এই দানের প্রতিদান দিয়ে খুশি করতে চাইলেন।
সুজাতার স্বামীর এক বিশাল গোশালা ছিল। তিনি তখন তার পালিত গাভীর পাল থেকে এক হাজার গাভী বেছে নিয়ে সেগুলিকে কয়েকদিন মধু মিশ্রিত খড় খাওয়ালেন। তারপর তাদের দুধ সংগ্রহ করে ওই এক হাজার গাভীর মধ্য থেকে উত্তম ৫০০টি বেছে নিয়ে তাদের গোলাপ ফুলের পাপড়ি, মিছরি পান করালেন। তারপর সেগুলির সংগৃহীত দুধ পান করালেন ওই ৫০০ গাভীর মধ্য থেকে উত্তম ২৫০টিকে। এভাবেই চলল যতক্ষণ না গাভীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮টিতে। তিনি এমন করেছিলেন কেবলমাত্র উত্তম স্বাদের অতি পুষ্টিকর দুধ পাবার জন্যে।
এরপর ওই আট গাভীর সংগৃহীত দুধ দিয়ে সুজাতা বৃক্ষদেবতার জন্যে পায়েস রান্না করতে বসলেন এবং তার কয়েকজন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন ওই বটগাছের চারিদিকের জঙ্গল ও ঘাস-পাতা পরিষ্কার করার জন্যে। এদিকে তিনি যখন পায়েস রান্না শেষ করেছেন, ঠিক তখনই তার এক সহচরী পূর্ণা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন এবং বললেন, যে বৃক্ষদেবতা স্বয়ং বটতলে ধ্যানে বসে আছেন।
এ সংবাদ পেয়ে আগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে সুজাতা দ্রুত ওই পায়েস একটা সোনার বাটি পূর্ণ করে নিরঞ্জনা নদীর তীরস্থ নির্দিষ্ট ওই বটবৃক্ষের কাছে গেলেন। যখন তিনি সেখানে পৌছলেন, দেখতে পেলেন সত্যিই এক সৌম্য-শান্ত ধ্যানী ওই বটতলে ধ্যানে রয়েছেন। সুজাতা তাঁকে বৃক্ষদেবতা মনে করলেন, সুজাতা পায়েসের বাটিটি ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থের সামনে রেখে অতি সাবধানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা জানালেন, ‘‘প্রভু, আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করুন। আমি যেমন সফলতা লাভ করেছি, তেমনই আপনিও ধ্যাননিমগ্ন বিষয়ে সফলতা প্রাপ্ত হন।
সিদ্ধার্থ জানালেন, তিনি বিশেষ কেউ নন, এক সাধারণ মানুষ, সুজাতা তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, তাই সুজাতা সিদ্ধার্থকে বললেন, আমি আপনার পরিচয় বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার রন্ধন করা এই পায়েস গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন। সিদ্ধার্থ কী মনে করে ওই পায়েস ৪৯ ভাগে ভাগ করেছিলেন, প্রতিদিনের জন্যে একভাগ ভেবে আর কী আশ্চর্যভাবে ৪৯তম দিনেই তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই দিন ছিল এক বৈশাখী পূর্ণিমা, চাঁদের শুভ্র আলোকে তিনি গাছের তলায় রাতের তৃতীয় প্রহরে বুদ্ধত্ব লাভ করে সিদ্ধার্থ বা ঋষি গৌতম থেকে হলেন প্রভু বুদ্ধদেব।
এদিকে সিদ্ধার্থকে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে তাঁর পাঁচজন সঙ্গী তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।
বোধিলাভের পর গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে তপুস্স ও ভল্লিক নামক বলখ অঞ্চলের দুইজন ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হয়, যাঁরা তাঁকে মধু ও বার্লি নিবেদন করেন। এই দুইজন বুদ্ধের প্রথম সাধারণ শিষ্য। বুদ্ধ তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নবলব্ধ জ্ঞানের কথা আলোচনার জন্য উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের দুইজনেরই ততদিনে জীবনাবসান হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি বারাণসীর নিকট ঋষিপতনের মৃগ উদ্যানে যাত্রা করে তাঁর সাধনার সময়ের পাঁচ প্রাক্তন সঙ্গী, যাঁরা তাঁকে একসময় পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদেরকে তাঁর প্রথম শিক্ষা প্রদান করেন।
পালি সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় লক্ষ্যণীয় যে, সমসাময়িক বাংলা অঞ্চলে রক্ষণশীলতার আবহের মধ্যেও বৌদ্ধ যুগে নারীদের সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এ জন্য বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও গৌতম বুদ্ধের উদার মনোভাবই মূলত চালিকাশক্তি। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পূর্বে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান তথা মাঙ্গলিক কর্মকাণ্ডে নারীদের স্থান ছিল গৌণ এবং নিঃসন্তান ও বিধবা নারীদের এসব অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কোনও ধরনের অধিকারও ছিল না। বুদ্ধ জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা এবং বৈষম্যব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘনিকায় এর সুত্ত মণ্ডলে বুদ্ধ বলেছেন, ‘সব মানুষ সমান, সে নারী বা পুরুষ, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যেই হোক না কেন।’ গৌতম বুদ্ধ নারী পুরুষ উভয়কেই তাঁর সধর্ম প্রচারের তুল্য অধিকার প্রদান করেন এবং বৌদ্ধসংঘে পুরুষের পাশাপাশি নারীর যোগদান নিশ্চিত করে মানবতার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উল্লেখ্য, বৌদ্ধসংঘে নারীর প্রবেশাধিকার প্রথম দিকে ছিল না। এমনকি বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রথমদিকে নারীদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি দানে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর আশংকা ছিল, নারীদের সংঘে প্রবেশের ফলে পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, একাগ্রতা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের প্রধান সোপানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য স্থবির আনন্দের অনুরোধ এবং বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী পাঁচশত শাক্যনারী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করলে গৌতম বুদ্ধ তা মেনে নেন।
গৌতমবুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্য করেননি। তাঁর প্রচারিত বাণী এবং নৈতিক শিক্ষানীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের কল্যাণের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। বৌদ্ধসংঘে প্রবেশের দ্বার বিবাহিত, অবিবাহিত, নিঃসন্তান, বিধবা এবং সকল শ্রেণির জাতি, ধর্ম ও গোত্র নির্বিশেষে সকল নারীর জন্যই উম্মুক্ত ছিল। এমনকি বারবণিতা এবং চণ্ডাল-কন্যাও সংঘে যোগদানপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাঁদের প্রতি সমান সমীহ প্রদর্শন করা হত। তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায় বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আম্রপালি নামে গণিকার জীবন পর্যালোচনায়।
এছাড়া পদুম্বতী, সামা, সুলসা সহ অনেক খ্যাতনামা নর্তকী ও বারাঙ্গনার জীবনী হতে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তাঁরা পাপপ্রধান মানসিকতা হতে মুক্তিলাভ করে আদর্শজীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং পরবর্তীতে জনগণের অতল শ্রদ্ধাও লাভ করেছেন।