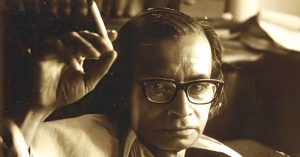ভূমি দখল করে রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা রাজাদের বরাবরই ছিল। এছাড়া রাজা-মহারাজা-জমিদারদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, এককথায় তাঁরা সৈনিক এবং যাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিলেন ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর লোক। ছত্রপতি শিবাজী পার্বত্য মাওয়ালি উপজাতিদের দিয়ে সৈন্যদল গঠন করে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। অন্যদিকে, মহারাণা প্রতাপসিংহের ভিলদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী বার বার মোগল সম্রাট আকবরের সামনে সমানে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। দুঃখের কথা এই, যে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মাতব্বররা সমাজের তথাকথিত নিচু জাতের মানুষকে কথায় কথায় জাতিচ্যুত করতেন, সেই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর লোকজনেরাই ছিলেন দেশের রক্ষক। তাঁদের বাহুবলের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল ভারতের নিরাপত্তা।
মির্জা নাথানের ‘বাহারিস্থান’ থেকে জানা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোচ, গারো, বাগদি, ডোম, হাড়ি, তিপ্রা শ্রেণির লোকজন সৈনিক হতেন। মির্জা নাথানের বক্তব্য অনুসারে, বাংলার বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া মুশা খাঁর এক পদাতিক সেনাপতি ছিলেন রমাই লস্কর। বাঙালি বীর ওসমান খাঁর ছিলেন হাড়ি জাতীয় সৈনিক। কোচবিহারের বীর চিলা রায় ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।
স্মার্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্ব জাহির করে বলে দিলেন, কলিতে মাত্র দুটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। এর ফলে কায়স্থ ও বৈশ্যরা হয়ে গেলেন শূদ্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে তাই দেখি ব্যাধ রাজা কালকেতুর মুখ দিয়ে কায়স্থ ভাঁড়ু দত্তকে বলছেন,—
‘হয়ে তুই রাজপুত, বলিস কায়স্থ সূত।
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।।’
তবে অভিযোগ ওঠে, রঘুনন্দন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮শ সূত্র থেকে ‘ইমানারীরবিধবা’ শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে তার ‘জাল’ পাঠ দিয়েছেন সতীদাহ সম্পর্কে। রঘুনন্দনের প্রবল বিরোধী ছিলেন বাংলার আর-এক স্মৃতিকার নুলো পঞ্চানন। তিনি তাঁর ‘গোষ্ঠী কথা’ গ্রন্থে বলেছেন, রঘুনাথ স্মৃতিশাস্ত্র লিখে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অবমাননা করেছেন।
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র অনুসারে, যুদ্ধ হচ্ছে ভিন্ন পথে রাজনীতিরই প্রয়োগ। পাশাপাশি একথাও বলা হয়েছে, একমাত্র উপায় না পেলে তবেই যুদ্ধ করা ভাল। কারণ, যুদ্ধ ছাড়া ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার মতো পথ খোলা রয়েছে। যুদ্ধ শেষ পথ। যুদ্ধে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। তাই শুধুমাত্র জমি দখল নয়, শত্রুকে বশ করার জন্যই দরকার যুদ্ধ।
যুদ্ধের জন্য সৈনিকদের সম্পর্কেও বেশকিছু কথা বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে গভীর লজ্জার বিষয় আর পালিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুর হাতে নিহত হলে তার প্রভুর ওপর পড়ে অপরাধের দায় এবং এ জন্য পরজন্মে তাকে কষ্ট পেতেই হবে। আর যুদ্ধ করতে করতে যে সৈনিক জীবন বিসর্জন দেয়, স্বর্গের পথ তার জন্য খোলা। তাই দেখা গেছে, যখন কোনও রাজপুত পরিবার জহরব্রতে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে, তখনও দুর্গ প্রাকারে দাঁড়িয়ে শেষ সৈনিকটি যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিচ্ছেন।
ছ’রকমের সৈন্যদল ছিল ভারতে। প্রথমত, পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করা সৈন্যদল, দ্বিতীয়ত, অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত সৈন্যদল, তৃতীয়ত, সৈন্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলি থেকে পাঠানো সৈন্যদল, চতুর্থত, বশ্যতাসূত্রে আবদ্ধ মিত্র রাজ্য থেকে আগত সৈন্যদল, পঞ্চমত, শত্রু সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈন্যদের নিয়ে তৈরি সৈন্যদল এবং ষষ্ঠত, পাহাড়-জঙ্গলে যুদ্ধ করতে দক্ষ উপজাতিদের নিয়ে গঠিত গেরিলা সৈন্যদল।
যে সব বণিক সংস্থা নিজেদের পণ্যবাহী গাড়ি ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি রক্ষার জন্য নিজস্ব ফৌজ রাখত, তারাই প্রয়োজনে রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। যেমন, পরবর্তীকালে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদল ছিল, ঠিক সেরকম ব্যবস্থাই ছিল। অর্থের বিনিময়ে লড়াই করতে দক্ষ ছিল ভারতের কেরল (মালাবার) ও কর্ণাটক (মহীশূর) থেকে আগত কিছু যোদ্ধারা, যারা মধ্য যুগের ভারত এবং সিংহলের বিভিন্ন রাজ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন।
যারা বংশপরম্পরায় সৈনিক বৃত্তি নিত, তারা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের পরিচয় দিত। তবে রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা অনেক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাই, যারা উচ্চ সামরিক পদে বহাল ছিলেন। মহাভারতের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এর একটি উদাহরণ। অন্যদিকে, সমাজের নিচুতলার মানুষ, যারা যুদ্ধে অংশ নিতেন, তারা আসলে ছিলেন ভাড়াটে যোদ্ধা। অর্থশাস্ত্রে বেশ কিছু গ্রামের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে, যেখান থেকে করের বদলে সৈন্য পাঠানো হত। উত্তর-পশ্চিম ভারত, রাজস্থান ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে সামরিক স্বভাবের লোকজনের চরিত্র আদি যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত মোটামুটি একই রকম রয়ে গেছে।
বাংলার বর্ণবিন্যাস গঠিত হয়েছে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও অন্ত্যজদের নিয়ে। সবার নিচে ছিল এই অন্ত্যজদের স্থান। বাংলার বর্মণরাজ হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টর স্মৃতি শাসন অনুসারে, অন্ত্যজ ও চণ্ডাল সমার্থক।
পাল ও সেন আমলের বিভিন্ন লিপিতে গৌড়-মালব-খস-হূন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। এইসব ভিনপ্রদেশি লোকজনদের বেতনভুক সৈন্য হিসেবে কাজ করাটা অসম্ভব নয়।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন,—
‘আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।’
কিছু প্রচলিত পদবিও সৈন্যবৃত্তির দিকে ইঙ্গিত করে, যেমন, সামন্ত, শাসমল, সাঁতরা, হাজরা ইত্যাদি। সামন্ত হচ্ছেন নায়ক। কবি ভারতচন্দ্র বলছেন,—
‘সম্মুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত কোকিল ভ্রমর সাথে।’

তেমনই পণ্ডিত হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের মতে, ‘সহস্রমল্ল’ থেকে শাসমল। বানানটি ‘সাসমল’ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার ‘সামন্ত রায়’ থেকে ‘সাঁতরা’। তেমনই, যে নায়কের অধীনে হাজার সৈন্য, তিনি ‘হাজারি’। আর এই ‘হাজারি’ থেকেই ‘হাজরা’ পদবি।
বর্তমানে বাঙালি সম্পর্কে নাক সিঁটকানো কথা বলা হয়ে থাকে, যেমন, তারা ভিতু, তারা যুদ্ধ করতে জানে না, তারা কেবল পালাতেই জানে, নিজের ভিটেমাটি পর্যন্ত দখলে রাখতে পারে না; হিংস্র জন্তুর মত অন্য গোষ্ঠীর লোকজন কেড়ে নেয় তার ভিটেমাটি, ঘরের লক্ষ্মী, ধন-সম্পদ সবকিছুই। কিন্তু বাঙালি তো এত দুর্বল ছিল না! যথেষ্ট যোদ্ধা ছিল এই বাঙালি, বিশেষ করে বাংলার নিম্নবর্গের মানুষ তো বীর ছিলেন এই বাংলার।
বাংলার ছড়ায় রয়েছে তারই প্রমাণ। যেমন, বহুল প্রচলিত এই ছড়াটি—
‘আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে;
ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজে
বাজতে বাজতে চললো ঢুলি
ঢুলি যাবে সে কমলা পুলি।’
এখানে দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর আগেও চলেছে ডোম, পিছনেও ডোম-বাহিনী, ঘোড়ায় চড়েছে ডোম; আবার তারাই যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধের বাজনা নিয়ে হাজির হয়েছেন সেনাদলে। উদ্দেশ্য, সেনাদের উৎসাহিত করা।

আসলে বাংলার বিভিন্ন ব্রাত্যজনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন বীরের বংশধর। তাঁরা জীবনের তাগিদে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকতেন ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের ডাক পড়লে হাজির হয়ে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জাতপাতের নামে বিভাজন ঘটিয়ে বাঙালিকে সুকৌশলে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই বাঙালির নামে ভিতু বদনাম জুটেছে।
বাংলায় শিশুদের খেলার মধ্যেও ছিল যুদ্ধের পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা। ‘আগডুম বাগডুম’ খেলা— তারই একটি উদাহরণ। ‘আগডুম বাগডুম’ খেলায় শিশুরা গোল হয়ে বসে একে অন্যের হাঁটু ছুঁয়ে ছড়া কেটে এ খেলা খেলত, যে খেলা তাদের পরবর্তী জীবনে তৈরি করত যোদ্ধার জীবন। বিনয় ঘোষ তাঁর ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ গ্রন্থে এই ছড়াকে জনসেনার যুদ্ধযাত্রার বিবরণ বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কানাড়ার বিয়েতে কালু ডোম ও তাঁর সঙ্গীরা এই সাজ সেজেছিলেন।
বাংলার এইসব প্রচলিত লৌকিক খেলাগুলি আজ আধুনিকতার প্রভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বীর বাঙালির নামে আজ ভীরুতার বদনাম!
বাঙালির জেগে ওঠার জন্য ফের দরকার পুরনো সংস্কৃতির শেকড় আঁকড়ে ধরা, ঘরে ফেরা।
তথ্যসূত্র:
১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব : নীহাররঞ্জন রায়, দে’জ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪১৬।
২. গৌড়ের ইতিহাস : রজনীকান্ত চক্রবর্তী, দে’জ, কলকাতা, ২০২১।
৩. বাংলার ইতিহাস : ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, র্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০২০।
4. The Wonder that was India : A. L. Basham, London, 1954.