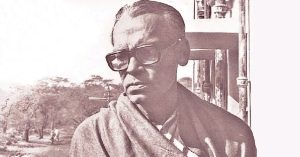জীবনে বহু খ্যাতিমান মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দার্শনিক শঙ্করাচার্য বলেছেন, অসার এই সংসারে গ্রন্থ ও সজ্জনসঙ্গই কেবল সার। সেদিক থেকে আমি নিতান্তই ভাগ্যবান। সান্নিধ্য পেয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শামসুর রাহমানের, অন্নদাশঙ্কর রায় ও আহমদ শরীফের, ফিরোজা বেগম-ওয়াহিদুল হক-কলিম শরাফীর, আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। তেমনই বাঙলা ছায়াছবির তিন দিকপাল সত্যজিৎ, মৃণাল ও ঋত্বিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। জীবনে এ বড় কম পাওয়া নয়।
ঋত্বিকের সঙ্গে আলাপের একটি প্রাক্পর্ব আছে। তাঁর ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবির শুটিং অনেকটাই হয়েছিল আমাদের পাড়ায়, মানিক সরকার নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে গল্প, আর আমাদের অশ্বিনীনগর-আজাদগড়-বিজয়গড় হল উদ্বাস্তু অঞ্চল। ছবিতে নায়িকা সুপ্রিয়ার যে প্রেমিক, পরে তার বোনকে বিয়ে করে, সেই নিরঞ্জন রায়-ও ছিলেন কাছাকাছি নেতাজীনগর কলোনির বাসিন্দা। ‘গঙ্গা’ ছবিতে সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে তাঁর অভিনয়-ও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাছাড়া আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি।
এসব ঘটনা ১৯৫৯/৬০ সালের। বালক ছিলাম, তাই সে-শুটিং দেখিনি আমি, দেখেছেন আমার বড় দুই ভাই। তবে পরবর্তীকালে সিনেমাটা দেখতে গিয়ে সেই বাড়ি, বাড়ির উঠোন, সামনের রাস্তা, নায়িকার বড় ভাই (অভিনয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায়) যে দোকান থেকে ব্লেড কিনেছিল, সেই নারায়ণ সাহার দোকান,– দুদিকে মুখ ফেরানো বলে দোকানটি ‘দুমুখী দোকান’ নামে খ্যাত ছিল, দেখে মজা পেতাম খুব। এখনও পাই। ছেঁড়া চটি হাতে সুপ্রিয়া যে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলেন, লক্ষবার সে পথে হেঁটেছি।
এর পরের অধ্যায় ঋত্বিককে নিয়ে বাড়িতে বড় ভাই ও তাদের বন্ধুদের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি শুনে ঋত্বিককে উপলব্ধির চেষ্টা। তখনও ঋত্বিকের কোনও ছবি দেখা হয়নি। আমাদের আমলে বছরে এক-আধটি ছবি দেখার সুযোগ মিলত, অভিভাবকের সঙ্গে, দেশাত্মবোধক বা শিশু চলচ্চিত্র। মনে আছে, ‘সুবর্ণরেখা’ মুক্তি পেল যখন, ১৯৬৫ সাল, আমাদের এক মাসতুতো বড় ভাই ছবি দেখে এসে জানালেন, হল থেকে বেরিয়ে আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন, এমন ছবি নির্মিত হওয়াও কি সম্ভব! তাঁর এই বিহ্বলতা দেখে আমি ছবিটি দেখার সঙ্কল্প নিয়ে বসুশ্রী হলে যাই। হায়, ছবিটি প্রাপ্তবয়স্কদের! আমার মতো চোদ্দো বছরের কিশোর তাই ব্যথাহত হয়ে ফিরে আসে।
অতঃপর ১৯৭৯। ঋত্বিককে, এবং তাঁর ছবিগুলো (Retrospective, পূর্বাপর। তখনও ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ তৈরি হয়নি। তাছাড়া ‘নাগরিক’-ও দেখার সুযোগ ছিল না। অতএব বাকি পাঁচটা। তাই-ই কি কম? পাঁচ-পাঁচটি রত্নখনি!) দেখার পরম সুযোগ জুটে গেল। সেসময় তো টিভির যুগ নয়, তাই রিলিজ করার সময় ছবি দেখতে না পারলে সেটি দেখার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হত, কবে কোন হলে মর্নিং শো নামক সিন্দাবাদে চড়ে আমাদের সুযোগ করে দেবে। এ কিন্তু মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি, বা বলা যাক তুমুল বর্ষণ। কেননা ঋত্বিকের সব ছবি দেখানোর আয়োজন করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ক্লাব, যেখানকার ছাত্র আমি, উপরন্তু ফিল্ম ক্লাবের সদস্য! এ এক অভাবিত সুযোগ। তদুপরি ঋত্বিক স্বয়ং আসবেন ছবি উদ্বোধনের দিন, বক্তৃতাও দেবেন। সোনায় সোহাগা একেবারে। ততদিনে ঋত্বিকের ছবি না দেখলেও তাঁর ছবি নিয়ে পড়েছি, আলোচনাও শুনেছি এঁর-ওঁর-তাঁর মুখে।
দেখলাম তাঁকে। লম্বা, রোগা, মুখ দিয়ে কথা ঝরছে লাভাস্রোতের মতো। কথা বলার সময় তাঁর বাহু ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে মুখাবয়ব, উচ্ছ্রিত বাক্যে যেন উপনিষদের মন্ত্রধ্বনি! বলছিলেন তাঁর ছবি নিয়ে, ছবির পশ্চাতে যে দেশভাগের মর্মন্তুদ বেদনা, নৈরাশ্য, হাহাকার, হতাশা আর সমূহ সর্বনাশের বিষাদ, তা মূর্ত হয়ে উঠছিল তাঁর উচ্চারণে। আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, তাঁর চোখ কোনও ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষে নিবদ্ধ ছিল না, ছিল অনন্ত আর অনিশ্চয়তায় প্রসারিত। তাঁর প্রতিটি বাক্য, বাক্যালাপের অণু-পরমাণু কী শিক্ষক, কী শিক্ষার্থী, মর্মে পৌঁছে যাচ্ছিল সবার। তাঁর ছবির উৎস যে দেশভাগের শোকবৈভব থেকে উঠে আসা অরুন্তুদ শোক, শ্রোতাদের মর্মে সেদিন তা গেঁথে দিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে গান্ধীকে নিয়ে বিতর্কিত উক্তি করে বসেছিলেন সেদিন, যার রেশ ভারতের পার্লামেন্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বুঝলাম সেদিন, ঋত্বিক এক আগুনের আখরে লেখা দধীচির নাম। সাধারণ পাঞ্জাবি-পাজামা-পরিহিত মানুষটি আসলে দেশ ও জনতার প্রান্তর-প্রহরারত সুকান্ত-কথিত কড়া পোশাকধারী এক ছদ্মবেশী চে, কাস্ত্রো, মাও জে দঙ-এর সমগোত্রীয় সৈনিক।
আর তাঁর ছবিগুলো? পরপর পাঁচদিনব্যাপী যা প্রদর্শিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং ও পি জি বিল্ডিং-এর মধ্যবর্তী বিবেকানন্দ মিলনায়তনে (প্রসঙ্গত জানাই, যাদবপুরে আরও একটি মঞ্চ, গান্ধী ভবন। তাছাড়া বিশাল এক ওপেন এয়ার থিয়েটার, গ্রীক প্রকরণে, সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় এখানে। এখন যাদবপুরের একদা-উপাচার্য ও ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের নামে আরও একটি মঞ্চ হয়েছে)। অভিভূত বললে কম বলা হবে, অসাধারণ বললে আরও কম বলা হবে, অনবদ্য, সুন্দর ও দ্রোহের সংঘাতে যেন কুসুমিত ইস্পাত, যেন আগ্নেয়গিরি থেকে আসা দিকভ্রান্ত কূলঙ্কষা নদীর তরঙ্গিত বন্যা, যেন মরুঝড়, দাবানল, টর্নেডো, বা এসবের সমবায়। ঋত্বিক মুহূর্তের মধ্যে বশ করে ফেললেন। দীক্ষা দিলেন নতুন বোধ ও জীবন, জগৎকে ভিন্ন ও মোহহীনভাবে দেখার।
এর কিছুকাল পরে সুযোগ হল তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের। আমার বড়ভাই ও তার বন্ধুরা মিলে একটি প্রকাশনা সংস্থা খোলেন, ‘সন্ধান সমবায় সমিতি’। আমিও ছিলাম এর অন্যতম অংশীদার। সেখান থেকে প্রথম যে বইটি বেরোয় (প্রথম ও একমাত্র!), সেটি ঋত্বিক ঘটকের ‘চলচ্চিত্র, আমি ও অন্যান্য’। বইটির জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন ঋত্বিক। ঠিক হয়, আমাদের পরবর্তী প্রকাশনা হবে ঋত্বিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে একটি অনুপম গ্রন্থ।
সেই সাক্ষাৎকার নিতে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আমিও। আমার যোগ্যতালাভ ঘটেছিল এক মজার কারণে,– তখন তো ঘরে ঘরে টেপ রেকর্ডার ছিল না, আমার ছিল। সেজন্য। তিনদিন ধরে তাঁর অনর্গল কথার পর কথা শুনে গেছি, বয়স্কদের পাশাপাশি আমিও প্রশ্ন করেছি। দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর। এক, তিনি কথা বলার সময় আত্মমগ্ন থাকতেন। কারও দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না। তাকাতেন হয় সুদূরে, আর নয়তো চোখ বুজে কথা বলতেন। আর দ্বিতীয় যা, তা হল ঋত্বিকের চোখ। এত উজ্জ্বল আর মরমী, এক-ই সঙ্গে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আর লুব্ধক নক্ষত্রের মতো দীপ্ত, তা আর কারও মধ্যে দেখিনি। সত্যজিৎ-মৃণালের মধ্যেও না, যদিও ঘটনাচক্রে ওই দু’জনের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল অনেক বেশি।
ছিন্ন পোশাক, ঘরে টেবিল-চেয়ারের বাহুল্য নেই, তিনি কখনও বসা, কখনও আধ-শোওয়া একটি সামান্য খাটে। পাশে তাঁর এক বড়ভাই, জাহাজে চাকরিসূত্রে সারা বিশ্ব ঘুরে বেরিয়েছেন। নাম লোকেশ। নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন তিনি, কম যেতেন না ছবি আঁকা-ছবি তোলায়। ভারতীয় নৌবাহিনীর পত্রিকা ‘ওশেনিয়েট’ সম্পাদনা করতেন একদা। ঋত্বিক কথা বলছেন, লোকেশ মিটিমিটি হাসছেন। যেন বেজায় মজা পাচ্ছেন।
একটি ঘটনা ঘটল সেসময়। ঋত্বিক-জায়া সুরমা দুই ভাইয়ের জন্য দু’গ্লাস দুধ নিয়ে ঢুকলেন। দুই ভাই এমন উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন, যেন এমন তামাশা আর হতেই পারে না। সুরমা অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে গেলেন। তখন সকাল দশটা হবে। ঋত্বিক কথা বলছেন, আর সমানে দেশি মদ খেয়ে চলেছেন। এঁকে দুগ্ধপোষ্য বানাবার সাধ্য আছে কারও। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল একবার বলি, এইভাবে আত্মধ্বংস– সাহস হয়নি।
এ গেল ১৯৭৫-এর ঘটনা। এরপর তাঁকে দেখি উত্তর কলকাতার একটি সিনেমাহলে, কাদের আয়োজনে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে-র প্রদর্শনীতে। কথা হয়নি। তখন তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ, কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল। এর কয়েকমাস পর তাঁর প্রয়াণ। মহাবোধি সোসাইটিতে যে স্মরণসভা হয়েছিল তাঁর, অন্যান্যদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে বলেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, মনে আছে।