নন্দিত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক গত ১৫. ১১. ২০২১-এ প্রয়াত হয়েছেন। পরিণত বয়সেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর, ৮২ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কাল আশি বছরকে যদি প্রতিতুলনায় আনি, তাহলে আমাদের খুব যে আফসোস থাকে, তা নয়। অথচ থাকেও আবার, যখন শতায়ু নাসিরউদ্দিন বা নীরদ সি. চৌধুরীর কথা ভাবি। হতাশা কেটেও যায় সুকান্ত, সোমেন চন্দ বা আবুল হাসানের স্বল্পায়ুর কথা ভেবে।
আসলে কৃতী মানুষদের প্রয়াণ এজন্যেই বেদনার যে আমরা জেনে যাই, কখনওই তাঁর কাছ থেকে পাঠকের পক্ষে মুগ্ধ, বিস্মিত, স্তম্ভিত হওয়ার মত কিছু পাব না। এক্ষেত্রে আমাদের সান্ত্বনা, তাঁর সারস্বত সাধনার ফুল্লকুসুমের বারবার বারবার স্বাদ নেওয়া তো আটকাচ্ছে না তাতে।
তাঁর মৃত্যু নানা কারণেই আমার কাছে বেদনার। বহু বছর ধরে তাঁর স্নেহ লাভ করেছি, সমৃদ্ধ হয়েছি তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় করে, তাঁর প্রশস্ত হৃদয় আর প্রসন্ন বরাভয়মুদ্রা আমাকে আপ্লুত করেছে। তাঁকে নিয়ে অজস্র স্মৃতির দেবমাল্য গাঁথবার তাই এই সামান্য প্রয়াস।
হাসানভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় কমবেশি চল্লিশ বছর। তবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে তাঁর বাঁশি শুনেছি আমি, তাঁর গল্পপাঠের মাধ্যমে। অন্যভাবেও।
আগে তাঁর গল্পপাঠের কথা বলে নিই। একদা পূর্ব-পাকিস্তান। পূর্ববঙ্গের লেখার সঙ্গে প্রাক্ ‘৭১ পর্বে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পরিচয় হওয়ার সুযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। হাসান আজিজুল হকের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়, এবং ১৯৬০-এ মাত্র একুশ বছর বয়সে সিকান্দার আবু জাফরের ‘সমকাল’ পত্রিকায় ‘শকুন’ গল্পের মাধ্যমে তিনি রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন, তবু ’৭১-পূর্ববর্তী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে তিনি প্রায় অপঠিত। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঁর ‘জীবন ঘষে আগুন’ গল্পটি, যা কলকাতা থেকে নির্মাল্য আচার্য এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটির মাধ্যমেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে ওঠেন। লেখাটিতে কমলকুমার মজুমদারের প্রভাব অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যা ওই সময়কার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও ছিল।
তাঁর লেখা সেসময় পড়া সম্ভব না হলেও তাঁর সম্পর্কে অবহিতি ছিল আমার স্কুলের এক শিক্ষকের মাধ্যমে। তাঁর নাম ছিল নগেন্দ্র দাস। ৬৫-তে কলকাতায় এসে আমাদের স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন খুলনার সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘সন্দীপন’-এর সঙ্গে যুক্ত। এখানে আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, জহরলাল রায়, খালেদ রশিদ, সাধন সরকার এবং হাসান আজিজুল হক প্রধান। এঁরা ‘সন্দীপন’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। স্যারের কাছে ‘সন্দীপন’-এর গল্প শুনতাম, এবং হাসান আজিজুল হক সম্পর্কেও। ‘সন্দীপন’ ভেঙে যায় সদস্যরা একে একে চাকরি ও অন্যান্য সূত্রে দেশের ও বহির্দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে। ‘সন্দীপন’ নিয়ে হাসানভাইয়ের একটি লেখা আছে তাঁর ‘চালচিত্রের খুঁটিনাটি’ বইতে।
বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কোনও লেখা পশ্চিমবঙ্গের কোনও পত্রপত্রিকায় সাতের দশকে প্রকাশিত হলেও তা আমার নজরে পড়েনি। তাঁর গল্পগ্রন্থ চোখে দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না।
এহেন মানুষটির সঙ্গে আমার আলাপ হল কলকাতায় ১৯৮৬/৮৭ সাল নাগাদ। উনি সেবার যাদবপুরে ওঁর ভাগ্নীর বাসায় উঠেছিলেন। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার বন্ধু একদা খুলনাবাসী শাহযাদ ফিরদাউস।
প্রথমদর্শনে মুগ্ধ করেছিল ওঁর চোখদুটি। যেমন প্রোজ্জ্বল তেমনই বাঙ্ময়। তাঁর দুচোখের মধ্যে স্বতন্ত্র দীপ্তি আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি।
সেদিন খুব একটা কথা হয়নি। ঠিক হল, পরদিন আমি আর ফিরদাউস গড়িয়াহাট যাব ওঁকে নিয়ে, কিছু কেনাকাটা করবেন উনি। মনে আছে, ওঁর ভাগ্নীর বাড়িতে ‘The Times of India’ দৈনিক পত্রিকাটি দেখে অবাক হযেছিলাম। তখনও কলকাতা থেকে এ পত্রিকাটির কোনও সংস্করণ বেরোত না, আসত বম্বে (এখনকার মুম্বাই) থেকে।
পরদিন বেরোনো গেল। এ দোকান সে দোকান ঘুরছি, সঙ্গে চলছে আমাদের কথাবার্তা। ‘জীবন ঘষে আগুন’-এর রচনাশৈলী নিয়ে প্রশ্ন করলাম। বললেন, ওটা ছিল ভাষা নিয়ে আমার পরীক্ষা। আমি এখন সে রীতি থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছি।
তখন আমাদের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল তুঙ্গে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেরিদা ও গার্সিয়া মার্কেজ। দেরিদাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে খুব মজা করে উত্তর দিলেন: ওইসব দেরিদা নেরুদা ঠিক আমাদের জন্য নয়। একজন ভিনদেশি লোকের সাহিত্য বুঝতে গেলে তাঁর দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পূর্বাপর পাঠ নেওয়া লাগে। আর ম্যাজিক রিয়ালিটি নিয়ে বললেন, ও জিনিসের অন্ত নেই উপমহাদেশের সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারত থেকে ঠাকুরমার ঝুলি, কোথায় নেই ম্যাজিক রিয়ালিটি?
সেবার তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি আগ্রহ তৈরি হল। কেনাকাটা-শেষে তিনি আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার করালেন। বাংলাদেশের বহু কবি-সাহিত্যিকের লেখা ততদিনে পাঠ করেছি, তাঁদের অনেকের বইও রয়েছে আমার সংগ্রহে। অথচ তাঁর কোনও আস্ত বই পড়া, এমনকি দেখার সুযোগ পর্যন্ত হয়নি। তার কারণ, একে তো তিনি লেখালেখি করেন কম, তায় তাঁর বই পশ্চিমবঙ্গে আসে না বললেই হয়। তবে একটি সুখবর শোনালেন তিনি, কলকাতার এক প্রকাশক তাঁর বই শিগগিরই ছাপতে চলেছে। এবং অচিরেই কলকাতা থেকে তাঁর একটি গল্পসংকলন বেরোয়। সেই থেকে তাঁর লেখার মুগ্ধ পাঠকে পরিণত হই। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে অভিনব ভগীরথ, উপলব্ধি করতে দেরি হয় না।
কলকাতায় তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি দেয় নিঃসন্দেহে রবিন ঘোষ সম্পাদিত ‘বিজ্ঞাপনপর্ব’। পত্রিকাটি তাঁর ওপর একটি সংখ্যা বের করে। সম্ভবত বাংলাদেশেও এর আগে তাঁর ওপর কোনও সংখ্যা বেরোয়নি। এটা ১৯৮৭/৮৮ সালের ঘটনা। যদ্দুর মনে পড়ে, রবিন ওঁর একটি বইও প্রকাশ করেছিলেন। এর পর থেকে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে হাসানচর্চা এক অনন্য মাত্রা পায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে হাসান আজিজুল হকের গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৯৮৯-এ আমার স্ত্রী কবি দেবাঞ্জলিকে নিয়ে বাংলাদেশে এলাম। নগেনস্যার একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন নাজিম মাহমুদকে, আমার ছাত্র সস্ত্রীক রাজশাহী যাচ্ছে। ব্যস, এইটুকু। সেবারের প্রায় দুমাসের ভ্রমণের শেষপর্বে ছিল রাজশাহী। ঢাকা থেকে প্রথমে গেলাম নাটোর। সেখানে দিন দুয়েক থেকে রাজশাহী এসে উঠলাম জুবেরি হাউস-এ। হাতমুখ ধুয়ে একটা রিকশ নিয়ে দেখা করতে গেলাম নাজিমভাইয়ের সঙ্গে। আমরা জুবেরি হাউসে উঠেছি শুনে ভর্ৎসনা করলেন, ‘কী! নগেনের ছাত্র তুমি, আমার এখানে না উঠে…’ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে জুবেরি হাউসে গমন, বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে তাঁর কোয়ার্টারে অধিষ্ঠান। এবং সেদিন সন্ধ্যাতেই আমাদের সম্মানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জড়ো করে তাঁর বাড়িতে ঘরোয়া গান ও আবৃত্তির আয়োজন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রোজিস্ট্রার তখন এবং ‘স্বনন’ নামে আবৃত্তি সংস্থার প্রাণপুরুষ। নিজে গীতিকার, আবৃত্তিকার, কবি।
তাঁর বাড়ির সান্ধ্য অনুষ্ঠানে হাসান আজিজুলও এলেন। এবং আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কুশলজিজ্ঞাসা, কলকাতার খবরাখবর জানতে চাওয়া। এবং সে-রাতের অনুষ্ঠান-শেষে নাজিম মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা: তোমার চেয়ে মলয়কে আতিথ্য দেবার অধিকার আমর বেশি, কেননা আমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে আগে। আর তাছাড়া তুমি তো সংসারীই নও। (নাজিমভাই সেসময় বিপত্নীক বলে এ কথা বলা।) এই কথা বলে নাজিমভাইকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমাদের দুজনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে ওঠা। সত্যের খাতিরে এবং চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এ কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের ব্যাগটা উনি নিজে বহন করলেন, আমাদের বারংবারের আপত্তি উপেক্ষা করে। জন্ম জন্ম অর্জিত পুণ্যের ফলেই ঘটেছিল বোধকরি, মনকে সান্ত্বনা দিই আজও।
যে সাত-আট দিন তাঁর বাসায় ছিলাম, সারস্বত-সংসর্গে দিনগুলি সত্যিই ছিল হীরকচিহ্নিত। আমরা আলোচনা করেছি দুই বাংলার সাহিত্য নিয়ে যেমন, তেমনই দেশকাল রাজনীতি নিয়েও। শিবনারায়ণ রায় এবং মহাশ্বেতাদেবী নিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল উত্তুঙ্গ। তিনি শিবনারায়ণের অধীনে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত গৃহকাতরতা তাঁকে গবেষণা অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসতে বাধ্য করে। তাঁর সম্পাদিত ‘গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী’ দেখালেন, উপহার দিলেন বেশ কিছু গল্পের বই এবং প্রবন্ধগ্রন্থ ‘সক্রেটিস’। তাঁকে বললাম, রজনীকান্ত গুহর সুবৃহৎ গ্রন্থটি তিনি পড়েছেন কিনা, যা সক্রেটিসের ওপর বাংলায় লেখা অত্যন্ত প্রামাণ্য বই, যেহেতু লেখক গ্রিক ভাষা জানতেন বলে বইটি লিখতে গিয়ে বহু গ্রিক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। না, তিনি পড়েননি।
সকালবেলা নাস্তার সময় দেখতাম, আমাদের জন্য কোনওদিন পরোটা তৈরি করছেন হাসানজায়া নাজমুনভাবি, কিন্তু হাসানভাই খাচ্ছেন মুড়ি। ‘বর্ধমানের লোক আমি, মুড়ি ছাড়া নাস্তা হয়? এ ছাড়া তাঁর প্রিয় আহার্য ছিল পোস্ত, যা বর্ধমান-বীরভূম-মেদিনীপুরের মানুষের কাছে অতি প্রিয়।
সকালে বাজারে নিয়ে যেতেন আমাকে, দু-তিন রকমের মাছ কেনা চাই তাঁর। যখন শুনলেন আমার স্ত্রী ইলিশ মাছ খায় না মাছটির গন্ধ সহ্য হয় না বলে, তখন বললেন, ‘তাহলে তো বেশি করে ইলিশ নিতে হয়, বিশেষ করে তোমার জন্য, কেননা স্ত্রী খায় না বলে বাড়িতে তোমারও তেমন খাওয়া হয় না।’ নিশ্ছিদ্র যুক্তি একেবারে।
বলেছি সারস্বত সংসর্গ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হত তাঁর বদান্যতায়। তাঁরা কেবল শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন মননশীল লেখক। সারোয়ার জাহান, সনৎকুমার সাহা, আলী আনোয়ার প্রমুখের সঙ্গে পরিচয়, জুলফিকার মতিনের সঙ্গে, ছিল অমৃতসলিলে অবগাহন। এঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালেও যোগাযোগ ছিল আমার। সনৎদা ও জুলফিকার ছাড়া সবাই এখন লোকান্তরিত, নাজিমভাইও।
পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের সম্পর্কে হাসানভাইয়ের অতি স্বচ্ছ ধারণা ছিল। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, ভগীরথ মিশ্র, বাণী রায়ের লেখা খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়তেন। বিভূতিভূষণ নিয়ে ছিলেন অসম্ভব ভক্তিনম্র। জানতে চেয়েছিলাম, গৌরকিশোর ঘোষের ‘প্রেম নেই’ উপন্যাসে যে মুসলিম জনজীবন, তা প্রামাণ্য মনে হয়েছে কিনা। বললেন, বিস্ময়করভাবে প্রামাণ্য।
একবার ‘দেশ’ পত্রিকায় বর্ধমানের ওপর একটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলাম (লেখকের নামটা মনে পড়ছে না, তবে তাঁর পদবি ছিল দাঁ)। সেখানে বর্ধমানের লেখক-তালিকায় তাঁর নাম না থাকার ত্রুটি উল্লেখ করেছিলাম। হাসানভাই পড়েছিলেন সে লেখা। কতবার যে প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন শিক্ষকদের কাছে।
তাঁর লেখা ‘চালচিত্রের খুঁটিনাটি’-র যে অংশে ‘সন্দীপন’ নিয়ে লিখেছেন তিনি, সেখানে নগেনস্যারের নাম নেই কেন জানতে চাইলাম। জিভ কেটে বললেন, ‘নগেন! কী সুন্দর কবিতা লিখত, গান লিখত! সাধনদা সুর দিতেন সে সব গানে, পরিবেশিত হত, হয় এখনও, ঢাকা বেতারে, সত্যি ভুল হয়ে গেছে।’
প্রশ্ন করেছিলাম আরও একটি বিষয় নিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের গল্প ‘পিকুর ডায়েরি’ এবং তা নিয়ে তাঁরই নির্মিত ছবি ‘পিকু’-র কাহিনি আশ্চর্যরকমভাবে মিলে যায় হাসানভাইয়ের গল্প ‘সারা দুপুর’-এর সঙ্গে। তাহলে কি সত্যজিৎ হাসানের গল্পটি নকল করেছেন? হাসানভাইয়ের গল্পটি আগে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই এই সংশয়। প্রশ্ন শুনে নিতান্ত সৌজন্যবশতই হাসানভাই চুপ করে রইলেন, জবাব দিলেন না কোনও। এটি তাঁর অবিনশ্বর উদারতা এবং আজানুলম্বিত মহত্বের পরিচয় আমার কাছে।
চলে আসার আগের রাতে ওঁর বাড়িতে গানের আসর। ওঁর মেয়ে শবনম, ডাকনাম সুমন, তখন বিএ-র ছাত্রী, গান গাইল। নাজিমভাই একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করলেন। পরদিন ভোরে ঢাকা রওনা হলাম। বিদায়মুহূর্তে হাসানভাইয়ের মানসিকতাটি আমার স্ত্রীর একটি লেখায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে, ‘বিদায় নেবার ভোরে হাসান ভাই-এর স্তব্ধ হয়ে গিয়ে আমাকে হাত ঊর্ধ্বে তুলে আশীর্বাদ, আজীবন আমায় আবেগায়িত করে রাখবে, রাখতে বাধ্য হবে।’
দেখা হয়েছে এরপরেও বহুবার, কলকাতায়, ঢাকায়, রাজশাহীতে। ‘৯৭-তে রাজশাহীতে গেলাম যখন, ওঁর মেয়ে শবনম তখন কলকাতায়। সুবিনয় রায় এবং গীতা ঘটকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য। হাসানভাই ওর ঠিকানা দিয়ে বললেন, যেন দেখভাল করি তার। কিছুদিন পর ঢাকায় ওঁর এক পুরনো ছাত্রী শিরীনের বাসায় এলেন, সারোয়ার জাহান সহ। আমি তখন শিরীনের বাড়িতে অতিথি। একদফা আড্ডা, সারোয়ারভাইয়ের অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন। হাসানভাই যে কত বড় রসিক ছিলেন, তা মিনিট পাঁচেক তাঁর সঙ্গে মিশলেই বোঝা যেত। আদ্যন্ত রসিকপুরুষ।
কলকাতায় ফিরে শবনমের সঙ্গে দেখা করলাম। ও তখন ঢাকুরিয়ায় থাকত। মাঝেমাঝেই আমাদের বাসায় নিয়ে আসতাম ওকে। এ সময় শিরীনও এলেন আমাদের বাসায় অতিথি হয়ে। খুব জমেছিল সে সময়টা। শিরীন চলে যেতে এলন নাজিমভাই। উঠলেন আমাদের বাসাতেই। শবনম তো চাচাকে পেয়ে আত্মহারা! নাজিমভাইয়ের বাল্যবন্ধু সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি যাওয়া হল, সঙ্গে শবনম। চিঠি ও ফোনের মাধ্যমে সে সব খবর নিয়মিত পৌঁছত হাসানভাইয়ের কাছে।
১৯৯৯-এ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ফোকাল কান্ট্রি ছিল বাংলাদেশ। মেলার উদ্বোধন করতে এলেন বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন বহু সাহিত্যিক, যাঁদের মধ্যে হাসানভাইও ছিলেন। দেখা হল। দেখা হতেই বললেন, শবনমের বিয়ে সামনেই। তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে। যাওয়া হয়নি তখন। তবে এর মাস দুই পরে ঢাকা গেলাম, দেখা করলাম সুমনের সঙ্গে। এখন সে দুই কনার জননী।
হাসানভাইয়ের সঙ্গে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য স্মৃতি তাঁর আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তির দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া। জানতে চাইলাম, পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া কী? হাসানজনোচিত উত্তর তাঁর, আমার লেখাটা হল ক্রিয়া, আর পুরস্কার পাওয়াটা তার প্রতিক্রিয়া, তাই না? জানতে চাইলে বলো আমার প্রতিপ্রতিক্রিয়া কী?
এর দীর্ঘদিন পরে ঢাকা থেকে ডা. মোহিত কামাল প্রকাশিত ‘শব্দঘর’ পত্রিকায় ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করি। পড়ে উনি এতটাই খুশি হয়েছিলেন আমার ওপর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকে তাঁর আরও লেখার সমালোচনা করতে বললেন।
তাঁকে নিয়ে আরও অনেকানেক স্মৃতি আছে। বগুড়ায় সাহিত্যসভা, ২০১৮। তাঁকে একান্তে পেয়ে আখতারুজ্জামান-মহাশ্বেতা দেবী-দেবেশ রায় নিয়ে তাঁর মুগ্ধতা জানলাম, তরুণ প্রজন্মের লেখকরা, একদিকে রবিশংকর বল ও অন্যদিকে শহীদুল জহির নিয়ে তাঁর অবহিতি বিস্মিত করল আমাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অকালমৃত্যু তাঁকে বেদনার্ত করে রাখে ভিতরে ভিতরে, জানালেন।
গতবছর তাঁর রাজশাহীর বাসায় গেছিলাম, তবে করোনাকালীন পরিস্থিতির জন্য দেখা করতে পারিনি। পরে ফোনে কথা হয়েছে দু-একবার।
চলে গেছেন তিনি, রেখে গেছেন তাঁর মনীষা। এখন সেইসব সুবর্ণপিটক নিয়েই আমাদের তাঁকে শিরোধার্য করা।
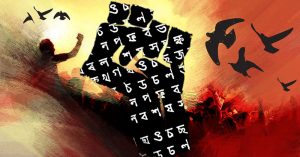
মাতৃভাষা: অবিনাশী হৃৎস্পন্দন ও বিশ্বজনীন উত্তরাধিকার
প্রতিটি ভাষার নিজস্ব একটি আলো আছে, সে নিজের দীপ্তিতেই ভাস্বর। পৃথিবীতে আজ প্রায় সাত হাজার ভাষা আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই শতাব্দীর শেষে তার অর্ধেকেরও বেশি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ তথ্য সত্যিই বেদনাদায়ক। একটি ভাষার মৃত্যু মানে কেবল কিছু শব্দের মৃত্যু নয়— সে মানে একটি জগৎদর্শনের অবলুপ্তি, একটি জাতির স্মৃতির চিরকালীন বিনাশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক বহুমাত্রিক। নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসা, তাকে চর্চায় রাখা, তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর তার সাথে অন্য সমস্ত ভাষার প্রতি আরও বেশি করে শ্রদ্ধাশীল হওয়া।








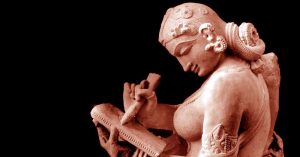





2 Responses
Valo lekha
ভালো লাগলো মলয় দা’।