রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। কেবল আলঙ্কারিক অর্থেই নয়, প্রকৃত-ই। ‘আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যতো উঠে ধ্বনি/ আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,’— তাঁর এই উচ্চারণ আক্ষরিকভাবেই সত্য। কবিতা, গান, প্রবন্ধ এবং নাটকে বৈশ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়, তা সে চীনে ইংরেজদের আফিমের ব্যবসার দুর্বিষহতা-ই হোক, কিংবা আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ, বা চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, অথবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রুজভেল্টকে লেখা তাঁর উৎকণ্ঠিত চিঠি।
আবার প্রবলভাবে তিনি ভারতীয়। বেদ-উপনিষদে তাঁর আকৈশোর অবগাহন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণে তিনি বোলপুরে গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। মারাঠী সাধক তুকারামের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন, আর কবীরের দোঁহা ইংরেজিতে। তবু এসব সত্ত্বেও তিনি আদ্যন্ত বাঙালি। মনেপ্রাণে বাঙালি। আর এই বাঙালিত্ব অর্জিত হয়েছিল শৈশবে গৃহের পরিবেশে। ছোটবেলাতেই যোগ্য শিক্ষকদের হাতে তাঁর ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা চললেও বাড়িতে তাঁকে বাংলাও দস্তুরমত শিখতে হয়েছে সেজদা হেমেন্দ্রনাথের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-তে লিখছেন, ‘যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।’
রবীন্দ্রনাথের বাঙালিত্ব অর্জিত হয়েছিল নানাপথে। বাড়িতে বাংলা বইয়ের অফুরন্ত সম্ভার, বাংলা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সাম্প্রতিকম লেখার সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, তাছাড়া ঠাকুরবাড়ি থেকেই প্রকাশিত হত একাধিক পত্রিকা,— তত্ত্ববোধিনী, বালক, ভারতী। কিশোর বয়স থেকেই এসব পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের যে সমালোচনা লিখেছিলেন, তা পড়ে বোঝা যায়, মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস-রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র তো বটেই, এমনকি হরুঠাকুরের পাঁচালীও তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল ওই বয়সের ভিতর। মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে যিনি শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদের সাহস রাখেন, তাঁর মাতৃভাষায় পারদর্শিতা অসংশয়িত।
কৈশোরে সাহচর্য পেয়েছেন বিহারীলাল, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের। আর শিলাইদহ-পর্বের টানা দশবছর তিনি গাঢ় স্নান করেন বাংলার ভূপ্রকৃতি আর সহজ গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে, যা তাঁর বাঙালিত্ব অর্জনের মহীসোপান। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন, ‘…কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মূষলধারাবর্ষণে।… এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসঙ্গম চলছিল। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।… সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে’ (সূচনা, ‘সোনার তরী’)।
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ ছিল না। বিশ্বভারতীতে তিনি বক্তৃতা দিতে উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে, কাজী নজরুল ইসলাম, আলাউদ্দীন খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদকে। গান শেখাতে আবদুল আহাদকে। বন্দে আলী মিয়া, জসীমউদ্দিন প্রমুখকে তিনি কাহিনির প্লট বলে দেন, যেমন দেন গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে পড়েন তাঁর-ই বদান্যতায়। লালন শাহ্ তাঁর কল্যাণেই পরিচিতি পান ইংল্যান্ড তথা ইয়োরোপে। বঙ্গভঙ্গকালীন সময়ে কলকাতার নাখোদা মসজিদে গিয়ে তিনি মুসলমানের হাতে রাখী পরিয়ে আসেন। বেগম সুফিয়া কামাল, আবুল ফজল, আবুল হোসেনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলে, যেমন চলে হেমন্তবালা দেবী, বুদ্ধদেব বসু বা বনফুলের সঙ্গে। এক অখণ্ড বাঙালিয়ানায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, জাতপাত, বর্ণ বা ধর্মের ঊর্ধ্বে।
নবজাতকের নামকরণে রুচিকর বাংলা শব্দ খুঁজেছেন, বৃক্ষলতাদির নামকরণেও। অমর্ত্য, নবনীতা, শান্তিদেব, কণিকা, চিত্রলেখা নামগুলি তাঁর-ই দেওয়া, যেমন বীলমণিলতা, সোনাঝুরি নাম রাখেন গাছেদের। আবার উত্তরায়নের বাড়িগুলির নাম শ্যামলী, কোনার্ক, উদীচী, উদয়ন, এসব-ও তাঁর দেওয়া। আম্রকুঞ্জ, তালধ্বজ, শালবীথি, এসব নাম-ও। বিজয়া (ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো), নলিনী (আনা তড়খড়), হৈমন্তী (অমিয় চক্রবর্তীর বিদেশিনী স্ত্রী হিওর্ডিস সিগার্ড [Hjordis Siggard])-কে, হিমের দেশ ডেনমার্কের মেয়ে বলে), এরকম বহু উদাহরণ পাই।
নিজের বহু লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সর্বদাই আগে বাংলায় লিখে তারপর তার অনুবাদ করতেন। অর্থাৎ প্রাথমিক ভাবনাটা মাতৃভাষার মাধ্যমেই মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হত। একমাত্র ব্যতিক্রম ‘The Child’ কবিতাটি। এটিই তিনি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে ‘শিশুতীর্থ’ নামে এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

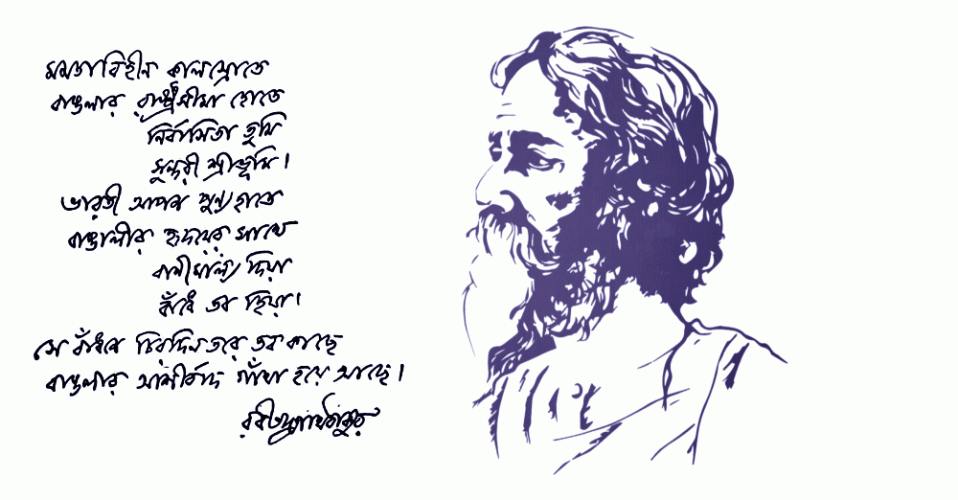













রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে নিজেদের জমিদারি বাঁচাবার জন্য এবং মুসলিম প্রজাদের ঠান্ডা করার জন্য নীচ জাতের হিন্দু প্রজাদের বসিয়েছিলেন – অন্য রবীন্দ্রনাথ