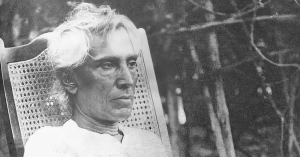বাড়ির বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়া এবং বাল্ব পাল্টানোর সঙ্গে ‘ওয়াট’ (Watt) শব্দটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ‘ওয়াট’ শব্দটির সঙ্গে কম-বেশি সকলেরই পরিচয় আছে। ‘ওয়াট’ আসলে শক্তির (Power) একটি একক। মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার বা শক্তি বোঝাতে বা ইলেকট্রিক-লাইটের বাল্ব বা মেশিন-পত্তরের শক্তি বা ক্ষমতা-র (Power) পরিমাপ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এই একক। কিন্তু কোত্থেকে এসেছে এই ওয়াট শব্দটি? অনেকেই হয়তো জানি, ‘জেমস ওয়াট’ (James Watt) নামের উদ্ভাবক, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীর সম্মানেই বৈদ্যুতিক শক্তি এবং তাপের একক হিসেবে ‘ওয়াট’ শব্দটি এসেছে।
কে ছিলেন এই জেমস ওয়াট? এই লেখায় অতি সংক্ষেপে সেই জেমস ওয়াটের কথা জানব আজ।
১৭৩৬ সালে স্কটল্যান্ডের একটি জায়গায় এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবারে জন্ম হয় জেমসের। তাঁর বাবা-র নামও ছিল জেমস ওয়াট। বাবা ছিলেন একজন সুদক্ষ কারপেন্টার। জাহাজ তৈরি করার একজন মেকানিক ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন কন্ট্রাক্টরও। তাঁর নিজেরও একটি জাহাজ ছিল। বাড়িতে যন্ত্রপাতি তৈরি করা এবং সারানোর জন্যে একটি ছোটখাটো ওয়ার্কশপের মতও ছিল তাঁর। সেই ওয়ার্কশপে থাকত প্রয়োজনীয় মেশিন টুলস। এমনকি সেখানে মেটাল-ফর্জিং করার ব্যবস্থাও ছিল। সেই ওয়ার্কশপের প্রতি বালক জেমসের ছিল দারুণ আকর্ষণ। বাবার কাছে এখানেই বালক জেমসের প্রথম ক্রাফটিং-এর হাতেখড়ি হয়।
জেমসের মা-ও পড়াশোনা জানতেন। ছোটবেলায় মায়ের কাছে অন্যান্য বিষয় এবং বাবার কাছে নিয়মিত অংক শিখেছেন জেমস। প্রাইমারি এবং পরে হাইস্কুলে পড়াশোনা করলেও জেমস বেশি পছন্দ করতেন বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করতে। নৌকো নিয়ে জেলেদের মাছ ধরে ফিরে আসা দেখতে পেতেন বাড়ির দাওয়ায় বসে। মাঝে মাঝে অদূরে বন্দরে জাহাজের ফিরে আসা দেখতেন বালক জেমস। সেই পালতোলা জাহাজ যে একদিন স্টিম-ইঞ্জিনেও চলতে সক্ষম হবে, তখন এমন কোনও স্বপ্ন জেমসের মাথায় এসেছিল কি না, আজ আর তা জানার কোনও উপায় নেই।
তবে তদানীন্তন পুরোনো মডেলের স্টিম ইঞ্জিনের সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয়েছে আরও অনেক পরে। জেমসের যখন মাত্র আঠারো বছর বয়স, মা মারা যান। তারপর থেকে বাবারও শরীর খারাপ হওয়া শুরু হয়। খারাপ সময় যখন আসে, সব কিছু যেন এক সঙ্গেই আসে। সেসময় থেকে বাবার ব্যবসাতেও নেমে এল চরম মন্দা।
তারপর এক বছরের জন্যে লন্ডনে গিয়ে নানান ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট তৈরির কাজ শিখে ফিরে এলেন জেমস। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাস্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্টে যন্ত্রপাতি সারানোর একটি অস্থায়ী কাজ পেলেন জেমস। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ধরনের নানান ইন্সট্রুমেন্টের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। যন্ত্রপাতি সারানো এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে জেমসের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মেধা দেখে, তাঁর ইউনিভার্সিটির চাকরিটি স্থায়ী হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সেখানকার কর্তৃপক্ষ জেমস-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ওয়ার্কশপ নির্মাণেরও দায়িত্ব দিলেন। ফিজিক্স এবং গণিতে জেমসের পড়াশোনা এবং জ্ঞানের গভীরতা সেখানকার অধ্যাপকদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জেমসের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান আর ব্যুৎপত্তি দেখে অধ্যাপকরা ক্লাসে যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কিছু পড়ানোর সময় মাঝে মাঝেই জেমস-কে ডেকে পাঠাতেন।

তখন কতই বা বয়স জেমসের। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। এর আগে জেমস শুনেছিলেন ‘নিউকমেন’ (Thomas Newcomen) নামের একজন প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে, স্টিম–এ চলতে সক্ষম সে ধরনের একটি ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে একজন অধ্যাপক ছাত্রদের দেখাতেন সেই ‘নিউকমেন ইঞ্জিন’। একদিন সেই ক্লাসে ডাক পড়ল জেমসের। ইঞ্জিনটি বিকল হওয়ায় তা সারানোর দরকার পড়েছে। তখন-ই আশ্চর্য হয়ে জেমস লক্ষ্য করেছিলেন, কত সামান্য শক্তি নিউকমেন মডেলের সেই ইঞ্জিনের! যাইহোক, বিকল ইঞ্জিনটি সারিয়ে তুললেন জেমস। কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হল তাঁর নতুন সিস্টেম-এ আমূল পরিবর্তন করে উচ্চ ক্ষমতার ইঞ্জিন তৈরির চেষ্টা। সেই কাজেও বছর দুয়েকের মধ্যে সফল হলেন জেমস ওয়াট। আশি শতাংশ কম জ্বালানি ব্যবহার করে জেমস ওয়াটের এই স্টিম ইঞ্জিন (বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত)। জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিনের এই উদ্ভাবনার সময়কেই অনেকে মনে করেন শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল।
তাঁর সম্বন্ধে বিশ্ববন্দিত রসায়ন বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি যা বলেছেন সেই কথাগুলি পড়ি— ‘James Watt was equally distinguished as a natural philosopher and chemist; his inventions demonstrate his profound knowledge of those sciences, and the peculiar characteristic of genius— the union of them for practical application.’
জেমস ওয়াটের মৃত্যুর দুশো বছর পেরিয়ে এসেছি। এই ব্রিটিশ ‘ম্যাথেমেটিক্যাল-ইন্সট্রুমেন্ট-মেকার’ ও ইঞ্জিনিয়ারকে আজ অন্তত একবার মনে করা দরকার। আরও একাধিক মেশিনারি উদ্ভাবনের সঙ্গে স্টিম ইঞ্জিনের আমূল পরিবর্তন করে নতুন রূপ দিয়েছেন তিনি। ‘লেটেন্ট-হিট’-এর (লীন তাপ) ধারণা দিয়েছেন উদ্ভাবনকারী ও ইঞ্জিনিয়ার জেমস ওয়াট। তাঁর উদ্ভাবনার সময়কাল থেকেই শিল্পবিপ্লবের শুরু হিসেবে ধরা হয় এবং ‘Father of the industrial revolution’ হিসেবে তাঁকে মান্যতা দেওয়া হয়। গ্লাসগো সিটি-সেন্টারের জর্জ স্কোয়ারে জেমস ওয়াটের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।
আজ ১৯ জানুয়ারি। জেমস ওয়াটের (১৭৩৬-১৮১৯) জন্মদিন। এই মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার, উদ্ভাবক, রাসায়নিক ও দার্শনিককে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।