ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (২৬.০৯.১৮২০-২৯.০৭.১৮৯১) অন্তহীন অবদানের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদানকে শীর্ষে রাখতে হবে, কেননা হাজার-দুই বছরের নারীসমাজের পশ্চাৎপদতা দূর হয় তার ফলে। আজ আমরা বাঙালি-সমাজে নারীর যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখি, তার প্রকৃত ভগীরথ নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর। আর কেবল বাঙালির-ই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও যে তাঁর ভূমিকা ছিল, তার প্রমাণ, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার বাইরেও সামাজিক আন্দোলন, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, বিধবাবিবাহ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।
স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ আর শিশু এবং নারীদের জন্য গ্রন্থরচনা (বর্ণপরিচয়, শকুন্তলা) তাঁর ত্রিমুখী কর্মধারা। বিজ্ঞানমনস্কতা তা্ঁকে একদিকে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ‘Indian Association for the Cultivation of Science’-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে অন্যদিকে বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে আগ্রহী করেছে।
তিনি তাঁর প্রগতিশীল ভাবধারা অর্জন করেন ১৮৩৮-এ ডিরোজিওর ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’-র সভ্যরূপে। এটি অবশ্য ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত হত।
তিনি ছিলেন বাল্যবিবাহবিরোধী, যদিও তাঁর বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে, ছ’বছরের কন্যার সঙ্গে। ১৮৭২-এ যে তৎকালীন সরকার তিন আইন পাশ করে, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ষোলো বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়া, বহুবিবাহ রোধ, এবং অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতির জোরে ১৮৮৩-তে প্রথম মহিলা বাঙালি চিকিৎসক কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে বিয়ে হতে পেরেছিল দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। আর বিদ্যাসাগর ১৮৫৬-তেই বিধবাবিবাহকে সরকারের মাধ্যমে আইনি স্বীকৃতি দেবার ভূমিকা পালন করেন। কেবল তা-ই নয়, নিজের উদ্যোগে শতাধিক বিয়ে দেন, সেই যুগে সর্বমোট বিরাশি হাজার টাকা ব্যয় করে (সূত্র: ইন্দ্র মিত্র, ‘করুণাসাগর বিদ্যাসাগর’)!
তবে ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে বিদ্যাসাগরের আগে ডিরোজিয়ানরাও বিধবাবিবাহে সোচ্চার ছিলেন। মুঘল আমলে স্বয়ং সম্রাট আকবর-ও চেষ্টিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িককালে অনেকেই। যেমন ১৮৪২-এ ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’ বিধবাবিবাহের সপক্ষে প্রবন্ধ ছাপে। জনৈক লেখক প্রশ্ন তোলেন, ‘বিধবাদের শরীর কি শরীর নয়? তাহারা কি মহাবল ইন্দ্রিয়বলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে’?

তবু বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ অচ্ছেদ্য। তাঁর ‘বিধবাবিবাহ প্রচারিত হওয়া উচিত কি না’ অকারণে পনেরো হাজার কপি ছাপতে হয়নি। অকারণে শান্তিপুরের তাঁতিরা কাপড়ে একথা বুনে দেননি ‘বেঁচে থাকুন বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/ সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের বিয়ে’! বিদ্যাসাগরের প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্রী লক্ষ্মীমণি এই শান্তিপুরের-ই মেয়ে।
বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে নারীমুক্তির অগ্রদূত। তবে আশ্চর্য লাগে ভাবতে, তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে নবাব ফয়েজউন্নিসাও (১৮৩৪-১৯০৩) যে নারীমুক্তির মশাল হাতে বিস্ময়কর কাজ করে গেছেন, তার খোঁজ তিনি পাননি! বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, নারীদের জন্য চিকিৎসালয় পর্যন্ত স্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগর জানলে খুশি হতেন, ১৮৮৯-তে ব্রিটেনের মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে ‘নবাব’ খেতাব পাওয়া ফয়েজউন্নেসা সংস্কৃত জানতেন। আর ১৮৬৫-তে যে বঙ্কিমের উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বেরোয়, তার মাত্র এগারো বছরের মাথায় ১৮৭৬-এ আত্মপ্রকাশ করে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার বাইরে সম্পূর্ণ নিজের অধ্যবসায়ে লেখাপড়া শেখা ফয়েজউন্নিসার। তাঁর ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভাব ‘রূপজালাল’ লিখে! বিদ্যাসাগর আছেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব-বলয়ের বাইরে থেকেও রাসসুন্দরী দাসী, বিনোদিনী, ফয়েজউন্নিসা, বেগম রোকেয়া প্রমুখ যে কী কঠিন প্রতিকূলতা ভেদ করে উঠে এসেছেন, তার ইতিহাস লেখা হয়নি আজ-ও। বিদ্যাসাগর এবং এঁদের সমান্তরাল পাঠ জরুরি।
সংস্কৃত ভাষাকে সহজে অধিগত করতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে জলবৎ তরলং করে হাজির করলেন ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ লিখে, আর বিশ্বের দু-প্রান্তের দুই যুগন্ধর নাট্যপ্রতিভাকে নিজস্ব অনুবাদরীতিতে কাছে এনে দিলেন,– কালিদাসের ‘শকুন্তলা’ আর শেকসপিয়ারের ‘Comedy of Errors’ (অনুবাদে নাম দেন ‘ভ্রান্তিবিলাস’)। বাঙালি শিশুমাত্রকেই শেখালেন ‘বর্ণপরিচয়’। মধুসূদনকে ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধারে প্রয়াসী তিনি বারবার। পঞ্চদশ শতকে ইওরোপের যে নবজাগরণ, তার-ই বার্তাবহ তিনি, তাই যুক্তিবাদ তাঁর আশ্রয়, বিজ্ঞান তাঁর সতত আরাধ্য, নারীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ তাঁর ইহলোকের ধ্যান।
সমসময় তাঁকে চেনেনি। বরং সর্বপ্রযত্নে বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে তাঁর প্রগতিশীল কাজকর্মকে। এই সময় ও বাঙালি সমাজ-ও কি চিনেছে তাঁকে? তাঁকে তাই শেষ জীবন কাটাতে হল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী থেকে দূরে সাঁওতাল পরগনায়। শেষ বয়সে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি, যাদের জন্য তাঁর এই কাজ, সব অপাত্রে দান! তাই ক্ষোভের সঙ্গে লিখে গেছেন, ‘এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়।’ বাঙালি সম্পর্কে এর চেয়ে মর্মান্তিক, চূড়ান্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উক্তি ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত আর হয় না।






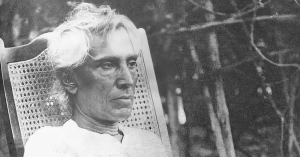







ভেতরকার অনেক সত্য জানা গেল।