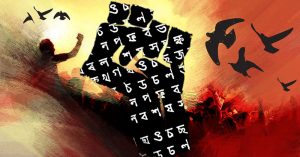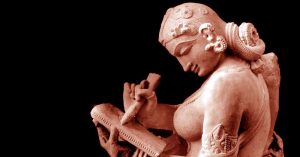অবিস্মরণীয় নজরুল
‘বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী’– তাঁর ‘আমার কৈফিয়ত’ পড়ে মনে হল নজরুল ইসলাম তাচ্ছিল্যের হাসিতে ফেটে পড়েছেন। উত্তরসূরিরা তাঁর মূল্যায়নে যে রকম লাজনম্র নববধূর মতো দ্বিধাকম্পিত বাক্যরাশি নিবেদন করে চলেছেন, এতটা তাঁর দূর প্রত্যাশায়ও ছিল না। নজরুলকে নিয়ে বাঙালি শিল্পীসমাজের, বিশেষত কবিদের, অস্বস্তির শেষ নেই। তাঁকে বাতিল করা যায় না স্বভাব-কবি বলে, কিন্তু গ্রহণ করায় সমস্যার ব্যাপ্তি প্রচুর। আমাদের সান্ধ্য লিরিক-বিতানে নজরুল প্রায় এক সাংস্কৃতিক উপদ্রব। যেন ইতিহাসের আয়নায় একটা ফাটা দাগ; যতই অপচয়িত প্রতিভা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, যে দিক দিয়েই তাকাই, পারা যায় না। জনতার সামনে ও সখ্যে তিনি আছেন। রূপসীর অধরোষ্ঠের পাশে একটি নিষ্প্রয়োজনের তিল যেন, কিন্তু উপেক্ষার উপায় নেই। সরকার আসে। সরকার যায়। কিন্তু উভয় বঙ্গেই সীমানা-নিরপেক্ষ ভাবে নজরুল ইসলামের ছাড়পত্রে সমর্থনের সিলমোহর গাঢ় থেকে গাঢ়তর ছাপ ফেলে যায়।
আমাদের যেমন সাহিত্যবিচার তাতে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এমনকী বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি যে অনুরক্তির আতিশয্যের মধ্যেও নজরুলের কাব্যে যে প্রবল অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমরা ভুলে যাই না। বরং দিনের পর দিন বঙ্গীয় কবি সমাজের অবস্থান, তাঁর প্রসঙ্গে, কঠোর হয়ে যাচ্ছে। সৌজন্যের মলাটে মুড়ে রাখা অবজ্ঞার ভঙ্গি খুঁজে পেতে সাধারণ বুদ্ধির অতিরিক্ত আর কোনও চর্চার দরকার পড়ে না। নজরুল যেন সত্যিই কাব্যের অতিশয়োক্তি; বিয়ারের উপচে পড়া ফেনা। এই তো সদ্য সদ্য আবার শামসুর রাহমানের ‘কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি’ নামের রচনাটি পড়ে উঠলাম। সেখানেও তো একই অনুযোগ যে ‘কবিতা তার স্তনের গোলাপকুঁড়ি’ উন্মোচন করলেও ‘গোলাপের উজ্জ্বলতা ছেড়ে’ নজরুল ‘বাগ্মিতা নামের দজ্জাল মেয়ের কাছে’ কেন ছুটে গেলেন! ফলাফল? শামসুর রাহমান সখেদে জানান– ‘যার ক্ষিপ্ত তুমুল নর্তনে স্বপ্নগুলি/ পড়লো ছড়িয়ে ভাঙা ঘুঙুরের মতো।’ আর বুদ্ধদেব বসু ‘প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস’ বিষয়ে সশ্রদ্ধ অবলোকনের প্রমাণ রাখলেও বলতে সঙ্কোচ করেননি– ‘যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে তিনি হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন’।
যারা তাঁর স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে প্রচারিত সেই বামপন্থীরাও নজরুলের উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করেন না। ম্যাকসিম গোর্কি একদা আলেকসেই তলস্তয়কে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তাঁর ‘অন্তর্গত নৈরাজ্য’ তাঁর প্রতিভার প্রাপ্য স্বীকৃতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নজরুল প্রসঙ্গেও ধ্রুপদী বামপন্থীদের আক্ষেপ অনেকটা এই রকম। নজরুলের কবিত্বে কলঙ্ক প্রচুর। সে সব দাগ মোছার কোনও অর্থ হয় না। সে তো ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেও অজস্র পদস্খলন। যেমন সাংবাদিকতা ও ভাঁড়ামি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত না থাকলে মধুসূদনকে হয়তো আধুনিকতার প্রবর্তক হিসেবে চেনা যেত না। নজরুলের ছেলেমানুষী না থাকলে জীবনানন্দের হাতে ভাষা আচমকা এত রূপবতী হয়ে উঠত না। নজরুল এক মস্ত ত্বরণ– তাঁকে অনুঘটক হিসেবে পেয়েই বাংলা ভাষা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে সক্ষম হল।
যদিও বলা হয় তাঁর সম্পর্কে, তবু নজরুল ধূমকেতুর মতো মহাকাশ রহস্য কিনা সন্দেহ আছে। নজরুলের অপরিকল্পিত উচ্ছ্বাস আমাদের ভাষার ঐতিহ্যগত সম্মোহন তছনছ করে দিয়েছিল। শব্দের নিয়ন্ত্রণহীন কাঁপন, ছন্দের অসংযম তো কমলবনে মত্ত কুরঙ্গবৎ। এই কবি, আজ মনে হয়, ভাগ্যক্রমে মনীষার পূজারী ছিলেন না। এই স্বভাব অ্যাজিট-প্রপ যে ভাবে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্লাবন ঘটিয়েছেন তাতে তত্সম ও তদ্ভব শব্দের আশ্রয়ে লালিত অনেক তপোবনের বিপর্যয় ঘটেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হাজার হোক, রবীন্দ্র অনুসারী। তাঁর পক্ষে অবিবেচনাপ্রসূত উন্মাদনা অসম্ভব। নজরুলের ভাষা সুষম যৌগ নয়, অনেকটা সংকর পদার্থ। কিন্তু ভাষার সুস্থিতি নড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে এই নোনাজল যথেষ্ট। ‘যোনিচক্রস্মৃতি’– এমন দু’একটি শব্দ ছাড়া জীবনানন্দের প্রথম বই ‘ঝরা পালক’ তো নজরুল সমীপে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত নমুনা। মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন সেনগুপ্ত– দু’জনেই বাংলা ভাষার বহমানতাকে প্রশ্ন করেননি। প্রথম জন বড় জোর মাতৃভাষাকে ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন দার্ঢ্য ও দ্বিতীয় জন সন্দিগ্ধ নাট্য। ভাষার ভারসাম্য ভেঙে দেওয়ায় নজরুলের অপরিণামদর্শী হানাদারি ইতিহাস বরং আকাঙ্ক্ষাই করেছিল। তার প্রমাণ সে যুগের শহরে মফস্সলে ছড়িয়ে থাকা যুবজনতার সমর্থন।
কী দুর্জয় সাহসে যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করেছিলেন! আর তাঁর স্বজাতিও তো সহ্য করেছিল সে সব পরুষবাক্য ও তিরস্কার। বসনহীনা সরস্বতী আঁকা যাদের কাছে আজ অপরাধ তাঁরা নজরুলের মতো বিধর্মী ভৃগু যে ভগবান-বুকে পদচিহ্ন আঁকতে সংকল্পবদ্ধ– জানতে পারলে কি পরিমাণ কুপিত হতেন আজ ভাবলেও শঙ্কা হয়! অন্য দিকে ‘খোদার আসন আরশ ছেদিয়া’ যে বিদ্রোহ বাসনা তা কখনওই কোনও মৌলবাদী বিশ্বাসের দ্বারা স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হওয়ার কথা নয়, তবু তো নজরুল নিজবাসভূমে পরবাসী ছিলেন না। তবে কি সে যুগে ধর্মবিশ্বাস ও প্রথাপালন আজকের মতো অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর ছিল না? উত্তর হাতের কাছে নেই কিন্তু নজরুলকে যে ‘হিন্দুর আফজল’ হতে হয়নি তার নিদর্শন তো তাঁর কাব্যে, গানে থরে থরে সাজানো রয়েছে।
মার্কসবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির মুসলিম সদস্য যদি ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্বার্থে নির্বাচনী প্রচারে হনুমানের চরণবারি পান করেন, যদি হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে মসজিদের ‘দোয়া’ নিতে হয় সংখ্যালঘু প্রীতির স্মারক হিসেবে তবে তা সেকুলার পরাবাস্তবতার চিহ্ন হোক বা না হোক নজরুলের বাস্তবতা হল এই যে, ঈদের দরগা ও তুলসীতলাকে তিনি বন্ধনীভুক্ত করতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সন্তানের সংলাপে কোনও মধ্যস্থতাকারীর তোয়াক্কা করেননি। ‘মৌ-লোভী যত মৌলবী’ তাঁর জাত মেরে দিয়েছে কিন্তু হিন্দু পুরুত তার জন্য তাঁকে ‘পাত নেড়ে’ বলার অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। নজরুলের জয় এখানেই যে, সংসদীয় নাস্তিকরা তাঁর মতো বেপরোয়া আস্তিককে দেখলে লজ্জায় মুখ লুকোয়!

একটা যুগ তাঁর ওষ্ঠে থরথর করে কেঁপেছে। ধর্মীয় ঘেরাটোপের বাইরে একটা জীবন যত রঙিন হয় ততটাই রঙিন ছিলেন তিনি। এক জন আধুনিক যতটা ধর্ম-অতিরিক্ত পরিসরে থাকতে পারেন সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় ততটাই ছিলেন কাজী নজরুল। হাত পেতে পান নিয়েছেন কিন্তু পারিতোষিক নেননি। অনিয়মের ব্রত পালন কম কথা নয়! স্বাধীন জীবনযাপন কম কথা নয় মোটেই!
উক্তির স্মরণযোগ্যতা যদি কবিতার অন্যতম শর্ত হয়, তবে নজরুলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/ কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র’। অথবা ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই’, এই পঙক্তিগুলির রচয়িতা কে সে কথা না জানলেও বাংলার পথেপ্রান্তরে এ সব লাইন ছড়িয়ে আছে, যেমন রামপ্রসাদের গান। যদি এই বিদ্যুৎ লেখাগুলিকে উপেক্ষাও করি, তবেও দেখব ‘আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি’, যিনি লিখতে পারেন তার কবিত্ব বোধ সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ নেই।
নজরুল আসলে আধুনিক কবিদের মতো নিজেকে ভাষার প্রদেশে সঙ্কুচিত রাখেননি। সেখানেই তাঁকে বোঝার পক্ষে আমাদের ভুল হয়ে যায়। তিনি আদিকবিদের মতো। সমাজের অসুস্থতার নিরাময় দাবি করেছেন প্রগলভতার মধ্যে। তিনি যদি নিতান্ত ভাষাকর্মী হয়ে জীবন নির্বাহ করতেন তাঁকে বিচার করার সময় আমাদের এত অসুবিধে হত না। বদলে তিনি তখনও কংগ্রেসের অহিংস নীতি, তখনও স্বরাজ্য দলের মধ্যপন্থাকে তছনছ করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছিল, দুর্ভাগা সেই দেশ যার এখনও কবিকে ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়ের মধ্যে দেখবার প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগা সেই দেশ যার বীরের প্রয়োজন হয়। ফলে তিনি কবি ও দেশনেতা দুই মূর্তিরই গায়ে কালি ছিটিয়ে দিলেন, তাতে সময় তাঁকে অধরোষ্ঠ দান করল, কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিকরা বিরক্ত হলেন। নজরুলকে আমি বলব না যে, তিনি মায়াকোভস্কির মতো ‘পাতলুন পরা মেঘ’ লিখতে পারতেন। তিনি তত দূর প্রতিভাবান ছিলেন না। কিন্তু যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তাকে অকাতরে দান করেছেন। নজরুল যখন বোহেমিয়ান হয়েছেন, তখন আকাশ বাতাস তাঁর উন্মাদনা দেখেছে। তিনি কলঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু প্রসাধিত নৈরাজ্য তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি অন্তরে এবং বাইরে যখন ভুল করতেন, তখন একই রকম ভুল করতেন আর সেই জন্যই যখন সময়ের ডাকে সাড়া দিতেন, তখন বঙ্গভাষী জনসমষ্টি অজস্র ভিড়ের মধ্যে থেকেও তাঁর কণ্ঠস্বর আলাদা করে চিনতে পারত।
যেমন গান, এ কথা সত্য যে, সঙ্গীতেও তাঁর শৃঙ্খলা ছিল না। ফুলের জলসা থেকে তিনি জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিতে পারতেন যে কোনও মুহূর্তে যুক্তিরহিত ভাবে। লিখতে পারতেন মার্চিং সং। তার পরমুহূর্তেই বাইজির পায়ের নুপূর অসঙ্গত ভাবে বেজে উঠত তাঁর গানে আর কখনও অকারণে উদাসীন এক কবি লিখে ফেলতেন– ‘ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান/ আসিবে আজি বন্ধু মোর’। নজরুল এ রকমই। অসঙ্গতির শব্দরূপ– সাবধানি, সদা সর্বদা সঙ্গতি-প্রেমিক উত্তরসূরি তাই তাঁর দেখা পায় না সহসা।
চিত্র: গুগল