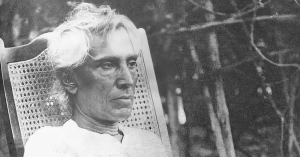শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.০৯.১৮৭৬-১৬.০১.১৯৩৮; বাংলা ৩১-এ ভাদ্র, ১২৮৩-২রা মাঘ, ১৩৪৪) কেবল বাংলার নয়, সমগ্র উপমহাদেশের এক বরেণ্য লেখক। ভারতীয় প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাস, তাঁর লেখা কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য চলচ্চিত্র, হয়েছে নাটক,– মঞ্চে, বেতারে, দূরদর্শনে, পাড়ায় পাড়ায়। কেবল ‘দেবদাস’ উপন্যাসটি-ই তো বাংলা, হিন্দি, তামিল, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষায় কম করে দশবার চিত্রায়িত হয়েছে, যা বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অনন্য। আর তাতে অভিনয় করেছেন কে. এল. সায়গল, দিলীপকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়া, নাগেশ্বর রাও, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শাহরুখ খান, জুবাইদা (প্রথম ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী), চন্দ্রাবতী দেবী, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, বেণু নাগাভাল্লি, ঐশ্বর্য রাই, মাধুরী দীক্ষিতের মতো বিখ্যাতরা।
শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর কাহিনি নিয়ে বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তাঁর সব কাহিনির চিত্রস্বত্ব কিনেছিলেন কানন দেবী, নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা ‘শ্রীমতী পিকচার্স’-এর মাধ্যমে বানাবেন বলে। বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা-ও করেছেন তিনি। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আর কোনও লেখকের ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে কি? শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সমসাময়িক এমন কোনও শিল্পী-সাহিত্যিক নেই, যাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি তাঁর প্রতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আনেন শরৎচন্দ্রের নাম, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অপুকে তার মাস্টারমশাই লেখা চালিয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, শরৎচন্দ্রের মতো লেখক হতে না পারলেও– এটাও একটা কমপ্লিমেন্ট বৈকি!
কোন গুণে শরৎচন্দ্র এত গুণী, যেজন্য আজ-ও স্মরণীয়, বরণীয় তিনি?
প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, নারীর প্রতি তাঁর সংবেদনশীল মন। বাঙালি নারীর সুখদুঃখ বেদনা হাসি কান্না-ই কেবল নয়, তার তিতিক্ষা, প্রেম, প্রয়োজনে গর্জে ওঠা, সততা, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তাদের যে বহুমাত্রিকতা, একের পর এক রচনায় তার চমৎকার বিশ্লেষণ আছে শরৎচন্দ্রে। কিন্তু তা কি নেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায়? আছে, তবে তার মাত্রাগত ফারাক রয়েছে। বঙ্কিমের আয়েশা, তিলোত্তমা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, রোহিণী, শৈবলিনী অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের সুচরিতা-লাবণ্য-দামিনী-এলা-চারুবালা (চারুলতা নয়, ‘নষ্টনীড়’-এর নায়িকার নাম কিন্তু আসলে চারুবালা), ভোলা যাবে না এদের। তবু, তবু শরৎচন্দ্রের নারী অনন্যা।
সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। ‘শাস্তি’ গল্পে চন্দরা স্বামীর প্রতি অভিমান করে নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বাঁচতে চায়নি। নিরুপমার বাবা প্রান্তিক অর্থনৈতিক অবস্থার লোক হয়েও মেয়ের বিয়েতে তিনহাজার টাকা যৌতুক দিতে রাজি হয় কেবল নিরুপমার ট্র্যাজেডিকে সম্ভব করে তুলতে। বাস্তবে কোনও পাত্রের বর এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করবে না। শরৎচন্দ্রের নারী বাস্তবে পা দিয়ে মহত্ব ও বৈচিত্র্যে অসাধারণ, যেমন অচলা, বিরাজ, সুনন্দা, কমল (‘শেষ প্রশ্ন’)। সংসারের বৈরিতাকে জয় করে কুসুম, রমা, সরযূরা। ‘ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি’ অন্নদাদি। আর কিরণময়ী, সাবিত্রী, অভয়াদের তো আমরা এখনও অভিনন্দনের ভাষা খুঁজে পাই না!
শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যের নিরিখে পাঠ করা জরুরি। বিশ শতকের সূচনায় ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে মানুষের মৌলিক পরিবর্তন ঘটছিল, যার প্রতিফলন দেখা যায় সে সময়কার ভারতীয় সাহিত্যে। শরৎচন্দ্রের যুগেই মুনসী প্রেমচাঁদ ‘নির্মলা’, উপন্যাসে বিধবা মেয়ের কাহিনি আনলেন, ‘গোদান’-এ আনলেন দরিদ্র কৃষকের হাহাকার ও আয়রনিকে। ওড়িয়া লেখক ফকিরমোহন সেনাপতির ‘ন মণ আট গুণ্ঠ’-তে আছে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি অত্যাচার ও নারীর অসহায়তা। আবার আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার গল্পে-উপন্যাসে পাই অসমিয়া মধ্যবিত্ত নরনারীর জেগে ওঠার সাহস ও বিপণ্নতা। অথবা কেরালার তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই ‘চেম্মিন’ উপন্যাসে সমুদ্রপারের জেলেজীবনের সংগ্রামকে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও পরিসর বাড়ছিল ক্রমশ, নতুন শতাব্দীর সভ্যতার সঙ্কটের সঙ্গে তাল রেখে। সমগ্র ভারতবর্ষ তার ঔপনিবেশিক শোষণের ভিতর আরও এক শোষণকে মোকাবিলা করছে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমানবী হয়ে বেঁচে থাকার বিপজ্জনক অবস্থান যখন সর্বনাশ আর তা থেকে উত্তরণের দোলাচলে। আর কেবল নারী-ই কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয় শরৎচন্দ্রের কাছে। রাজনীতি করতেন তিনি। স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম তাঁর সত্তায়। ‘পথের দাবী’ তার-ই ফসল, যে বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পাঞ্জাবি লেখক নানক সিং-এর মতো জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রত্যক্ষ করা ‘সাদা রক্ত’-উপন্যাসের জন্মদাতা নন তিনি, কিন্তু হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর রাজনীতি-সংপৃক্তি কম ছিল না।
সর্বভারতীয় যে লেখকদের কথা বলা হল, তাঁদের মধ্যমণি কিন্তু আধুনিক ভারতীয় লেখকদের মধ্যে তিনি-ই। এজন্যই তাঁকে অনুবাদ করা হয় ভারতীয় নানা ভাষায় নানা সময়ে। তবুও কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মূল্যায়িত হননি আজ-ও। বেশ কিছু অনুবাদ ছিল তাঁর, প্রথমজীবনে কলকাতা বাসকালে, হিন্দি থেকে ইংরেজিতে, যা হারিয়ে গেছে চিরতরে। বারো বছর রেঙ্গুন-পেরু পর্বে আগুন লেগে পুড়েছে তাঁর আঁকা ছবি, ‘চরিত্রহীন’-এর পাণ্ডুলিপি, পরে আবার যা লেখেন। দলিত সাহিত্য, হালের সাহিত্যবিচারে আগন্তুক সংজ্ঞা, সেখানে তাঁর ‘অভাগীর স্বর্গ’ নিয়ে স্থান পান তিনি মহাশ্বেতা দেবী, প্রফুল্ল রায়, অনিল ঘড়াই, মনোরঞ্জন ব্যাপারীদের সঙ্গে, অরুণা চক্রবর্তী-সম্পাদিত ‘Rising from the Dust: Dalit Stories from Bengal’-এ। অরুণা তো ‘শ্রীকান্ত’ অনুবাদ করে দিল্লির সাহিত্য অকাদেমি-ও পেয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা আইডিয়াল বা ভাবের বাহন হয়ে আসে। ‘শাস্তি’ গল্পের চন্দরা যে সমাজ থেকে উঠে এসেছে, সেখানে স্বামীর প্রতি অভিমান করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি সে। ‘ছুটি’ গল্পে ফটিকের অন্তিম যে দার্শনিক সংলাপ, ‘মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাবো’, এটি একটি আদর্শায়িত উচ্চারণ। ‘রামের সুমতি’-তে রাম বা অভাগীর স্বর্গ’-তে অভাগী কখনওই এমন বাক্য বলবে না। তাই শরৎচন্দ্র চরিত্রনির্মাণে বাস্তবানুগ। কোনও কোনও সমালোচক তাঁর লেখায় ফরাসি ঔপন্যাসিক এমিল জোলার যে অনুস্মৃতি দেখেন, কতকাংশে তা যথাযথ। সে দিক দিয়ে জার্মান হাউপ্টমান, আমেরিকান জ্যাক লন্ডনের বাস্তববাদী রচনার সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। আমাদের ধারণা, সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে যে নবধারাপাত দেখা দিয়েছিল হিন্দি-উর্দু সাহিত্যে মুনসী প্রেমচাঁদের মাধ্যমে, বিশেষ করে তাঁর ‘নির্মলা’ ও ‘গোদন’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের ভারতীয় সাবঅলটার্ন জনজীবনের অসহায়তা ও আয়রনির, বা সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালার (১৮৯১-১৯৬১) উপন্যাস ও ছোটগল্প যে কৃষকচেতনার অঙ্কুর ফুটিয়ে তুলেছে, বা বিংশ শতাব্দীতে জন্মে মালয়ালম ঔপন্যাসিক তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই (১৯১২-১৯৯৯) ভারতীয় কথাসাহিত্যকে যে আরও প্রসারতা দিলেন সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের জীবন নিয়ে লেখা তাঁর ‘চেম্মিন’ (চিংড়ি) উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদী সাহিত্য সেসবের সঙ্গেই সমান্তরাল পাঠ দাবি করে। আমরা পাশাপাশি ওড়িয়া ঔপন্যাসিক ফকিরমোহন সেনাপতির (১৮৪৩-১৯১৮) ‘ন মণ আট গুণ্ঠ’ (উনিশ বিঘা দুই কাঠা) উপন্যাসে ভূমিহীন কৃষকের ওপরে নির্মম অত্যাচারের কাহিনি মনে রাখব। রুশ বিপ্লব তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, ভাবা যায়! আর চীনের কৃষকদের মর্মান্তিক দুর্দশার চিত্র পার্ল এস বাকের ‘গুড আর্থ’-এ আমরা পাব আরও ঢের দেরিতে, ১৯৩১-এ।
উড়িষ্যার ‘সবুজগোষ্ঠী’-র আন্দোলন, কলকাতার কল্লোল গোষ্ঠী, হিন্দি বলয়ে ‘ছায়াবাদী’ আন্দোলন শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভার জন্ম দিতে পারেনি। শেষবিচারে তাই তো তিনি অমর কথাসাহিত্যিক।
শরৎচন্দ্র নিয়ে কিছু অনিবার্য কৌতূহল আছে। তাঁর সময়কার কাজী নজরুল, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি কখনও? ভাল হিন্দি জানতেন তিনি। হিন্দি ভাষায় লেখালেখি করতেন যাঁরা, বিশেষ করে প্রেমচাঁদ, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বা নিরালা (শেষের দুজন কলকাতা থেকেছেন), রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে কি কোনওই যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি তাঁর? তাঁদের কোনও বিখ্যাত বই নিয়ে শরৎচন্দ্রের কোনও মন্তব্য পাওয়া গিয়েছে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটে বিখ্যাত উপন্যাস তাঁর জীবিতকালে বেরিয়েছে, কোনওটা পড়েননি তিনি? বা ‘পথের পাঁচালী’? সতীনাথ ভাদুড়ী, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর নিয়ে কোনও মন্তব্য?
বিশ শতকের গোড়া থেকে একাদিক্রমে বারো বছর তিনি বর্মায় ছিলেন। সে সময় দেশটি সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে আধুনিক হচ্ছে। ১৯০৪-এ প্রথম বর্মী উপন্যাস বেরোয়, যদিও তা ভিক্টর হিউগোর ‘কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো’-র অনুবাদ। বর্মায় ঔপনেবিশতাবিরোধী আন্দোলন ‘Hkit san’ (Testing of Time) শুরুর মুখে, ডাগন খিন খিন-এর মতো মহিলা ঔপন্যাসিকের জন্ম হবে অচিরে, সেদেশে ছাপাখানা এল, সাময়িকপত্র, সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব। এক যুগ সেখানে বাস করে শরৎচন্দ্রের কি কোনওরকম পরিচয়, যোগাযোগ হয়নি সেখানকার সাহিত্যের সঙ্গে? বারো বছর বাস করেও কি তিনি শেখেননি বার্মিজ ভাষা? রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম আরও পরে, তখন তিনি চলে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বর্মী সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি নীরব? একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি।
পরিশিষ্টবচন।।
পরীক্ষার ফি সময়মতো জোগাড় হয়নি বলে শরৎচন্দ্র এফ. এ. পরীক্ষায় বসতে পারেননি। পরবর্তীকালে অত্যাশ্চর্য ঘটে তাঁর বৈষয়িক সাফল্য। হাওড়া ও কলকাতায় তিনটি বাড়ি ছিল তাঁর, ছিল গাড়ি।
পরাধীন দেশে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করে শতকরা মাত্র দশভাগ সাক্ষরের দেশে এই অর্জন অভাবিত!