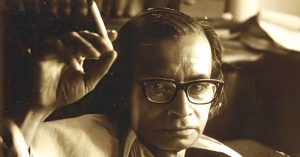সেরার সেরা ‘সেরা’
তিব্বতের বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তিব্বতীয় জনবসতি ও বড় মনাস্ট্রির অস্তিত্ব যে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায়, সেটা জানতাম। কিন্তু দুই অর্থেই দ্বিতীয় স্থানে যে জায়গাটি, সেটির অবস্থান যে দক্ষিণ কর্ণাটকের কোডাগু ও মহীশূর জেলার সীমানায় বাইলাকুপ্পিতে, সেটা জানা ছিল না। জানব কী করে? মনে মনে যখনই কোনও মনাস্ট্রির কথা কল্পনা করি, প্রেক্ষাপট হিসাবে আপনাআপনিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে রুক্ষ ঝলসানো পাহাড়। কর্ণাটকে যে পাহাড় নেই, তা নয়। সাতদিন ধরে কোডাগু জেলায় কাবেরী নদীর উৎসমুখ তল-কাবেরী থেকে নদীর পাড় বরাবর আমরা যে হেঁটেছিলাম, সেটাই তো পাহাড়ময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও কোডাগু বা কুর্গ জেলার আসল খ্যাতি কফি উৎপাদনের জন্য, পাহাড়ের হালকা ঠান্ডামাখা আদুরে বিছানায় যার চাষ হয়। কিন্তু সে পাহাড়ের বুক খুবই সতেজ, সর্বস্ব হারাবার কোনও হাহাকার নেই। এখানে এসে বুদ্ধদেব সময় নষ্ট করবেন কেন?
তল-কাবেরী থেকে হাঁটা শুরুর সাতদিন পর আমরা যখন কুশলনগর পৌঁছলাম তার একদিন আগে থেকেই পাহাড় হাওয়া, শুধুই সমভূমি। এখানেই এসেই জানতে পারলাম বাইলাকুপ্পির কথা। আর দেরি নয়, একটা অটোরিকশা ভাড়া করে মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে এলাম বাইলাকুপ্পির নামদ্রলিং মনাস্ট্রিতে। বাইরের ভূমিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ভিতরটা কী রাজকীয় হতে পারে। গেটের বাইরে দুটি স্তম্ভে লেখা নিংমাপা মনাস্ট্রি। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি বিশাল এলাকা জুড়ে আবাসিক ঘর, বিভিন্ন অফিস ও গুম্ফার ব্যাপ্তি। বাগান এবং খোলা জায়গায় মেরুন রঙের পোশাক পরিহিত লামাদের ঘোরাঘুরি। মেন অফিসে ঢুকে দেয়ালের তাক থেকে একটা বই নিয়ে চোখ বোলাচ্ছি, চোখে পড়ল এক জায়গায় লেখা, ‘It was in 1970 that the group of 197 Sera Jey monks with 103 of Sera Mey monks established a special monastery within the resettlement of Bylakuppe as a counterpart of the Tibetan Sera Jey Monastery which follows Ningmapa as well as Gelugpa school of thoughts and practices’। উল্টেপাল্টে দেখে অনেক দোনোমনা করে বইটা কিনেই ফেললাম।

কয়েক বছর ধরে একসময় নিছক কৌতূহলবশত তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বেশ মজে ছিলাম। প্রথমেই যে এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা শুরু করে দিয়েছিলাম, তা নয়। সেটা হয়েছিল পরম্পরা সূত্রে। পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারি এর উৎস ১৯৮৬ সালে। সে-বছর নেপাল হিমালয়ের গোঁসাইকুণ্ড-ল্যাংটাং অঞ্চলে পদযাত্রার সময় পথে প্রতিটি জায়গায় খাওয়া-থাকার জায়গায় আমাদের পদে পদে হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অনেকবার আমরা তিনবন্ধু নেপাল হিমালয়ে পদযাত্রায় গিয়েছি। সেইসব পদযাত্রায় বারবার একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাদা চামড়ার বিদেশিদের জন্য যতটাই খাতির, আমাদের জন্য ঠিক ততটাই দুর্ব্যবহার। কারণটা কী, বোঝা দুঃসাধ্য ছিল না। প্রতিটি আশ্রয়ে সাহেবরা জনপ্রতি যত টাকা খরচ করত, সেটা আমাদের দশ জনের খরচের সমান। সে-সময় যারাই নেপাল হিমালয়ে ট্রেক করতে যেতেন, সবার কাছেই এমন অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম। বিশ্বায়নের ফলে এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আমেরিকা তথা বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দার ফলে এখন ভারতীয় যাত্রীরা প্রায় সাহেবদের সমগোত্রীয় হয়ে গেছে। তাঁরা এখন বুঝতে পারবেন না, সে সময় অবস্থা কতটা সঙ্গিন ছিল। সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল এভারেস্ট বেসক্যাম্প থেকে ফিরে আসার পথে কুনজুমে। আমার অসুস্থ সঙ্গীকে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে কুনজুম এসে পৌঁছেছিলাম। সে সময় কুনজুমে দুটি মাত্র লজ বা হোটেল ছিল। যে হোটেলটিতে প্রথমে আমাদের আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি, কিন্তু সময় ও অসুস্থ সঙ্গীর কথা জানিয়ে অনুরোধ করলে শেষপর্যন্ত হোটেলের মূল চত্বর ছাড়িয়ে একপ্রান্তে একটি ভাঙাচোরা ঘরে থাকতে দিতে রাজি হয়েছিল, সেই হোটেলের মালিক মিংমা শেরপা। স্যার এডমন্ড হিলারির ‘স্কুল হাউস ইন দ্য ক্লাউড’ বইয়ে এই কুনজুম গ্রাম ও মিংমা শেরপার সম্পর্কে কত প্রশস্তি লেখা আছে। তাঁদের কাছে এরকম দুর্ব্যবহার!

তখন থেকেই আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকল। বিদেশি পর্বতাভিযাত্রীদের লেখায় শেরপাদের বিষয়ে যে এত প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা কতখানি সত্য? শেরপাদের কি দুটো রূপ-– একটা সচ্ছল শ্বেতাঙ্গদের জন্য ও অন্যটি অশ্বেতাঙ্গদের জন্য? নাকি সাহেবরা নিজেদের পর্বতারোহণের স্বার্থে ভাল মালবাহকের প্রয়োজনে শেরপাদের ভিতর সেই সম্ভাবনা আবিষ্কার করে সত্যমিথ্যা মিশিয়ে নিজেদের মতো করে তাঁদের একটা ইমেজ নির্মাণ করেছে? ভিতরে একটা গোঁ চেপে গেল। প্রায় একদশক ধরে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আমি আমার নিজের মতো করে ফিল্ডওয়ার্ক করি, কিছু বইপত্রও পড়ি। নেপাল তো আছেই, যে দার্জিলিং আগে শুধু বেড়াতে গেছি সেই দার্জিলিংয়ের শেরপা মনাস্ট্রিতে এবং শেরপা বুদ্ধিস্ট অ্যাসোশিয়েশনে বারবার ঢুঁ মেরেছি, এইচ.এম.আই.-এ কোর্স করাকালীন আমাদের প্রশিক্ষক নিমা তাসি ও নোয়াং গম্বু-সহ বিখ্যাত আং শেরিং শেরপার সাথে একাধিকবার কথা বলেছি। এইচ.এম.আই-এর তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ মেজর কুলবন্ত সিং ধামির সৌজন্যে এইচ.এম.আই. লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন সময় কাটিয়েছি। আমার মনে যে সংশয় বা প্রশ্নের তোলপাড় হচ্ছিল, সেগুলির উত্তর ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকল। তবে সেই সমর্থন পরিষ্কারভাবে পেলাম পর্বতাভিযাত্রীদের লেখা থেকে নয়, কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে ও ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পাওয়া নৃতত্ত্ববিদদের লেখা থেকে। ক্রিস্তফ হ্যামিনদ্রফ, জোনাথন নিল, জেমস ফিসার, শেরি অরটনার, ভিনকেন অ্যাডামস, বারবারা ব্রোয়ার এমন অনেক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ; যাঁরা দিনের পর দিন এসব অঞ্চলে সত্যনিষ্ঠ সমীক্ষা করেছেন তাঁদের মতামত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শেরপা নির্মাণ পর্বে লেখা সাহেব, বিশেষত ব্রিটিশ পর্বতাভিযাত্রীদের মতামতের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তবে একটা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এল আমার ধারণায়। কোনও রাগ নয়, নিভৃতে মাথা নীচু করে দার্জিলিং-এর শেরপাদের প্রণাম জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রথমে পূর্ব তিব্বতের খাম থেকে পালিয়ে আসা এবং পরে নিজেদের দেশ হিসাবে গড়ে তোলা সোলু-খুম্বু থেকেও সচ্ছল শেরপাদের নিষ্পেষণে বাস্তুত্যাগী দরিদ্র শেরপারা এই দার্জিলিংয়ের টুংসুং বস্তিতে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিল, ক্রীতদাসের ভূমিকা থেকে খোলাবাজারে স্বাধীনভাবে নিজেদের শ্রম বিক্রি করার পর্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে পেরেছিল।
তখন সাহেবি জমানা। কাজকর্মের ফাঁকে সাহেবরা বিভিন্ন কাজে বা অনুসন্ধানে, বা নিছক অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মাঝে মাঝেই পাহাড়ে যায়। বিভিন্ন দেশগুলিও ইতিমধ্যে পর্বতারোহণের জন্য বিভিন্ন আটহাজারি শৃঙ্গগুলির ঠিকাদারি নিয়ে নিয়েছে। ইটালিয়ানরা কে-টু, জার্মানরা নাঙ্গা পর্বত, জাপানিরা মানাসলু। কিন্তু সবার আগেই জাত্যাভিমানের কারণে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে বুক করে ফেলেছে পৃথিবীর সেরা উপনিবেশিক ব্রিটিশরা। সবার আগে দরকার উপযুক্ত মালবাহক। তখন সারা হিমালয় জুড়ে ভাল মালবাহকের ছড়াছড়ি। গাড়োয়ালি, কুমায়ুনি, তিব্বতি, লেপচা, নেপালি ও শেরপা-– সকলেই বলে আমায় দেখ। সাহেবদের লেখায় সে-সব মালবাহকদের নিয়েও অনেক প্রশস্তি আছে। এইরকম চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় নিজেদের আগাপাশতলা বিবর্তিত করে সকলকে হারিয়ে যে বিশ্বখ্যাত শেরপা ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল, সেই মহৎ ঐতিহ্যের স্রষ্টা খুম্বু থেকে বিতাড়িত এই দার্জিলিংয়ের শেরপারা। তাঁদের প্রণাম না জানিয়ে উপায় নেই।

সেই শেরপাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কিছু চর্চা করতে হয়েছিল। যে-কোনও একটা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও মানসিক অবস্থান অনেকাংশে নির্মিত হয় বা পরিচালিত হয় সেই জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সে-সময় তিনবছর ধরে একটি বিখ্যাত পত্রিকায় এই নিয়ে আমায় ধারাবাহিক লিখতে হয়েছিল। তখনই জেনেছিলাম থরবেদ, নিংমাপা, গেলুগপা ইত্যাদির বিষয়ে। দিনভর সব কাজকর্মের ভিতর শুধু নয়, রাতের ঘুমেও শেরপারা তাঁদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে আমার মাথায় ঘোরাফেরা করতে থাকত, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন পন্থার নামগুলি ভিতরের মালমসলা নিয়ে আমার মাথায় বিক্রিয়া করতে থাকত। একসময় ‘অনেক হয়েছে, আর নয়’ বলে ওই চক্কর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। এখানে এসে আবার ওই চক্করে পড়ে গেলাম!
ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে এসে ঢুকলাম গোল্ডেন টেম্পলের ভিতরে। একটা হলঘর, উচ্চতায় প্রায় তিনতলার সমান। দরজা ও দেওয়াল জুড়ে ম্যুরাল-– ঈশ্বরের কাছে শয়তানের পরাজিত হওয়ার কাহিনি আশ্রিত। আবছা আলো, শান্ত পরিবেশ, নীচে কার্পেটে বসে আছেন অনেকে। কেউ এমনি বসে আছেন, কেউ ধ্যান করছেন। বেদির ওপরে তিনটি বড় সোনালি স্ট্যাচু, প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চতার। মাঝখানে বুদ্ধদেব, তাঁর বাঁদিকে পদ্মসম্ভব বা গুরু রিনপোচে এবং ডানদিকে বুদ্ধ অমিতায়ুস। এখানে এলে মন ভাল না হয়ে উপায় নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে একসময় দুজনে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের অটোচালক একজন নিপাট ভদ্রলোক। কর্নাটকি উচ্চারণে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে উনি জানালেন, ‘এখানে আরও তিনটি গুম্ফা আছে, সব তো এখন আর দেখা যাবে না। একটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার তরফ থেকে গিফট’। পনেরো মিনিটেই অটো এসে দাঁড়াল সেই মনাস্ট্রির গেটের সামনে।

বাইরে থেকে এই মনাস্ট্রিগুলি সব একই রকম লাগে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানা-বোঝা না থাকলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কাছে সবই সমান। সেভাবেই সব দেখতে দেখতে একজায়গায় এসে দেখি, সবুজ লনের একপ্রান্তে দুপাশে অনেক লামা বসে আছেন, মাঝখানের জায়গায় চারজন লামা তর্কাতর্কি করছেন। দুপক্ষে দুজন করে চারজন। বাহু সঞ্চালন করে তর্কাতর্কি হচ্ছে বটে, কিন্তু চারজনের মুখেই হালকা হাসির আভাস। অন্য লামারা বসে বসে দেখছেন সেই দৃশ্য। বেশ কিছুক্ষণ এমন চলার পর ওই চারজন চলে গেলেন, বসে থাকা লামাদের ভিতর দুপাশ থেকে দুজন করে চারজন উঠে এসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। বিকাশ আমায় জিজ্ঞাসা করল, ‘ব্যাপারটা কী বল তো, নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে নাকি?’ মুখে কিছু উত্তর দিলাম না, শুধু বুঝবার চেষ্টা করতে থাকলাম ব্যাপারটা কী। মাথায় হলুদ টুপি পরা কয়েকজন সন্ন্যাসী দেখছি, তার মানে এরা গেলুগ সম্পদায়ের। এখানে ঢোকার মুখেই একজায়গায় ‘সেরা জে মনাস্ট্রি’ লেখাটি চোখে পড়েছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম নিয়ে খোঁজখবর করাকালীন ‘সেরা’-র কথা পড়েছিলাম। তিব্বতের কোথাও নাকি ‘সেরা’ নামে একটা বড় মনাস্ট্রি আছে, যেটি গেলুগ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সংগঠন বা মন্দির। অষ্টম শতাব্দীতে পদ্মসম্ভব (তিব্বতীয়দের কাছে গুরু রিনপোচে) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে তিব্বতে আসেন। তার আগে সেখানে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রসাধনার প্রচলন ছিল। সেই প্রচলিত তন্ত্রসাধনার সাথে মহাযানপন্থী পদ্মসম্ভব প্রচারিত বুদ্ধধর্মের মিশেলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রচলন শুরু হয়েছিল। এই ঘরানায় বিশ্বাসীদের বলা হত নিংমাপা। বলা বাহুল্য, প্রায় সব তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রথম কয়েক শতক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কয়েক শতকে কাগু ও শাক্য এবং মাত্র ছ’শো বছরের কিছু আগে এই গেলুগ পন্থার আবির্ভাবের সাথে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম তথা নিংমাপা গোষ্ঠী খণ্ডিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে। বয়সে সবচেয়ে নবীন হলে হবে কী, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ভিতর গেলুগ তত্ত্বে বিশ্বাসীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, এটাকেই এখন তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

গেলুগ পন্থায় ধর্মাচরণ পদ্ধতি অন্যদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই পন্থায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষাদানের ওপর। বুদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক স্কুল-কলেজ তো বটেই, এমনকি গেলুগ মনাস্টিক ইউনিভার্সিটিও আছে তিব্বতে। ওদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিক্ষাদান পর্যায়ে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই মুখের ভাষার সাথে সাথে অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেন তাঁদের প্রশ্ন এবং উত্তরের নির্যাস। চেষ্টা করা হয়, যাতে একজন শিক্ষকের সাথে একজন ছাত্রেরই সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। এর তিনটে প্রধান কারণের কথা পড়েছি। প্রথম কারণ, গুম্ফায় সবার সাথে লাইন দিয়ে বসে নিজের পুঁথি পড়তে পড়তে একঘেয়েমি আসতে পারে, ঘুম পেতে পারে, কেউ ফাঁকি মারতেও পারে। দ্বিতীয় কারণ, মুখের সাথে শারীরিক মুদ্রার ব্যবহার চোখকে প্রাণবন্ত করে বক্তব্যকে কার্যকরীভাবে এবং আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপিত করতে পারে। আমাদের দেশে বাউল বা কীর্তনীয়াদের পরিবেশনায় যেমন হয় আর কী! তৃতীয় কারণটা উচ্চমার্গের–- শরীর-মনকে এক তারে বাঁধার উন্নত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই অনুশীলন। এখানে বোধহয় সেইরকমের শিক্ষাদান চলছে? আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অফিসঘরে ঢুকে ওদের উপহার দেওয়া একটা চটি বই নিয়ে একসময় বেরিয়ে এলাম। বইটিতে লেখা ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের আক্রমণে তিব্বতের ‘সেরা’ মনাস্ট্রিকে ধ্বংস করে দেওয়া, সব পুঁথি পুড়িয়ে দেওয়া ও কয়েক হাজার সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলার পর কয়েকজন কীভাবে হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিলেন। কীভাবে তাঁরা ভারত সরকার ও কর্নাটক সরকারের সহযোগিতায় এখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কীভাবে গড়ে তুলেছিলেন এই মনাস্ট্রি। এখানে কী কী আছে, কতজন সন্ন্যাসী আছেন ইত্যাদি।

এরপর পনেরো বছর পার হয়ে গেছে। রেশমপথের সুবাস নেব বলে ২০১৯ সালে কিরঘিজস্তান ও চীনের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখে তিব্বতের লাসায় এসে পৌঁছেছি। প্রথম দুটো দিন লাসা শহর, পোতালা প্রাসাদ এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখে ভালই কেটে গেল। তৃতীয় দিন আমাদের গাইড লোবসাং জানাল, আমরা আজ ‘সেরা’ মনাস্ট্রি দেখতে যাব। নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। শেরপাদের নিয়ে অনুসন্ধান পর্বে ও বাইলাকুপ্পিতে তিব্বতের যে ‘সেরা’ মনাস্ট্রির কথা পড়েছি, তার অবস্থান এখানেই কাছাকাছি কোথাও! আমার ধারণা ছিল না। গোটা তিব্বত জুড়ে কয়েকশো বিখ্যাত মনাস্ট্রি আছে, সেরকমই কোথাও ‘সেরা’ বলে একটা মনাস্ট্রি আছে, এই ছিল আমার ধারণা। উৎসাহ নিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। মাত্র আড়াই কিলোমিটার পথ, পনেরো মিনিটেই বাস এসে দাঁড়াল মন্দির চত্বরের বাইরে। গেলুগপন্থার স্রষ্টা সংখাপা (Tsongkhapa)-র প্রিয় শিষ্য জেসতুন রিনচেনের উদ্যোগে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত এই মনাস্ট্রি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। পুবদিকে একটা বড় প্রার্থনা ঘর, তার পিছনে সন্ন্যাসী ও ছাত্রদের থাকার ঘর। অনেকক্ষণ ধরেই কানে হালকা হৈ-চৈয়ের আওয়াজ আসছিল। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে একসময় সবাই এসে উপস্থিত হলাম একটা পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গণে। ভিতরে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ! প্রাঙ্গণ জুড়ে প্রায় একশো জোড়া লামা একসাথে তর্কাতর্কি করছেন। প্রতিটি জোড়ায় একজন বসে ও অন্যজন দাঁড়িয়ে হাত-পা খেলিয়ে চোখমুখের অঙ্গভঙ্গি করে তর্ক করছেন, সাথে বাঁহাতের তালুর ওপর ডানহাতের তালুর পিছন দিয়ে তালি দিচ্ছেন। কিন্তু সবারই মুখে হাসি, চোখে দীপ্তি। বয়স দেখে বোঝা যাচ্ছে, বসে থাকা জন ছাত্র, অন্যজন শিক্ষক। পাশে দাঁড়িয়ে লোবসাং জানাল যে, শিক্ষাদানের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে। না বললেও চলত। এমনটাই তো পড়েছি গেলুগপা শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে, এমনটাই তো আমার কল্পনায় ছিল। ছবি তোলার দিকে কারও খেয়াল নেই। নিজের অজান্তেই কখন যেন আমরাও ডুবে গেছি ওই প্রাণবন্ত আবহের গভীরে। ঐতিহ্য হস্তান্তরের এই উজ্জ্বল প্রক্রিয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আমাদের চোখমুখ। ফিরে চলার জন্য লোবসাংয়ের তাগিদ আমাদের কানে ঢুকছিল না। সময়ের কথা ভুলে গিয়ে বুঁদ হয়ে দেখছিলাম সবাই।
একসময় অবশ্য বেরিয়ে এসে বাসে বসতে হল। চলমান বাসের জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে বাইরে ভাসিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম বাইলাকুপ্পিতে যে শিক্ষানুশীলন আমরা দেখেছিলাম, সেটি ছিল যেন নিছক আচার পালন। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে অনুভবের সার্থক প্রয়োগ ছাড়া এখানের এই শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্ভব নয়। শিক্ষায়তন জুড়ে এই প্রাণের মেলা কি অন্য কোথাও আছে? ‘সেরা’-র উদ্দেশে কুর্নিশ জানিয়ে নিজের মনেই বললাম, ‘সেরা’ যেন এমন সেরা থেকেই সবাইকে পথ দেখাতে পারে।
চিত্র: লেখক