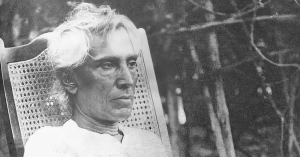বেশ বুঝতে পারি মানুষের কৌতূহল আর ফুঁপি কখনও ফুরোয় না, ফুরাতে চায় না। মানুষের সেই অনন্ত ফুঁপি আর অজানাকে জানার সূত্র ধরে ধরে আমি কেবলই তত্ত্বতালাশ করে বেড়াই, কেবলই জেনে-বুঝে বেড়াই। কখনও নির্জনে, কখনও-বা স্বজনে। কখনও আখড়া-আশ্রমে, কখনও মেলা-পার্বণে। নইলে এত বছর পর আবার কেন লালনকে নিয়ে লিখতে হবে? আর পাঁচজন গবেষক-পণ্ডিত কিংবা লোকসংস্কৃতিবিদের মত দোলপূর্ণিমায় বা কার্তিকের তিরোধান দিবসে ছেঁউড়িয়ায় কিংবা নদীয়ার আসাননগরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের লালনোৎসবে গিয়ে সাহিত্যের পণ্ডিতদের দু-একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনলেই তো জানা-বুঝা হয়ে যায়! অথবা ভক্তিমান সাধুগুরু-ভক্তদের মত আখড়ায় গিয়ে প্রণাম নিবেদন কিংবা সাধুসঙ্গ করলেই তো সব পাট চুকে যায়! আমিও তো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারতাম, লালন ফকির উচ্চস্তরের সুফি সাধক ছিলেন এবং পবিত্র কোরানের ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। আমিও তো মেহেরপুরের কাজীপুর গ্রামের ফকির দবিরউদ্দিন শাহের মত বিশ্বাস করতে পারতাম যে, ‘লালন একজন আল্লাহর ছিলেন।’ কুষ্টিয়ার ফকির মন্টু শাহের মত আমিও মনে করতে পারতাম, ‘সিরাজ সাঁই বলে কোনো লোক ছিলেন না।’ সিরাজ আসলে লালনের কাল্পনিক গুরু। কারণ লালন নিজেই কলিযুগের অবতার। (আজাদ রহমান: লালন মত লালন পথ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃষ্ঠা: ৩০) কোনও কোনও ভাবশিষ্য বলেছেন, ‘লালন স্বয়ং মহাভাবসমুদ্র, এ কারণেই তিনি জগত গুরু, ত্রাতা ও দাতা। তাঁকে বাংলা ভাষায় কবিবেশে নবি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। প্রকৃত বিচারে ফকির লালন মাতৃযোনিসম্ভূত সাধারণ মানব সন্তান নন, তাঁকে অযোনিসম্ভূত বলে সিদ্ধ সাধকগণ উল্লেখ করেছেন।… শাব্দিক ব্যাখ্যা দিয়ে লালনকে বোঝানোর সাধ্য নেই এ নরাধমের। তাঁর এককণা শ্রীচরণধূলির যোগ্যও আমি নই। তিনি দয়াল, এই ভরসায় বাঞ্ছা করি তার মহানাম কীর্তনের। বিশ্বাস করি, জগতবাসীর আত্মমুক্তির শেষ উপায় বা সর্বোত্তম পন্থা এটিই।’ (আবদেল মাননান: লালন দর্শন, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ: ১৮) কিন্তু সব মত খারিজ করে দিয়ে গ্রাম-জনপথে ঘুরে বেড়ানো তার্কিক কুদ্দুস ফকির কিংবা বাদল শাহ বলেছেন, লালন একজন সাধারণ মানুষ, কেবলই মানুষ।
সত্যি বলতে কি, অবিভক্ত বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লালন এক মহারহস্যময় চরিত্রের নাম। তাঁকে ঘিরে তর্ক-বিতর্ক আছে, ধোঁয়াশা আছে, আছে দারুণ বর্ণাঢ্যতা। আছে লাঠালাঠি, আছে কাদা ছোড়াছুড়ি। এক সময় দু-বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী লালনকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। মান্য করত চৈতন্যদেবের নতুন অবতার হিসেবে। কেউ আবার তাঁকে অলি মনে করে তাঁর নামে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করত। তবে দেশভাগ, সমাজ-রাজনীতির ভাঙাগড়া এবং পরিবর্তনের আপতিক মোচড়ে মানুষের ধ্যান-ধারণা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে, তারপরও লালনকে নিয়ে জনমনে ও বুদ্ধিজীবী মহলে ঔৎসুক্য কমেনি। বরং তাঁকে ঘিরে প্রতিদিন জন্ম হচ্ছে ধোঁয়াশা, নতুন নতুন তর্ক। লালনকে নিয়ে চাপান-উতোর, তর্ক-প্রতর্ক, অনিঃশেষ কৌতূহল প্রমাণ করে যে, লালনের জীবন-কাহিনির মধ্যে বেশ কিছু নাটকীয়তা আছে এবং তাঁর গানের ভেতরে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা উসকিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে জীবনসত্যের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে। তা না হলে তাঁকে নিয়ে এত কৌতূহল, এত তর্ক-বিতর্ক থাকবে কেন? কেন বাঙালি জাতিসত্তার উজ্জীবনে তাঁকে সামনে নিয়ে আসা হবে? বিবিসি কর্তৃক প্রণীত বাঙালির তালিকা প্রকাশের পর, হাল আমলের নাগরিক বুদ্ধিজীবীরাও তাঁকে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধির সমাজ গড়ার সারথি হিসেবে, প্রতীক হিসেবে মান্য করছেন। সেই দিক থেকে লালন আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংস্কৃতিসেবীদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন। ঢুকে পড়েছেন সদর রাস্তা থেকে সটান অন্দর-মহলে। যদিও লালন তাঁর জীবনের কোনও পর্বেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশেননি এবং তাদের পক্ষে বলার দায় অনুভব করেননি। তাঁর অবস্থান ছিল নিম্নবর্গীয় হিন্দু-মুসলমান ও প্রান্তিক মানুষের পক্ষে। তিনি সারাজীবন প্রথাগত নামে বাড়াবাড়ি, আচারসর্বস্বতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন প্রবলভাবে। কিন্তু আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তাদের সুশীল সংস্কৃতিসেবীরা সেটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে তাদের ভুল ব্যাখ্যার কারণে ফকির লালন হয়ে উঠেছেন কেবলই চারণকবি, বাউলসম্রাট কিংবা মরমী সাধক। সাহিত্যের পণ্ডিতরা মনে করছেন, লালন সাহিত্যের সামগ্রী। আর তরিকতি-ফকির ও ক্ষয়িষ্ণু ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে তিনি ভেঙে ভেঙে খাওয়ার সম্পত্তি।
এখানে একটি উদাহরণ নতুন করে না উল্লেখ করে পারছি না— রামকৃষ্ণদেবের উদাহরণ। স্কুল-কলেজে তিনি পড়েননি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বহরও তাঁর ছিল না। তারপরও তিনি গদাধর থেকে রামকৃষ্ণদেব হয়েছিলেন, এক পর্যায়ে তাঁর ধর্মভাবনা বিবেকানন্দের মাধ্যমে পশ্চিমা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি গ্রামে জন্মেছিলেন, কিন্তু পরিপুষ্ট হন কলকাতার শহুরে এলিটদের নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতায়। রানি রাসমণির বদান্যতা, কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের সাহচর্য এবং গিরিশ ঘোষ-বিবেকানন্দের মত শিষ্যদের নিঃশর্ত আনুগত্য পেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একজন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব হতে পারেন। কিন্তু এক দুর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রাম-জনপদের বিত্ত-বৈভবহীন পরিবারে জন্ম নেয়া এবং অকুলীন পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা এক গেঁয়ো-নিরক্ষর বাউল কী করে ফকির লালন সাঁই হয়ে উঠলেন, তা এক বিস্ময়কর রহস্য। তাঁকে নিয়ে যাঁরা গবেষণা বা লেখালেখি করেছেন বা করছেন, তাঁরা সেই রহস্যের জট খুলতে পারেননি আজও। কিন্তু সময় এসেছে সেই রহস্যের জট উন্মোচন করে আসল লালনকে প্রতিষ্ঠার।
লালনের ধর্ম-পরিচয়ের অস্পষ্টতাও তাঁর নিরাসক্ত জীবন-কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। যারা এবং যাদের পূর্বপুরুষরা এককালে লালনকে ‘ব্রাত্য, মন্ত্রহীন, বেশরা-ফকির’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরিরাই এখন তাঁকে বাঙালি জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মান্য করে তাঁর শ্রীচরণতলে ধূপধুনো দিচ্ছেন। যে অন্নদাশঙ্কর রায় কুষ্টিয়া মহকুমার প্রশাসক থাকাকালীন লালন আখড়ায় যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেননি একদিনের জন্যও, তিনিই আবার লালনকে নিয়ে রচনা করেন এক মহামূল্যবান আকরগ্রন্থ। তাঁর অকুলীন ও মহিমাহীন সমাধিপ্রাঙ্গণে এখন বানানো হচ্ছে লালন কমপ্লেক্স, গবেষণা কেন্দ্র, লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র আরও কত কী! তাই অনেক লেখকই নিরাসক্তভাবে তাঁর জীবনী লেখার পরিবর্তে, তাঁর মাহাত্ম্যকীর্তন রচনা করছেন। অনেকে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ঢেকে দিয়ে তাঁকে মুসলিম সুফি সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু লালন কি জাতপাত মানতেন? মানতেন না। হিতকরী পত্রিকা থেকে জানা যায় যে,
“মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল, হরে-নামও দরকার হয় নাই।… তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না।’’
লালন নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বসন্তকুমার পাল ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন অগ্রগণ্য। লালন সম্পর্কে বসন্তকুমার পালকৃত লালন-জীবনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মতিলাল দাশের মত লালন-গবেষকরাও তাঁর মতামতকে মেনে নিয়েছেন কিংবা সমর্থন দিয়েছেন। গবেষক বসন্তকুমারের পৈতৃক নিবাস ধর্মপাড়া, লালনের জন্মভিটা ভাঁড়ারা গ্রামের পাশেই অবস্থিত। সেই সূত্রে লালনকে জানা-বোঝা এবং ক্ষেত্রানুসন্ধান বসন্তকুমারের পক্ষে যতটা সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক ছিল, ততটা অন্যদের পক্ষে ছিল না। অন্যদিকে, মনসুরউদ্দিন ছিলেন নিষ্ঠাবান সংগ্রহ, হারামণির সংকলক ও শেকড়-সন্ধানী লোকগবেষক। সাড়ে তিন দশক ধরে শত শত লালনগীতি গভীর অভিনিবেশসহকারে সংগ্রহ করে হারামণির পাতায় লিপিবদ্ধ করেন। বসন্তকুমার যেভাবে লালনের জীবন-কাহিনি বয়ান করেছেন, তাতে গবেষক মনসুরউদ্দিনের সমর্থন ছিল। দুজনের ভাষ্য সংক্ষেপ করে বলা যায়:
লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কুমারখালিসংলগ্ন গড়াই তীরের ভাঁড়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে, পদবি কর (মতান্তরে রায়)। বাবার নাম মাধব ও মাতা পদ্মাবতী। বাবা-মার একমাত্র সন্তান লালন শৈশবে বাবাকে হারান এবং সেই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি পাননি। চাপড়ার ভৌমিকরা তাঁর মাতুলবংশ। ছোটবেলা থেকে লালন গানবাজনার পরিমণ্ডল বিশেষত কীর্তন ও কবিগান ভালবাসতেন। ধর্মভাবও ছিল স্বভাবগত। অল্প বয়সে পিতৃহীনতার কারণে তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়েন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধের কারণে স্ত্রী ও মাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দাসপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বারুণী তিথি উপলক্ষে সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান এবং ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। অচেতন লালনকে তাঁর সঙ্গীরা জলে ভাসিয়ে দেয় এবং গ্রামে ফিরে তারা রটিয়ে দেয় যে, লালন মারা গেছে। তার মা ও স্ত্রী এবং গ্রামবাসী— এই মিথ্যে রটনা বিশ্বাস করে নেয়। মিথ্যে হলেও গ্রামবাসী এটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। কারণ আঠারো শতকে অবিভক্ত বাংলার গ্রামদেশে বারবার কলেরা-বসন্ত মহামারিরূপে হানা দিত, এতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। প্লেগ-গুটি বসন্ত-কলেরার প্রকোপে ভারতবর্ষেও লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
লালনের জীবন-কাহিনি বাঁকবদল করে বা নতুনভাবে নির্মিত হয় কুমারখালির নিকটবর্তী কালীগঙ্গার তীরে, যেখানে তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। এক স্নেহশীলা মুসলমান নারীর নিবিড় পরিচর্যা ও মমতায় সুস্থ হয়ে ওঠেন, লাভ করেন এক নতুন-জীবন। কিন্তু গুটিবসন্ত তাঁর শরীর ও মনের ওপর যে-ছাপ মেরে দেয়, যে-দগদগে ক্ষত এঁকে দেয়, তা সারাজীবনেও তিনি মোচন করতে পারেননি। সুস্থ হয়ে লালন বাড়ি ফিরলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্র, ধর্ম ও সমাজের বিধান অনুসারে তিনি সেখানে আশ্রয় পেলেন না। কেন-না যার নামে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং যিনি যবন-মুসলমানের গৃহে অন্ন গ্রহণ করেছেন, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী, তাঁর জাত চলে গেছে; তিনি হয়ে গেছেন অস্পৃশ্য। হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। সমাজ ও পরিবারের এহেন নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত লালন চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে আসলেন গুরু সিরাজ সাঁইয়ের কাছে। সিরাজ সাঁই তাঁকে বায়াত করলেন এক নতুন লোকায়ত মানবধর্মে। এই ধর্মের কোনও শাস্ত্র কেতাব নেই, কোনও মহাপুরুষ নেই। সাম্প্রদায়িক মত ও প্রথাগত ধর্ম পরিত্যাগ করে সিরাজের প্রেরণা ও কারিগর সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে তিনি একটি আখড়া গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে, তাঁর মরমী গান, মানবিক-আচরণ ও ভাব-ভাবুকতায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তবে তাঁর শিষ্যরা অধিকাংশই ছিলেন গরিব মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু। অভিজাত শ্রেণি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। একজন মারফতি সাধক এবং নীলকর-সামন্তবাদ-শোষক-জমিদারবিরোধী প্রতিবাদী ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্রমাগত বিস্তৃত হয় অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে। গড়ে ওঠে বিশাল শিষ্যমণ্ডলী।
অনুমান ও লোকশ্রুতি-নির্ভর এমন লালন-জীবনকাহিনি সর্বাংশে সত্য এমন কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই। লালনকে বোঝার জন্য তাঁর জীবন-কাহিনি যে খুব জরুরি তাও নয়। তিনি যে জাতপাত, ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি, সাম্প্রদায়িকতাকে খারিজ করে দেয়া, বিশুদ্ধ মানবধর্মে আস্থাশীল সাহসদীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন— সেটাই জরুরি। কিন্তু অজ্ঞ-অন্ধ কিংবা ধান্দাবাজ মানুষ লালনের জাতিত্ব নিয়েই টানাটানি করে চলেছেন, একের এক নির্মাণ নিয়ে করে চলেছেন নানান কেচ্ছা-কাহিনি। ‘লালনের গঙ্গাস্নানের অভিযান মুখে মুখে পালটে যায় কখনও নবদ্বীপ অভিমুখে, কখনও বা শ্রীক্ষেত্রে এবং এমনকি রাজশাহীর খেতুরির দিকে।… বসন্তরোগাক্রান্ত লালন পরিত্যক্ত হন সঙ্গীসাথিদের দ্বারা, কখনও এমনকি নিজের বাবা-মা দ্বারা। অভিযানের সময়ে তাঁর বয়স নিয়েও নানা কাহিনী নানা বয়ান। মুমূর্ষু লালনের উদ্ধারকর্তা কারও মতে একজন মুসলমান নারী, কারও মতে মুসলমান ফকির। (সুধীর চক্রবর্তী: ব্রাত্য লোকায়ত লালন, রচনা সংগ্রহ। কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা: ৩১০) লালনের জীবন-কাহিনির ওপর একটি সূক্ষ্ম আবরণ বা প্রলেপ আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে নানা বিতর্ক ও মতান্তর। কিন্তু এসব কাহিনির মধ্যে কোনও মিথ্যাচার বা বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে একদল নতুন গবেষক এবং কিছু সাধুগুরু মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। লালনের হিন্দু-পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তারা বলতে চাইছেন যে, লালন জন্মসূত্রে মুসলমান। ১৯৬৩ সালে গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলী এম এ হাইয়ের নকশা অনুসারে লালনের সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এটি দেখলে দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মকবরার কথা মনে পড়ে যায়। এভাবেই পাকিস্তানি শাসনামলে লালনের ইসলামিকরণ শুরু হয়। লালন যে মুসলমান, এ কথা প্রথম বলেছিলেন মুহম্মদ আবু তালিব। তিনি তাঁর ‘লালন পরিচিতি’ (১৯৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন: “বর্তমান লেখকই সর্বপ্রথমে… লালনকে যশোহর জেলার হরিশপুর নিবাসী এবং জন্মগতভাবে মুসলমান দাবি করেন। ১৩৬০ সালের (আগস্ট ১৯৫৩ ঈসায়ী) ভাদ্র সংখ্যা মাহে নাও পত্রিকায় তিনি সমস্ত প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করে বলেন— আনুমানিক ১১৭৩ (১৭৭৬ ইংরেজি) সালে যশোহর জেলার হরিনাথকুঞ্জ থানার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের এক খোনকার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন লালন শাহ।’ পাঞ্জু শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দিনও তাঁর ‘ভাবসংগীত’ গ্রন্থে লালন ফকিরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করেছেন। সত্যিই কি তিনি মুসলমান ছিলেন? আবার খোন্দকার গোত্রভুক্ত? তাহলে তো তিনি খান্দান মুসলমান ছিলেন? কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মত গবেষকরা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ও যথাযথভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালিয়ে বলছেন অন্য কথা। তিনি ভারতী পত্রিকায় লিখেছেন:

“লালনের মত অতি উদার ও সরল ছিল। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন ও শিষ্যদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতেন। লালন হিন্দু নাম, শাহ উপাধি মুসলমানজাতীয়— সুতরাং অনেকেই তাঁহাকে জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিত। তিনি উত্তর না দিয়া স্বপ্রণীত নিম্নলিখিত গানটি শুনাইতেন—
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
লালন বলে, জাতির কীরূপ দেখলাম না এ নজরে।”
সম্ভবত ইচ্ছে করেই লালন তাঁর জাতি পরিচয়টা গোপন রেখেছিলেন। এর পিছনে হয়তো অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, তিনি হয়তো সবার মধ্যে নিজের একটি গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি চাইতেন ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষ যেন তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এ কারণে কখনওই নিজেকে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননি, এমনকি বাউল সাধক কিংবা সুফি-সাধক হিসেবেও উপস্থাপন করতে চাননি। তাই এমন সব ধর্মীয় আচরণ তিনি করতেন যাতে করে সর্বধর্মের মানুষ তাঁকে নিজেদের লোক মনে করে গৌরব অনুভব করত। হিতকরী পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বয়ান থেকে জানা যায়:
‘‘লালন কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপনজন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আচার-ব্যবহারের মিল থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিত দেখিয়া হিন্দুরা ইঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত।”
আসলে, লালন ছিলেন উদার ও নির্ভীক চিত্তের ব্যক্তি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও ছিলেন আগ্রসরচিন্তাসম্পন্ন মানবতাবাদী। ছিলেন শোষিত-বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত মানুষ, তাই শোষণ, পীড়ন, অসাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে একটি বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান হতে পারেন, আবার হিন্দুও হতে পারেন। তাঁর জন্ম খান্দান-খোন্দকার বংশে কিংবা কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চবর্ণে হলেও হতে পারে। কিন্তু যাপন করতেন নিম্নবর্গের বেশরা বা অবৈদিক জীবন। এক গাঢ় অভিমান ও ব্যথা নিয়ে প্রথাগত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ত্যাগ করেছিলেন সমাজ-সংস্কার, শিষ্ট সমাজের মেকি আচার-আচরণ ও কায়-কারবার। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বেছে নিয়েছিলেন গভীর নির্জন পথ। লোকালয় ছেড়ে বাসিন্দা হন ভিন্ন এক জগতের। গ্রহণ করেন নিগূঢ় লোকায়ত ধর্ম যার অপর নাম হিউম্যানিজম। কৌশলগত কারণে অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানে জন্ম, ধর্ম, বংশ ও পারিবারিক পরিচয় উহ্য রেখেছিলেন। জনারণ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খুঁজতে চেয়েছিলেন এক নিঃসীম একাকিত্ব। ডুব দিতে চেয়েছিলেন মনের অতলে। খুঁজতে চেয়েছিলেন অরূপ-রতন। কিন্তু কালের বৈরী প্রতিক্রিয়া, বিশেষত শোষণ, পীড়ন, নারীনিগ্রহ, জাতের নামে বাড়াবাড়ি, জমিদার-নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচার এই আত্মনিমগ্ন সাধককে রূপসাগরে ডুব দিয়ে থাকতে দেয়নি। বরং একতারা ফেলে আখড়া থেকে বেরিয়ে বাধ্য হন প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্দৈব তাণ্ডব রুখতে। অন্যায়-অবিচার, অসাম্য, ভেদবুদ্ধি, শক্তিমানদের তাণ্ডব রুখতে গিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন ‘মানুষ সত্যের উপাসক’। নির্দ্বিধ হয়েই ঘোষণা করতে চাই, তিনি ছিলেন মানবধর্মের মহিমায় উদ্ভাসিত এক বলিষ্ঠ লোকনায়ক। কেন লালনকে মরমী সাধক বলা হয়? আক্ষরিক অর্থে লোকনায়ক বলতে যা বোঝায়, সর্বতোভাবে তিনি ছিলেন তা-ই। আজকে যারা লালনের মুসলিম পরিচয় ও উৎস নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন, তারা জেনেশুনে অন্যায় করছেন। সত্যকে গোপন করতে চাইছেন। কিংবা তাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কোন উদ্দেশ্যে লালন সম্পর্কে তারা এ জাতীয় ভাষ্য বা বয়ান নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন, তা আমরা ভালভাবেই বুঝে নিতে পেরেছি। নিশ্চয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁকে নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করার মতলব আঁটা হচ্ছে।