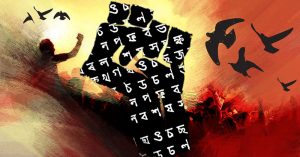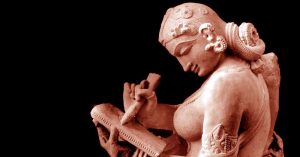কলকাতার গানের বাড়ি
বহু বছর আগের সেই রাত। তখনও কলকাতায় আসেনি বিদ্যুতের আলো। বাড়িতে বাড়িতে তখন রকমারি ঝাড়লন্ঠন আর বাহারি সেজবাতি। বহুবাজারের এই বাড়িতেও শিল্পী এবং অগণ্য শ্রোতার মাথার উপর জ্বলছে ঝাড়লন্ঠন। বেলজিয়াম-বর্ন কাটগ্লাসের প্রিজমে ছড়ানো নানা রঙের নকশা প্রতিফলনে ঠিকরে যাচ্ছে দেওয়ালের মার্বেলে। ছড়ানো কার্পেটে ভদ্রজন। চিকের আড়ালে মহিলারা রয়েছেন, দোতলার থামের আড়ালে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে পারাবত পরিবার। কী করে যেন জেনে গেছে তারাও যে, এই ক’রাতে শব্দ করতে নেই। গান চলছে যে! বেহাগের গান্ধারে নিবিষ্ট সবাই। পাঙ্খাবরদারের নিরন্তর আকর্ষণ ঝুলন্ত টানাপাখাকে দুলিয়ে দিচ্ছে চৌতালের তালে তালে। হেমন্তের রাতে গরম হয়তো তেমন নেই, কিন্তু বাজনের প্রয়োজন। কারণ এ গান গাইতে প্রচুর পরিশ্রম। বাট করছেন শিল্পী, নিখুঁত লয়ের মাপে। খানিক আগেই পাখোয়াজিকে একটু ছাড় দিয়েছিলেন শিল্পী। সুযোগ বুঝে বাদক প্রতিপক্ষকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলতে যাচ্ছিলেন প্যাঁচের কেরামতিতে কিন্তু পাল্টা প্যাঁচের কায়দায় শিল্পী বাদককে পরাস্ত করে ফেললেন। গানের খেলায় কার হার, কার বা জিত? এই পাখোয়াজিরাই অনর্গল একুশটা ধা মেরে ধ্রুপদিয়াকে আসর ছাড়া করে দিতে পারতেন আবার শিল্পী এমন ধ্রুপদ নিলেন যে, পাখোয়াজির সম খুঁজতেই প্রাণান্ত।
এই বাড়িতে এখন এক দুরন্ত বাট আড় কুয়াড় বিয়াড়– এর পাল্লা পেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে বসমে পড়ল। অনেক শ্রোতার কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল পানের পিক। ঘুমন্ত অনেক শ্রোতা হঠাৎ জেগে উঠলেন। সরবে হর্ষধ্বনি উঠল। “বেশ বেশ বেশ”। গৃহকর্তা অধিকারী মশাই অর্থাৎ রামকানাই অধিকারী নিজে পাখোয়াজি, পশ্চিমী শিল্পী মনমোহনের বিস্তর তালিম নিয়েছেন। শশব্যস্ত রামকানাই তারিফ জানিয়ে এলেন শিল্পীকে।
রামকানাই অধিকারীর সেই আমল আর নেই। নেই বহুবাজারের রাস্তা ধরে চলা ঘোড়ায় টানা ট্রাম, নেই জুড়িগাড়ি, পালকি, নেই সেই কার্পেট, রুপোর পানদানি। ঝাড়লন্ঠনের খাঁজে বিলিতি ওয়্যাক্স ক্যান্ডেল লাইটের বদলে এসে গেছে আধুনিক বাল্ব। বহুবাজার এলাকার শশীভূষণ দে স্ট্রিট ধরে নেবুলতার দিকে খানিকটা যেতেই ডানহাতি গলিতে লাল রঙের দুটি পুরনো বাড়ি চোখে পড়বে। একই গড়নের বাড়িদুটি, মাঝামাঝি একফালি পথদুটি বাড়িকে ভেদ করে চলে গেছে এবং সাকিন নম্বরও ভিন্ন হয়ে গেছে। সেকালের প্রাসাদনগরী কলকাতার শৈল্পিক জাতের মাপকাঠিতে হয়তো বাড়িটি নেহাতই সাদামাটা কিন্তু বাড়িটি নজর কারে এক নকশাদার অদ্ভুত সাঁকোর জন্য। দোতলায় রাস্তার আড় বরাবর এই ঝুলন্ত সাঁকো দুই বাড়ির সংযোগ সেতু– অন্দরবাসিন্দাদের এবাড়ি-ওবাড়ি পারাপারের পথ। গলি তস্য গলির কঙ্কালসার সব বাড়ির মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যবান, স্বতন্ত্র এবং আভিজাত্যপূর্ণ এই লাল বাড়িটি। বাড়ির নাম অধিকারী বাড়ি আর ঝুলন উৎসব খুব ঘটা করে হয় বলে আরেক নাম ঝুলনবাড়ি। এবাড়িতেই আদিপুরুষ রামকানাই জন্মেছিলেন ১৮৪৬ সালে, পিতামহ কৃষ্ণমোহন তেজারতি ব্যবসা করতেন। তিনিই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। রামকানাইয়ের আমল থেকে ব্যবসা আরো বড় হল। বাড়িটির সংস্কার এবং পুনর্বধন ঘটল শুধু সঙ্গীতের প্রয়োজনে। রে পামারের থামওলা সাঁকোও তৈরি হয়ে গেল ও বাড়িতে গান শুনতে যাবার জন্য। ক্রমে তাবড় গুণীর যাতায়াতের পীঠস্থান হয়ে উঠল এই বাড়িটি।
এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু যদুভট্টের গানে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন রামকানাই অধিকারী। সে ১৮৭০-৭৫ সালের কথা। হীরুবাবু-শ্যামবাবু থেকে শুরু করে এটি কানন, ভিজি যোগ, মশকুর আলি খাঁ সাহেব, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতন স্বনামধন্য শিল্পী এই বাড়িতে গান গেয়েছেন। যদুভট্ট রামকানাইয়ের থেকে ছ’ বছরের বড়, মাত্র ছেচল্লিশ বছরের জীবনে বিশাল খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। কে না তার শিষ্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই পুত্র জ্যোতিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ তালিম নিচ্ছিলেন যদুভট্টের কাছে। যদুভট্টের জোড়াসাঁকোর যাতায়াত এই বাড়ি থেকেই ছিল। বাংলার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যদুনাথ ভট্টাচার্য এক যুগান্তকারী পুরুষ। ১৮৪০ সালে জন্মগ্ৰহণ করেন যদুভট্ট। জীবনের অনেকটা সময় তাঁর কেটেছিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের খাদাকুড়ি গ্ৰামে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যদুভট্টের কাছে সঙ্গীত শিক্ষাগ্রহণ করলেও বন্দেমাতরম গানটির প্রথম সুর নাকি তৈরি করেছিলেন যদুভট্ট। ভাটপাড়ায় বসে তিনি এই সুর তৈরি করেন। সেইসময় এই গানটি তৈরি করা হয়েছিল রাগ- মালহার, তাল কাওয়ালি-তে।
‘জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। জোড়াসাঁকো বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা চলছে দেশীয় গানের চর্চা। বালক রবিকেও পাঠানো হল গান শেখার জন্য বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে। রবীন্দ্রনাথের যখন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স, বিষ্ণুপুর ঘরানার যদুভট্ট আসেন কলকাতায়। তাঁর কাছে শুরু হয় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা। অপরদিকে পাথুরেঘাটার প্রিন্স সুরেন্দ্রমোহন টেগোর বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে নাড়া বেঁধেছেন তখন। ফলে বিষ্ণুপুর ঘরানার সব তাবড় তাবড় গাইয়েদের সমাবেশ ঘটত জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা রাজবাড়িতে। বিষ্ণুপুর ঘরানা ও তার রাগগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আত্মিকতা ও ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনেক গানে।
কলকাতার শিল্পীরা, যেমন অঘোর চক্রবর্তী, বিহারীবাবু, রাধিকা গোস্বামী– এ বাড়ির নাড়ির টানে বাঁধা ছিলেন। পরবর্তী কালে দানীবাবু, মহিম মুখার্জি, যোগেন ব্যানার্জি, ধীরেন ভট্টাচার্য, দুর্লভ ভট্টাচার্য, কেশব মিত্র; আরও পরে রাজীবলোচন দে, দীনু হাজরা প্রমুখ অনেক ধ্রুপদিয়া পাখোয়াজির কলাক্ষেত্র এটি। চল্লিশের দশকে জ্ঞান গোস্বামী আসতেন। এখানে গান গেয়েছেন এ কানন, মালবিকা কানন। তাঁদের স্মৃতির পাতায় উঠে এসেছে নানা ঘটনা। কানন বলেছিলেন, নানা গুণীর পদচিহ্ন রক্ষিত এ বাড়িতে গান গেয়েই নাকি তিনি প্রাণঘাতী রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।
কলকাতায় এক সময় অনেক বাড়ির বেশ অন্যরকম পরিচয় ছিল। কোনওটা ঘড়িওয়ালা বাড়ি, কোনওটা পাখির বাড়ি, কোনওটা দোল-দুর্গোৎসব বাড়ি। এছাড়াও বেশ কিছু বাড়ি ছিল যাদের বুকের স্পন্দন বাঁধা ছিল সুরের সঙ্গে। ধ্রুপদ, ধামাল, খেয়াল, ঠুমরির স্রোত বয়ে যেত সে বাড়ির অন্দরে। তেমনই গানের বাড়ি বহুবাজারের অধিকারী বাড়ি। ধ্রুপদ-ধামারের ঐতিহ্য সংরক্ষণে যার অবদান বহুশ্রুত। আবার কলকাতার ঝুলন প্রসঙ্গে ‘ঝুলনবাড়ি’-র কথা বিশেষ উল্লেখ্য। এই নামেই পরিচিত বউবাজারের রামকানাই অধিকারীর বাড়ি। প্রায় ২০০ বছর আগে এই পরিবারের আদিপুরুষ কৃষ্ণমোহন অধিকারী ঝুলন উৎসবের প্রচলন করেন। পরে তাঁর পৌত্র রামকানাই অধিকারী সাড়ম্বরে এই উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। এই বাড়ির রাধাবল্লভ জিউর ঝুলন উৎসব আজও বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে। এ বাড়িতে এই ঝুলন উৎসব হয় পাঁচ দিন ধরে। আর তাই এই পাঁচ দিনে দেবতাকে বিভিন্ন বেশে সাজানো হয়। প্রথম দিন রাখাল বেশ, দ্বিতীয় দিন যোগী বেশ, তৃতীয় দিনে সুবল বেশ, চতুর্থ দিনে হয় কোটাল বেশ এবং শেষ দিনে রাজ বেশ। প্রথম দিনে হোম করে ঝুলন উৎসবের সূচনা করা হয়। এর পরে দেবতাকে এক এক দিন এক এক রকমের ভোগ নিবেদন করা হয়। পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও পাঁচ দিনের এই উৎসবে আত্মীয় সমাগম হয়। সঙ্গে চলে ধ্রুপদী সঙ্গীতের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আজও অধিকারী বাড়ি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই বাড়ির প্রতিটি অলিন্দে ধ্রুপদ ধামালের উচ্চারিত ধ্বনি, সুর ও মর্মর!
চিত্র: গুগল