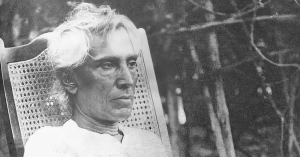দুর্গাপুজো এলেই আমাদের পাড়ার নিতাইদার তারস্বরে এই গগনবিদারী চিৎকার মনে পড়ে। আর টের পাই, দিনের পর দিন যে মা-বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে আজ জামাপ্যান্ট, কাল জুতো, পরশু বেল্ট কিনে এনে আসন্ন পুজোর মৌতাতে মশগুল থাকা, বা পূজাবার্ষিকী (আমাদের কৈশোরে দেব সাহিত্য কুটীর-এর শারদীয়া বার্ষিকীটি ছিল প্রায় একমাত্র আনন্দপাঠ, যেখানে শিবরাম-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-বনফুল-তারাশঙ্করের গল্প, কল্পবিজ্ঞান নিয়ে ক্ষীতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক, বিমলচন্দ্র ঘোষের ছড়া, পি. সি. সরকারের ম্যাজিকের ওপর লেখা নিয়ে প্রায় পাঁচশো পাতার মহাভোজের আয়োজন থাকত। ছিল বাজি, ঢাকের বোল, সকালবেলায় উঠোন জুড়ে বৃন্তচ্যুত শিউলির সুবাস ও সমারোহ, বাড়িতে রোজ দারুণ দারুণ সব খাবার, আর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে সে বছরে বেরোনো পুজোর গান শোনা,– হেমন্ত, লতা, সন্ধ্যা, সতীনাথ, মানবেন্দ্র! কিন্তু এর কিছুই পরিপূর্ণ আনন্দ এনে দিতে পারত না, পঞ্চমীর সন্ধ্যায় কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনার পর নিতাইদার সেই তারস্বরে চিৎকার, ‘দুর্গা মাঈ কী, জয়!’ শোনার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। তাই এখনকার দুর্গাপুজো যতই হাজার আলো-প্যান্ডেল-প্রতিমার জৌলুস আর পোশাক-আশাকে ভূষিত থাক না কেন, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিপূর্ণতার অভাব। অভাব টের পাই আরও অনেক কিছুর-ই। গ্ল্যামার বেড়েছে, আন্তরিকতায় ঘাটতি। পত্রপত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, মান নিম্নমুখী। অঞ্জলি বেড়েছে, ভক্তি কমেছে।
পুজো দেখা আমার অত্যন্ত শখের জিনিস। কেবল দুর্গাপুজোই নয়, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী, নবদ্বীপ-শান্তিপুরের রাস, কৃষ্ণনগরের বারো দোল, বারাসতের কালী আমাকে আকর্ষণ করে নানা কারণে। যাই কলকাতার টালিগঞ্জে আমার বাড়ির কাছেই আনোয়ার শাহ্ রোডে টিপু সুলতানের শাহী মসজিদে মহররম দেখতে, ওই এক-ই উদ্দেশ্যে যাই তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা-খ্যাত নারকেলবেড়িয়ায় মহররমের তাজিয়া দেখতে। মহাবোধি সোসাইটিতে দেখতে যাই বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধজয়ন্তী দেখতে। কলকাতায়, ঢাকায়, দিনাজপুর ও বরিশালের চার্চে বড়দিন আর গুড ফ্রাইডেতেও গেছি। চেষ্টা করেছি সবার রঙে রং মেলাতে। কলকাতাতেই দেখেছি গুজরাতিদের নবরাত্র, অসমীয়াদের বিহু, পঞ্জাবিদের নানকজয়ন্তী (ঢাকাতেও একবার), আর মালয়ালীদের ওনাম, সাঁওতালদের কর্মা, রাজস্থানীদের তীজ-সমারোহ। উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাবেশ, সমবেত আনন্দ উপভোগ, এসব দেখতে ভাল লাগে। সেক্ষেত্রে দুর্গাপুজো দেখার অভিজ্ঞতা তো সবচেয়ে প্রলম্বিত ও অধিক বৈচিত্র্যময়। মূর্তিনির্মাণ দেখা থেকে শুরু হয় আমার, আর শেষ হয় বিসর্জনে।
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ, দু’জায়গার দুর্গাপুজো দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তাই দুটি স্থানের পূজার মিল-অমিল নিয়ে কিছু বলি। বাংলাদেশের দুর্গাপুজো দেখার সূচনা আমার ১৯৯৮-তে। সেবার পুজো দেখবার জন্যই ঢাকায় আসা। ছিলাম সিদ্ধেশ্বরী লেনে। তাই ওখানকার কালীবাড়ির পুজোমণ্ডপ ঘিরে প্রতিমানির্মাণ দেখার সুযোগ ঘটেছিল। খেয়াল করলাম, এখানে মন্দির বা পুজোমণ্ডপেই প্রতিমা তৈরি করানো হয়। কলকাতার চেয়ে প্রথম পার্থক্য এটা। কলকাতায় সামান্য কিছু বনেদি বাড়ির পুজো ছাড়া প্রতিমা মণ্ডপে তৈরি হয় না, কুমোরপাড়া ও অন্য বেশ কয়েকটি প্রতিমা তৈরির স্থান থেকে প্রতিমা আনা হয়। দ্বিতীয় পার্থক্যটা আমাকে অবাক না করে পারেনি। ঢাকা বা সমগ্র বাংলাদেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুজোর চাঁদা আদায়ের চল খুব একটা নেই। মণ্ডপে এসেই পাড়ার লোক চাঁদা দেন। জবরদস্তি করে চাঁদা আদায়ের যে বীভৎসতা কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আছে, তা অন্তত ঢাকা আর বরিশালে দেখিনি। পুজোর দিনেও অনেকে এসে প্যান্ডেলের পাশে চাঁদা আদায়কারীদের টেবিলের সামনে এসে চাঁদা দিয়ে যান। পাড়ার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। স্বেচ্ছায় এসে চাঁদা দিয়ে যান। এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার অন্যতম বড় দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন মহম্মদ আলী পার্কের মুসলমানরা। আরও আশ্চর্যের, কলকাতার দক্ষিণ বন্দর এলাকার দুর্গাপূজা কেবল মুসলিমদের উদ্যোগেই যে হয় তা-ই নয়, এ পূজার পুরোহিত-ও একজন মুসলিম,– শেখ জাহাঙ্গির!
বাংলাদেশের দুর্গাপ্রতিমার মুখে দেবীভাবটা বড় মধুর। কলকাতা, বা সারা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কুমারটুলি আর কৃষ্ণনগরে দেবীমূর্তির অসাধারণত্ব আছে যেমন, আবার বছর ত্রিশ-চল্লিশ ধরে ‘থিমপুজো’ বলে অভিনব মূর্তি মাটি ছাড়া নানা বস্তু দিয়ে তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে শৈল্পিকতা আছে কোথাও কোথাও, আছে কিছু উদ্ভটত্ব-ও। স্বনামধন্য শিল্পীদের মধ্যে রমেশ পাল কিংবদন্তি হয়ে আছেন। আছেন সনাতন রুদ্রপাল। বাংলাদেশে প্রতিমা নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই সম্ভবত। তবে কী চট্টগ্রাম, কী বরিশাল, আর কী ঢাকা-দিনাজপুর, প্রতিমায় অতীন্দ্রিয়তা ও অনশ্বর বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। আর একচালা প্রতিমাও এখানকার বৈশিষ্ট্য। কলকাতার প্রতিমা একচালা সাধারণত পারিবারিক পুজোয়। বিচ্ছিন্নভাবে রাখা মূর্তিগুলিই বেশি।
কলকাতার পুজোমণ্ডপে আলোকসজ্জার তুমুল বাড়াবাড়ি। চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা এই কাজে দক্ষ। দর্শক আলোকসজ্জায় মোহিত হয়ে মূল যে মূর্তি, অনেক সময়েই তার দিকে মনোযোগী হতে পারেন না। বাংলাদেশের পুজোপ্যান্ডেলে আলোকসজ্জার এ-হেন বাড়াবাড়ি নেই। মূর্তি-ই প্রধান এখানে। সীমিত অথচ দৃষ্টিনন্দন আলোয় মণ্ডপ আলোকিত হয়। তবে ইদানীং কলকাতার অনুকরণে ঢাকাবাসীরাও প্রচুর আলোকসজ্জায় মাতছেন।
কলকাতার পুজোয় সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় মহম্মদ আলী পার্ক ও কলেজস্ট্রিটকে কেন্দ্র করে। লাখেলাখে দর্শক। বলা হয়ে থাকে, মূল প্রতিমা দর্শনের আগে ভিড়ে এত লোকের পাদুকা পদচ্যুত হয় যে, তা সংগ্রহ করতে পারলে গোটা দশেক জুতোর দোকান দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখেছি ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুজোয় দিনের বেলাতেই দর্শনার্থীদের যে ভিড় হয়, তা মহম্মদ আলীর রাতের ভিড়কে লজ্জা দেবে। ভিড় হয় ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে, রমনা কালীবাড়িতে, গুলশনে, বনানী, খামারনাড়ি ও সিদ্ধেশ্বরীর মণ্ডপে। তবে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যশালী পুজোর আয়োজন না দেখলে ঢাকা তথা বাংলাদেশের দুর্গাপুজো দেখা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংখ্যায় প্রচুর, আয়োজনে উদার ও আতিথ্যে অকৃপণ (তা অবশ্য বাংলাদেশের সর্বত্র)। অলিতে গলিতে পুজো এখানে।
আর আছে ঢাকা বিশ্নবিদ্যালয়ে জগন্নাথ হলের পুজো। বাংলাদেশেও মৃৎশিল্পীদের পাড়ায় প্রতিমা তৈরি হয়ে মণ্ডপে নিয়ে আসার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। দিনাজপুর জেলার গোন্দলগ্রাম বাংলাদেশের এক আশ্চর্য গ্রাম, যেখানে গিয়ে জেনেছি, নিকট অতীতেও এ-গ্রামে কোনও মুসলমানের বাস ছিল না। এখন আছে। গ্রামে বেশ কয়েকঘর কুমোরের বাস। দেবমূর্তি গড়া ছাড়াও হাঁড়িপাতিল ইত্যাদিও গড়েন তাঁরা, দারিদ্র্যজীর্ণ জীবনের মাঝেও। তাঁদের মুখের একটি প্রবাদ স্মৃতিধার্য হয়ে আছে, ‘হাত্তি ঠেলা যায়, কাত্তি ঠেলা যায় না’, কিনা হাতিকে ঠেলা দিয়ে নড়ানো গেলেও কার্তিকের নিরন্নতা ঠেলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। একদা এরকম অবস্থা থাকলেও এখন আর এমন দৈন্য নেই আর। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক পুজো-আয়োজকদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে।
কলকাতার নতুন এক সংযোজন ‘খুঁটি পুজো’, অর্থাৎ যে বাঁশ দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হবে, তার আরাধনা! এ জিনিস অদ্যাপি বাংলাদেশে অজ্ঞাত। সম্ভবত কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবগুলো মরশুমের শুরুতে যে ‘বারপুজো’ (গোলপোস্ট) করে, তার-ই অনুকরণ এটা।
কলকাতায় পুজোর সময় অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কালীঘাট মন্দিরে। মন্দিরচত্বরে কোনও দুর্গাপুজো হয় না। তবে বিকেল থেকে এয়োস্ত্রীদের সিঁদুর খেলা হয়। সেসময় ওখানে কোনও পুরুষমানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। দুর্গাপুজোয় কালীমন্দিরে সিঁদুরখেলা, এ এক অভিনব অনুষ্ঠান বৈকি!
ঢাকার বাইরে বরিশালে একবার পুজোর প্রতিমা দেখা ও মূল্যায়নের অন্যতম বিচারক হওয়ার সূত্রে দেখেছি, বরিশাল শহরের বেশ কয়েকটি পুজোর আয়োজন কত সম্ভ্রান্ত! দেখে মুগ্ধ হয়েছি কাশীপুরের মুখার্জি পরিবারের পুজো, মাধবপাশার পুজো। তবে বাংলাদেশের সবচেয়ে জৌলুসপূর্ণ এবং সম্ভবত দুই বাংলার সর্ববৃহৎ আয়োজনের পুজোটি দেখা হয়নি এখনও। সেটি হল বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ হাকিমপুরে শিকদারদের বাড়ির পুজো। শুনেছি পাঁচশোর ওপর মূর্তি থাকে সেখানে। পরমাশ্চর্য!
কুমারী পূজা। বাংলাদেশের নানা জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের পুজোগুলি সম্ভ্রান্ততা ও ভক্তির সংমিশ্রণে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে স্বভাবতই আয়োজন সবচেয়ে বেশি, যেখানে ১৯০০ সালের রীতি অনুসরণ করে (স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরে সেবার প্রথম কুমারীপুজো করেছিলেন) কুমারীপুজো হয়ে থাকে, যা মিশনের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠেও হয়। তাছাড়া চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, বরিশালের মিশনেও দেখেছি শুদ্ধাচারে পুজো অনুষ্ঠিত হতে। দেখেছি বেলুড়েও। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে-বাংলাদেশে কোনও ভেদ নেই। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে প্রতিবারের মতো এ বছরেও মহাষ্টমীর দিন কুমারী পূজা হয়েছে। সাতবছরের মেয়ে লাবণ্য চট্টোপাধ্যায় পূজিতা হয়েছে এবার, শাস্ত্র অনুযায়ী যার নাম হয়েছিল ‘মালিনী’।
দুর্গাপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ঢাক। ঢাক, শিউলি-কাশফুল আর আকাশে সাদা মেঘ, দেবী দুর্গার অবধারিত আবহ। সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার গান। ঢাকের কথায় মনে পড়ে, পুজোর দু-তিন দিন আগে থেকে শিয়ালদা স্টেশন ঘিরে ঢাকিরা তাঁদের বাদ্য নিয়ে জড়ো হন, আর সমানে শ’য়ে শ’য়ে ঢাক বাজতে থাকে চত্বর জুড়ে। এঁরা বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ঢাকি, পুজোপ্যান্ডেলে ঢাক বাজানোর অর্ডার পেতে সমবেত। বৃহত্তর কলকাতার পুজো-উদ্যোক্তারা এখান থেকে ঢাকি সংগ্রহ করে নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যান, পুজোর ক’দিন মণ্ডপে রাখেন, খাদ্য জোগান, মজুরি দেন, যাতে পুজোয় ঢাকিদের বাদ্যে মুখরিত হতে দেখা যায় পুজোমণ্ডপ।
এ জিনিস বাংলাদেশের কোথাও কোথাও আছে। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি এর একটি উদাহরণ। জনশ্রুতি আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে স্থানীয় সামন্তরাজা নবরঙ্গ রায়ের আমল থেকে এর সূত্রপাত। নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, হবিগঞ্জ থেকে ঢাকিরা আসেন পুজোর ক’দিন ঢাক বাজাবার বরাত পাওয়ার জন্য। এটা এখানকার বার্ষিক চিত্র।
কলকাতায় যেমন, তেমনই বাংলাদেশেও কেবল নারীদের পরিচালনায় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ জেলার সাহাপাড়ায় (কোটচাঁদপুরে) হয় পুজোটি। উদ্যোক্তা নবারন মহিলা সঙ্ঘ। সভাপতি বেবিরাণী সাহা।
মৃৎশিল্পী সঞ্জিত পাল। মাদারীপুরের এই শিল্পীর দাবি, ১৯৯০ থেকে তিনি প্রতিমা গড়ে আসছেন। এ পর্যন্ত তিনি নাকি পঞ্চাশ হাজার প্রতিমা গড়েছেন। দেবী দুর্গা ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, এসব মিলিয়ে।
একসময় কলকাতায় পুজোর সময় নতুন নতুন সব সিনেমা আসত হলে। ছিল পুজোর গান। এখন সেসব কেবল স্মৃতি। নামকে ওয়াস্তে এক-আধটা ছবি রিলিজ করে হয়ত, আর ফল্গুর অন্তঃস্রোতের মতো পুজোয় কিছু গান-ও বেরোয়। তবে সে গান নিয়ে সঙ্গীতরসিকদের এখন আর আদৌ আগ্রহ আছে কি না সন্দেহ। বাংলাদেশে কিন্তু পুজোয় ছবির উদ্বোধন হচ্ছে, খবর বেরিয়েছে, পূজায় ‘বান্ধব’ নিয়ে আসছে মৌ’! অভিনেত্রী মৌ খান পরিচালক সুজন বড়ুয়ার এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর হ্যাঁ, পুজোর গান-ও বেরিয়েছে ঢাকায়। আর রেডিও-টেলিভিশনে পুজোর ক’দিন পুজোর গান পরিবেশিত হচ্ছে, থাকছে পুজো নিয়ে হরেক অনুষ্ঠানমালা।
পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের বাঙালি-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে প্রতিবছর বেরোয় অসংখ্য পত্রপত্রিকা। বাংলাদেশে বেরোয় ঈদে। কিন্তু বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো পুজো উপলক্ষে ক্রোড়পত্র বের করে। চার বা দুপৃষ্ঠার। তাছাড়া ঢাকেশ্বরী মন্দির, বিভিন্ন পুজোসংগঠনে যুক্ত বিভিন্ন ক্লাব, এরাও করে। দেশের সব গুণী লেখকদের রচনা স্থান পায় এসব পত্র-পত্রিকায়।
দিনাজপুরের মতো শার্শার মৃৎশিল্পীদের কথাও একটু বলা যাক। শার্শা বনগাঁ থেকে সামান্য দূরে, বেনাপোলে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে কুমোরপাড়া, যাঁদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র কুড়ি-বাইশ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। শার্শার বেনাপোল, গোড়পাড়া, লক্ষ্মণপুর, জামতলা, ললিত পাল, চায়না রানি পাল, জগন্নাথ পাল। বালুন্ডা ও বগআঁচরায় ২৪/২৫ ঘর মৃৎশিল্পীদের বাস। মাটির পুতুল গড়েন মূলত। মাটির মূর্তির পাশাপাশি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য মাটির খেলনাও বানান এরা। তবে প্লাস্টিকের দাপটে পিছু হটছে তাঁদের কারুবাসনা!
দুর্গাপুজোয় লাগে একশো আটটি পদ্ম। বর্ধমান, বীরভূম মূলত এসব বিপুল চাহিদা জোগান দেয়। বাংলাদেশে নদী খাল বিল অফুরন্ত। তাই পদ্মের অভাব নেই। তবুও সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায় সোনাকান্ত বিল পদ্মে ভরে যায় এসময়ে। আর কাশফুল? নদীর চরে, জলাভূমিতে কিংবা পাহাড়ি এলাকায় এই ঘাসজাতীয় উদ্ভিদটি দেখতে পাওয়া যায়। তেমনই ফুলে ভরে ওঠে হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, পদ্মাপাড়ের চর আর নেত্রকোনার পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে।
ঢাকায় দেখেছি বিবাহিত মহিলারা পুজোয় নতুন শাঁখা কিনে পরেন। ঢাকার শাঁখারীবাজার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাঁখাশিল্পে নিয়োজিত। অসংখ্য কারুকাজমণ্ডিত তাঁদের শাঁখা। থিমপুজোর সন্ধান মিলল নাটোরে। মুসুর ডালের দুর্গামূর্তি।
প্রসঙ্গ শেষ করব বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের লোকজন মিলে সারাবছর ধরে মুষ্টিভিক্ষার মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তা দিয়ে পুজো আয়োজনের কথা বলে। সাতানিপাড়ায়। মহল্লার বিয়াল্লিশটি পরিবার থেকে মুষ্টির চাল সংগ্রহ। এ যেন রাই কুড়িয়ে বেল! সম্বৎসর সংগ্রহ করে যা ওঠে, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে মাতৃ-আরাধনা! তুলনারহিত!
সব পরিক্রমা, বিসর্জন আর সুখস্মৃতির শেষে কানে বাজে নিতাইদার উদাত্ত কণ্ঠ, ‘জয় দুর্গামাঈ কী!’
চিত্র: ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দুর্গাপুজো।