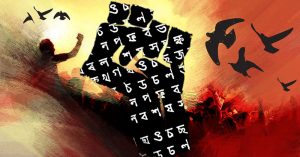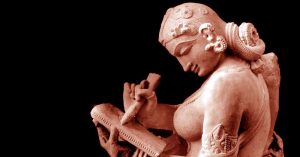অথ রসিকরাজ বঙ্কিমচন্দ্র রসোপাধ্যায় কথা
দুর্গেশনন্দিনী-তে বিদ্যা দিগগজ গজপতির ‘মনোমোহিনী’ আশমানি তাঁকে উপন্যাসের অনন্য চরিত্র বিমলা প্রদত্ত ‘রসিকরাজ রসোপাধ্যায়’ উপাধি দ্বারা সম্বোধন করত রসিকতা করে। আমরা গজপতি-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁরই শেখানো বিশেষণে বিশেষিত করলাম তাঁর নায্য প্রাপ্য তাঁকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। তাঁর সমগ্র সাহিত্য পাঠে বিশেষ রসাস্বাদনের আনন্দ-ঘন অভিজ্ঞতা পাঠকদের সঞ্চয়ে রয়েছে, আমরা জানি। আমরা ‘সাহিত্যসম্রাট’-এর সাহিত্য-সাম্রাজ্য থেকে কেবল উপন্যাস-অঙ্গনে ঘুরে যে রস-সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি সে সকল থেকে কতিপয় মাত্র বর্তমান নিবন্ধের পাঠকসমীপে তুলে ধরতে চাই। তার আগে মনে করিয়ে দেওয়া উচিতকর্ম যে, অনেক ‘নীরস সিঁড়ি’ ভেঙে তবে তাঁর রসের সাগর থেকে অঞ্জলিভরে রস তুলে আনতে হয়। আত্মসচেতন স্রষ্টা নিজেই গল্প শোনানোর ফাঁকে পাঠকদের শুনিয়ে দিয়েছেন সে বার্তা। দরিদ্র কালিদাসকে ফুল দিত রোজ এক মালিনী। তার দাম দিতে না পেরে কবি তাঁকে তাঁর রচিত কাব্যের প্রথম শ্রোতা হওয়ার ‘মান’ দিতেন। মালিনী একদিন ‘মেঘদূত’ শুনতে শুনতে বলল, তোমার কবিতায় রস কই? কালিদাস বললেন, স্বর্গে উঠতে গেলে লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তেমনি তাঁর ‘মেঘদূত কাব্য-স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে’ এবং নীরস কবিতাগুলি সেই সিঁড়ি। কালিদাসের কাহিনি শুনিয়ে এরপর বিষবৃক্ষ-স্রষ্টা বললেন, তাঁর এই কাব্যের ‘‘রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকপ্রেমী মধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙিলে সে রসমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না।’’ বস্তুত সব ক’টি উপন্যাসেই তিনি এভাবে ‘নীরস পরিচ্ছদ’ মাঝে মধুর রসের ঝিকিমিকি ফুটিয়েছেন। কিছু নমুনা দেওয়া যাক যেগুলি থেকে গজপতি সম্পর্কে উচ্চারিত তাঁর একটি মন্তব্য তাঁর নিজের সম্পর্কেও যে কতখানি প্রযোজ্য তা স্পষ্ট হবে। মন্তব্যটি এরূপ, ‘‘তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক; রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল।’’ গজপতি যেদিন তেমন তৃষ্ণার প্রাবল্যে সুন্দরী বিমলাকে দেখে বলে ফেলল, ‘‘দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে। সেদিনই বিমলা তাঁর নাম রেখেছিল, ‘রসিকরাজ রসোপাধ্যায়।’’ গল্প জমিয়ে তুলতে তুলতে নানাপ্রকারের রস পরিবেশন করার ‘তৃষ্ণা’ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও ‘বড় প্রবল ছিল’। রস নির্মল হাস্যরস, কৌতুকরস হয়, আবার মর্মস্পর্শী করুণ রসও হয়। নিজ কাহিনিতে সর্বপ্রকার রসসিঞ্চনেই তিনি হয়েছিলেন সিদ্ধকাম।
রমণীর রূপ বর্ণনায় দক্ষ রসিকরাজের সৃষ্ট নির্মল হাস্যরসের দুটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। দুর্গেশনন্দিনী-র তিলোত্তমা ও বিমলার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে তাঁর রসিকমনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন দেখে নেওয়া যাক। ‘‘পাঠক কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমলপ্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন?… যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপে অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, সে এ মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায় এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণকম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।’’ এখানে সাহিত্যসম্রাট পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়ে তার প্রেমিকমনে যে রস সঞ্চার করতে চেয়েছেন তা হল নারী সৌন্দর্য্যের পৃথকীকরণসঞ্জাত কামনামুক্ত, প্রেম-প্রদীপ্ত মনের আধারে পুঞ্জীভূত অনুভূতির কোমল রস। পাশাপাশি তাঁর রসিকমনের প্রকট প্রকাশ ঘটেছে অ-যুবতী বিমলার দেহসৌন্দর্যের প্রাচুর্য বর্ণনায়। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়ার বেশভূষা। কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়। যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক; পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিবেন। বিমলার দেহ-মনের রস-সংবাদ দিতে গিয়ে যে পরিহাস তার স্রষ্টা প্রবীণ পাঠকের সঙ্গে করলেন তাতে তাঁর প্রচুর পরিমাণে রসসিক্ত মনের পরিচয় আর অপ্রকাশিত থাকতে পারে না।
দিগগজ খেতে বসেছে। ব্রাহ্মণের বাকবন্ধ আহার। আশমানি এসে সে সময় তাঁকে উপকথা শোনানোর উপদ্রব শুরু করল এবং তাঁকে তার এঁটো খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করার কৌশল অবলম্বন করল। রূপবতী আশমানির পানে চেয়ে গল্প শুনতে শুনতে দিগগজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাত্রস্থ হাত, নিকটস্থ মাখা ভাতের গ্রাস তুলিয়া, চুপি চুপি দিগগজের মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগগজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশমানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ‘তবে রে বিটলে, আমার এঁটো নাকি খাবিনে?’ (দুর্গেশনন্দিনী)
বাক্য দিয়ে এমন উপভোগ্য চিত্র আঁকা কত সহজে সম্ভব করেছেন রস-বিশেষজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র। পাঠক পড়তে পড়তে জীবনের সর্বপ্রকার, গ্লানিভার মুক্ত হতে পারবেন তবেই না সে সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে যথার্থ সাহিত্য পদবাচ্য! একলা পাঠকও প্রাণভরে না হেসে পারবেন না বর্ণিত দৃশ্যখানি মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট কল্পিত হতে দেখে। নির্মল হাস্যরস পরিবেশনে দক্ষতার আর একটি নমুনা। ‘‘এই পুরী বহু সংখ্যক আত্মীয়, কুটুম্ব, কন্যা ভগিনী, পিসীত ভগিনী, বিধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য, পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প পরনিন্দা, বালকের হুড়োহুড়ি, বালিকার রোদন, ‘জল আন’, ‘কাপড় দে’, ‘ভাত রাঁধলে না’, ‘ছেলে খায় নাই’, ‘দুষ নাই’, ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর রন্ধনশালা। সেখানে আরও জাঁক… কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া আছেন, কেননা তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ স্নানকালে বহুতৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাজি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন যেন রাখাল পাচনীহস্তে গোরু ঠেঙাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা লাউ, কুমড়া, পটল, শাক কুটিতেছে; তাহাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণা তুলসী প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাগীর শরীর গৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছৌ মারিতেও ছাড়িতেছে না।… কোথাও অনধিকার প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাতা অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বন করিতেছে।’’ (বিষবৃক্ষ) সামনে দেখা দৃশ্যও যেন এত প্রকাশ্য হয় না যেমন করে সাহিত্যসম্রাট তুলে ধরেছেন তাঁর অনুপম বর্ণনায়। তার উপর তাতে আবার সে বর্ণনা রসে টইটুম্বুর।
কৌতুক-রস পরিবেশনে আধুনিকতা লক্ষনীয়— ইন্দিরা ধনীকন্যা। দরিদ্র শ্বশুরঘরে তাকে পাঠানো হয়নি। অতঃপর প্রচুর অর্থলাভে সক্ষমতা অর্জন করে তার স্বামী পিতৃগৃহকে ইন্দিরার বাসযোগ্য করে তুলল। ইন্দিরার জবানীতে জানা গেল— ‘‘তারপর আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ‘আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র, নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জনা করিবেন, হাল আইনে তাঁহাকে ‘আমার উপেন্দ্র বলিয়া ডাকাই সম্ভব’), বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটিতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।’’ (ইন্দিরা) বঙ্কিমচন্দ্রের কালে আমার উপেন্দ্র বলার সাহসিকতা নায়িকার মুখ দিয়ে প্রকাশ করে যে আধুনিকতা আমাদের আলোচ্য সাহিত্যস্রষ্টা দেখিয়েছেন তাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পর্কিত সেকালের রক্ষণশীল মনোভাব বিষয়ে তাঁর কৌতুকপূর্ণ মনোভাবেরও স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। আরেকটি ক্ষেত্রেও একই বিষয়ে তাঁর পরিহাস-প্রিয় মনের অভিব্যক্তি লক্ষনীয়। ইন্দিরার ছোট বোন কামিনীর প্রশ্নের উত্তরে শ্বশুরবাড়ি কেমন তার বর্ণনা দিয়েছে ইন্দিরা— ‘‘সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র ওঠে।’’ (ইন্দিরা) এই বর্ণনায় যুবতী ইন্দিরার স্বপ্নিল মনের মনোভাব চিত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে তার নির্মাতার বিবাহে ইচ্ছুক বাসনানুভবও বাক্যে রূপ নিয়েছে। একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিকতাকামী মনের কামনাও বাক্যগুলিতে রূপায়িত হয়েছে। কালের বদল চেয়েছেন তিনি এবং এভাবে সে চাওয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
করুণ রস ফোটানোর কারিগর রজনী জন্মান্ধ যুবতী এবং দরিদ্রঘরের কন্যা। তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা তাই ক্ষীণ। সে সেকথা বিলক্ষণ জানে। তবু সে বিয়ে করে ফেলল একাধিকবার স্বয়ম্বরা হয়ে। সে মনুমেন্টকে বিয়ে করে ‘মনুমেন্টমহিষী’ হল পনের বছর বয়সে। সতের বছর বয়সে সে আরেকটি বিয়ে করে ফেলল। প্রতিবেশী কায়স্থ কালীচরণ বসুর চারবছরের শিশুপুত্র বামাচরণ হল তার বর। একদিন একদল বরযাত্রী রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে দেখে বামাচরণ জানতে চাইল কে অমন সেজে যাচ্ছে। রজনী বলল, বর যাচ্ছে বিয়ে করতে। শিশু বায়না ধরল সে ‘বল’ হবে। তার কান্না থামে না। একটি সন্দেশ তার হাতে দিয়ে রজনী প্রশ্ন করল, ‘‘কেমন, তুই আমার বর হবি?’’ শিশু সম্মতি জানাল, হব। এবার ইন্দিরা-স্রষ্টার কাছে পাঠক শুনতে পেল করুণ রসের কাহিনি শোনানোর অভিনব স্বর— ‘‘সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, ‘হাঁ গো, বলে কি কলে গো?’ বোধ হয়, তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি (রজনী ফুলওয়ালি) বলিলাম, ‘বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।’ বামাচরণ স্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।
আমার এই দুই বিবাহ। এখন একালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য, আমি সতী বলাইতে পারি কি?’’ (রজনী) এখন একে অবশ্য করুণ রস না ব্যঙ্গরস বলা যাবে তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে একে তীব্র, সরস ব্যঙ্গে ভরা করুণ রস বললে সে সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কথা নয়।
কৌতুক ও করুণ রসের মিশ্রণ তৈরিতে সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাচিকা ‘বুড়া বামন ঠাকুরাণী’-র সাধ হয়েছে সে বাড়ির কর্ত্রী ‘গৃহিণী’-র মতো চুলে কলপ দিয়ে চুল কালো করবে। ইন্দিরার কাছে সাহায্য চাইল সে এ ব্যাপারে। ইন্দিরা তাকে কলপের শিশি দিল। তারপর উভয়ের বয়ানে শোনা যাক পরের বৃত্তান্ত, ‘‘ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী, রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে, অন্ধকারে তাহা চুলে মাখাইয়াছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই, কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকালবেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলো পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত, কিছু সাদা, কিছু রাঙা, কিছু কালো; আর মুখখানি কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনি বেড়ালের মত। দেখিবামাত্র পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে যখন পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া ওঠে। হারানী হাসিতে হাসিতে বেদম হইয়া সুভাষিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, বৌঠাকুরাণী, আমাকে জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়িতে থাকিতে পারিব না দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব কোন্ দিন।’’ (ইন্দিরা) পাচিকাঠাকুরাণীর করুণ অবস্থা যেমন সত্য তেমনই সত্য করে তোলা হয়েছে অন্যদের কৌতুকবোধ। রসিকোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানাও সত্য হয়ে উঠেছে তাতে।
জড় প্রকৃতির বর্ণনাতেও একই ক্ষমতার বহিপ্রকাশ লক্ষ করে তাঁকে প্রণতি জানাতে হয়। বঙ্কিম-কলমে স্ফুরিত হয়েছে সোজাসাপটা সত্য। ‘‘কত তুমি জড় প্রকৃতি, তোমায় কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,-জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিনী। কালী তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। যেন কত আদর জান আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্য সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি মা তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।’’ (চন্দ্রশেখর) এই ‘কোটি কোটি প্রণাম’ নিবেদনের মধ্যেও চারিয়ে দেওয়া হয়েছে করুণ ও কৌতুক রসের ধারা। বস্তুত গোটা বিশ্বপ্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনই এমন হেঁয়ালি-ভরা। এমন ‘‘জীবন লইয়া কি করিব?’’ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান রত থাকার নাম-ই তো মানব জীবন! জীবনকে যেমন যুক্তির বশে তেমনই অনুভবের রসে ভরিয়ে তোলার মন্ত্রে শুনিয়েছিলেন রসিকরাজ রসোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র।
চিত্র: গুগল