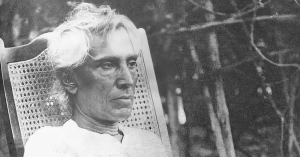ভা স্ক র দা স
ডানপন্থী দেশের গাড়িতে সামনের সিটের যাত্রীকে ডানদিকে বসতে হয়। আর বসলেই বাঁ হাতটা চলে যায় মাথার পেছনে, টেনে আনে সিটবেল্টটা। ট্র্যাফিকের নিয়ম কড়া, তার ওপর পেছনের সিটে বসা ছয় বছরের নাতনির নিয়ম করে উচ্চারণ করা সাবধানবাণী উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। জন্মইস্তক ওদেশেই, তবু অনর্গল প্রায় শুদ্ধ বাংলায় তার বকম বকম চলছেই। তার মধ্যে তার দাদা আর দিদুনকে নানারকম শাসন আর শিক্ষা তো আছেই।
তাতে অবশ্য ভালই হয়েছে। এই রাস্তার যে অংশটা বিচের ধার দিয়ে, সেখানে সমুদ্র ডানদিকে। জানলা দিয়ে চোখের ইশারায় তাকে ডাকাডাকি করতে কোনও বাধা নেই। এখানে মানে আমেরিকার অরিগ্যান রাজ্যের পোর্টল্যান্ড থেকে লিঙ্কন সিটি যাবার রাস্তায়। শেষটাই লক্ষ্য। ওখানে আজ, মানে ২৫ জুন ২০২৩ দুদিনের ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবের দ্বিতীয় দিন।

পেরিয়ে আসা বাকি রাস্তার প্রায় সবটাই ছিল বিশাল মাপের গাছের বনভূমির বুক চিরে চলা। রাস্তার দুধারে এক-দেড়শো ফুট উঠে যাওয়া রেডউড, পাইন, বার্চের ঋজু কাণ্ড, তাকে ঘিরে সমকোণে বেরিয়ে থাকা পাতাভরা ডালপালার সমাহার। কাচবন্ধ গাড়ির জানালা ভেদ করেও তার বনজ গন্ধ ভেতরে পৌঁছে যায়। রাস্তার পাশের দাঁড়ানোর বে-তে গাড়ি রেখে দরজা খুলে বাইরে এলে তার নিজস্ব শব্দরাও পাশে এসে বসে। ঠান্ডা হাওয়া মুখ গলার অবারিত চামড়ায় ছোঁয়– রোদে দাঁড়ালে সেটা আদর, কিন্তু ছায়া হলেই হুলের মতো ফোটে। বেশ ক’বার এই ধরনের পথে যেতে যেতে ওদের সঙ্গে একটা জানপহেচান হয়ে গেছে। তাই এলেই এখন মান্না দের গানটা মনে পড়ে যায়। ‘আজ আবার সেই পথে, দেখা হয়ে গেল…’।
বাঁদিকে অরণ্য যেখানে নাতিউচ্চ টিলার গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছে, সেখানে কিছু দূরে দূরে দেখা যায় বড় রাস্তার ধার থেকে পায়ে চলা পথ শুরু হয়ে আড়াআড়ি চলে যাচ্ছে বনের গভীরে। তাদের কিছু কিছুর মুখে সাইনবোর্ড, তাতে লেখা ‘গোল্ডেন ট্রেল’ কিংবা ‘বিইকন ট্রেল’। আসলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এই কোস্টাল নিচু পাহাড়শ্রেণির অরণ্যে একসময় বাস করত প্রাচীন আদিবাসীরা। প্যাসিফিক নর্থ-ওয়েস্টের এই প্রাকৃতিক আবাসে আজ থেকে ছ’হাজার বছর আগে থেকে আমেরিকার আদি বাসিন্দারা সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা ছিল hunter gatherer অর্থাৎ শিকারনির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কৃষিকাজের সঙ্গে কোনও সংশ্রব ছিল না তাদের। পরবর্তী কালে ইউরোপ থেকে এসে নব্য আমেরিকান হওয়া মানুষরা বারবার এই অ্যালসি (Alsea) গোষ্ঠীর মানুষদের সমুদ্রের পাড় থেকে বাস্তুচ্যুত করে বনের ভেতরের দিকে ঠেলে দেয়, বাধ্য করে সামুদ্রিক প্রাণীশিকারের পরিবর্তে বনের ফলপাকড় আর নদীর পাড়ে কৃষিকাজ করে জীবনধারণ করতে। অনভিজ্ঞতায় ব্যর্থ হয় তাদের প্রচেষ্টা। পুরনো পরিচিত জীবনযাপনের তাগিদে বারবার তারা আসতে চেষ্টা করে সমুদ্রের পাড়ে। আর বারবার তাদের হঠে যেতে হয় নব্য আমেরিকানদের পেশীশক্তির কাছে হার স্বীকার করে। পাহাড়ের পিঠ জুড়ে তাদের সেই পায়ে চলা পথের চিহ্ন আজ বেঁচে আছে এখানকার এক বিস্তৃত পাকদণ্ডীজাল হয়ে, আজকে যাদের ডাকা হয় ট্রেল বলে। ছুটির দিনে ব্যাকপ্যাক পিঠে চাপিয়ে এসব রাস্তায় কয়েক ঘণ্টার হাইকিং আজ আমেরিকানদের প্রিয় যাপন, তাদের বাচ্চাদের প্রকৃতিপাঠের ব্ল্যাকবোর্ড।

এমনি করে প্রায় দুঘণ্টা কেটেছে। কিছুটা হঠাৎ করেই ডানদিকে গাছপালা শেষ, বালির চরের অপার বিস্তারের ওপারে সমুদ্রের নীল জল। নীল শাড়িতে সাদা ঢেউয়ের ইঞ্চি পাড়। পুরীর সমুদ্রের ঢেউয়ের শোভা বা বিক্রম, দুইই বাড়ন্ত। যেন শাসনে থাকা সভ্য শিশুর মাপা উচ্ছ্বাস। পেটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়লে এগিয়ে এসে পায়ের পাতাটুকু ছুঁয়ে ফিরে যাবে। হাওয়া যদিও মাত্রাছাড়া। সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে বিচে দাঁড়ানো বসা মানুষগুলোর পোশাক, তাদের মাথার কাপড়ের ছাউনির ওড়াউড়ি দেখলে।
আমরা যে এসে গেছি লিংকন সিটি বিচে! তাকে চেনা যাচ্ছে সেখানে ওড়া ঘুড়ির সমারোহ দেখে। আজ এখানেই কাইট ফেস্টিভ্যাল। খালের মতো ডি নদী এখানে বিশাল ডেভিলস লেকের সঙ্গে সমুদ্রকে যুক্ত করেছে। গিনেসের রেকর্ডে ডি নদী একসময় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীর শিরোপা পেয়েছিল। মাত্র ৪৪০ ফুট লম্বা এ নদীর এই শিরোপা নিয়ে লড়াই বাঁধে মন্টানার সঙ্গে। চাপানউতোর এই পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, গিনেস তাদের নথিতে শিরোপাটারই অবলুপ্তি ঘটায়। এই ডি রিভার স্টেট রিক্রিয়েশন সাইট-এই অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ঘুড়ির উৎসব।

এ উৎসবের মূলত দুটো ভাগ। একটি হল সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে নানা মডেলের ঘুড়ি ওড়ানো। আর অন্যটি শুধু ঘুড়ি ওড়ানোর খেলায় মেতে উঠে আকাশের বুকে বিচিত্র বুনোটের নকশা তৈরি করা। সেইজন্য বিরাট বিচকে দুটো ভাগে ভেঙে ফেলা হয়েছে। দুটো বিশাল চতুর্ভুজ যাদের সীমানা করা হয়েছে পতাকা লাগানো নিচু দড়ি দিয়ে। দুয়ের মাঝে পনেরো ফুট চওড়া রাস্তা যার ওপর দিয়ে মানুষ চলে যেতে পারবে সমুদ্রের জল অব্দি। বড় রাস্তা আর বিচের মাঝে চওড়া ফুটপাথ যেখানে মঞ্চ করা হয়েছে, কিছু চেয়ার পাতা হয়েছে দর্শকদের জন্যে। মঞ্চ থেকে ঘোষণা চলছে, চলছে মিউজিক। কিছুটা উচ্চগ্রামের। ডেসিবেলের ঊর্ধ্বসীমা এখানে কত জানা নেই, তবে কান একটু কষ্টে পড়ছে। স্থানীয় মানুষ নানারকম খাবারের দোকান দিয়েছে। ক’টি স্যুভেনির শপ ঘুড়ি লাটাই, টিশার্ট, ম্যাগনেট এসব সাজিয়ে বসেছে। এই ফুটপাথের ধার থেকেই বিচের শুরু।
এক চতুর্ভুজে সাজানোর ঘুড়িরা উড়ছে। ঘুড়ি বলছি বটে, আসলে এরা হাওয়া ভরা বেলুনশ্রেণির। বিশালাকৃতি পাখি, অক্টোপাস, তিমি, আকাশে পতপত করে উড়ছে। দুরন্ত হাওয়ায় উড়ে যাওয়া আটকাতে এক-একটিকে প্রচণ্ড শক্ত নাইলন গোত্রের কিছুর দড়ি দিয়ে মাটিতে গাঁথা শক্ত খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ বেশ কয়েকটি দড়ি। নানা আকারের আর রঙের বেলুনরা এই যে হাওয়ায় একমুখী হয়ে ভেসে আকাশপানে চেয়ে আছে, তার বেশ একটা সাঙ্গীতিক ছন্দ আছে। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বর কিন্তু বিন্যাসের গুণে একত্রে মিলে সুরেলা হয়ে উঠেছে। বিরাট আকারের রঙিন কাঁকড়া বাঁধা রয়েছে বালির ওপরে। তাদের উঁচিয়ে থাকা গোল গোল চোখ দেখে বাচ্চাদের মজাও আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে। সেটা তাদের সোল্লাস চিৎকার আর লাফানোয় মালুম পড়ছে। তবে দড়ির সীমানা টপকে তাদের কাছে যাবার চেষ্টা কেউ করে না এখানে। একাধিক কাঁকড়ার দলের ওপর আকাশে ওড়া অক্টোপাসের শুঁড়ের লম্বা ছায়ারা নড়াচড়া করছে। চতুর্ভুজের কোনাগুলোকে সাজানো হয়েছে নানা আকারের আর রঙের নিশান দিয়ে। হাওয়ায় এ ওর গায়ে ঢলে পড়লে রঙিন আলোর বিস্ফোরণ হচ্ছে যেন। ‘রায়ট অফ কালারস’ বোধহয় একেই বলে।

অন্য চতুর্ভুজের চৌহদ্দিতে ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা চলছে। তবে মজা এইটাই যে, আমাদের ঘুড়ি ওড়ানোর ধারণার সঙ্গে এদের ঘুড়ি বা তার ওড়াউড়ির বিষয়টা একেবারেই মেলে না। এই ওড়ানোর ঘুড়িগুলো কিন্তু দ্বিমাত্রিক। প্রধানত দুটি আকারের। একটা প্রজাপতির আকার, অন্যটি প্রচলিত চৌকো অত্যন্ত লম্বা বাহারি লেজ সহ। তবে মাপে বিশাল। প্রজাপতিরা অন্তত ৬ থেকে ৮ ফুট চওড়া। অন্যটি কিছুটা ছোট। প্রত্যেক ঘুড়িতে অনেকগুলো সুতো লাগানো যেটা একজনের হাতে আছে একটা যন্ত্রে বাঁধা। ঘুড়িরা উড়ছে দলবদ্ধ হয়ে। দেখলাম একজন ওড়ালেন তিনটি ঘুড়ি। তার দুটির নিয়ন্ত্রণ দুই হাতে, অন্যটি করছেন কোমর দিয়ে। না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। তিনটি ঘুড়ি সমান্তরালভাবে উড়ছে ওপরে, তারপর হয়তো ডানদিকে বেঁকে একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরে মধ্যে এসে আবার বাঁদিকে ঘুরে আগের নকশাটা ফুটিয়ে তুলছে আকাশের গায়ে। এরকম অজস্র প্যাটার্ন তোলাটাই ঘুড়ির কাজ। তিন বা চারজনের দল যখন আসছে, তখনও একাধিক ঘুড়ির এই সিম্ফনি চলছে আকাশমঞ্চে। আর এর সবকিছুই হচ্ছে নির্দিষ্ট আবহসঙ্গীতের তালে তালে। এটাই নিয়ম।
একসময় আটজনের একটি দল এল। এরা কেউ কারও সঙ্গে আগে কোনও রিহার্সাল করেনি। একজন দলনেতার নাম ঘোষণা হল। ঘুড়ির জগতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক। তাইওয়ান আর ইটালিতে খেলা দেখিয়ে তিনি দুদিন আগে ফিরেছেন। তিনি মাইকে নির্দেশ দেবেন আর বাকিরা সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। নির্দেশ পালনের সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম। তাতে কী! এদের আছে ঘুড়ি ওড়ানোও একটা প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অধীত বিদ্যা। রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। তাই এই নির্দেশ দেওয়া আর মানার অভ্যাস এদের কাছে নতুন নয়।

সেই জোরেই পরের আধঘণ্টা সময় আটজন পাইলট (যিনি ওড়ান, তাঁকে এরা এই নামে ডাকে) আকাশের বুকে রাজ্যপাট বসিয়ে ফেললেন। আটটি ঘুড়ি একসঙ্গে ঊঠছে, নামছে; একবার সকলে মিলে একটা বৃত্ত বানিয়ে ফেলছে, পরক্ষণেই নিচের কোনও বিন্দু থেকে কোনাকুনি আটদিকে উঠে একটা বোকে বানিয়ে ফেলছে। আনুভূমিক চলনে চারটে ঘুড়ি ডান থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে, অন্য চারটি প্রথমগুলির ফাঁক দিয়ে দিয়ে উল্টোদিকে ধাবমান। ত্রিভুজের আকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে, তার পরক্ষণেই তারার মতো খসে পড়ছে নিচের দিকে। সবটাই যেহেতু হচ্ছে আবহসঙ্গীতের তালে তালে, তাই পুরো বিষয়টিকে একটা ব্যালে নৃত্যের থেকে কম কিছু মনে করা যাচ্ছে না।
দর্শকদের দৃষ্টি বিস্ফারিত। তারিফের অস্ফুট শব্দেরা, শিষ্ট হাততালির মৃদু আওয়াজ মিশে যাচ্ছে সমুদ্রের জলের আর হাওয়ার শব্দে। আমার নাতনির চঞ্চল পাদুটিও স্থির হয়ে গেছে।
বিকেল পৌনে চারটে বাজতে আসন্ন সমাপ্তির ঘোষণা হল মাইকে। পনেরো মিনিট পরে বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে রাখা বেলুন ঘুড়িরা নেমে গেল মাটিতে। তাদের পেটের ভেতরের হাওয়া শুষে নিল যন্ত্র। দ্বিমাত্রিক নাইলনের প্রজাপতি, অক্টোপাস আর তিমিরা পাট পাট হয়ে ঢুকে পড়ল যে যার ব্যাগে। নিমেষে দড়ি, নিশান, খুঁটিরা বাক্সবন্দি হল। বিরাটকায় মিউজিক সিস্টেম চলে গেল ক্যারিয়ার ট্রাকের পেটে। ঘুড়ি ওড়ানোর সংরক্ষিত চতুর্ভুজ ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গেছে। পাইলটরা তাঁদের বাক্স গুছিয়ে নিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুজ পমেটমের মুখোশ চিরে বেরিয়ে এল সাগরবেলার চিরাচরিত মুখ আর অবয়ব। বস্তুত, আধ ঘণ্টা বাদে ফেলুদা এলেও বুঝতে পারতেন না এখানে কোনও মেলা হয়েছে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ইতিউতি ঘুরে যখন গাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি, তখন স্মৃতির চোরকাঁটা পায়ের কাপড়ে টান দিল। চোখ বুজে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আট বছরের নন্দ আর ওর ছয় বছরের ভাই আমাদের বাড়ির পাশের মাঠের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে। নন্দর হাতে গোলাপী রঙের মাঞ্জাসুতো জড়ানো লাটাই। আর ভাই মাথায় করে নিয়ে চলেছে একটা ঘুড়ি। বনবাদাড় টপকানো জীবনপণ দৌড় শেষে প্রভাতদের বাড়ির আগাছা ভরা পাঁচিলে আটকে থাকা ঘুড়িটা লুটতে ঝুঁকি নিতে হয়েছিল খুব। কারণ ওটার জন্যে দৌড়েছিল লম্বু হরেন। শেষে ওর বগলের তলা দিয়ে ডজ করে ওরা বেরিয়ে এসেছে ঘুড়ি নিয়ে। কোনায় একটু ছিঁড়ে গেলেও গদের আঠা দিয়ে জুড়ে কান্নিকটা একটু ঠিক করে নিলে আর একবার ওড়ানো যাবে। এটা একটা পেটকাটি চাঁদিয়াল। ওদের বাড়ির তিনটে বাড়ির পরের ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়ায় দীপেনরা। ওদের ওপর খুব রাগ নন্দর। একদিন পেয়ারা ভাগ করা নিয়ে কথা কাটাকাটিতে দীপেন ওকে বলেছিল, তোরা ভদ্দরলোক নাকি! তোর বাবা তো…। আজ নিজেদের ছাদে উঠে ঘুড়িটা দেবে চোদ্দো বছরের জ্যার্তুতো দাদা হেমন্তকে। হেমন্তদা দারুণ ঘুড়ি ওড়ায়। শুধু একটা ওপর চাপ্পা, দীপেনরা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে!
সবিতার মন ওড়ে বিকাশের জন্যে। ওর ভাইয়ের ঘুড়ির সঙ্গে সেও উড়ে যায় সবাইকার চোখ এড়িয়ে, নিষেধ ছাড়িয়ে বিকাশদের ছাদের মাথায়। বিকাশের ঘুড়ির সুতো গোঁত খেয়ে নেমে যখন ওর সুতোয় জড়ায়, তখন সবিতা অন্য এক আলিঙ্গনের কল্পনার পাখা উড়িয়ে দেয় আকাশপথে। আকাশের গায়ে কান পেতেই শোনে ওর কথা।
ঘুড়ির সুতোয় জড়ানো ছেলেবেলায় টান পড়ে। সে টান দেবার ক্ষমতা কোনও কর্পোরেট কাইট ফেস্টিভ্যালের নেই।