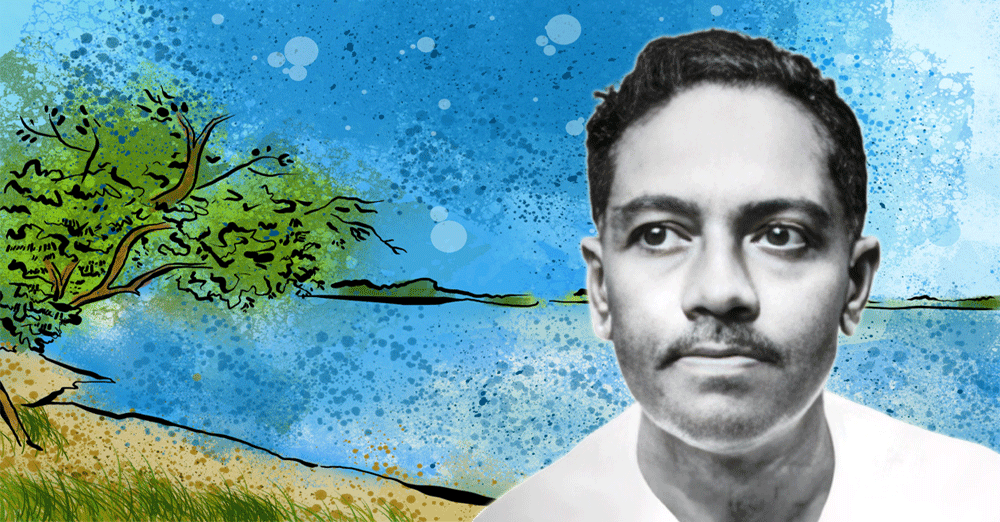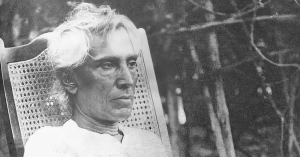হেমন্ত প্রিয় ঋতু ছিল তাঁর। অজস্র কবিতায় তিনি হেমন্তের ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতি, ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বৈভবপূর্ণ। কিন্তু হেমন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে ততটা ধরা দেয়নি, যা জীবনানন্দে দিয়েছে। মহাকবি কালিদাসের ‘ঋতুসংহার’ কাব্যেও হেমন্তের বিশদ বর্ণনা আছে। তবে কাব্যটি প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর আবেগ ও গান্ধর্ব-আশ্রয়ী। সেজন্য ঋতু ও প্রেমের সংযোগ লক্ষ্য করি সেখানে। তবু হেমন্তকালকে কালিদাস চিহ্নিত করেন ‘চিরসন্তাপের ঋতু’ বলে। ক্রৌঞ্চের ডাক, বিরহী প্রিয়ার জন্য দীর্ঘশ্বাস এ-ঋতুর চিহ্ন। আর হ্যাঁ, খেতভরা ধানের কথাও লিখে গেছেন তিনি।
রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দেখছি, বনবাসকালে গোদাবরীতে স্নান করার সময় লক্ষ্মণ রামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, রামের প্রিয়তম ঋতু শরৎ সমাগত। নীহারে জর্জরিত প্রকৃতি, মধ্যাহ্নে সুখসেব্য রোদ্দুর, দক্ষিণায়ণের সূচনাকাল। রাতে তুষার, বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য।
হেমন্তের বৈভব ও বৈশিষ্ট্য দেশি-বিদেশি বহু কবির রচনায় মেলে। শেকসপিয়রের সনেট থেকে (বিশেষ করে ৭৩-সংখ্যক) গ্যেটের কবিতায়। গ্যেটের একটি বিখ্যাত কবিতা ‘Herbstgefuhi (Autumn Feelings)। কবিতাটিতে বিষাদ ও রিক্ততা হাত ধরাধরি করে আছে। আবার জীবনের নশ্বরতা ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের কথা আছে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতে, যা বহুসময় হেমন্তের আবহ নিয়ে আসে বলে সমালোচকেরা মনে করেন।
গৌতম বুদ্ধের জীবনী-গণনাকারীরা তাঁর গৃহত্যাগের ভবিষ্যদ্বাণী করলে পিতা শুদ্ধোধন তাঁকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত করতে চেয়ে অন্য নানা আয়োজনের মতো ছয় ঋতুর উপযোগী ছ’টি প্রসাদ নির্মাণ করে দেন। সেখানেও হেমন্তের বর্ণনা আছে।
তবু হেমন্তকাল ও জীবনানন্দ অভিন্ন, ওতপ্রোত ও পরস্পর পরিপূরক। তাঁর কবিতায় বারবার নানা অনুষঙ্গে, বিভঙ্গে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হেমন্তের বসতি যেন। ‘হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু/ শিশিরের জল’, ‘ধানক্ষেতে, মাঠে,/ জমিছে ধোঁয়াটে/ ধারালো কুয়াশা’! কুয়াশা আর শিশির, এই দুই অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হেমন্তের, চিনিয়ে দেন তিনি। ‘চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল/ তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল’, হেমন্তকে বাহন করে এই যে প্রকৃতির অপরূপতা মেলে ধরা, তা অন্য কোন বাঙালি কবির আছে? অথচ বৈষ্ণব কবি থেকে শুরু করে আজকের কবিরা অনেকেই এই প্রায়-অননুভূত ঋতুকে নিয়ে কবিতা লিখতে ছাড়েননি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তো লিখেই ফেললেন ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ কাব্যগ্রন্থ! না, তিনি কিন্তু পোস্টম্যান নন সেখানে। কেবল এক পোস্টম্যানকে ‘দেখেছেন’ মাত্র!
জীবনানন্দের একই বয়সী কাজী নজরুল। হেমন্তের কবিতা ও গানে মুখর তিনিও। তবু হেমন্ত বন্দনায়, হেমন্তের রূপনির্মাণে মেরুপ্রতিম ব্যবধান দু’জনের মধ্যে। নজরুলেও আমন ধান, শিশিরস্নাত শীতল বাতাস, তারপর ‘ঝিলের জলে কাঁচা রোদের মানিক’, আছে। হেমন্তের খাদ্য নিয়েও কৌতুক তাঁর কবিতায়, ‘শিরনি রাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত!’ তার পাশে জীবনানন্দ, ‘সেইখানে উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে/ হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল, রাঙা/ চুপে চুপে ডুবে যায় জ্যোৎস্নায়/ পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা/ চেয়ে দেখে/ সোনার বলের মতো সূর্য আর/ রূপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা’ (গোধূলিসন্ধির নৃত্য)।
জসীম উদ্দীন বা সুধীন্দ্রনাথ নন, হেমন্তের এক ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর জীবনানন্দ। ‘কলমীলতায় দোলন লেগেছে, ফুরালো ফুলের আয়ু’ (জসীমউদ্দিন), বা ‘ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্ত-লোহিত/ তরুণ তরুণী-শূন্য বনবীথি চ্যুতপত্রে ঢাকা’ (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)-র সঙ্গে তুলনা করা যাক ‘মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায়/ কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে’, অথবা ‘আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি/ বিকেলের এই রং, রোদের শূন্যতা,/ রোদের নরম রোম, ঢালু মাটি,/ বিবর্ণ বাদামী পাখি/ হলুদ বিচালি/ পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে ঘাসে/ কুড়ানীর মুখে তাই নাই কোনো কথা’! আমরাও কথাহারা এসব দৈবী উচ্চারণে!
কেবল বিভূতিভূষণ। একমাত্র তাঁর লেখাকেই, হেমন্তভাবনাকেই জীবনানন্দের পাশে দাঁড় করানো যায়। ‘ছেলেবেলার সেই প্রথম হেমন্তকালে, আমাদের গ্রামের উত্তর-দক্ষিণ মাঠে যখন আস্তে আস্তে সোনালী রং ধরছে আর অচিন তলার পাকা রাস্তায় ছাতিমফুলের উগ্র গন্ধে বাতাস হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত, বিকেল ফুরিয়ে আসছে স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতেই, পশ্চিম আকাশে আবির ঢালা মন খারাপ করার পাশে সন্ধ্যাতারার টিপটি পরা আকাশপট!’
হেমন্তের সঙ্গে পরানের রাখী বাঁধা ছিল বলেই কি শরতে আহত হয়ে (১৪-ই অক্টোবর ১৯৫০-এ ট্রাম-অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাঁর), হেমন্তে নির্বাণ নেবেন বলেই ২২-এ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন কবি? জীবনানন্দ, এই নামে আর কোনও বাঙালির নাম নেই। সম্ভবত তাঁর মতো হেমন্তপ্রেমিক না থাকাই তার কারণ।
চিত্রণ: চিন্ময় মুখোপাধ্যায়